নুসরাত জাহান

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যেন একটি বেনারসি শাড়ির আঁচল, যার এক প্রান্তে সোনালি জরির কাজ আর অন্য প্রান্তে গলিত সুতোয় দাগ পড়া দারিদ্র্যের ছাপ। একই চাদরে ঢাকা দুটি পৃথিবী, যার একটি অস্তিত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং অন্যটি বিলাসিতায় গা ভাসানোর মতো। একদিকে বৈভবের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে প্রয়োজনের হাহাকার।
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা স্বাধীনতার অর্ধশতক পরেও যেন শুধু একটি শহর নয়, একটি অদৃশ্য শ্রেণিবৈষম্যের চিত্রপট। এই শহরের এক কোণে যেমন দামি অ্যাপার্টমেন্ট, চকচকে গাড়ি, বিলাসবহুল ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে গড়ে ওঠা ধনীদের রাজত্ব, অন্য কোণে স্যাঁতসেঁতে ঘর, কাদামাখা রাস্তা, টিনের চালার নিচে গড়ে ওঠা দরিদ্রদের জীবনসংগ্রাম। এখানে যেমন রয়েছে গুলশান-বনানীর ঝলমলে আলো, তেমনই রয়েছে মিরপুর, কড়াইল ও রায়েরবাজারের বস্তির অন্ধকার দিক। এই দ্বৈত রূপই যেন ঢাকাকে বিভক্ত করে ফেলেছে দুই ভাগে—বস্তি আর বিলাসবহুলতায়।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ঢাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ বস্তিতে বাস করে। ২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকার বস্তিবাসীদের অধিকাংশই দৈনিক আয় করেন ২০০-৩০০ টাকা। তারা পায় না নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষার ন্যূনতম সুবিধা। অপরদিকে বিলাসবহুল এলাকায় একজন মানুষের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ হয়তো এক রাতের ডিনারে পাঁচ হাজার টাকার বেশি। এই ফারাক শুধু সংখ্যায় নয়, এটি এক নির্মম বাস্তবতা।
রাজধানীর অদৃশ্য বৈষম্যের কারণ কী?
বাংলাদেশের রাজধানীর অদৃশ্য বৈষম্যের অন্যতম কারণ শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বারবার উপেক্ষিত হওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী। জীবন নির্বাহের জন্য পুরো উপার্জনের টাকা চলে যায় পেট ভরতে, আর মাথা গোঁজার ভাড়া দিতে। তাই বাধ্য হয়ে অল্প টাকায় থাকার জন্য ঠাঁই নিতে হচ্ছে বস্তিতে। আবার বস্তিতে বাস করেও জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। প্রতিবছর বিভিন্ন কারণে বস্তিতে আগুন লেগে যায়। এই আগুন লাগার অন্যতম কারণ প্রভাবশালীদের দ্বারা অবৈধভাবে বস্তির জমি দখলের চেষ্টা। সীমিত সুযোগ-সুবিধা, নিম্ন শিক্ষার হার ও কর্মসংস্থানের অভাবে দরিদ্ররা শহরের কেন্দ্রে অবস্থান করেও থেকে যায় উন্নয়নের বাইরে, যা অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল কারণ।
ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের অবসান কোথায়?
ধনী-গরিবের বৈষম্যের অবসান করতে হলে ঢাকার উন্নয়ন হতে হবে সমতা ও অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে। বস্তির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করে পুনর্বাসনের প্রকল্প গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার যদি বস্তিবাসীদের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর আবাসনের ব্যবস্থা করে, তবে তারা উন্নয়নের আওতাভুক্ত হতে পারবে। বস্তিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নগর ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। সমাজের উচ্চ শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এবং নিম্ন শ্রেণিকে উন্নয়নের আওতায় আনতে জনসচেতনতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করতে হবে।
ঢাকা শহরের এই বিভক্ত চিত্র শুধু গঠনগত বৈষম্য নয়, একটি মনোভাবগত সংকটও। ‘নিজে ভালো আছি’ বলে অন্যের দিকে অবহেলার দৃষ্টি দেওয়ার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। দরিদ্র মানুষ সমাজের বোঝা নয়, তারা সমাজের অবহেলিত শ্রেণি। বস্তিতে বসবাস করা প্রতিটি ব্যক্তি লড়াই করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। শহরের সৌন্দর্য তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন গুলশান-বনানীর শিশিরভেজা ভোর একদিন কড়াইল বস্তির শিশুটির চোখেও এক নতুন সম্ভাবনার আলো হয়ে ধরা দেবে।
আমাদের রাজধানীকে সবার জন্য বসবাসযোগ্য করে তুলতে হবে। অন্যথায় এই বিভক্ত ঢাকা আমাদের ফিরিয়ে দেবে বিভাজন, বিষণ্নতা আর বঞ্চনা।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যেন একটি বেনারসি শাড়ির আঁচল, যার এক প্রান্তে সোনালি জরির কাজ আর অন্য প্রান্তে গলিত সুতোয় দাগ পড়া দারিদ্র্যের ছাপ। একই চাদরে ঢাকা দুটি পৃথিবী, যার একটি অস্তিত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং অন্যটি বিলাসিতায় গা ভাসানোর মতো। একদিকে বৈভবের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে প্রয়োজনের হাহাকার।
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা স্বাধীনতার অর্ধশতক পরেও যেন শুধু একটি শহর নয়, একটি অদৃশ্য শ্রেণিবৈষম্যের চিত্রপট। এই শহরের এক কোণে যেমন দামি অ্যাপার্টমেন্ট, চকচকে গাড়ি, বিলাসবহুল ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে গড়ে ওঠা ধনীদের রাজত্ব, অন্য কোণে স্যাঁতসেঁতে ঘর, কাদামাখা রাস্তা, টিনের চালার নিচে গড়ে ওঠা দরিদ্রদের জীবনসংগ্রাম। এখানে যেমন রয়েছে গুলশান-বনানীর ঝলমলে আলো, তেমনই রয়েছে মিরপুর, কড়াইল ও রায়েরবাজারের বস্তির অন্ধকার দিক। এই দ্বৈত রূপই যেন ঢাকাকে বিভক্ত করে ফেলেছে দুই ভাগে—বস্তি আর বিলাসবহুলতায়।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ঢাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ বস্তিতে বাস করে। ২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ঢাকার বস্তিবাসীদের অধিকাংশই দৈনিক আয় করেন ২০০-৩০০ টাকা। তারা পায় না নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষার ন্যূনতম সুবিধা। অপরদিকে বিলাসবহুল এলাকায় একজন মানুষের দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ হয়তো এক রাতের ডিনারে পাঁচ হাজার টাকার বেশি। এই ফারাক শুধু সংখ্যায় নয়, এটি এক নির্মম বাস্তবতা।
রাজধানীর অদৃশ্য বৈষম্যের কারণ কী?
বাংলাদেশের রাজধানীর অদৃশ্য বৈষম্যের অন্যতম কারণ শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বারবার উপেক্ষিত হওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠী। জীবন নির্বাহের জন্য পুরো উপার্জনের টাকা চলে যায় পেট ভরতে, আর মাথা গোঁজার ভাড়া দিতে। তাই বাধ্য হয়ে অল্প টাকায় থাকার জন্য ঠাঁই নিতে হচ্ছে বস্তিতে। আবার বস্তিতে বাস করেও জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। প্রতিবছর বিভিন্ন কারণে বস্তিতে আগুন লেগে যায়। এই আগুন লাগার অন্যতম কারণ প্রভাবশালীদের দ্বারা অবৈধভাবে বস্তির জমি দখলের চেষ্টা। সীমিত সুযোগ-সুবিধা, নিম্ন শিক্ষার হার ও কর্মসংস্থানের অভাবে দরিদ্ররা শহরের কেন্দ্রে অবস্থান করেও থেকে যায় উন্নয়নের বাইরে, যা অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূল কারণ।
ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের অবসান কোথায়?
ধনী-গরিবের বৈষম্যের অবসান করতে হলে ঢাকার উন্নয়ন হতে হবে সমতা ও অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে। বস্তির উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করে পুনর্বাসনের প্রকল্প গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার যদি বস্তিবাসীদের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর আবাসনের ব্যবস্থা করে, তবে তারা উন্নয়নের আওতাভুক্ত হতে পারবে। বস্তিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নগর ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। সমাজের উচ্চ শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এবং নিম্ন শ্রেণিকে উন্নয়নের আওতায় আনতে জনসচেতনতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করতে হবে।
ঢাকা শহরের এই বিভক্ত চিত্র শুধু গঠনগত বৈষম্য নয়, একটি মনোভাবগত সংকটও। ‘নিজে ভালো আছি’ বলে অন্যের দিকে অবহেলার দৃষ্টি দেওয়ার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। দরিদ্র মানুষ সমাজের বোঝা নয়, তারা সমাজের অবহেলিত শ্রেণি। বস্তিতে বসবাস করা প্রতিটি ব্যক্তি লড়াই করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। শহরের সৌন্দর্য তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন গুলশান-বনানীর শিশিরভেজা ভোর একদিন কড়াইল বস্তির শিশুটির চোখেও এক নতুন সম্ভাবনার আলো হয়ে ধরা দেবে।
আমাদের রাজধানীকে সবার জন্য বসবাসযোগ্য করে তুলতে হবে। অন্যথায় এই বিভক্ত ঢাকা আমাদের ফিরিয়ে দেবে বিভাজন, বিষণ্নতা আর বঞ্চনা।

আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই
১৪ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভোগ নিরসনে এসে নিজেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর
১৪ ঘণ্টা আগে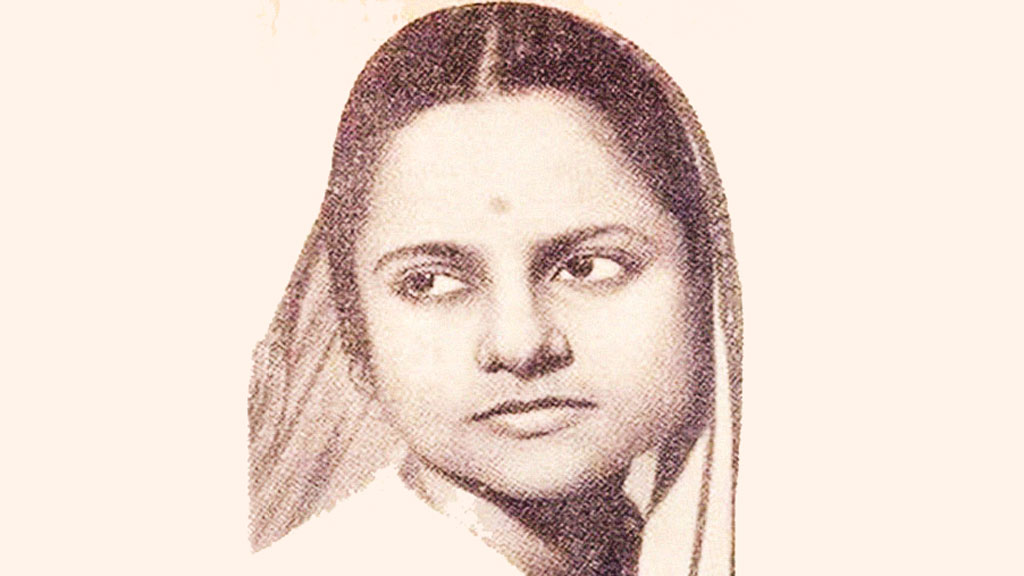
মীরা দেববর্মন ছিলেন বাংলা গানের এক অসামান্য গীতিকার, যিনি কৃতী স্বামী এবং সন্তানের নামের আড়ালে ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছেন আপন সৃষ্টির কারণেই। অনেকের হয়তো জানা নেই, আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি প্রয়াত শচীন দেববর্মনের স্ত্রী এবং উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তি সুরকার রাহুল দেববর্মনের মাতা মীরা দেববর্মন অসংখ্য জন
১৫ ঘণ্টা আগে
না, বারনই নদ বাঁচানোর কোনো মোক্ষম উপায় আমাদের জানা আছে, এ রকম কথা বলব না। যে নদকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’, সে নদই এখন মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালের ভাষায় বলা যায়, নদটি এখন আইসিইউতে। যেকোনো সময় আসতে পারে তার মৃত্যুসংবাদ।
১৫ ঘণ্টা আগেসেলিম জাহান

আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই ঘটেছে অধিকৃত ফিলিস্তিনে। ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছর বিশ্বব্যাপী শিশু নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ২৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। এর মধ্যে শিশু ধর্ষণ এবং শিশুদের অন্য রকমের যৌন নির্যাতন ৩৪ শতাংশ বেড়ে গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও নিত্যদিন ছেলেশিশুদের তুলনায় মেয়েশিশুরাই নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার বেশি হয়।
যুক্তরাজ্যে প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন নিপীড়ন বা নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। নাইজেরিয়ায় প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ছয়জন কোনো না কোনোভাবে নির্যাতিত হয়েছে। বৈশ্বিকভাবে, ১৫-১৯ বছরের কিশোরীদের মধ্যে দেড় কোটি কিশোরী তাদের জীবনকালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে।
বাংলাদেশেও শিশু নিপীড়ন ও নির্যাতন একটি আশঙ্কাজনক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দুটি সমীক্ষা এবং সেই সঙ্গে ‘বাংলাদেশের পোশাককর্মীদের শিশুসন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কৌশলসমূহ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় একটি আশঙ্কাজনক চিত্র বেরিয়ে আসে।
আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সমীক্ষা অনুসারে, এ বছরের গত ৯ মাসে ৩৫৯ জন মেয়েশিশু ধর্ষিত হয়েছে, যে সংখ্যা ২০২৪ সালের সারা বছরের মোট সংখ্যার বেশি। এর মধ্যে মাত্র ৩০০ ঘটনা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয়েছে। তার মানে, ৫৯টি ঘটনার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। যারা ধর্ষিত হয়েছে, তাদের বয়সের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। নির্যাতিত মেয়েশিশুদের মধ্যে ৪৯ জনের বয়স ৬ বছরের কম, ৯৪ জনের বয়স ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে এবং ১০৩ জনের বয়স ১৩-১৯ বছর। ১৩৯টি মেয়েশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সময়কালে ৭ থেকে ১২ বছরের ৩০ জন ছেলে ধর্ষিত হয়েছে। যার মধ্যে ২০টি ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সমীক্ষার উপাত্তগুলো নেওয়া হয়েছে দেশের ১৪টি জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে। এ সমীক্ষা অনুসারে, শুধু গত সেপ্টেম্বরে সারা দেশে ৯২ জন মেয়েশিশু নানান রকমের নিপীড়ন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ২৮টি ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। পোশাককর্মীদের সন্তানদের নিরাপত্তা বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বলা হয়েছে, দেশের ১০ জন মেয়েশিশুর মধ্যে ৯ জনই নানান রকমের শারীরিক শাস্তি বা নিপীড়নের শিকার হয়। সেই সঙ্গে এটাও উঠে এসেছে যে ২০২৪ সালের তুলনায় এ বছর নারী নিপীড়নের ঘটনা তিন-চতুর্থাংশ বেড়ে গেছে। সারা দেশে শিশুদের জন্য গঠিত আদালতগুলোতে ২৩ হাজার মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।
যদিও উপর্যুক্ত তিনটি গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা-প্রণালির মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এর প্রতিটিই কতগুলো আশঙ্কাজনক প্রবণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রথমত, শিশুদের নির্যাতন নানানভাবে হতে পারে—শারীরিক শাস্তি থেকে মানসিক নির্যাতন, এমনকি যৌন হয়রানি কিংবা ধর্ষণও। দ্বিতীয়ত, সব বয়সের শিশুরা নির্যাতিত হতে পারে, এমনকি একেবারে ছোট্ট শিশুও। তৃতীয়ত, নিজ গৃহ কিংবা নিজ বিদ্যালয় বা মাদ্রাসাও শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থান নয়। কারণ, বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নির্যাতিত শিশুদের নিকটাত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী কিংবা শিক্ষক। চতুর্থত, নানান সময়ই ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক মানসিকতা, প্রতিবন্ধকতা, পারিবারিক চাপ কিংবা অনিরাপত্তার আশঙ্কার কারণে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উপস্থাপিত হয় না। পঞ্চমত, শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার সমাধান করতে দেশের বিচারব্যবস্থা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শিশু নির্যাতন বিষয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থায় রাশি রাশি জমে ওঠা অনিষ্পন্ন মামলাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।
এসব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়—এক. শিশুদের, বিশেষত মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কেন বাড়ছে এবং দুই. এটা প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে। প্রথম প্রশ্নটির কোনো সোজা জবাব নেই। বুঝতে হবে, যেখানে অতি ছোট শিশুদেরও এ রকম হীন অপরাধ থেকে রেহাই দেওয়া হয় না, সেখানে সমাজে একটি গভীর নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পচন ঘটছে। কারা এসব অপরাধে অপরাধী এবং কী কারণ তাদের এমন জঘন্য অপরাধে উদ্বুদ্ধ করে?
মেয়েশিশুদের প্রতি সহিংসতার পেছনে থাকে চরম বিষাক্ত পুরুষতান্ত্রিকতা, যেটা প্রায়ই পুরুষ আরোপিত অবদমন এবং আক্রমণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সমাজে কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণে অবদমিত যৌনতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ-জাতীয় অবদমনও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অন্যতম কারণ হতে পারে। বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি মাধ্যমগুলোতে পর্নোগ্রাফিসহ নানা রকমের অশ্লীল বিষয়বস্তু এখন বিস্তৃতভাবে লভ্য। এগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ছেলেদের মনোজগতে মেয়েদের ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক, অসুস্থ বিকৃত মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উপাত্ত এটাও দেখাচ্ছে যে নারীর বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধে অপরাধীদের বয়সকাল ১৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সেই সঙ্গে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এবং ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের ক্রমাগত সাফল্য এবং অর্জন ছেলেদের মনে একটি নিরাপত্তাহীনতা ও হীনম্মন্যতার জন্ম দিচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতার এই পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের হতাশা এবং জীবনের ব্যর্থতা। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের ঘৃণা আর সহিংসতার মাধ্যমে।
প্রশ্ন হচ্ছে, এ চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে কী কী করা যেতে পারে। এর জন্য একটি সার্বিক এবং সর্বাত্মক ব্যবস্থাকাঠামো প্রয়োজন, যার মধ্যে আইনগত, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রম থাকবে। আইনগত দিক থেকে তদন্ত এবং বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমান স্থিত দীর্ঘসূত্রতার অবসান হওয়া একান্ত দরকার। তার জন্য যারা সহিংসতার শিকার এবং যারা ঘটনার সাক্ষী, তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন যথাযথভাবে বলবৎ করতে হবে। নানান সময়ে কলঙ্ক এবং সামাজিক লজ্জার ভয়ে বহু যৌন নির্যাতনের ঘটনা উদ্ঘাটিত হয় না, সেগুলো সম্পর্কে অভিযোগও করা হয় না। ফলে যথাযথ ন্যায্য বিচার বিঘ্নিত হয়। সুতরাং এ বিষয়গুলো পরিবার, বিদ্যালয়, মাদ্রাসার মতো সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় খোলাখুলিভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। ধর্মীয় নেতারা, সমাজে বিজ্ঞজনেরা যাঁরা আমাদের পথপ্রদর্শক এবং সংবাদমাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করছেন যাঁরা, তাঁরা এসব ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি সবল ভূমিকা রাখতে পারেন।
আনুষ্ঠানিকভাবে একটি অভিযোগ করার পরে বিচারের প্রক্রিয়াকে নষ্ট করার জন্য অপরাধী যাতে রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা চাপ প্রয়োগ করতে না পারে, তার জন্য একটি কাঠামো প্রতিস্থাপন অত্যন্ত জরুরি। যদিও শিশু নির্যাতন রোধের আইনগত কাঠামোর মধ্যে তদন্ত ও মামলার নিষ্পত্তির জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, তবু সেসব ব্যাপারে আইনগত অস্পষ্টতা, নির্যাতিত নারীদের বয়ঃসীমা সম্পর্কে বিতর্ক, তদন্ত ফলাফলের অসংগতি সুষ্ঠু বিচারপ্রক্রিয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এসবের নিরসন প্রয়োজন। অপরাধ করেও আইনগত ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে পড়ার সংস্কৃতিকেও রোধ করতে হবে।
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পারিবারিক উপদেশ ও নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোট থাকতেই শিশুদের ব্যক্তিগত সীমারেখা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে কোন স্পর্শটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয়। এগুলো লঙ্ঘিত হলে কীভাবে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে শিশু নিরাপত্তা পর্ষদ গঠন করলেও তৃণমূল পর্যায়ে শিশু নির্যাতন চিহ্নিতকরণ এবং তার প্রতিকার করার সুযোগ তৈরি করা যায়। পর্নোগ্রাফি এবং ক্ষতিকর তথ্যপ্রযুক্তি থেকে শিশুদের রক্ষা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।
চূড়ান্ত বিচারে, পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমন্বিত কাজের মাধ্যমে শিশুদের, বিশেষত মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে।
লেখক: সেলিম জাহান
ভূতপূর্ব পরিচালক, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই ঘটেছে অধিকৃত ফিলিস্তিনে। ২০২৩ সালের তুলনায় গত বছর বিশ্বব্যাপী শিশু নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ২৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। এর মধ্যে শিশু ধর্ষণ এবং শিশুদের অন্য রকমের যৌন নির্যাতন ৩৪ শতাংশ বেড়ে গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও নিত্যদিন ছেলেশিশুদের তুলনায় মেয়েশিশুরাই নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার বেশি হয়।
যুক্তরাজ্যে প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন নিপীড়ন বা নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। নাইজেরিয়ায় প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ছয়জন কোনো না কোনোভাবে নির্যাতিত হয়েছে। বৈশ্বিকভাবে, ১৫-১৯ বছরের কিশোরীদের মধ্যে দেড় কোটি কিশোরী তাদের জীবনকালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে।
বাংলাদেশেও শিশু নিপীড়ন ও নির্যাতন একটি আশঙ্কাজনক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দুটি সমীক্ষা এবং সেই সঙ্গে ‘বাংলাদেশের পোশাককর্মীদের শিশুসন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কৌশলসমূহ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় একটি আশঙ্কাজনক চিত্র বেরিয়ে আসে।
আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সমীক্ষা অনুসারে, এ বছরের গত ৯ মাসে ৩৫৯ জন মেয়েশিশু ধর্ষিত হয়েছে, যে সংখ্যা ২০২৪ সালের সারা বছরের মোট সংখ্যার বেশি। এর মধ্যে মাত্র ৩০০ ঘটনা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয়েছে। তার মানে, ৫৯টি ঘটনার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। যারা ধর্ষিত হয়েছে, তাদের বয়সের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। নির্যাতিত মেয়েশিশুদের মধ্যে ৪৯ জনের বয়স ৬ বছরের কম, ৯৪ জনের বয়স ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে এবং ১০৩ জনের বয়স ১৩-১৯ বছর। ১৩৯টি মেয়েশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সময়কালে ৭ থেকে ১২ বছরের ৩০ জন ছেলে ধর্ষিত হয়েছে। যার মধ্যে ২০টি ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সমীক্ষার উপাত্তগুলো নেওয়া হয়েছে দেশের ১৪টি জাতীয় পর্যায়ের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে। এ সমীক্ষা অনুসারে, শুধু গত সেপ্টেম্বরে সারা দেশে ৯২ জন মেয়েশিশু নানান রকমের নিপীড়ন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ২৮টি ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। পোশাককর্মীদের সন্তানদের নিরাপত্তা বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বলা হয়েছে, দেশের ১০ জন মেয়েশিশুর মধ্যে ৯ জনই নানান রকমের শারীরিক শাস্তি বা নিপীড়নের শিকার হয়। সেই সঙ্গে এটাও উঠে এসেছে যে ২০২৪ সালের তুলনায় এ বছর নারী নিপীড়নের ঘটনা তিন-চতুর্থাংশ বেড়ে গেছে। সারা দেশে শিশুদের জন্য গঠিত আদালতগুলোতে ২৩ হাজার মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।
যদিও উপর্যুক্ত তিনটি গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা-প্রণালির মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এর প্রতিটিই কতগুলো আশঙ্কাজনক প্রবণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রথমত, শিশুদের নির্যাতন নানানভাবে হতে পারে—শারীরিক শাস্তি থেকে মানসিক নির্যাতন, এমনকি যৌন হয়রানি কিংবা ধর্ষণও। দ্বিতীয়ত, সব বয়সের শিশুরা নির্যাতিত হতে পারে, এমনকি একেবারে ছোট্ট শিশুও। তৃতীয়ত, নিজ গৃহ কিংবা নিজ বিদ্যালয় বা মাদ্রাসাও শিশুদের জন্য নিরাপদ স্থান নয়। কারণ, বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নির্যাতিত শিশুদের নিকটাত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী কিংবা শিক্ষক। চতুর্থত, নানান সময়ই ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক মানসিকতা, প্রতিবন্ধকতা, পারিবারিক চাপ কিংবা অনিরাপত্তার আশঙ্কার কারণে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উপস্থাপিত হয় না। পঞ্চমত, শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার সমাধান করতে দেশের বিচারব্যবস্থা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শিশু নির্যাতন বিষয়ে আমাদের বিচারব্যবস্থায় রাশি রাশি জমে ওঠা অনিষ্পন্ন মামলাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।
এসব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়—এক. শিশুদের, বিশেষত মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কেন বাড়ছে এবং দুই. এটা প্রতিরোধে কী করা যেতে পারে। প্রথম প্রশ্নটির কোনো সোজা জবাব নেই। বুঝতে হবে, যেখানে অতি ছোট শিশুদেরও এ রকম হীন অপরাধ থেকে রেহাই দেওয়া হয় না, সেখানে সমাজে একটি গভীর নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পচন ঘটছে। কারা এসব অপরাধে অপরাধী এবং কী কারণ তাদের এমন জঘন্য অপরাধে উদ্বুদ্ধ করে?
মেয়েশিশুদের প্রতি সহিংসতার পেছনে থাকে চরম বিষাক্ত পুরুষতান্ত্রিকতা, যেটা প্রায়ই পুরুষ আরোপিত অবদমন এবং আক্রমণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সমাজে কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণে অবদমিত যৌনতার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ-জাতীয় অবদমনও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অন্যতম কারণ হতে পারে। বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি মাধ্যমগুলোতে পর্নোগ্রাফিসহ নানা রকমের অশ্লীল বিষয়বস্তু এখন বিস্তৃতভাবে লভ্য। এগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ছেলেদের মনোজগতে মেয়েদের ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক, অসুস্থ বিকৃত মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উপাত্ত এটাও দেখাচ্ছে যে নারীর বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধে অপরাধীদের বয়সকাল ১৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সেই সঙ্গে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এবং ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের ক্রমাগত সাফল্য এবং অর্জন ছেলেদের মনে একটি নিরাপত্তাহীনতা ও হীনম্মন্যতার জন্ম দিচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতার এই পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের হতাশা এবং জীবনের ব্যর্থতা। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের ঘৃণা আর সহিংসতার মাধ্যমে।
প্রশ্ন হচ্ছে, এ চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে কী কী করা যেতে পারে। এর জন্য একটি সার্বিক এবং সর্বাত্মক ব্যবস্থাকাঠামো প্রয়োজন, যার মধ্যে আইনগত, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কার্যক্রম থাকবে। আইনগত দিক থেকে তদন্ত এবং বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমান স্থিত দীর্ঘসূত্রতার অবসান হওয়া একান্ত দরকার। তার জন্য যারা সহিংসতার শিকার এবং যারা ঘটনার সাক্ষী, তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন যথাযথভাবে বলবৎ করতে হবে। নানান সময়ে কলঙ্ক এবং সামাজিক লজ্জার ভয়ে বহু যৌন নির্যাতনের ঘটনা উদ্ঘাটিত হয় না, সেগুলো সম্পর্কে অভিযোগও করা হয় না। ফলে যথাযথ ন্যায্য বিচার বিঘ্নিত হয়। সুতরাং এ বিষয়গুলো পরিবার, বিদ্যালয়, মাদ্রাসার মতো সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় খোলাখুলিভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। ধর্মীয় নেতারা, সমাজে বিজ্ঞজনেরা যাঁরা আমাদের পথপ্রদর্শক এবং সংবাদমাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করছেন যাঁরা, তাঁরা এসব ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি সবল ভূমিকা রাখতে পারেন।
আনুষ্ঠানিকভাবে একটি অভিযোগ করার পরে বিচারের প্রক্রিয়াকে নষ্ট করার জন্য অপরাধী যাতে রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা চাপ প্রয়োগ করতে না পারে, তার জন্য একটি কাঠামো প্রতিস্থাপন অত্যন্ত জরুরি। যদিও শিশু নির্যাতন রোধের আইনগত কাঠামোর মধ্যে তদন্ত ও মামলার নিষ্পত্তির জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, তবু সেসব ব্যাপারে আইনগত অস্পষ্টতা, নির্যাতিত নারীদের বয়ঃসীমা সম্পর্কে বিতর্ক, তদন্ত ফলাফলের অসংগতি সুষ্ঠু বিচারপ্রক্রিয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এসবের নিরসন প্রয়োজন। অপরাধ করেও আইনগত ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে পড়ার সংস্কৃতিকেও রোধ করতে হবে।
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পারিবারিক উপদেশ ও নির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোট থাকতেই শিশুদের ব্যক্তিগত সীমারেখা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে কোন স্পর্শটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয়। এগুলো লঙ্ঘিত হলে কীভাবে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে শিশু নিরাপত্তা পর্ষদ গঠন করলেও তৃণমূল পর্যায়ে শিশু নির্যাতন চিহ্নিতকরণ এবং তার প্রতিকার করার সুযোগ তৈরি করা যায়। পর্নোগ্রাফি এবং ক্ষতিকর তথ্যপ্রযুক্তি থেকে শিশুদের রক্ষা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।
চূড়ান্ত বিচারে, পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমন্বিত কাজের মাধ্যমে শিশুদের, বিশেষত মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে।
লেখক: সেলিম জাহান
ভূতপূর্ব পরিচালক, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যেন একটি বেনারসি শাড়ির আঁচল, যার এক প্রান্তে সোনালি জরির কাজ আর অন্য প্রান্তে গলিত সুতোয় দাগ পড়া দারিদ্র্যের ছাপ। একই চাদরে ঢাকা দুটি পৃথিবী, যার একটি অস্তিত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং অন্যটি বিলাসিতায় গা ভাসানোর মতো। একদিকে বৈভবের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে প্রয়োজনের হাহাকার।
১৯ আগস্ট ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভোগ নিরসনে এসে নিজেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর
১৪ ঘণ্টা আগে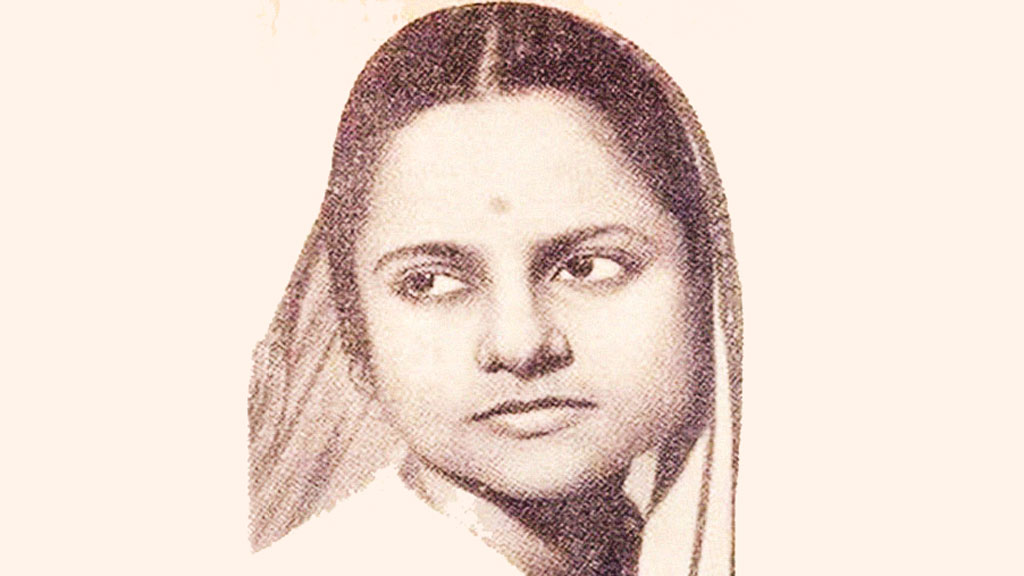
মীরা দেববর্মন ছিলেন বাংলা গানের এক অসামান্য গীতিকার, যিনি কৃতী স্বামী এবং সন্তানের নামের আড়ালে ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছেন আপন সৃষ্টির কারণেই। অনেকের হয়তো জানা নেই, আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি প্রয়াত শচীন দেববর্মনের স্ত্রী এবং উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তি সুরকার রাহুল দেববর্মনের মাতা মীরা দেববর্মন অসংখ্য জন
১৫ ঘণ্টা আগে
না, বারনই নদ বাঁচানোর কোনো মোক্ষম উপায় আমাদের জানা আছে, এ রকম কথা বলব না। যে নদকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’, সে নদই এখন মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালের ভাষায় বলা যায়, নদটি এখন আইসিইউতে। যেকোনো সময় আসতে পারে তার মৃত্যুসংবাদ।
১৫ ঘণ্টা আগেমাসুদ–উর রহমান

১. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভোগ নিরসনে এসে নিজেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবহনব্যবস্থা এবং সড়ক পরিবহন খাতের সমস্যা দূরীকরণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে কাজ করা।
ছয়-সাত বছর ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ আশুগঞ্জ-আখাউড়া চার লেন প্রকল্প বাস্তবায়নের অতি ধীরগতিতে অবর্ণনীয় কষ্ট করে আসছে। গরমে ঘেমে, রোদ-বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থেকে অনেক প্রবাসী যেমন তাঁদের বিদেশগামী ফ্লাইট মিস করেছেন, তেমনি অনেক অসুস্থ মানুষও সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে না পেরে অ্যাম্বুলেন্সেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেহাল সড়কে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে এবং এতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়েছে স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা এবং অফিসগামী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। একটি উন্নয়ন প্রকল্প এত দীর্ঘদিন ধরে চলার নজিরও সম্ভবত এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম।
গত বছর থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ছয় লেন প্রকল্প। দুই প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ধাক্কাধাক্কিতেই যৌথ অধিকারে থাকা আশুগঞ্জ-বিশ্বরোডের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি নাজুক। উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সড়কে যে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হয়, সেটি সম্ভবত প্রকল্প পরিচালকেরা জানেনই না। ফলে ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাস্তার এই অংশে, সেই অংশে অর্থাৎ অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নকাজ শুরু করে। এই অপরিকল্পিত সড়ক প্রশস্তকরণের কারণে সাত বছর ধরে আশুগঞ্জ থেকে কসবার তিনলাখপীর পর্যন্ত দীর্ঘ পথে মানুষকে অসহনীয় দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। পাশাপাশি এ বছরের শুরু থেকে আশুগঞ্জ-মাধবপুর অংশে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার সড়কপথ অনেকটা অচল হয়ে পড়ে। কয়েক মাস ধরে প্রশাসনের নির্লিপ্ততায়, ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব পালনের অবহেলায় রাস্তায় চরম অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছিল। এতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হতো জনসাধারণকে। অবস্থা এতই বেগতিক হচ্ছিল যে এক মাস ধরে ঢাকা-সিলেট সড়ক যোগাযোগ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সড়কপথের এই বাড়তি চাপ এসে পড়ল রেলপথের ওপর। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের ছাদে চড়ে, দরজার হ্যান্ডেলে ঝুলে যাতায়াত করা যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের চিত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্যে হয়তো টনক নড়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তারই জেরে কিনা সড়ক ও সেতু উপদেষ্টার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের দিন-তারিখ ঠিক হলে দ্রুত রাস্তার সংস্কারে যেন হুলুস্থুল পড়ে যায়। উপদেষ্টাকে খুশি করতে ত্বরিত রাস্তা সংস্কারে নেমে আসে সওজ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।
কিন্তু তাদের শেষরক্ষা হয়নি। তারা যানজটমুক্ত সড়ক উপহার দিতে পারেনি উপদেষ্টাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপদেষ্টা যানজটে পড়ে শুধু যে শারীরিক কষ্ট করেছেন, তা-ই শুধু নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ট্রলের শিকার হয়েছেন।
এত দিন দুর্ভোগে কষ্ট করা মানুষগুলো উপদেষ্টার এই কষ্ট দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য লিখে হয় মনের ঝাল মিটিয়েছেন অথবা সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।
অবশ্য রাজনৈতিক সরকারের মন্ত্রীদের এমন অবস্থা কখনোই হতো না, যেমন অতীতে হয়নি। প্রশাসনিক কার্যক্রমের আগেই স্থানীয় নেতা-কর্মীরা রাস্তা পরিষ্কার করে একেবারে নির্বিঘ্নে মন্ত্রীকে যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছে দিতেন। অতীতে ভালো রাস্তায়ও মন্ত্রী-এমপিদের অনেককে সহজ যাতায়াতের জন্য উল্টো পথে চলে কিংবা রাস্তা আটকে যানজট তৈরি করে জনগণকে দুর্ভোগে ফেলে ধুলা উড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে দেখেছি। তখন কি মানুষের এ রকম কষ্ট হতো না? বড় নেতাদের দুঃশাসন আর পাতিনেতাদের অতি বাড়াবাড়ির কারণে সাধারণে জন্ম নেওয়া ক্ষোভের প্রকাশই কিন্তু গত আগস্টে সরকার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। আজ যাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বা যাঁরা অচিরেই সরকারে আসবেন মনে করে গোঁফে তা দিচ্ছেন, তাঁরা কি জনগণের সেই বিষাক্ত নিশ্বাসের আঁচ অনুভব করতে পারছেন?
২. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মহত্তম চেতনায়। একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সে পথে যেতে আমরা বারবার হোঁচট খেয়েছি। সহনশীলতা ও মানবিক রাজনীতি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি, উল্টো রাজনীতির কেন্দ্রে চলে এসেছে প্রতিশোধ, ষড়যন্ত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুছে দেওয়ার প্রবণতা। রাজনৈতিক অঙ্গনে মতবিরোধ থাকবেই এবং এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। মতবিরোধ নিরসনে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিল অতীতে খুব একটা মুখ্য হয়নি। যুক্তি দিয়ে তাঁদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে দমন-পীড়নের নামে রাস্তায় ফয়সালাই হয়েছে বেশি। আঠারো শতকের ইউরোপে গণতন্ত্র বিকাশের সময় বারবার বলা হয়েছিল, ‘আই ডিজঅ্যাপ্রুভ অব হোয়াট ইউ সে, বাট আই উইল ডিফেন্ড টু দ্য ডেথ ইউর রাইট টু সে ইট’। অর্থাৎ ভিন্নমতকে মেনে নেওয়া গণতন্ত্রের প্রাণ। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনীতির মূল সুর হয়ে দাঁড়ায়, ‘তুমি ভিন্নমত পোষণ করছ, তাই তোমাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।’
ধারণা করা হয়েছিল, ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে এই মানসিকতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হবে কিন্তু কিসের কী? হলো না কিছুই। আর হলো না বলেই সেফ এক্সিট এখন আলোচনার অন্যতম মূল বিষয়। হয়তো কোনো কোনো উপদেষ্টা তাঁদের গত বছরাধিক সময়ের কর্মের দিকে ফিরে তাকিয়ে নিরাপদ বোধ করছেন না। সরকার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতিও বিগত সরকারের মতো হবে ভেবে যারপরনাই উদ্বিগ্ন। এমনটি কেন হলো?
কেন আপনারা গণ-অভ্যুত্থানের আবেগটুকু বুঝতে পারলেন না? আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, এই সেফ এক্সিট গণতন্ত্রের পথে উত্তরণে কখনোই মঙ্গল বয়ে আনেনি, আনবেও না। নির্বাচনের আরও মাস কয়েক বাকি। কাজেই বর্তমান সরকারের উচিত, যথাযথ তদন্ত করে অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে কারা জড়িত কিংবা বিরুদ্ধমতকে নিষ্পেষণ করার সঙ্গে কারা জড়িত, কারা ক্ষমতা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা। একজন নির্দোষও শাস্তি পাক, তা কখনোই কাম্য হতে পারে না। যাঁরা ক্ষমতা পেয়ে দেশের জন্য সততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে, বিরুদ্ধমতের তির্যক মন্তব্যেও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে দেশের মানচিত্র অক্ষত রেখে, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিকে সমুন্নত রেখে, সর্বোপরি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তারা কেন সরে যাবে? তারাই তো থাকবে। কথায় আছে না, ‘যে সহে সে রহে।’
লেখক: মাসুদ উর রহমান
কলেজশিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী

১. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভোগ নিরসনে এসে নিজেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবহনব্যবস্থা এবং সড়ক পরিবহন খাতের সমস্যা দূরীকরণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে কাজ করা।
ছয়-সাত বছর ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ আশুগঞ্জ-আখাউড়া চার লেন প্রকল্প বাস্তবায়নের অতি ধীরগতিতে অবর্ণনীয় কষ্ট করে আসছে। গরমে ঘেমে, রোদ-বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থেকে অনেক প্রবাসী যেমন তাঁদের বিদেশগামী ফ্লাইট মিস করেছেন, তেমনি অনেক অসুস্থ মানুষও সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছাতে না পেরে অ্যাম্বুলেন্সেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেহাল সড়কে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে এবং এতে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটছে। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়েছে স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা এবং অফিসগামী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। একটি উন্নয়ন প্রকল্প এত দীর্ঘদিন ধরে চলার নজিরও সম্ভবত এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রথম।
গত বছর থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ছয় লেন প্রকল্প। দুই প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ধাক্কাধাক্কিতেই যৌথ অধিকারে থাকা আশুগঞ্জ-বিশ্বরোডের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে বেশি নাজুক। উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সড়কে যে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হয়, সেটি সম্ভবত প্রকল্প পরিচালকেরা জানেনই না। ফলে ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাস্তার এই অংশে, সেই অংশে অর্থাৎ অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নকাজ শুরু করে। এই অপরিকল্পিত সড়ক প্রশস্তকরণের কারণে সাত বছর ধরে আশুগঞ্জ থেকে কসবার তিনলাখপীর পর্যন্ত দীর্ঘ পথে মানুষকে অসহনীয় দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। পাশাপাশি এ বছরের শুরু থেকে আশুগঞ্জ-মাধবপুর অংশে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার সড়কপথ অনেকটা অচল হয়ে পড়ে। কয়েক মাস ধরে প্রশাসনের নির্লিপ্ততায়, ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব পালনের অবহেলায় রাস্তায় চরম অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছিল। এতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হতো জনসাধারণকে। অবস্থা এতই বেগতিক হচ্ছিল যে এক মাস ধরে ঢাকা-সিলেট সড়ক যোগাযোগ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সড়কপথের এই বাড়তি চাপ এসে পড়ল রেলপথের ওপর। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের ছাদে চড়ে, দরজার হ্যান্ডেলে ঝুলে যাতায়াত করা যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের চিত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্যে হয়তো টনক নড়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তারই জেরে কিনা সড়ক ও সেতু উপদেষ্টার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের দিন-তারিখ ঠিক হলে দ্রুত রাস্তার সংস্কারে যেন হুলুস্থুল পড়ে যায়। উপদেষ্টাকে খুশি করতে ত্বরিত রাস্তা সংস্কারে নেমে আসে সওজ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।
কিন্তু তাদের শেষরক্ষা হয়নি। তারা যানজটমুক্ত সড়ক উপহার দিতে পারেনি উপদেষ্টাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপদেষ্টা যানজটে পড়ে শুধু যে শারীরিক কষ্ট করেছেন, তা-ই শুধু নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ট্রলের শিকার হয়েছেন।
এত দিন দুর্ভোগে কষ্ট করা মানুষগুলো উপদেষ্টার এই কষ্ট দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য লিখে হয় মনের ঝাল মিটিয়েছেন অথবা সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।
অবশ্য রাজনৈতিক সরকারের মন্ত্রীদের এমন অবস্থা কখনোই হতো না, যেমন অতীতে হয়নি। প্রশাসনিক কার্যক্রমের আগেই স্থানীয় নেতা-কর্মীরা রাস্তা পরিষ্কার করে একেবারে নির্বিঘ্নে মন্ত্রীকে যথাযথ গন্তব্যে পৌঁছে দিতেন। অতীতে ভালো রাস্তায়ও মন্ত্রী-এমপিদের অনেককে সহজ যাতায়াতের জন্য উল্টো পথে চলে কিংবা রাস্তা আটকে যানজট তৈরি করে জনগণকে দুর্ভোগে ফেলে ধুলা উড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে দেখেছি। তখন কি মানুষের এ রকম কষ্ট হতো না? বড় নেতাদের দুঃশাসন আর পাতিনেতাদের অতি বাড়াবাড়ির কারণে সাধারণে জন্ম নেওয়া ক্ষোভের প্রকাশই কিন্তু গত আগস্টে সরকার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। আজ যাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন বা যাঁরা অচিরেই সরকারে আসবেন মনে করে গোঁফে তা দিচ্ছেন, তাঁরা কি জনগণের সেই বিষাক্ত নিশ্বাসের আঁচ অনুভব করতে পারছেন?
২. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মহত্তম চেতনায়। একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সে পথে যেতে আমরা বারবার হোঁচট খেয়েছি। সহনশীলতা ও মানবিক রাজনীতি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি, উল্টো রাজনীতির কেন্দ্রে চলে এসেছে প্রতিশোধ, ষড়যন্ত্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুছে দেওয়ার প্রবণতা। রাজনৈতিক অঙ্গনে মতবিরোধ থাকবেই এবং এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। মতবিরোধ নিরসনে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিল অতীতে খুব একটা মুখ্য হয়নি। যুক্তি দিয়ে তাঁদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে দমন-পীড়নের নামে রাস্তায় ফয়সালাই হয়েছে বেশি। আঠারো শতকের ইউরোপে গণতন্ত্র বিকাশের সময় বারবার বলা হয়েছিল, ‘আই ডিজঅ্যাপ্রুভ অব হোয়াট ইউ সে, বাট আই উইল ডিফেন্ড টু দ্য ডেথ ইউর রাইট টু সে ইট’। অর্থাৎ ভিন্নমতকে মেনে নেওয়া গণতন্ত্রের প্রাণ। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনীতির মূল সুর হয়ে দাঁড়ায়, ‘তুমি ভিন্নমত পোষণ করছ, তাই তোমাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।’
ধারণা করা হয়েছিল, ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে এই মানসিকতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হবে কিন্তু কিসের কী? হলো না কিছুই। আর হলো না বলেই সেফ এক্সিট এখন আলোচনার অন্যতম মূল বিষয়। হয়তো কোনো কোনো উপদেষ্টা তাঁদের গত বছরাধিক সময়ের কর্মের দিকে ফিরে তাকিয়ে নিরাপদ বোধ করছেন না। সরকার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতিও বিগত সরকারের মতো হবে ভেবে যারপরনাই উদ্বিগ্ন। এমনটি কেন হলো?
কেন আপনারা গণ-অভ্যুত্থানের আবেগটুকু বুঝতে পারলেন না? আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, এই সেফ এক্সিট গণতন্ত্রের পথে উত্তরণে কখনোই মঙ্গল বয়ে আনেনি, আনবেও না। নির্বাচনের আরও মাস কয়েক বাকি। কাজেই বর্তমান সরকারের উচিত, যথাযথ তদন্ত করে অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে কারা জড়িত কিংবা বিরুদ্ধমতকে নিষ্পেষণ করার সঙ্গে কারা জড়িত, কারা ক্ষমতা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনা। একজন নির্দোষও শাস্তি পাক, তা কখনোই কাম্য হতে পারে না। যাঁরা ক্ষমতা পেয়ে দেশের জন্য সততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে, বিরুদ্ধমতের তির্যক মন্তব্যেও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে দেশের মানচিত্র অক্ষত রেখে, আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিকে সমুন্নত রেখে, সর্বোপরি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তারা কেন সরে যাবে? তারাই তো থাকবে। কথায় আছে না, ‘যে সহে সে রহে।’
লেখক: মাসুদ উর রহমান
কলেজশিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যেন একটি বেনারসি শাড়ির আঁচল, যার এক প্রান্তে সোনালি জরির কাজ আর অন্য প্রান্তে গলিত সুতোয় দাগ পড়া দারিদ্র্যের ছাপ। একই চাদরে ঢাকা দুটি পৃথিবী, যার একটি অস্তিত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং অন্যটি বিলাসিতায় গা ভাসানোর মতো। একদিকে বৈভবের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে প্রয়োজনের হাহাকার।
১৯ আগস্ট ২০২৫
আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই
১৪ ঘণ্টা আগে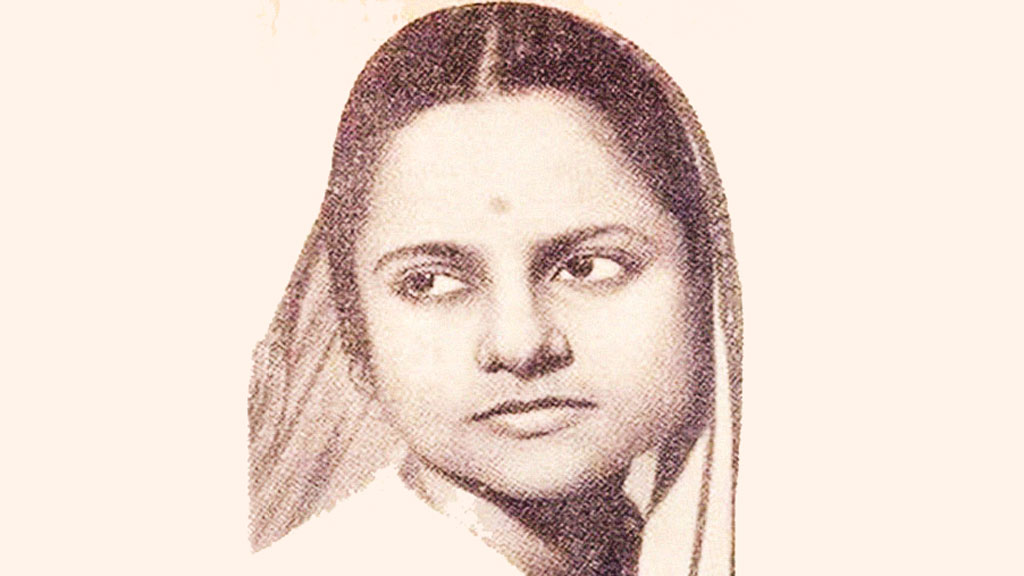
মীরা দেববর্মন ছিলেন বাংলা গানের এক অসামান্য গীতিকার, যিনি কৃতী স্বামী এবং সন্তানের নামের আড়ালে ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছেন আপন সৃষ্টির কারণেই। অনেকের হয়তো জানা নেই, আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি প্রয়াত শচীন দেববর্মনের স্ত্রী এবং উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তি সুরকার রাহুল দেববর্মনের মাতা মীরা দেববর্মন অসংখ্য জন
১৫ ঘণ্টা আগে
না, বারনই নদ বাঁচানোর কোনো মোক্ষম উপায় আমাদের জানা আছে, এ রকম কথা বলব না। যে নদকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’, সে নদই এখন মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালের ভাষায় বলা যায়, নদটি এখন আইসিইউতে। যেকোনো সময় আসতে পারে তার মৃত্যুসংবাদ।
১৫ ঘণ্টা আগেআবদুল্লাহ আল মোহন
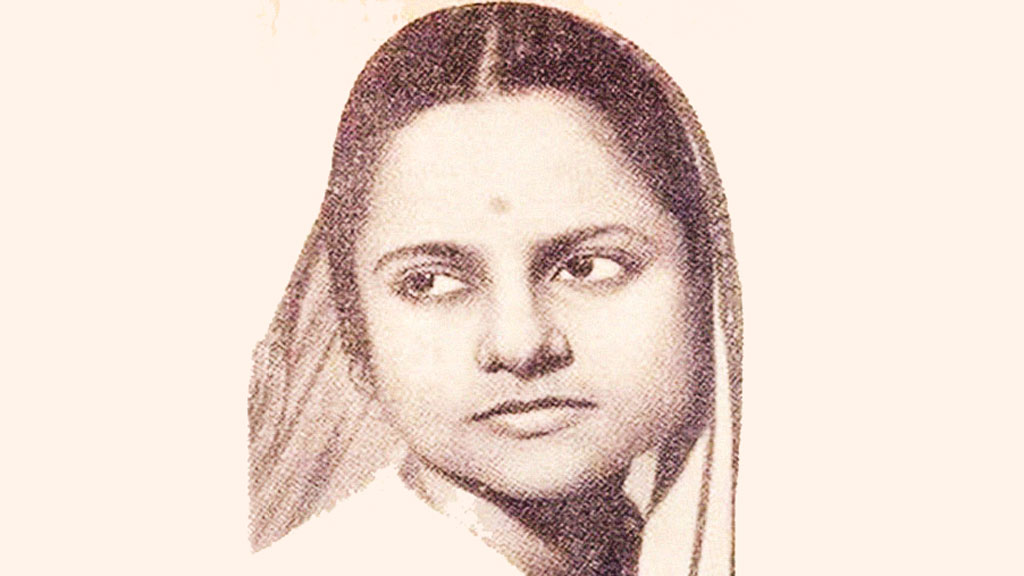
মীরা দেববর্মন ছিলেন বাংলা গানের এক অসামান্য গীতিকার, যিনি কৃতী স্বামী এবং সন্তানের নামের আড়ালে ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছেন আপন সৃষ্টির কারণেই। অনেকের হয়তো জানা নেই, আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি প্রয়াত শচীন দেববর্মনের স্ত্রী এবং উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তি সুরকার রাহুল দেববর্মনের মাতা মীরা দেববর্মন অসংখ্য জনপ্রিয় গানের একজন নিভৃতচারিণী গীতিকার। মীরা দেববর্মন রচিত, শচীন দেববর্মনের সুরে ও কণ্ঠে সুপরিচিত কয়েকটি গান হলো ‘বিরহ বড় ভালো লাগে’, ‘গানের কলি সুরের দুরিতে’, ‘ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা’, ‘বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে’, ‘কালসাপ দংশে আমায়’, ‘কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া’, ‘কী করি আমি কী করি’, ‘না আমারে শশী চেয় না’, ‘নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক’, ‘শোন গো দখিন হাওয়া’, ‘তাকদুম তাকদুম বাজাই’ ইত্যাদি।
যিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার এক অভিজাত পরিবারের কন্যা। মীরা দেববর্মন ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন জানা গেলেও সঠিক তারিখ উদ্ধার করা যায়নি।
একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় শচীন দেববর্মন আরব সাগরপারে থেকেও প্রতিনিয়ত খবর নিতেন, বাংলার দামাল ছেলেরা যুদ্ধে কতটা জয় হাসিল করতে পারল। ভালো খবরের জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। তাঁর আত্মা তখন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম। শচীনকর্তার আবেগ ও আকুতি বুঝতে পেরেছিলেন মীরা। আর তাই ১৯৭১ সালে রেকর্ড করা হলো ‘তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল’।
১৯৩৭ সালে এলাহাবাদে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে শচীন দেববর্মনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও প্রেম। ১৯৩৮ সালে তাঁরা বিবাহ করেন। মীরা দেববর্মন তাঁর স্বামী ও পুত্রের সংগীতজীবনে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। আর নিজেকে রেখেছেন অন্তরালে। তিনি সফল ছিলেন একাধারে গীতিকার, সংগীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী হিসেবে। প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন যেমন, একই সঙ্গে যুগের তুলনায় সঠিকভাবে তালিমও পেয়েছিলেন। আর তাই সংগীতের সব ক্ষেত্রে সমান পারদর্শিতা ছিল তাঁর। নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন, সম্পূর্ণ ছিল সুরের জ্ঞান।
মীরা দেববর্মনের দাদু রায়বাহাদুর কমলনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস। দাদু ও দিদিমার বাড়িতে জন্ম থেকে থাকতে হয় পারিবারিক কারণে। তারপর কলকাতার সাউথ এন্ডে বসবাস শুরু করেন তাঁদের সঙ্গে। সেখানে শুরু হয় পড়াশোনার সঙ্গে সংগীতের তালিম। বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষা সমানতালে চলে। ১৯৩৭ সাল থেকে শচীন দেববর্মনের কাছে গান শিখতে শুরু করেন। এ ছাড়া তিনি সংগীতগুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছেন। কীর্তন ও ঠুমরি শেখেন সংগীতাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ দেবের কাছে। ১৯৩০ সালে আনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসংগীতে শিক্ষালাভ করেন এবং শান্তিনিকেতনে অমিতা সেনের কাছে নৃত্যে তালিম নিয়েছিলেন।
মীরা দেববর্মনকে নিয়ে সংগীতবোদ্ধাদের অভিমত যথার্থই মনে হয়, ‘শাস্ত্রীয় সংগীতের তুখোড় জ্ঞানসম্পন্ন গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, রবীন্দ্রসংগীতেও সমান দক্ষতা, গানের কথাকার হিসেবে আধুনিকমনস্কতা, শব্দের ব্যবহার, মাটির কাছাকাছি থাকার প্রবণতা—অবাক হতে হয়। শচীন দেববর্মনের যে গানগুলোর সুরের আবেশে মাতাল হই এবং নিয়ত গুনগুন করি, সেগুলোর অনেক সুরই মীরা দেববর্মনের সহায়তায় তৈরি হয়েছে।’
মীরা দেববর্মন বিয়ের বছরে অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতা থেকে অডিশন দিয়ে উত্তীর্ণ হন। সেই সঙ্গে শুরু করেন পড়াশোনাও। আইএ পরীক্ষায় বসলেন। কিন্তু সংগীতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় পড়াশোনায় ইতি দিয়ে সংগীতের পথ ধরেই হাঁটলেন। স্বামীর সঙ্গে বোম্বে গেলেন, নতুন অধ্যায় শুরু হলো। বোম্বেতে গিয়ে ফৈয়াজ মহম্মদ খানের কাছে তালিম নিলেন। সংগীতের পিপাসা ছিল অসীম। নিজেকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চলছিল নিরন্তর। ১৯৪৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও, বোম্বে থেকে অডিশন পাস করে ঠুংরি ও গজল পরিবেশন করতেন। সেই সময় তিনি দুটি নাটক শান্তি ও নয়া প্রভাতের গানের কথা রচনা করেন। অনেক গানের রেকর্ডও করেন। আবার সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবেও তিনি ছিলেন একজন সফল মানুষ। নয়া জমানা, তেরে মেরে স্বপ্নে, শর্মিলী, অভিমান, বারুদ, প্রেমনগর—বিখ্যাত এই চলচ্চিত্রগুলোর সহযোগী সংগীত পরিচালক ছিলেন তিনি।
১৯৭৫ সালে স্বামী এবং ১৯৯৪ সালে পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর জীবন জটিল হয়ে পড়ে। এই মৃত্যুশোক তাঁকে অনেকটাই মানসিক ভারসাম্যহীন করে তোলে। জীবনের শেষ দিনগুলো বেদনার হয়ে উঠেছিল এই অসামান্য গীতিকার, সুরমালিকার। কথায় কথায় মালা গেঁথেছিলেন যিনি, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কথা। কেবল শচীন দেববর্মনের গান শুনলে নড়েচড়ে উঠতেন। চেতনার জগৎ তাঁর কাছে মূল্য হারিয়েছিল। এমন অবস্থায় ত্রিপুরা সরকার সহযোগিতার হাত বাড়ালে তাঁকে মুম্বাইয়ে স্থানান্তর করা হয়। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে মুম্বাইয়ে রাহুল দেববর্মনের বাড়িতে নিয়ে রাখা হয়। ওই বছরের ১৫ অক্টোবর দীর্ঘদিন রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়।
লেখক: আবদুল্লাহ আল মোহন
সহযোগী অধ্যাপক, ভাসানটেক সরকারি কলেজ
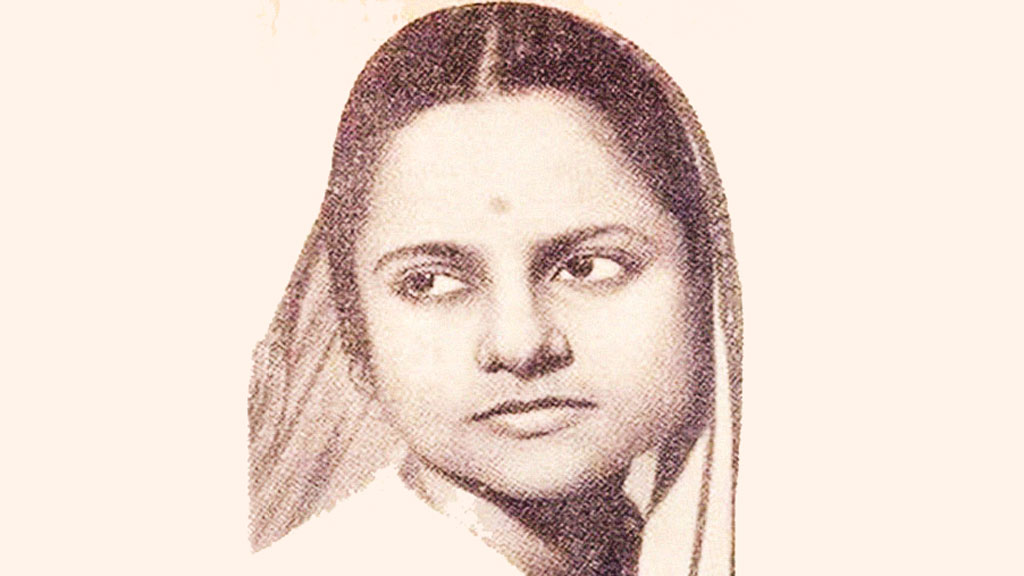
মীরা দেববর্মন ছিলেন বাংলা গানের এক অসামান্য গীতিকার, যিনি কৃতী স্বামী এবং সন্তানের নামের আড়ালে ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছেন আপন সৃষ্টির কারণেই। অনেকের হয়তো জানা নেই, আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি প্রয়াত শচীন দেববর্মনের স্ত্রী এবং উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তি সুরকার রাহুল দেববর্মনের মাতা মীরা দেববর্মন অসংখ্য জনপ্রিয় গানের একজন নিভৃতচারিণী গীতিকার। মীরা দেববর্মন রচিত, শচীন দেববর্মনের সুরে ও কণ্ঠে সুপরিচিত কয়েকটি গান হলো ‘বিরহ বড় ভালো লাগে’, ‘গানের কলি সুরের দুরিতে’, ‘ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা’, ‘বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে’, ‘কালসাপ দংশে আমায়’, ‘কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া’, ‘কী করি আমি কী করি’, ‘না আমারে শশী চেয় না’, ‘নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক’, ‘শোন গো দখিন হাওয়া’, ‘তাকদুম তাকদুম বাজাই’ ইত্যাদি।
যিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার এক অভিজাত পরিবারের কন্যা। মীরা দেববর্মন ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন জানা গেলেও সঠিক তারিখ উদ্ধার করা যায়নি।
একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় শচীন দেববর্মন আরব সাগরপারে থেকেও প্রতিনিয়ত খবর নিতেন, বাংলার দামাল ছেলেরা যুদ্ধে কতটা জয় হাসিল করতে পারল। ভালো খবরের জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। তাঁর আত্মা তখন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম। শচীনকর্তার আবেগ ও আকুতি বুঝতে পেরেছিলেন মীরা। আর তাই ১৯৭১ সালে রেকর্ড করা হলো ‘তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল’।
১৯৩৭ সালে এলাহাবাদে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে শচীন দেববর্মনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও প্রেম। ১৯৩৮ সালে তাঁরা বিবাহ করেন। মীরা দেববর্মন তাঁর স্বামী ও পুত্রের সংগীতজীবনে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। আর নিজেকে রেখেছেন অন্তরালে। তিনি সফল ছিলেন একাধারে গীতিকার, সংগীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী হিসেবে। প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন যেমন, একই সঙ্গে যুগের তুলনায় সঠিকভাবে তালিমও পেয়েছিলেন। আর তাই সংগীতের সব ক্ষেত্রে সমান পারদর্শিতা ছিল তাঁর। নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন, সম্পূর্ণ ছিল সুরের জ্ঞান।
মীরা দেববর্মনের দাদু রায়বাহাদুর কমলনাথ দাশগুপ্ত ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস। দাদু ও দিদিমার বাড়িতে জন্ম থেকে থাকতে হয় পারিবারিক কারণে। তারপর কলকাতার সাউথ এন্ডে বসবাস শুরু করেন তাঁদের সঙ্গে। সেখানে শুরু হয় পড়াশোনার সঙ্গে সংগীতের তালিম। বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষা সমানতালে চলে। ১৯৩৭ সাল থেকে শচীন দেববর্মনের কাছে গান শিখতে শুরু করেন। এ ছাড়া তিনি সংগীতগুরু ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নিয়েছেন। কীর্তন ও ঠুমরি শেখেন সংগীতাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ দেবের কাছে। ১৯৩০ সালে আনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্রসংগীতে শিক্ষালাভ করেন এবং শান্তিনিকেতনে অমিতা সেনের কাছে নৃত্যে তালিম নিয়েছিলেন।
মীরা দেববর্মনকে নিয়ে সংগীতবোদ্ধাদের অভিমত যথার্থই মনে হয়, ‘শাস্ত্রীয় সংগীতের তুখোড় জ্ঞানসম্পন্ন গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, রবীন্দ্রসংগীতেও সমান দক্ষতা, গানের কথাকার হিসেবে আধুনিকমনস্কতা, শব্দের ব্যবহার, মাটির কাছাকাছি থাকার প্রবণতা—অবাক হতে হয়। শচীন দেববর্মনের যে গানগুলোর সুরের আবেশে মাতাল হই এবং নিয়ত গুনগুন করি, সেগুলোর অনেক সুরই মীরা দেববর্মনের সহায়তায় তৈরি হয়েছে।’
মীরা দেববর্মন বিয়ের বছরে অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতা থেকে অডিশন দিয়ে উত্তীর্ণ হন। সেই সঙ্গে শুরু করেন পড়াশোনাও। আইএ পরীক্ষায় বসলেন। কিন্তু সংগীতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় পড়াশোনায় ইতি দিয়ে সংগীতের পথ ধরেই হাঁটলেন। স্বামীর সঙ্গে বোম্বে গেলেন, নতুন অধ্যায় শুরু হলো। বোম্বেতে গিয়ে ফৈয়াজ মহম্মদ খানের কাছে তালিম নিলেন। সংগীতের পিপাসা ছিল অসীম। নিজেকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চলছিল নিরন্তর। ১৯৪৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও, বোম্বে থেকে অডিশন পাস করে ঠুংরি ও গজল পরিবেশন করতেন। সেই সময় তিনি দুটি নাটক শান্তি ও নয়া প্রভাতের গানের কথা রচনা করেন। অনেক গানের রেকর্ডও করেন। আবার সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবেও তিনি ছিলেন একজন সফল মানুষ। নয়া জমানা, তেরে মেরে স্বপ্নে, শর্মিলী, অভিমান, বারুদ, প্রেমনগর—বিখ্যাত এই চলচ্চিত্রগুলোর সহযোগী সংগীত পরিচালক ছিলেন তিনি।
১৯৭৫ সালে স্বামী এবং ১৯৯৪ সালে পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর জীবন জটিল হয়ে পড়ে। এই মৃত্যুশোক তাঁকে অনেকটাই মানসিক ভারসাম্যহীন করে তোলে। জীবনের শেষ দিনগুলো বেদনার হয়ে উঠেছিল এই অসামান্য গীতিকার, সুরমালিকার। কথায় কথায় মালা গেঁথেছিলেন যিনি, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কথা। কেবল শচীন দেববর্মনের গান শুনলে নড়েচড়ে উঠতেন। চেতনার জগৎ তাঁর কাছে মূল্য হারিয়েছিল। এমন অবস্থায় ত্রিপুরা সরকার সহযোগিতার হাত বাড়ালে তাঁকে মুম্বাইয়ে স্থানান্তর করা হয়। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে মুম্বাইয়ে রাহুল দেববর্মনের বাড়িতে নিয়ে রাখা হয়। ওই বছরের ১৫ অক্টোবর দীর্ঘদিন রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়।
লেখক: আবদুল্লাহ আল মোহন
সহযোগী অধ্যাপক, ভাসানটেক সরকারি কলেজ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যেন একটি বেনারসি শাড়ির আঁচল, যার এক প্রান্তে সোনালি জরির কাজ আর অন্য প্রান্তে গলিত সুতোয় দাগ পড়া দারিদ্র্যের ছাপ। একই চাদরে ঢাকা দুটি পৃথিবী, যার একটি অস্তিত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং অন্যটি বিলাসিতায় গা ভাসানোর মতো। একদিকে বৈভবের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে প্রয়োজনের হাহাকার।
১৯ আগস্ট ২০২৫
আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই
১৪ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভোগ নিরসনে এসে নিজেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর
১৪ ঘণ্টা আগে
না, বারনই নদ বাঁচানোর কোনো মোক্ষম উপায় আমাদের জানা আছে, এ রকম কথা বলব না। যে নদকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’, সে নদই এখন মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালের ভাষায় বলা যায়, নদটি এখন আইসিইউতে। যেকোনো সময় আসতে পারে তার মৃত্যুসংবাদ।
১৫ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

না, বারনই নদ বাঁচানোর কোনো মোক্ষম উপায় আমাদের জানা আছে, এ রকম কথা বলব না। যে নদকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’, সে নদই এখন মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালের ভাষায় বলা যায়, নদটি এখন আইসিইউতে। যেকোনো সময় আসতে পারে তার মৃত্যুসংবাদ। সবাই জানে, কেন নদটির মরণদশা, অথচ কেউই তা ঠিক করার পরিকল্পিত উদ্যোগ নিচ্ছে না।
বারনই নদ মরে গেলে এর চারপাশের মানুষের জীবনেও তার প্রভাব পড়বে। এরই মধ্যে পড়তেও শুরু করেছে। রাজশাহী থেকে আমাদের প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, ময়লা-দুর্গন্ধে নদের কাছে যেতে পারছে না মানুষ। তার মানে, নদটি কি ক্লিনিক্যালি ডেথ হিসেবেই রয়েছে?
১৩ অক্টোবর ‘জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বারনই নদী রক্ষায় করণীয়’ শীর্ষক একটি সভা হয়েছে রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা মহিলা ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে। নওহাটার নদের পাড়ে হয় গম্ভীরার আয়োজন। নদ রক্ষায় একটি মানববন্ধনও হয়। এ যেন প্রায় মৃত একটি নদকে বাঁচানোর জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা। কিন্তু মেডিকেল বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত কি কার্যকর হবে?
আগে দেখা যাক, কারা এই নদের সর্বনাশ করল? নদের আশপাশের বসতির শৌচাগারগুলোর বর্জ্য এসে পড়ে ড্রেনে, ড্রেন থেকে আসে খালে, খাল থেকে চলে যায় নদে। কী অসাধারণ এক ব্যবস্থা! সরকারি মহলের কেউই বুঝি জানে না, মল এসে নদের পানিকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। কেউই বুঝি জানে না, এই পানির সংস্পর্শে এলে যেকোনো মানুষেরই চর্মরোগ হতে পারে। কেউই হয়তো জানে না, নদের পানি এমন মাত্রায় দূষিত হয়েছে যে মাছও বেঁচে থাকতে পারছে না! পবার দুয়ারি থেকে নওহাটা এলাকার মানুষের দুর্গন্ধের কারণে দরজা-জানালা সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখতে হয়। আর দখলদারেরা? নির্বিঘ্নে তারা দখল করে নিয়েছে এবং নিচ্ছে নদটি। এর সীমা কতটা আর কোনটা দখলদারেরা কবজা করে নিয়েছে, তা নিয়েও কারও মাথাব্যথা নেই। এই নদের সীমানা নির্ধারণ করে দখলদারদের উচ্ছেদ করা কি সম্ভব হবে? এলাকাবাসীর মল ও বর্জ্য যেন নদে গিয়ে না পড়ে, তার জন্য কি কোনো পরিকল্পনা করতে পারবে প্রশাসন?
দুঃখের বিষয়, নদ বাঁচলে এলাকাবাসীর জীবন বাঁচবে, এই কথা উপলব্ধি করতে পারে না মানুষ। শুধু নিজে ঠিকঠাকমতো বাঁচতে পারলেই হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর জীবনের হদিস দিতে পারছে কি না, সেই ভাবনা না থাকলে আদতে কত দূর এগিয়ে যাওয়া যায়?
বারনই নদ ধুঁকছে। যে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, সে গানও তো হুমকির মুখে। লোকজ সংস্কৃতি বাঁচানোর কার্যকর কোনো পথের দিশা কি দেখা যাচ্ছে কোথাও? নদটি বাঁচাতে হলে সবার আগে নদের এই দুর্দশা কেন হলো, সেটা খুঁজে বের করে তার প্রতিকার করতে হবে। নদটিকে ভালো না বাসলে এর ললাটে মৃত্যুই লেখা আছে।

না, বারনই নদ বাঁচানোর কোনো মোক্ষম উপায় আমাদের জানা আছে, এ রকম কথা বলব না। যে নদকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’, সে নদই এখন মৃত্যুশয্যায়। হাসপাতালের ভাষায় বলা যায়, নদটি এখন আইসিইউতে। যেকোনো সময় আসতে পারে তার মৃত্যুসংবাদ। সবাই জানে, কেন নদটির মরণদশা, অথচ কেউই তা ঠিক করার পরিকল্পিত উদ্যোগ নিচ্ছে না।
বারনই নদ মরে গেলে এর চারপাশের মানুষের জীবনেও তার প্রভাব পড়বে। এরই মধ্যে পড়তেও শুরু করেছে। রাজশাহী থেকে আমাদের প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, ময়লা-দুর্গন্ধে নদের কাছে যেতে পারছে না মানুষ। তার মানে, নদটি কি ক্লিনিক্যালি ডেথ হিসেবেই রয়েছে?
১৩ অক্টোবর ‘জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বারনই নদী রক্ষায় করণীয়’ শীর্ষক একটি সভা হয়েছে রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা মহিলা ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে। নওহাটার নদের পাড়ে হয় গম্ভীরার আয়োজন। নদ রক্ষায় একটি মানববন্ধনও হয়। এ যেন প্রায় মৃত একটি নদকে বাঁচানোর জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা। কিন্তু মেডিকেল বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত কি কার্যকর হবে?
আগে দেখা যাক, কারা এই নদের সর্বনাশ করল? নদের আশপাশের বসতির শৌচাগারগুলোর বর্জ্য এসে পড়ে ড্রেনে, ড্রেন থেকে আসে খালে, খাল থেকে চলে যায় নদে। কী অসাধারণ এক ব্যবস্থা! সরকারি মহলের কেউই বুঝি জানে না, মল এসে নদের পানিকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। কেউই বুঝি জানে না, এই পানির সংস্পর্শে এলে যেকোনো মানুষেরই চর্মরোগ হতে পারে। কেউই হয়তো জানে না, নদের পানি এমন মাত্রায় দূষিত হয়েছে যে মাছও বেঁচে থাকতে পারছে না! পবার দুয়ারি থেকে নওহাটা এলাকার মানুষের দুর্গন্ধের কারণে দরজা-জানালা সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখতে হয়। আর দখলদারেরা? নির্বিঘ্নে তারা দখল করে নিয়েছে এবং নিচ্ছে নদটি। এর সীমা কতটা আর কোনটা দখলদারেরা কবজা করে নিয়েছে, তা নিয়েও কারও মাথাব্যথা নেই। এই নদের সীমানা নির্ধারণ করে দখলদারদের উচ্ছেদ করা কি সম্ভব হবে? এলাকাবাসীর মল ও বর্জ্য যেন নদে গিয়ে না পড়ে, তার জন্য কি কোনো পরিকল্পনা করতে পারবে প্রশাসন?
দুঃখের বিষয়, নদ বাঁচলে এলাকাবাসীর জীবন বাঁচবে, এই কথা উপলব্ধি করতে পারে না মানুষ। শুধু নিজে ঠিকঠাকমতো বাঁচতে পারলেই হলো, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর জীবনের হদিস দিতে পারছে কি না, সেই ভাবনা না থাকলে আদতে কত দূর এগিয়ে যাওয়া যায়?
বারনই নদ ধুঁকছে। যে গম্ভীরা গানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, সে গানও তো হুমকির মুখে। লোকজ সংস্কৃতি বাঁচানোর কার্যকর কোনো পথের দিশা কি দেখা যাচ্ছে কোথাও? নদটি বাঁচাতে হলে সবার আগে নদের এই দুর্দশা কেন হলো, সেটা খুঁজে বের করে তার প্রতিকার করতে হবে। নদটিকে ভালো না বাসলে এর ললাটে মৃত্যুই লেখা আছে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা যেন একটি বেনারসি শাড়ির আঁচল, যার এক প্রান্তে সোনালি জরির কাজ আর অন্য প্রান্তে গলিত সুতোয় দাগ পড়া দারিদ্র্যের ছাপ। একই চাদরে ঢাকা দুটি পৃথিবী, যার একটি অস্তিত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং অন্যটি বিলাসিতায় গা ভাসানোর মতো। একদিকে বৈভবের বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে প্রয়োজনের হাহাকার।
১৯ আগস্ট ২০২৫
আজকে সারা বিশ্বে শিশুরা ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার। এটা যে শুধু যুদ্ধ কিংবা সংঘাতসংকুল অঞ্চলে ঘটছে, তা-ই নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও এ-জাতীয় সহিংসতা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে, গত বছর বিশ্বব্যাপী ২২ হাজারের বেশি শিশুর কুশল এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারই
১৪ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভোগ নিরসনে এসে নিজেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা। উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর
১৪ ঘণ্টা আগে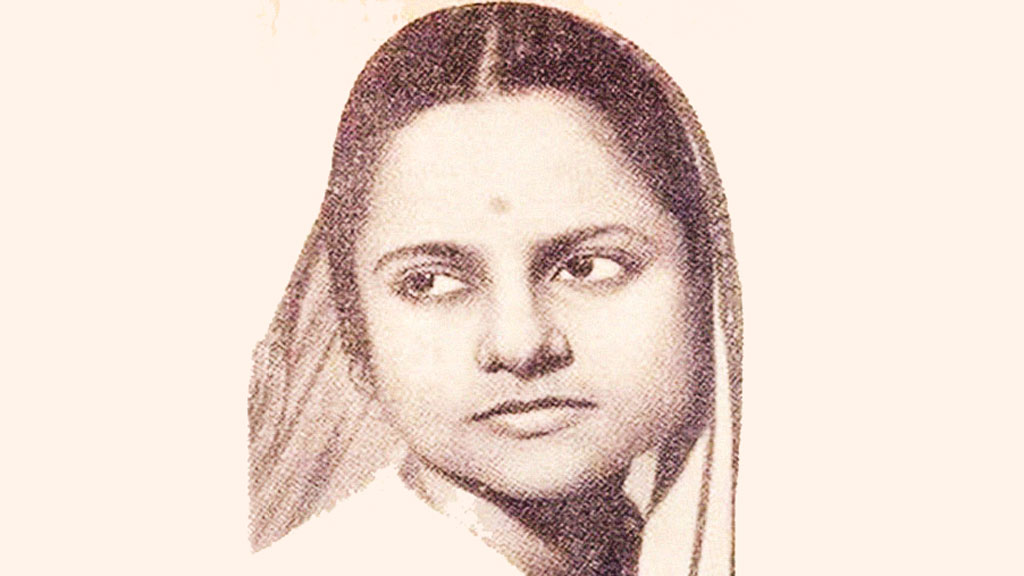
মীরা দেববর্মন ছিলেন বাংলা গানের এক অসামান্য গীতিকার, যিনি কৃতী স্বামী এবং সন্তানের নামের আড়ালে ছড়িয়ে গিয়ে জড়িয়ে আছেন আপন সৃষ্টির কারণেই। অনেকের হয়তো জানা নেই, আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি প্রয়াত শচীন দেববর্মনের স্ত্রী এবং উপমহাদেশের আরেক কিংবদন্তি সুরকার রাহুল দেববর্মনের মাতা মীরা দেববর্মন অসংখ্য জন
১৫ ঘণ্টা আগে