সেলিম জাহান
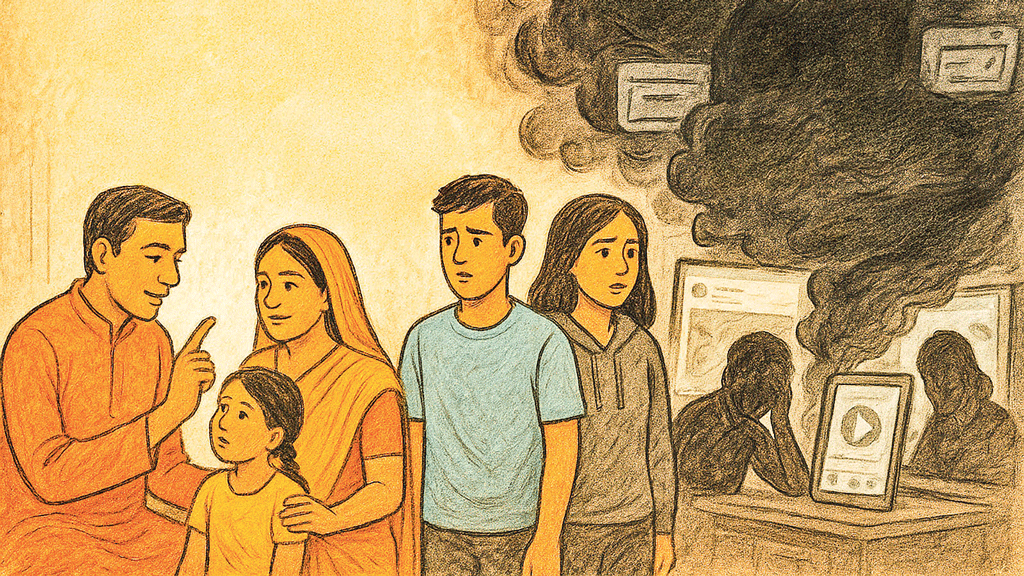
আর পাঁচজনের মতো গালিগালাজে আমার হাতেখড়ি ছোটবেলাতেই। অন্য দশজনের মতো এ বিষয়ে আমার দীক্ষা বন্ধুদের কাছেই। কোনো কোনো বন্ধুর গালিগালাজের সম্ভার ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তাদের মধ্যে একজনের গালিগালাজের সম্ভার শুধু আভিধানিক পর্যায়ের ছিল, তাই সেই সম্ভারের যথাসময়ে এবং যথাযথ প্রয়োগের শৈল্পিক প্রয়োগের পারঙ্গমতায় আমরা অবাক মানতাম। বরিশালের মতো মফস্বল শহরে বেড়ে উঠেছি, তাই আমাদের গালিগালাজের আধার যেমন ছিল সর্বজনীন, তেমনি সেই আধারে বরিশালের স্থানীয় লোকজ গালিগালাজও ছিল। পাকিস্তানের কারণে উর্দু গালি ব্যবহারের রেওয়াজ আমাদের কালে ছিল।
কিন্তু গালিগালাজের জ্ঞান সঞ্চয় এবং বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমার কোনো লাভ হলো না। সেই জ্ঞানভান্ডার ব্যবহারের কোনো সুযোগই পেলাম না দুটি কারণে। এক. ভালো ছাত্র হওয়ায় বরিশাল শহরে একটু-আধটু জানাশোনা ছিল বলে আমার মুখ থেকে গালি বেরোবে, এটা ছিল নৈবচ নৈবচ—এমনকি আমার গালিগালাজের দীক্ষাগুরু বন্ধুদের কাছেও। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য। একবার শুধু রাস্তায় রেগে গিয়ে একটি গালি দিয়েছিলাম বলে পাশের দোকান থেকে অশ্বিনীদা বেরিয়ে এসে আমার গালে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং অধীত বিদ্যা ব্যবহারের কোনো সুযোগই আমার থাকল না।
তা ছাড়া আমার যেসব বন্ধুবান্ধব কথায় কথায় গালি বা খিস্তির শব্দ ব্যবহার করত, খেয়াল করে দেখলাম যে তাদের বাড়ির ভেতরেও গালির চল ছিল। তাদের মা-বাবাও গালিগালাজ করতেন। আমাদের বাড়িতে তার কোনো সুযোগই ছিল না। আমার বাবার গালি শব্দ ছিল একটাই—‘বদমাশ’—ভদ্রলোক সারা জীবনে এর ওপরে আর উঠতে পারলেন না। আমার মায়ের গালির শব্দভান্ডার আরেকটু বিস্তৃত ছিল—‘শয়তান’, ‘বান্দর’, ‘ইবলিস’, ‘বদমাইশ’ ইত্যাদি। তবে এগুলো গালি পদবাচ্য কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং এই শব্দাবলি অভ্রান্তভাবে নিক্ষিপ্ত হতো তাঁর সন্তানদের প্রতি। ভদ্রমহিলাকে আমরা আসলে কম জ্বালাইনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নানান ইংরেজি গালি শেখা গেল ইংরেজি মাধ্যমে পড়া বান্ধবদের কল্যাণে। তবে বাংলা মাধ্যমে পড়ার কারণে সব ইংরেজি গালির অর্থ যে বুঝি, তা নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত অঙ্গন—সুতরাং বুঝে, না বুঝে আমি সেসব গালিগালাজের যত্রতত্র ব্যবহার করতে থাকলাম। একদিন একটি বাক্যে এমন একটি গালি ব্যবহার করার পর ক্যাডেট কলেজে পড়া এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি যে শব্দটি ব্যবহার করলে, তার মানে কি তুমি জানো?’ আমার ‘না’ উত্তর শুনে সে আমাকে বলল, ‘শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জঘন্য।’ সে শব্দটির অর্থ বলে খুব শান্ত স্বরে আমাকে বলল, ‘যে শব্দের মানে তুমি জানো না, সে শব্দ তোমার ব্যবহার করা উচিত নয়।’ সেদিন যে শিক্ষা আমার বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তা সারা জীবন মেনে চলেছি।
গালিগালাজের ব্যাপারে তিনটি বিষয় চিরকাল জেনে এসেছি। প্রথমত, সাধারণ ভাষা এবং গালির ভাষার মধ্যে যোজন দূরত্ব আছে। এখন যে ভাষা অনবরত ব্যবহার করা হচ্ছে বলায়, লেখায় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, সেখানে সাধারণ ভাষা আর গালির ভাষার মধ্যকার ভিন্নতা অপসৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও দেখেছি, মানুষ গালির ভাষা ব্যবহার করে, যখন সে রেগে যায়, অন্যকে ছোট করতে চায়, পরিহাস করতে চায়। তবে সাধারণ অবস্থায় মানুষ গালির ভাষা ব্যবহার করে না।
দ্বিতীয়ত, গালিগালাজের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অমার্জিত ভাব। সাধারণ ভাষার একধরনের পরিশীলন থাকে। সে ভাষা প্রমিত হতে হবে, এমনটা নয়, কিন্তু সেটা মার্জিত হয়। সেই মার্জিত ব্যাপার গালিগালাজে থাকে না। সেই ভাষা বড় নগ্ন। সাধারণ ভাষার একটি সর্বজনগ্রাহ্যতা থাকে, গালিগালাজে একটি বিভাজন থাকে। সব গালিগালাজ সর্বত্র সমভাবে ব্যবহার করা হয় না—তার স্থান পরিপ্রেক্ষিত আছে, গোষ্ঠী পরিপ্রেক্ষিত আছে, বয়স পরিপ্রেক্ষিত আছে।
তৃতীয়ত, কথ্য ভাষা আর গালির ভাষা এক নয়। প্রমিত ভাষা নয় কথ্য ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা; কিন্তু সেগুলো গালির ভাষা নয়। নানান আঞ্চলিক ভাষায় নানান কথ্য শব্দ আছে, যেগুলো হয়তো পরিশীলিত নয়, হয়তো সেগুলো অশ্লীল, কিন্তু গালিগালাজ নয়।
সব গালিগালাজের মধ্যে একধরনের অশ্লীলতার গন্ধ থাকে, কিন্তু সব অশ্লীল শব্দই গালি নয়।
আজ জীবনের এ প্রান্তে এসে বর্তমান সময়ে মানুষের কথায়, লেখায়, মন্তব্যে আমি হতবুদ্ধি, বড় অসহায় বোধ করছি, অনেকটা দিশেহারাও বলা চলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তো বটেই, নাটকেও গালাগালির ছড়াছড়ি। জানি এবং মানি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন ঘটে, শব্দসম্ভার বদলায়, গালিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি প্রজন্মই তাদের প্রজন্মের জন্য কিছু নির্বাচিত শব্দের প্রচলন ও ব্যবহার শুরু করে, নতুন নতুন গালিও আবিষ্কার করে। পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে আবার বদলায়। কিন্তু সাধারণ ভাষা আর গালির ভাষার পার্থক্য বজায় থাকে।
অথচ বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখি যে গালির ভাষাই কখন যেন সাধারণ বক্তব্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গালির ভাষা ভিন্ন কথা হয় না, বলা হয় না, লেখা হয় না। কারও বক্তব্যের সঙ্গে মতের অমিল হলে সাধারণ ভাষায় তাকে তা বলা হয় না, বলা হয় গালি দিয়ে। কাউকে পছন্দ না হলে গালির মাধ্যমে তার চরিত্র হনন করা হয়। গালির তুবড়ি ছুটিয়ে কাউকে অপদস্থ করা হয়। দেখেশুনে মনে হয়, গালিগালাজ আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সেই গালিগালাজের একটি মূল আঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অশ্লীলতা। কাউকে গালি দিতে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো চরম অশ্লীল।
তিনটি বিষয় আমাকে শঙ্কিত করে। এক. আমি খুব অবাক বিস্ময়ে দেখি যে যাঁদের আমি শিক্ষিত, মার্জিত, সুকুমারবৃত্তির সঙ্গে জড়িত মনে করি, তাঁরাও আজ গালিগালাজের সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছেন, সেই বলয়ে বিচরণ করছেন। জানি না এর কারণ কী। তরুণদের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের জননন্দিতা বৃদ্ধির জন্য, নাকি এটাকে আধুনিকতা ভেবে আধুনিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়?
দুই. তরুণসমাজ এই গালিগালাজের সংস্কৃতির মধ্যেই তাদের আত্মসত্তা এবং আত্মপরিচয়কে সম্পৃক্ত করেছে। এটা কি তাদের বিদ্রোহ, নাকি এর মধ্যেই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য তারা খুঁজছে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আত্মপরিচয় প্রকাশের, স্বকীয়তা প্রতিস্থাপনের আরও তো নানান রকমের পন্থা আছে। সেখানে অশ্লীল গালিগালাজের পথই কি শ্রেয়?
তিন. গালিগালাজের ক্ষেত্রে একরকমের শ্রেণিভেদ আছে। যেমন আমরা বন্ধুদের ক্ষেত্রে যে গালি দিতাম, তা আর কারও প্রতি ব্যবহার করতাম না। কিন্তু আজ ছোটরা নির্বিচার যেসব গালিগালাজ বড়দের প্রতি ছুড়ে দেয়, তা অচিন্তনীয়। বড়দের ক্ষেত্রেও এখন সে কথা প্রযোজ্য।
শেষের কথা বলি। গালিগালাজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু তা একটি জাতির সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে, জাতির সংস্কৃতি হতে পারে না। আমরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হই।
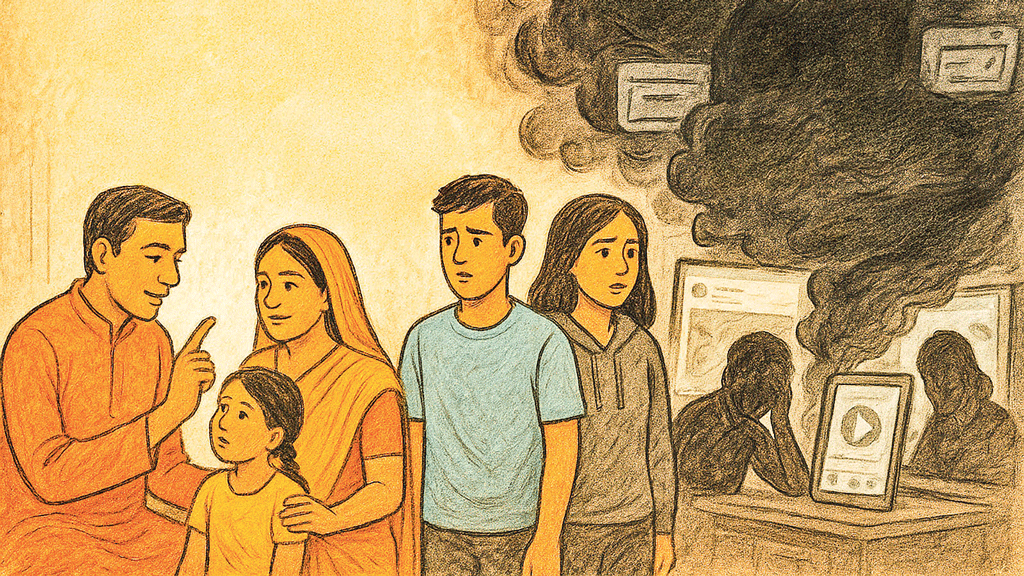
আর পাঁচজনের মতো গালিগালাজে আমার হাতেখড়ি ছোটবেলাতেই। অন্য দশজনের মতো এ বিষয়ে আমার দীক্ষা বন্ধুদের কাছেই। কোনো কোনো বন্ধুর গালিগালাজের সম্ভার ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তাদের মধ্যে একজনের গালিগালাজের সম্ভার শুধু আভিধানিক পর্যায়ের ছিল, তাই সেই সম্ভারের যথাসময়ে এবং যথাযথ প্রয়োগের শৈল্পিক প্রয়োগের পারঙ্গমতায় আমরা অবাক মানতাম। বরিশালের মতো মফস্বল শহরে বেড়ে উঠেছি, তাই আমাদের গালিগালাজের আধার যেমন ছিল সর্বজনীন, তেমনি সেই আধারে বরিশালের স্থানীয় লোকজ গালিগালাজও ছিল। পাকিস্তানের কারণে উর্দু গালি ব্যবহারের রেওয়াজ আমাদের কালে ছিল।
কিন্তু গালিগালাজের জ্ঞান সঞ্চয় এবং বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমার কোনো লাভ হলো না। সেই জ্ঞানভান্ডার ব্যবহারের কোনো সুযোগই পেলাম না দুটি কারণে। এক. ভালো ছাত্র হওয়ায় বরিশাল শহরে একটু-আধটু জানাশোনা ছিল বলে আমার মুখ থেকে গালি বেরোবে, এটা ছিল নৈবচ নৈবচ—এমনকি আমার গালিগালাজের দীক্ষাগুরু বন্ধুদের কাছেও। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য। একবার শুধু রাস্তায় রেগে গিয়ে একটি গালি দিয়েছিলাম বলে পাশের দোকান থেকে অশ্বিনীদা বেরিয়ে এসে আমার গালে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং অধীত বিদ্যা ব্যবহারের কোনো সুযোগই আমার থাকল না।
তা ছাড়া আমার যেসব বন্ধুবান্ধব কথায় কথায় গালি বা খিস্তির শব্দ ব্যবহার করত, খেয়াল করে দেখলাম যে তাদের বাড়ির ভেতরেও গালির চল ছিল। তাদের মা-বাবাও গালিগালাজ করতেন। আমাদের বাড়িতে তার কোনো সুযোগই ছিল না। আমার বাবার গালি শব্দ ছিল একটাই—‘বদমাশ’—ভদ্রলোক সারা জীবনে এর ওপরে আর উঠতে পারলেন না। আমার মায়ের গালির শব্দভান্ডার আরেকটু বিস্তৃত ছিল—‘শয়তান’, ‘বান্দর’, ‘ইবলিস’, ‘বদমাইশ’ ইত্যাদি। তবে এগুলো গালি পদবাচ্য কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং এই শব্দাবলি অভ্রান্তভাবে নিক্ষিপ্ত হতো তাঁর সন্তানদের প্রতি। ভদ্রমহিলাকে আমরা আসলে কম জ্বালাইনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নানান ইংরেজি গালি শেখা গেল ইংরেজি মাধ্যমে পড়া বান্ধবদের কল্যাণে। তবে বাংলা মাধ্যমে পড়ার কারণে সব ইংরেজি গালির অর্থ যে বুঝি, তা নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত অঙ্গন—সুতরাং বুঝে, না বুঝে আমি সেসব গালিগালাজের যত্রতত্র ব্যবহার করতে থাকলাম। একদিন একটি বাক্যে এমন একটি গালি ব্যবহার করার পর ক্যাডেট কলেজে পড়া এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি যে শব্দটি ব্যবহার করলে, তার মানে কি তুমি জানো?’ আমার ‘না’ উত্তর শুনে সে আমাকে বলল, ‘শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জঘন্য।’ সে শব্দটির অর্থ বলে খুব শান্ত স্বরে আমাকে বলল, ‘যে শব্দের মানে তুমি জানো না, সে শব্দ তোমার ব্যবহার করা উচিত নয়।’ সেদিন যে শিক্ষা আমার বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তা সারা জীবন মেনে চলেছি।
গালিগালাজের ব্যাপারে তিনটি বিষয় চিরকাল জেনে এসেছি। প্রথমত, সাধারণ ভাষা এবং গালির ভাষার মধ্যে যোজন দূরত্ব আছে। এখন যে ভাষা অনবরত ব্যবহার করা হচ্ছে বলায়, লেখায় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, সেখানে সাধারণ ভাষা আর গালির ভাষার মধ্যকার ভিন্নতা অপসৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও দেখেছি, মানুষ গালির ভাষা ব্যবহার করে, যখন সে রেগে যায়, অন্যকে ছোট করতে চায়, পরিহাস করতে চায়। তবে সাধারণ অবস্থায় মানুষ গালির ভাষা ব্যবহার করে না।
দ্বিতীয়ত, গালিগালাজের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অমার্জিত ভাব। সাধারণ ভাষার একধরনের পরিশীলন থাকে। সে ভাষা প্রমিত হতে হবে, এমনটা নয়, কিন্তু সেটা মার্জিত হয়। সেই মার্জিত ব্যাপার গালিগালাজে থাকে না। সেই ভাষা বড় নগ্ন। সাধারণ ভাষার একটি সর্বজনগ্রাহ্যতা থাকে, গালিগালাজে একটি বিভাজন থাকে। সব গালিগালাজ সর্বত্র সমভাবে ব্যবহার করা হয় না—তার স্থান পরিপ্রেক্ষিত আছে, গোষ্ঠী পরিপ্রেক্ষিত আছে, বয়স পরিপ্রেক্ষিত আছে।
তৃতীয়ত, কথ্য ভাষা আর গালির ভাষা এক নয়। প্রমিত ভাষা নয় কথ্য ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা; কিন্তু সেগুলো গালির ভাষা নয়। নানান আঞ্চলিক ভাষায় নানান কথ্য শব্দ আছে, যেগুলো হয়তো পরিশীলিত নয়, হয়তো সেগুলো অশ্লীল, কিন্তু গালিগালাজ নয়।
সব গালিগালাজের মধ্যে একধরনের অশ্লীলতার গন্ধ থাকে, কিন্তু সব অশ্লীল শব্দই গালি নয়।
আজ জীবনের এ প্রান্তে এসে বর্তমান সময়ে মানুষের কথায়, লেখায়, মন্তব্যে আমি হতবুদ্ধি, বড় অসহায় বোধ করছি, অনেকটা দিশেহারাও বলা চলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তো বটেই, নাটকেও গালাগালির ছড়াছড়ি। জানি এবং মানি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন ঘটে, শব্দসম্ভার বদলায়, গালিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি প্রজন্মই তাদের প্রজন্মের জন্য কিছু নির্বাচিত শব্দের প্রচলন ও ব্যবহার শুরু করে, নতুন নতুন গালিও আবিষ্কার করে। পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে আবার বদলায়। কিন্তু সাধারণ ভাষা আর গালির ভাষার পার্থক্য বজায় থাকে।
অথচ বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখি যে গালির ভাষাই কখন যেন সাধারণ বক্তব্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গালির ভাষা ভিন্ন কথা হয় না, বলা হয় না, লেখা হয় না। কারও বক্তব্যের সঙ্গে মতের অমিল হলে সাধারণ ভাষায় তাকে তা বলা হয় না, বলা হয় গালি দিয়ে। কাউকে পছন্দ না হলে গালির মাধ্যমে তার চরিত্র হনন করা হয়। গালির তুবড়ি ছুটিয়ে কাউকে অপদস্থ করা হয়। দেখেশুনে মনে হয়, গালিগালাজ আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সেই গালিগালাজের একটি মূল আঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অশ্লীলতা। কাউকে গালি দিতে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো চরম অশ্লীল।
তিনটি বিষয় আমাকে শঙ্কিত করে। এক. আমি খুব অবাক বিস্ময়ে দেখি যে যাঁদের আমি শিক্ষিত, মার্জিত, সুকুমারবৃত্তির সঙ্গে জড়িত মনে করি, তাঁরাও আজ গালিগালাজের সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছেন, সেই বলয়ে বিচরণ করছেন। জানি না এর কারণ কী। তরুণদের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের জননন্দিতা বৃদ্ধির জন্য, নাকি এটাকে আধুনিকতা ভেবে আধুনিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়?
দুই. তরুণসমাজ এই গালিগালাজের সংস্কৃতির মধ্যেই তাদের আত্মসত্তা এবং আত্মপরিচয়কে সম্পৃক্ত করেছে। এটা কি তাদের বিদ্রোহ, নাকি এর মধ্যেই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য তারা খুঁজছে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আত্মপরিচয় প্রকাশের, স্বকীয়তা প্রতিস্থাপনের আরও তো নানান রকমের পন্থা আছে। সেখানে অশ্লীল গালিগালাজের পথই কি শ্রেয়?
তিন. গালিগালাজের ক্ষেত্রে একরকমের শ্রেণিভেদ আছে। যেমন আমরা বন্ধুদের ক্ষেত্রে যে গালি দিতাম, তা আর কারও প্রতি ব্যবহার করতাম না। কিন্তু আজ ছোটরা নির্বিচার যেসব গালিগালাজ বড়দের প্রতি ছুড়ে দেয়, তা অচিন্তনীয়। বড়দের ক্ষেত্রেও এখন সে কথা প্রযোজ্য।
শেষের কথা বলি। গালিগালাজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু তা একটি জাতির সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে, জাতির সংস্কৃতি হতে পারে না। আমরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হই।

দেশে মনে হয় সাহিত্যচর্চা ভালোই চলছে; বিশেষ করে রাজশাহীর বিভিন্ন জেলায়—অন্তত পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের লেখা বইগুলো তো তা-ই বলে। পুলিশের চাকরির সুবাদে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই লেখা যায় তদন্ত, আইনকানুন, নিয়মনীতি ও প্রশিক্ষণবিষয়ক বই। তাঁরা দায়িত্বের ফাঁকে এসব বই লেখেন, আর সেসব নাকি শত শত ক্রেতা...
১১ ঘণ্টা আগে
ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে লালনের গান যখন ছড়িয়ে পড়া শুরু করল শহর থেকে নগরে, দেশের আনাচকানাচে; অভিযোগের তিরটাও ধেয়ে এল তাঁর দিকে। লালনের আখড়ায় গান করেন এমন অনেকে অভিযোগ তুললেন, ও তো ঠিকঠাক গাইতেই জানে না সাঁইজির গান। ফরিদা পারভীন বললেন, ‘অভিযোগ তো করতেই পারে, যেহেতু কোনো বাউলতান্ত্রিকতা...
১১ ঘণ্টা আগে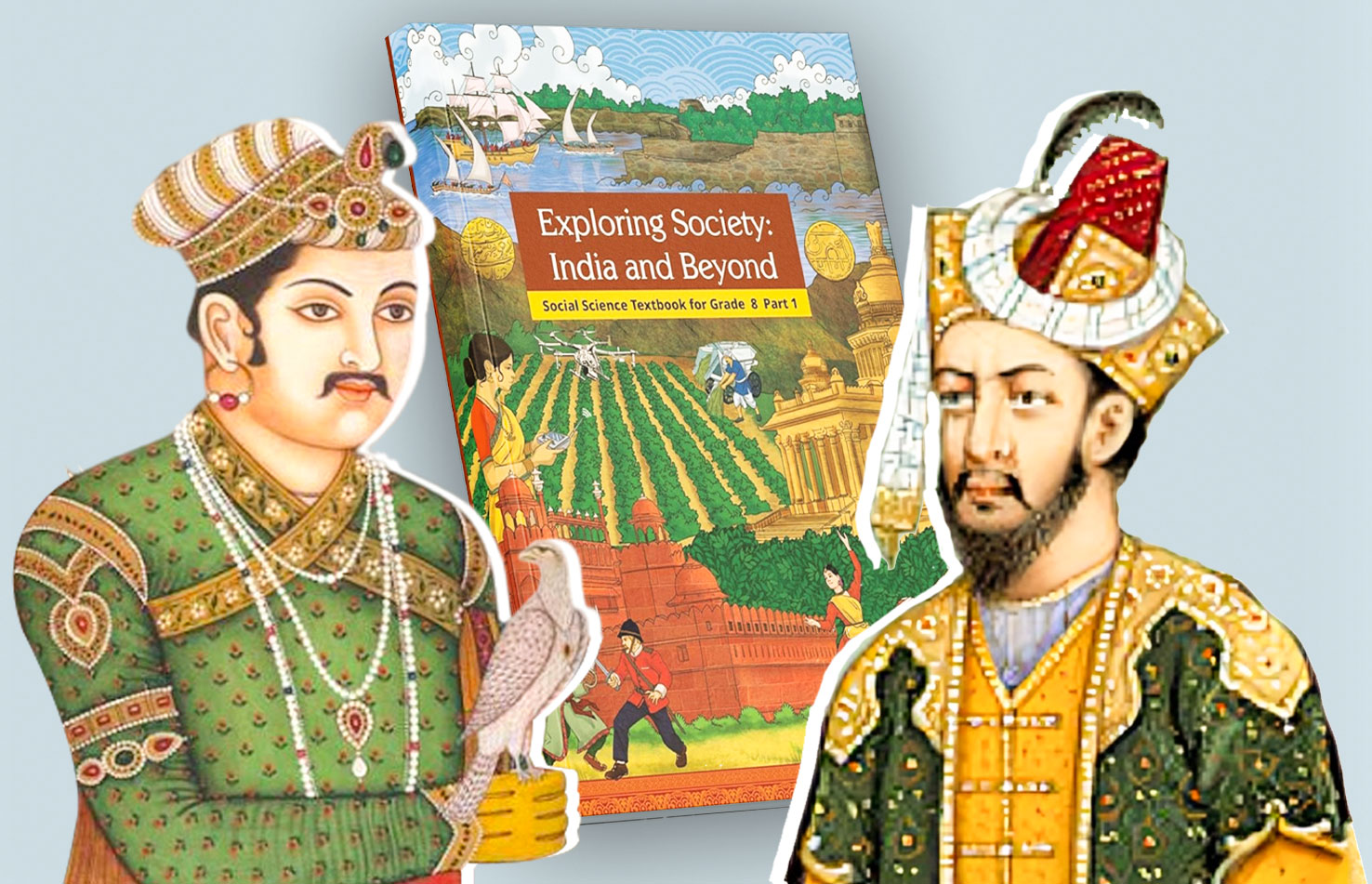
১৯৩৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের আগপর্যন্ত ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের দাবি ছিল মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি ডোমিনিয়ন বা অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে এর তিন মাস পর ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত...
১ দিন আগে
নেদারল্যান্ডসের ডেন হেগ শহরে ভাতের রেস্তোরাঁ খুঁজে ফিরছিলাম। ভারতীয় রেস্তোরাঁ একটা পাওয়া গেল, নাম ‘রমনা’। নাম শুনেই বললাম, এটা বাংলাদেশিই হবে। গত শতকের ষাট-সত্তরের দশকে ঢাকায় এই নামে একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁ ছিল। আমরা যে হোটেলে ছিলাম তার থেকে হাঁটা পথ দূরত্বে, সদলবলে চললাম রমনার...
১ দিন আগে