এম এস রানা, ঢাকা

ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে লালনের গান যখন ছড়িয়ে পড়া শুরু করল শহর থেকে নগরে, দেশের আনাচকানাচে; অভিযোগের তিরটাও ধেয়ে এল তাঁর দিকে। লালনের আখড়ায় গান করেন এমন অনেকে অভিযোগ তুললেন, ও তো ঠিকঠাক গাইতেই জানে না সাঁইজির গান। ফরিদা পারভীন বললেন, ‘অভিযোগ তো করতেই পারে, যেহেতু কোনো বাউলতান্ত্রিকতা নিয়ে আমি গান করি না। হয়তো এই অনুভূতিতে তাঁদের মনে হতে পারে, আমার গলা থেকে (লালনের গান) তাঁদের মতন হয় না। তবে চেষ্টা করি, সততার সঙ্গে গান করি, লালন ফকিরের গান।’
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কুষ্টিয়ায় দোলপূর্ণিমার মহাসমাবেশে প্রথমবার লালনের গান পরিবেশন করেন ফরিদা পারভীন। এর পেছনেও রয়েছে এক গল্প। গুরু মকছেদ আলী সাঁই তাঁকে বলেছিলেন দোলপূর্ণিমায় লালনের একটা গান গাইতে। ফরিদা পারভীন তখন ক্ল্যাসিক্যাল চর্চা করেন এবং নজরুলসংগীত করেন। লালন ফকিরের গানের কথা শুনে তাই তাচ্ছিল্য নিয়ে বলেছিলেন, এসব ফকির-ফাকরার গান আমার ভালো লাগে না। মেয়ের অনীহা দেখে বাবা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালেন। বললেন, ‘ভালো না লাগলে আর গাইবি না।’ এরপর মকছেদ আলীর কাছে তালিম নিলেন ফরিদা পারভীন।
দোলপূর্ণিমার মহাসমাবেশে গাইলেন ‘সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন’। গান শুনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন শ্রোতারা। অনুরোধ জানান আরও গাইবার। কিন্তু তিনি তো এই একটি গানই শিখেছেন। সেই গান দিয়েই লালনের ভাবজগতে প্রবেশ ফরিদা পারভীনের। এরপর যতই পাড়ি দিয়েছেন পথ, মুগ্ধ হয়েছেন লালনের গানে ও বাণীতে। ভাবনার অতলে তল খুঁজেছেন সাঁইজির আধ্যাত্মিকতায় ও দর্শনে। এক একে সব ছেড়েছেন, নজরুল কিংবা আধুনিক, বুকের মাঝে ধারণ করেছেন কেবল লালন। মকছেদ আলী সাঁই, খোদা বক্স সাঁই, করিম সাঁই, ব্রজেন দাসসহ গুরুপরম্পরার সাধকদের কাছে তালিম নিয়েছেন। ধীরে ধীরে লালনের বাণীর মর্মার্থ বুঝেছেন, আধ্যাত্মিকতা ও বাউলদর্শনের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা বেড়েছে, ভক্তি বেড়েছে। লালনের গানে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন। ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে লালনের গান কেবলই এক সংগীত নয়, হয়ে ওঠে অনন্য এক জীবনদর্শন।
১৯৭৩ সালে বাউলশিল্পীদের ঢাকায় এনে লালনের গান রেকর্ডের পরিকল্পনা করেন ওস্তাদ মকছেদ আলী। তিনি তখন রেডিওর ট্রান্সক্রিপশনে কর্মরত। তাঁর আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন ফরিদা পারভীন। ১৫ মিনিটের একটি একক সংগীতানুষ্ঠান করতে হবে। আবদুল হামিদ চৌধুরী, কমল দাশগুপ্ত, সমর দাসের মতো গুণীজনদের সামনে সেদিন ভয়ে বুকটা ঢিপঢিপ করলেও কণ্ঠের জোরে ঠিকই প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন। পরের বছর থেকে গানের প্রয়োজনে প্রায় নিয়মিতই তাঁর ঢাকায় আসতে হতো। এসে উঠতেন পুরানা পল্টনের মেট্রোপলিটন হোটেলে। দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর এই হোটেল হয়ে উঠেছিল তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি। ১৯৯৬ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন ফরিদা পারভীন।
লালনের গানের আগে আধুনিক গানে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ফরিদা পারভীন। তাঁর গাওয়া ‘এই পদ্মা এই মেঘনা’, ‘তোমরা ভুলেই গেছ মল্লিকাদির নাম’, ‘তুমি রাত আমি রাতজাগা পাখি’, ‘বুকের পাথরগুলো কিছুতেই সরানো গেল না’ কিংবা ‘ও পাখি রে আয় দেখে যা কেমন আছি’—এসব গান এখনো শ্রোতাদের মন উদ্বেলিত করে।
ফরিদা পারভীনের জন্ম ১৯৫৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর, নাটোরে। চিকিৎসক বাবা দেলোয়ার হোসেনকে পেশাগত কারণে থাকতে হয়েছে নানা শহরে। ফরিদা পারভীনের শৈশবটাও তাই রঙিন হয়েছে বিভিন্ন শহরের আলোয়। তবে জীবনের সিংহভাগ সময় তাঁর কেটেছে কুষ্টিয়ায়। তাই অনেকে ভাবতেন, তিনি বুঝি কুষ্টিয়ার মেয়ে। কুষ্টিয়ায় মীর মশাররফ হোসেন বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স পাস করেন। বিয়ে করেছিলেন প্রখ্যাত গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী আবু জাফরকে। তাঁদের চার সন্তান—এক মেয়ে, তিন ছেলে। আবু জাফরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ২০০৫ সালে প্রখ্যাত বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিমকে বিয়ে করেন ফরিদা পারভীন।
৫ বছর বয়সে মাগুরায় কমল চক্রবর্তীর কাছে গানের হাতেখড়ি ফরিদা পারভীনের। এরপর শিখেছেন ওস্তাদ মীর মোজাফফর আলী, রবীন্দ্রনাথ রায়, ইব্রাহিম খান, মোতালেব বিশ্বাস, আবদুল গণির কাছে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রাজশাহী বেতারে নজরুলশিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন ফরিদা পারভীন। নজরুল, আধুনিক আর দেশাত্মবোধক গানে যাত্রা শুরু হলেও শেষাবধি লালনেই সিদ্ধ ও ঋদ্ধ হয়েছেন তিনি। কিন্তু কেন ছাড়লেন নজরুলসংগীত কিংবা আধুনিক গান? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘একসময় আমার ভেতরে আরজি হলো—আমি তো নজরুলের গান গেয়ে ফিরোজা বেগম হতে পারব না। আধুনিক গান করে ফেরদৌসী রহমান হতে পারব না, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হতে পারব না। সে জন্য আমার কণ্ঠে লালন সাঁইজির গান যখন শ্রোতারা ভালোবেসে গ্রহণ করল, আমার ভেতরে একটা ঐশ্বরিক অনুরণন ঘটেছিল যে, সাঁইজির গান করলেই সবচাইতে ভালো হবে।’
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরি স্কেচ, রণজিৎ কুমার, পরেশ ভট্টাচার্য কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস, সুনির্মল বসু, শওকত ওসমানের ছোটগল্প, সৈয়দ হাসান ইমাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তানভীর মোকাম্মেল কিংবা গৌতম ঘোষের সিনেমা লালনকে চিনিয়েছে, জানিয়েছে লালনের জীবন সম্পর্কে। অন্যদিকে ফরিদা পারভীন লালন সাঁইজির গানকে, তাঁর বাণীকে আখড়া থেকে তুলে এনে দেশে, বিদেশে, সাধারণ থেকে অসাধারণে ছড়িয়ে দিয়েছেন, জনপ্রিয় করেছেন। তাঁর পরিশীলিত আর আধুনিক কণ্ঠ লালনের গানকে মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রোতার কাছে সমাদৃত করেছে। গাজী আবদুল হাকিম বলেছিলেন, ‘লালনের গানকে আখড়া থেকে তুলে সারা পৃথিবীর ড্রইংরুমে পৌঁছে দিয়েছেন ফরিদা পারভীন।’ সংগীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফরিদা পারভীন পেয়েছেন একুশে পদক (১৯৮৭), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩), জাপানের ফুকুওয়াকা পুরস্কারসহ (২০০৮) অসংখ্য পুরস্কার। বিবিসির জরিপেও সর্বকালের সেরা বাংলা গানের তালিকায় রয়েছে তাঁর গাওয়া গান।
মূলধারায় লালনের গান বা আধুনিকায়ন নিয়েও ফরিদা পারভীনের ভাবনা ছিল ইতিবাচক। তবে না জেনে, না বুঝে লালনের বাণী ও সুর নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার পক্ষে ছিলেন না। কেননা এতে সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংস হয় বেশি। তাই তিনি বলেছেন, ‘লালনের যে বাণী, সাঁইজির যে গান, সেটা দীর্ঘদিন আখড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই নগরের শিল্পীদের কণ্ঠে এসে তা নতুন মাত্রা পেল। রবীন্দ্রনাথের গান যেমন হেমন্তের কণ্ঠে এসে নতুন মাত্রা পেল, অনেকটা তেমন। মূলধারায় আসতেই হবে। আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারে আমার আপত্তি নাই। মূল সুরটা ঠিক রেখে, বাণী ঠিক রেখে যদি করা যায়, সেটা ভালো কিছুই
বয়ে আনবে। তবে যন্ত্রের ঝনঝনানি যেন গানকে ছাপিয়ে না যায়। অনেকে ফিউশনের নামে কনফিউশন তৈরি করছেন। এটা উচিত নয়।’
ফরিদা পারভীনের মতে, সংগীত হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু ধরে, মৃত্যুর আগপর্যন্ত একে ভালোবেসে যেতে হয়, ভালোবেসে গ্রহণ করতে হয়, চর্চা চালিয়ে যেতে হয়। তিনিও আমৃত্যু লালনকে ধারণ করেছেন, নতুন প্রজন্মের মাঝে লালনকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। লালনের গান শেখানোর জন্য অচিন পাখি নামে স্কুল গড়েছেন। মনের বাসনা ব্যক্ত করে বলেছেন, ‘সাঁইজি যেমন তাঁর শিষ্যদের মাঝে বেঁচে আছেন, আমার মাঝে আমার গুরু বেঁচে আছেন, তেমনি আমার অচিন পাখির ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আমি বেঁচে থাকতে চাই।’
ফরিদা পারভীন জানতেন, মানুষের মনে বেঁচে থাকাটাই প্রকৃত অমরত্ব। সেই অমরত্ব লাভের আশাতেই কি পরম স্রষ্টা—মনের মানুষের সনে মিলনের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাঁর মন? ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে সে জন্যই কি থেমে গেলেন তিনি, আমাদের মাঝে রেখে গেলেন তাঁর কর্মযজ্ঞ।

ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে লালনের গান যখন ছড়িয়ে পড়া শুরু করল শহর থেকে নগরে, দেশের আনাচকানাচে; অভিযোগের তিরটাও ধেয়ে এল তাঁর দিকে। লালনের আখড়ায় গান করেন এমন অনেকে অভিযোগ তুললেন, ও তো ঠিকঠাক গাইতেই জানে না সাঁইজির গান। ফরিদা পারভীন বললেন, ‘অভিযোগ তো করতেই পারে, যেহেতু কোনো বাউলতান্ত্রিকতা নিয়ে আমি গান করি না। হয়তো এই অনুভূতিতে তাঁদের মনে হতে পারে, আমার গলা থেকে (লালনের গান) তাঁদের মতন হয় না। তবে চেষ্টা করি, সততার সঙ্গে গান করি, লালন ফকিরের গান।’
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কুষ্টিয়ায় দোলপূর্ণিমার মহাসমাবেশে প্রথমবার লালনের গান পরিবেশন করেন ফরিদা পারভীন। এর পেছনেও রয়েছে এক গল্প। গুরু মকছেদ আলী সাঁই তাঁকে বলেছিলেন দোলপূর্ণিমায় লালনের একটা গান গাইতে। ফরিদা পারভীন তখন ক্ল্যাসিক্যাল চর্চা করেন এবং নজরুলসংগীত করেন। লালন ফকিরের গানের কথা শুনে তাই তাচ্ছিল্য নিয়ে বলেছিলেন, এসব ফকির-ফাকরার গান আমার ভালো লাগে না। মেয়ের অনীহা দেখে বাবা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালেন। বললেন, ‘ভালো না লাগলে আর গাইবি না।’ এরপর মকছেদ আলীর কাছে তালিম নিলেন ফরিদা পারভীন।
দোলপূর্ণিমার মহাসমাবেশে গাইলেন ‘সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন’। গান শুনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন শ্রোতারা। অনুরোধ জানান আরও গাইবার। কিন্তু তিনি তো এই একটি গানই শিখেছেন। সেই গান দিয়েই লালনের ভাবজগতে প্রবেশ ফরিদা পারভীনের। এরপর যতই পাড়ি দিয়েছেন পথ, মুগ্ধ হয়েছেন লালনের গানে ও বাণীতে। ভাবনার অতলে তল খুঁজেছেন সাঁইজির আধ্যাত্মিকতায় ও দর্শনে। এক একে সব ছেড়েছেন, নজরুল কিংবা আধুনিক, বুকের মাঝে ধারণ করেছেন কেবল লালন। মকছেদ আলী সাঁই, খোদা বক্স সাঁই, করিম সাঁই, ব্রজেন দাসসহ গুরুপরম্পরার সাধকদের কাছে তালিম নিয়েছেন। ধীরে ধীরে লালনের বাণীর মর্মার্থ বুঝেছেন, আধ্যাত্মিকতা ও বাউলদর্শনের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা বেড়েছে, ভক্তি বেড়েছে। লালনের গানে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন। ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে লালনের গান কেবলই এক সংগীত নয়, হয়ে ওঠে অনন্য এক জীবনদর্শন।
১৯৭৩ সালে বাউলশিল্পীদের ঢাকায় এনে লালনের গান রেকর্ডের পরিকল্পনা করেন ওস্তাদ মকছেদ আলী। তিনি তখন রেডিওর ট্রান্সক্রিপশনে কর্মরত। তাঁর আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন ফরিদা পারভীন। ১৫ মিনিটের একটি একক সংগীতানুষ্ঠান করতে হবে। আবদুল হামিদ চৌধুরী, কমল দাশগুপ্ত, সমর দাসের মতো গুণীজনদের সামনে সেদিন ভয়ে বুকটা ঢিপঢিপ করলেও কণ্ঠের জোরে ঠিকই প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন। পরের বছর থেকে গানের প্রয়োজনে প্রায় নিয়মিতই তাঁর ঢাকায় আসতে হতো। এসে উঠতেন পুরানা পল্টনের মেট্রোপলিটন হোটেলে। দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর এই হোটেল হয়ে উঠেছিল তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি। ১৯৯৬ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন ফরিদা পারভীন।
লালনের গানের আগে আধুনিক গানে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ফরিদা পারভীন। তাঁর গাওয়া ‘এই পদ্মা এই মেঘনা’, ‘তোমরা ভুলেই গেছ মল্লিকাদির নাম’, ‘তুমি রাত আমি রাতজাগা পাখি’, ‘বুকের পাথরগুলো কিছুতেই সরানো গেল না’ কিংবা ‘ও পাখি রে আয় দেখে যা কেমন আছি’—এসব গান এখনো শ্রোতাদের মন উদ্বেলিত করে।
ফরিদা পারভীনের জন্ম ১৯৫৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর, নাটোরে। চিকিৎসক বাবা দেলোয়ার হোসেনকে পেশাগত কারণে থাকতে হয়েছে নানা শহরে। ফরিদা পারভীনের শৈশবটাও তাই রঙিন হয়েছে বিভিন্ন শহরের আলোয়। তবে জীবনের সিংহভাগ সময় তাঁর কেটেছে কুষ্টিয়ায়। তাই অনেকে ভাবতেন, তিনি বুঝি কুষ্টিয়ার মেয়ে। কুষ্টিয়ায় মীর মশাররফ হোসেন বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স পাস করেন। বিয়ে করেছিলেন প্রখ্যাত গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী আবু জাফরকে। তাঁদের চার সন্তান—এক মেয়ে, তিন ছেলে। আবু জাফরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ২০০৫ সালে প্রখ্যাত বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিমকে বিয়ে করেন ফরিদা পারভীন।
৫ বছর বয়সে মাগুরায় কমল চক্রবর্তীর কাছে গানের হাতেখড়ি ফরিদা পারভীনের। এরপর শিখেছেন ওস্তাদ মীর মোজাফফর আলী, রবীন্দ্রনাথ রায়, ইব্রাহিম খান, মোতালেব বিশ্বাস, আবদুল গণির কাছে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রাজশাহী বেতারে নজরুলশিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন ফরিদা পারভীন। নজরুল, আধুনিক আর দেশাত্মবোধক গানে যাত্রা শুরু হলেও শেষাবধি লালনেই সিদ্ধ ও ঋদ্ধ হয়েছেন তিনি। কিন্তু কেন ছাড়লেন নজরুলসংগীত কিংবা আধুনিক গান? সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘একসময় আমার ভেতরে আরজি হলো—আমি তো নজরুলের গান গেয়ে ফিরোজা বেগম হতে পারব না। আধুনিক গান করে ফেরদৌসী রহমান হতে পারব না, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হতে পারব না। সে জন্য আমার কণ্ঠে লালন সাঁইজির গান যখন শ্রোতারা ভালোবেসে গ্রহণ করল, আমার ভেতরে একটা ঐশ্বরিক অনুরণন ঘটেছিল যে, সাঁইজির গান করলেই সবচাইতে ভালো হবে।’
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরি স্কেচ, রণজিৎ কুমার, পরেশ ভট্টাচার্য কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস, সুনির্মল বসু, শওকত ওসমানের ছোটগল্প, সৈয়দ হাসান ইমাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তানভীর মোকাম্মেল কিংবা গৌতম ঘোষের সিনেমা লালনকে চিনিয়েছে, জানিয়েছে লালনের জীবন সম্পর্কে। অন্যদিকে ফরিদা পারভীন লালন সাঁইজির গানকে, তাঁর বাণীকে আখড়া থেকে তুলে এনে দেশে, বিদেশে, সাধারণ থেকে অসাধারণে ছড়িয়ে দিয়েছেন, জনপ্রিয় করেছেন। তাঁর পরিশীলিত আর আধুনিক কণ্ঠ লালনের গানকে মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রোতার কাছে সমাদৃত করেছে। গাজী আবদুল হাকিম বলেছিলেন, ‘লালনের গানকে আখড়া থেকে তুলে সারা পৃথিবীর ড্রইংরুমে পৌঁছে দিয়েছেন ফরিদা পারভীন।’ সংগীতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফরিদা পারভীন পেয়েছেন একুশে পদক (১৯৮৭), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩), জাপানের ফুকুওয়াকা পুরস্কারসহ (২০০৮) অসংখ্য পুরস্কার। বিবিসির জরিপেও সর্বকালের সেরা বাংলা গানের তালিকায় রয়েছে তাঁর গাওয়া গান।
মূলধারায় লালনের গান বা আধুনিকায়ন নিয়েও ফরিদা পারভীনের ভাবনা ছিল ইতিবাচক। তবে না জেনে, না বুঝে লালনের বাণী ও সুর নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার পক্ষে ছিলেন না। কেননা এতে সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংস হয় বেশি। তাই তিনি বলেছেন, ‘লালনের যে বাণী, সাঁইজির যে গান, সেটা দীর্ঘদিন আখড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই নগরের শিল্পীদের কণ্ঠে এসে তা নতুন মাত্রা পেল। রবীন্দ্রনাথের গান যেমন হেমন্তের কণ্ঠে এসে নতুন মাত্রা পেল, অনেকটা তেমন। মূলধারায় আসতেই হবে। আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারে আমার আপত্তি নাই। মূল সুরটা ঠিক রেখে, বাণী ঠিক রেখে যদি করা যায়, সেটা ভালো কিছুই
বয়ে আনবে। তবে যন্ত্রের ঝনঝনানি যেন গানকে ছাপিয়ে না যায়। অনেকে ফিউশনের নামে কনফিউশন তৈরি করছেন। এটা উচিত নয়।’
ফরিদা পারভীনের মতে, সংগীত হচ্ছে গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু ধরে, মৃত্যুর আগপর্যন্ত একে ভালোবেসে যেতে হয়, ভালোবেসে গ্রহণ করতে হয়, চর্চা চালিয়ে যেতে হয়। তিনিও আমৃত্যু লালনকে ধারণ করেছেন, নতুন প্রজন্মের মাঝে লালনকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। লালনের গান শেখানোর জন্য অচিন পাখি নামে স্কুল গড়েছেন। মনের বাসনা ব্যক্ত করে বলেছেন, ‘সাঁইজি যেমন তাঁর শিষ্যদের মাঝে বেঁচে আছেন, আমার মাঝে আমার গুরু বেঁচে আছেন, তেমনি আমার অচিন পাখির ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আমি বেঁচে থাকতে চাই।’
ফরিদা পারভীন জানতেন, মানুষের মনে বেঁচে থাকাটাই প্রকৃত অমরত্ব। সেই অমরত্ব লাভের আশাতেই কি পরম স্রষ্টা—মনের মানুষের সনে মিলনের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাঁর মন? ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে সে জন্যই কি থেমে গেলেন তিনি, আমাদের মাঝে রেখে গেলেন তাঁর কর্মযজ্ঞ।

দেশে মনে হয় সাহিত্যচর্চা ভালোই চলছে; বিশেষ করে রাজশাহীর বিভিন্ন জেলায়—অন্তত পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের লেখা বইগুলো তো তা-ই বলে। পুলিশের চাকরির সুবাদে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই লেখা যায় তদন্ত, আইনকানুন, নিয়মনীতি ও প্রশিক্ষণবিষয়ক বই। তাঁরা দায়িত্বের ফাঁকে এসব বই লেখেন, আর সেসব নাকি শত শত ক্রেতা...
১১ ঘণ্টা আগে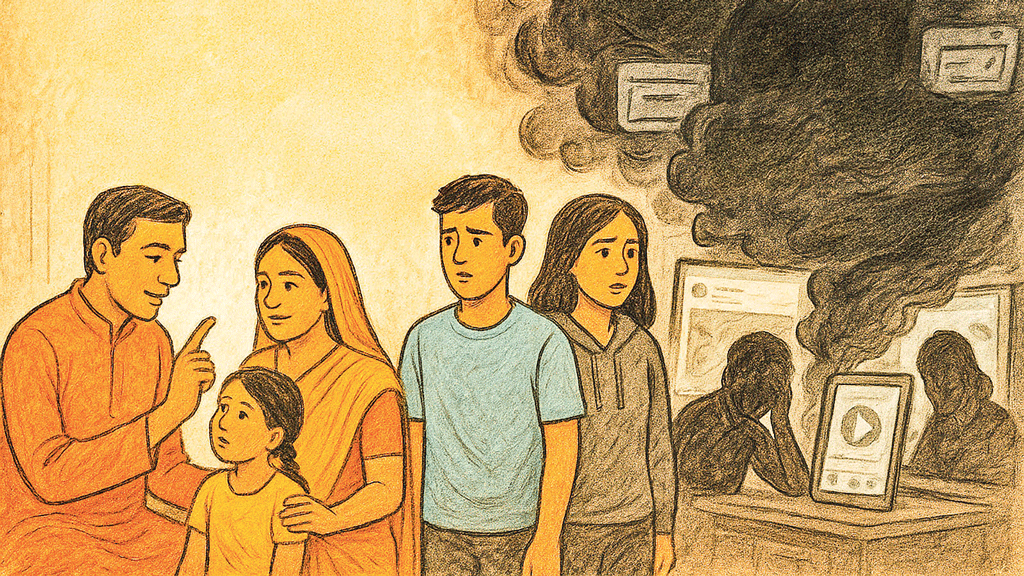
আর পাঁচজনের মতো গালিগালাজে আমার হাতেখড়ি ছোটবেলাতেই। অন্য দশজনের মতো এ বিষয়ে আমার দীক্ষা বন্ধুদের কাছেই। কোনো কোনো বন্ধুর গালিগালাজের সম্ভার ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তাদের মধ্যে একজনের গালিগালাজের সম্ভার শুধু আভিধানিক পর্যায়ের ছিল, তাই সেই সম্ভারের যথাসময়ে এবং যথাযথ প্রয়োগের শৈল্পিক প্রয়োগের...
১১ ঘণ্টা আগে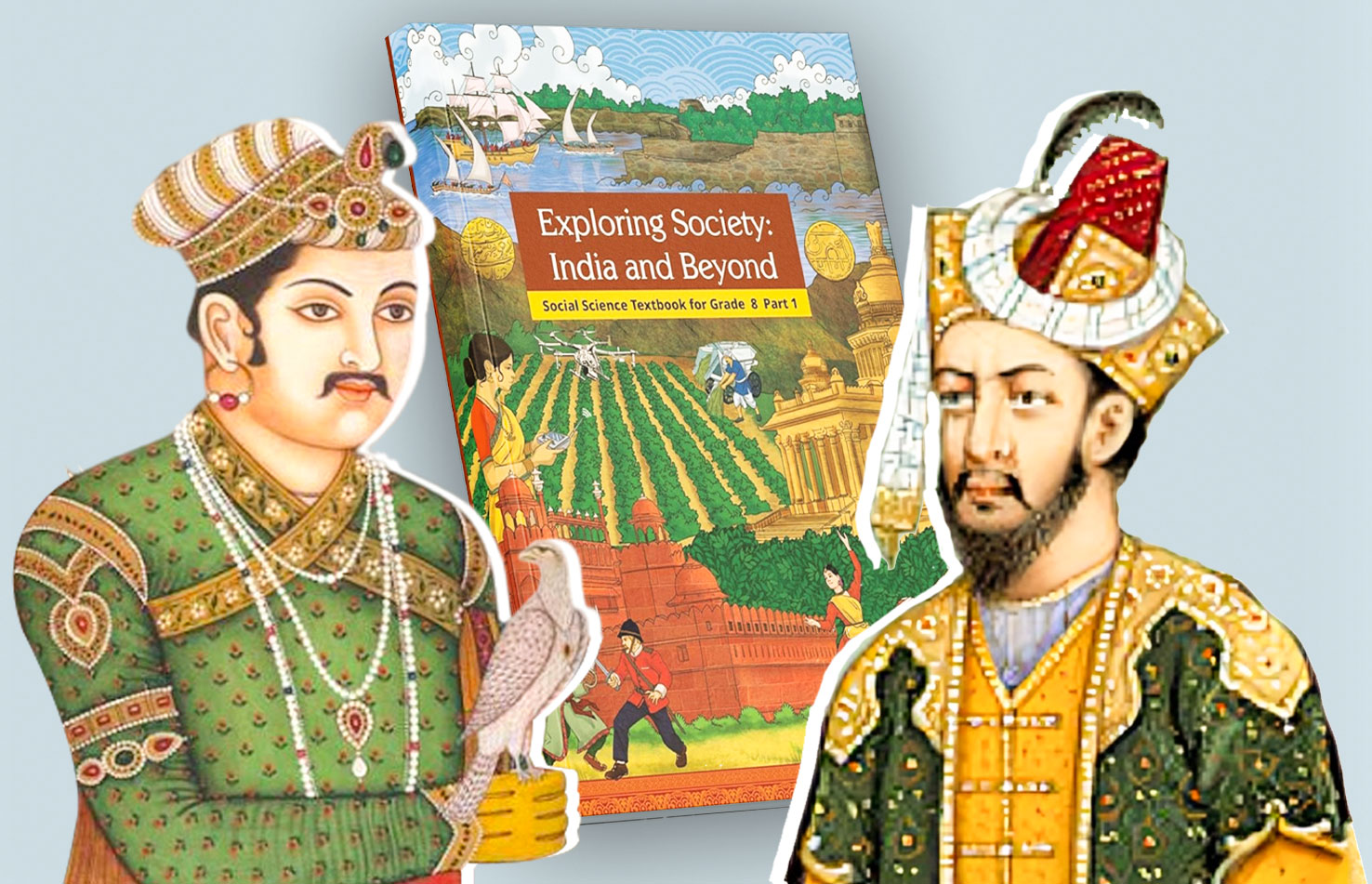
১৯৩৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের আগপর্যন্ত ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের দাবি ছিল মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি ডোমিনিয়ন বা অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে এর তিন মাস পর ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত...
১ দিন আগে
নেদারল্যান্ডসের ডেন হেগ শহরে ভাতের রেস্তোরাঁ খুঁজে ফিরছিলাম। ভারতীয় রেস্তোরাঁ একটা পাওয়া গেল, নাম ‘রমনা’। নাম শুনেই বললাম, এটা বাংলাদেশিই হবে। গত শতকের ষাট-সত্তরের দশকে ঢাকায় এই নামে একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁ ছিল। আমরা যে হোটেলে ছিলাম তার থেকে হাঁটা পথ দূরত্বে, সদলবলে চললাম রমনার...
১ দিন আগে