মিশকাতুল ইসলাম মুমু

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য হত্যাকারী।
ঢাকা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং দ্রুত বর্ধনশীল শহর। উন্নয়নের হাতছানি যেমন এখানে অসংখ্য মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে, তেমনি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই শহরের পরিবেশের ওপর ফেলেছে এক ভয়াবহ প্রভাব। নির্মল বাতাস আজ এখানে দুর্লভ। শীতের শুষ্ক মৌসুম এলেই ধোঁয়াশা আর ধুলার এক অসহ্য চাদরে ঢেকে যায় আকাশ, যা কেবল দৃষ্টিসীমাকেই সীমিত করে না, বরং শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে যখন মেশে যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নির্মাণাধীন এলাকার ধুলাবালু, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বর্ষার আগমন কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এলেও, দূষণের মূল উৎসগুলো তখনো সক্রিয় থাকে, যার ফলে বাতাসের গুণগত মানের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় না।
বিশ্ব বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজ্যুয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার একাধিক এলাকা বর্তমানে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষস্থানীয়। বিশেষত, শীতকালে ঢাকা প্রায়ই বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় এক নম্বরে উঠে আসে। একিউআই (বায়ুমান সূচক) স্কোর ২০০ ছাড়িয়ে গেলে এটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং ৩০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে স্কোর হলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ঢাকায় এই স্কোর প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে, যা প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন লাখ লাখ যানবাহন চলাচল করে, যার মধ্যে অনেক পুরোনো ও অননুমোদিত গাড়ি রয়েছে। এসব গাড়ির ইঞ্জিন থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নিম্নমানের জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইডসহ নানা ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যানজট পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে, কারণ স্থবির গাড়িগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমাগত দূষণ ছড়িয়ে যায়। শহরের আশপাশে গড়ে ওঠা অসংখ্য শিল্পকারখানা ও ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, যা শহরের বাতাসের পিএম ২.৫ (অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা) মাত্রা বাড়াচ্ছে এবং অপরিশোধিত বর্জ্য ঢাকার বাতাসে মিশে গিয়ে দূষণকে আরও তীব্র করে তুলছে। শীতকালে এই ইটভাটাগুলোর কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় দূষণের মাত্রাও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ে। নির্মাণকাজের অনিয়ন্ত্রিত ধুলাবালুও ঢাকার বাতাস দূষণের অন্যতম কারণ; শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত ভবন নির্মাণ ও রাস্তাঘাট সংস্কারের ফলে বাতাসে স্থায়ীভাবে ধুলার আস্তর গড়ে উঠছে। শহরের গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে রাখা বা পোড়ানোর মাধ্যমে বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে জলবায়ুগত ও ভৌগোলিক কারণও যুক্ত রয়েছে; বিশেষ করে শীতকালে বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় দূষিত কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার বদলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জমা হয়ে থাকে। শুষ্ক আবহাওয়া ধুলাবালু উড়তে সাহায্য করে, ফলে বাতাসের গুণগত মান আরও খারাপ হয়।
ঢাকার বিষাক্ত বাতাস আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর ফেলছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব। দূষিত বায়ুর কারণে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসারসহ নানা শ্বাসযন্ত্রের রোগ দ্রুত বাড়ছে, যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে শিশু ও বয়স্কদের ওপর। শিশুদের ফুসফুসের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হ্রাসের মতো সমস্যাও ক্রমবর্ধমান। গর্ভবতী নারীরা এই দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে এলে তা তার অনাগত সন্তানের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।
শুধু স্বাস্থ্যে নয়, অর্থনীতিতেও এই দূষণের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট। দূষণজনিত অসুস্থতায় মানুষের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব, যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ঢাকার দূষিত বাতাস দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে, যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ ও পর্যটনের সম্ভাবনাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
এই ভয়াবহ বায়ুদূষণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে ঢাকার বাতাসকে পুনরায় নির্মল করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রথমত, যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি সড়ক থেকে অপসারণ, উন্নতমানের জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত ইঞ্জিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে গণপরিবহনব্যবস্থা আধুনিক ও কার্যকর করে ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে—মেট্রোরেল ও বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, শিল্পকারখানা ও ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃতীয়ত, নির্মাণকাজের সময় ধুলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নিয়মকানুন প্রণয়ন ও তার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে—যেমন নির্মাণস্থলে পানি ছিটানো, কাপড়ে ঢেকে রাখা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করতে হবে। চতুর্থত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও অত্যন্ত জরুরি; বর্জ্য পৃথক্করণ, সঠিক প্রক্রিয়াকরণ এবং যত্রতত্র ফেলা ও পোড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চমত, শহরের চারপাশে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, যা বায়ু পরিশোধনের প্রাকৃতিক উপায়। এ ছাড়া বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। একই সঙ্গে, বায়ুমানের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তা জনগণের সামনে উপস্থাপনের জন্য উন্নত বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সবাই সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে পারে। সবশেষে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক চুক্তি ও প্রটোকলগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এই সব উদ্যোগ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই ঢাকার বাতাস আবার স্বচ্ছ ও সুস্থ করা সম্ভব হবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য হত্যাকারী।
ঢাকা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং দ্রুত বর্ধনশীল শহর। উন্নয়নের হাতছানি যেমন এখানে অসংখ্য মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে, তেমনি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই শহরের পরিবেশের ওপর ফেলেছে এক ভয়াবহ প্রভাব। নির্মল বাতাস আজ এখানে দুর্লভ। শীতের শুষ্ক মৌসুম এলেই ধোঁয়াশা আর ধুলার এক অসহ্য চাদরে ঢেকে যায় আকাশ, যা কেবল দৃষ্টিসীমাকেই সীমিত করে না, বরং শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে যখন মেশে যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নির্মাণাধীন এলাকার ধুলাবালু, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বর্ষার আগমন কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এলেও, দূষণের মূল উৎসগুলো তখনো সক্রিয় থাকে, যার ফলে বাতাসের গুণগত মানের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় না।
বিশ্ব বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজ্যুয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার একাধিক এলাকা বর্তমানে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষস্থানীয়। বিশেষত, শীতকালে ঢাকা প্রায়ই বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় এক নম্বরে উঠে আসে। একিউআই (বায়ুমান সূচক) স্কোর ২০০ ছাড়িয়ে গেলে এটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং ৩০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে স্কোর হলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ঢাকায় এই স্কোর প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে, যা প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন লাখ লাখ যানবাহন চলাচল করে, যার মধ্যে অনেক পুরোনো ও অননুমোদিত গাড়ি রয়েছে। এসব গাড়ির ইঞ্জিন থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নিম্নমানের জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইডসহ নানা ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যানজট পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে, কারণ স্থবির গাড়িগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমাগত দূষণ ছড়িয়ে যায়। শহরের আশপাশে গড়ে ওঠা অসংখ্য শিল্পকারখানা ও ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, যা শহরের বাতাসের পিএম ২.৫ (অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা) মাত্রা বাড়াচ্ছে এবং অপরিশোধিত বর্জ্য ঢাকার বাতাসে মিশে গিয়ে দূষণকে আরও তীব্র করে তুলছে। শীতকালে এই ইটভাটাগুলোর কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় দূষণের মাত্রাও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ে। নির্মাণকাজের অনিয়ন্ত্রিত ধুলাবালুও ঢাকার বাতাস দূষণের অন্যতম কারণ; শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত ভবন নির্মাণ ও রাস্তাঘাট সংস্কারের ফলে বাতাসে স্থায়ীভাবে ধুলার আস্তর গড়ে উঠছে। শহরের গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে রাখা বা পোড়ানোর মাধ্যমে বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে জলবায়ুগত ও ভৌগোলিক কারণও যুক্ত রয়েছে; বিশেষ করে শীতকালে বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় দূষিত কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার বদলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জমা হয়ে থাকে। শুষ্ক আবহাওয়া ধুলাবালু উড়তে সাহায্য করে, ফলে বাতাসের গুণগত মান আরও খারাপ হয়।
ঢাকার বিষাক্ত বাতাস আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর ফেলছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব। দূষিত বায়ুর কারণে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসারসহ নানা শ্বাসযন্ত্রের রোগ দ্রুত বাড়ছে, যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে শিশু ও বয়স্কদের ওপর। শিশুদের ফুসফুসের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হ্রাসের মতো সমস্যাও ক্রমবর্ধমান। গর্ভবতী নারীরা এই দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে এলে তা তার অনাগত সন্তানের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।
শুধু স্বাস্থ্যে নয়, অর্থনীতিতেও এই দূষণের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট। দূষণজনিত অসুস্থতায় মানুষের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব, যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ঢাকার দূষিত বাতাস দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে, যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ ও পর্যটনের সম্ভাবনাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
এই ভয়াবহ বায়ুদূষণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে ঢাকার বাতাসকে পুনরায় নির্মল করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রথমত, যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি সড়ক থেকে অপসারণ, উন্নতমানের জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত ইঞ্জিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে গণপরিবহনব্যবস্থা আধুনিক ও কার্যকর করে ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে—মেট্রোরেল ও বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, শিল্পকারখানা ও ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃতীয়ত, নির্মাণকাজের সময় ধুলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নিয়মকানুন প্রণয়ন ও তার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে—যেমন নির্মাণস্থলে পানি ছিটানো, কাপড়ে ঢেকে রাখা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করতে হবে। চতুর্থত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও অত্যন্ত জরুরি; বর্জ্য পৃথক্করণ, সঠিক প্রক্রিয়াকরণ এবং যত্রতত্র ফেলা ও পোড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চমত, শহরের চারপাশে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, যা বায়ু পরিশোধনের প্রাকৃতিক উপায়। এ ছাড়া বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। একই সঙ্গে, বায়ুমানের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তা জনগণের সামনে উপস্থাপনের জন্য উন্নত বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সবাই সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে পারে। সবশেষে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক চুক্তি ও প্রটোকলগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এই সব উদ্যোগ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই ঢাকার বাতাস আবার স্বচ্ছ ও সুস্থ করা সম্ভব হবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
মিশকাতুল ইসলাম মুমু

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য হত্যাকারী।
ঢাকা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং দ্রুত বর্ধনশীল শহর। উন্নয়নের হাতছানি যেমন এখানে অসংখ্য মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে, তেমনি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই শহরের পরিবেশের ওপর ফেলেছে এক ভয়াবহ প্রভাব। নির্মল বাতাস আজ এখানে দুর্লভ। শীতের শুষ্ক মৌসুম এলেই ধোঁয়াশা আর ধুলার এক অসহ্য চাদরে ঢেকে যায় আকাশ, যা কেবল দৃষ্টিসীমাকেই সীমিত করে না, বরং শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে যখন মেশে যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নির্মাণাধীন এলাকার ধুলাবালু, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বর্ষার আগমন কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এলেও, দূষণের মূল উৎসগুলো তখনো সক্রিয় থাকে, যার ফলে বাতাসের গুণগত মানের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় না।
বিশ্ব বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজ্যুয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার একাধিক এলাকা বর্তমানে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষস্থানীয়। বিশেষত, শীতকালে ঢাকা প্রায়ই বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় এক নম্বরে উঠে আসে। একিউআই (বায়ুমান সূচক) স্কোর ২০০ ছাড়িয়ে গেলে এটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং ৩০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে স্কোর হলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ঢাকায় এই স্কোর প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে, যা প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন লাখ লাখ যানবাহন চলাচল করে, যার মধ্যে অনেক পুরোনো ও অননুমোদিত গাড়ি রয়েছে। এসব গাড়ির ইঞ্জিন থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নিম্নমানের জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইডসহ নানা ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যানজট পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে, কারণ স্থবির গাড়িগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমাগত দূষণ ছড়িয়ে যায়। শহরের আশপাশে গড়ে ওঠা অসংখ্য শিল্পকারখানা ও ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, যা শহরের বাতাসের পিএম ২.৫ (অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা) মাত্রা বাড়াচ্ছে এবং অপরিশোধিত বর্জ্য ঢাকার বাতাসে মিশে গিয়ে দূষণকে আরও তীব্র করে তুলছে। শীতকালে এই ইটভাটাগুলোর কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় দূষণের মাত্রাও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ে। নির্মাণকাজের অনিয়ন্ত্রিত ধুলাবালুও ঢাকার বাতাস দূষণের অন্যতম কারণ; শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত ভবন নির্মাণ ও রাস্তাঘাট সংস্কারের ফলে বাতাসে স্থায়ীভাবে ধুলার আস্তর গড়ে উঠছে। শহরের গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে রাখা বা পোড়ানোর মাধ্যমে বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে জলবায়ুগত ও ভৌগোলিক কারণও যুক্ত রয়েছে; বিশেষ করে শীতকালে বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় দূষিত কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার বদলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জমা হয়ে থাকে। শুষ্ক আবহাওয়া ধুলাবালু উড়তে সাহায্য করে, ফলে বাতাসের গুণগত মান আরও খারাপ হয়।
ঢাকার বিষাক্ত বাতাস আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর ফেলছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব। দূষিত বায়ুর কারণে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসারসহ নানা শ্বাসযন্ত্রের রোগ দ্রুত বাড়ছে, যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে শিশু ও বয়স্কদের ওপর। শিশুদের ফুসফুসের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হ্রাসের মতো সমস্যাও ক্রমবর্ধমান। গর্ভবতী নারীরা এই দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে এলে তা তার অনাগত সন্তানের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।
শুধু স্বাস্থ্যে নয়, অর্থনীতিতেও এই দূষণের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট। দূষণজনিত অসুস্থতায় মানুষের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব, যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ঢাকার দূষিত বাতাস দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে, যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ ও পর্যটনের সম্ভাবনাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
এই ভয়াবহ বায়ুদূষণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে ঢাকার বাতাসকে পুনরায় নির্মল করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রথমত, যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি সড়ক থেকে অপসারণ, উন্নতমানের জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত ইঞ্জিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে গণপরিবহনব্যবস্থা আধুনিক ও কার্যকর করে ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে—মেট্রোরেল ও বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, শিল্পকারখানা ও ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃতীয়ত, নির্মাণকাজের সময় ধুলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নিয়মকানুন প্রণয়ন ও তার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে—যেমন নির্মাণস্থলে পানি ছিটানো, কাপড়ে ঢেকে রাখা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করতে হবে। চতুর্থত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও অত্যন্ত জরুরি; বর্জ্য পৃথক্করণ, সঠিক প্রক্রিয়াকরণ এবং যত্রতত্র ফেলা ও পোড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চমত, শহরের চারপাশে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, যা বায়ু পরিশোধনের প্রাকৃতিক উপায়। এ ছাড়া বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। একই সঙ্গে, বায়ুমানের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তা জনগণের সামনে উপস্থাপনের জন্য উন্নত বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সবাই সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে পারে। সবশেষে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক চুক্তি ও প্রটোকলগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এই সব উদ্যোগ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই ঢাকার বাতাস আবার স্বচ্ছ ও সুস্থ করা সম্ভব হবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য হত্যাকারী।
ঢাকা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এবং দ্রুত বর্ধনশীল শহর। উন্নয়নের হাতছানি যেমন এখানে অসংখ্য মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে, তেমনি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এই শহরের পরিবেশের ওপর ফেলেছে এক ভয়াবহ প্রভাব। নির্মল বাতাস আজ এখানে দুর্লভ। শীতের শুষ্ক মৌসুম এলেই ধোঁয়াশা আর ধুলার এক অসহ্য চাদরে ঢেকে যায় আকাশ, যা কেবল দৃষ্টিসীমাকেই সীমিত করে না, বরং শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে যখন মেশে যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নির্মাণাধীন এলাকার ধুলাবালু, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বর্ষার আগমন কিছুটা স্বস্তি নিয়ে এলেও, দূষণের মূল উৎসগুলো তখনো সক্রিয় থাকে, যার ফলে বাতাসের গুণগত মানের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় না।
বিশ্ব বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এয়ার ভিজ্যুয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকার একাধিক এলাকা বর্তমানে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষস্থানীয়। বিশেষত, শীতকালে ঢাকা প্রায়ই বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় এক নম্বরে উঠে আসে। একিউআই (বায়ুমান সূচক) স্কোর ২০০ ছাড়িয়ে গেলে এটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং ৩০১ থেকে ৫০০-এর মধ্যে স্কোর হলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ঢাকায় এই স্কোর প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছে যাচ্ছে, যা প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
ঢাকা মহানগরীতে প্রতিদিন লাখ লাখ যানবাহন চলাচল করে, যার মধ্যে অনেক পুরোনো ও অননুমোদিত গাড়ি রয়েছে। এসব গাড়ির ইঞ্জিন থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া এবং নিম্নমানের জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইডসহ নানা ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। যানজট পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে, কারণ স্থবির গাড়িগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ক্রমাগত দূষণ ছড়িয়ে যায়। শহরের আশপাশে গড়ে ওঠা অসংখ্য শিল্পকারখানা ও ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, যা শহরের বাতাসের পিএম ২.৫ (অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা) মাত্রা বাড়াচ্ছে এবং অপরিশোধিত বর্জ্য ঢাকার বাতাসে মিশে গিয়ে দূষণকে আরও তীব্র করে তুলছে। শীতকালে এই ইটভাটাগুলোর কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় দূষণের মাত্রাও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ে। নির্মাণকাজের অনিয়ন্ত্রিত ধুলাবালুও ঢাকার বাতাস দূষণের অন্যতম কারণ; শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত ভবন নির্মাণ ও রাস্তাঘাট সংস্কারের ফলে বাতাসে স্থায়ীভাবে ধুলার আস্তর গড়ে উঠছে। শহরের গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থা, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে রাখা বা পোড়ানোর মাধ্যমে বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে জলবায়ুগত ও ভৌগোলিক কারণও যুক্ত রয়েছে; বিশেষ করে শীতকালে বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় দূষিত কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার বদলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি জমা হয়ে থাকে। শুষ্ক আবহাওয়া ধুলাবালু উড়তে সাহায্য করে, ফলে বাতাসের গুণগত মান আরও খারাপ হয়।
ঢাকার বিষাক্ত বাতাস আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর ফেলছে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব। দূষিত বায়ুর কারণে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসারসহ নানা শ্বাসযন্ত্রের রোগ দ্রুত বাড়ছে, যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে শিশু ও বয়স্কদের ওপর। শিশুদের ফুসফুসের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। একই সঙ্গে হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হ্রাসের মতো সমস্যাও ক্রমবর্ধমান। গর্ভবতী নারীরা এই দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে এলে তা তার অনাগত সন্তানের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।
শুধু স্বাস্থ্যে নয়, অর্থনীতিতেও এই দূষণের নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট। দূষণজনিত অসুস্থতায় মানুষের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব, যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ঢাকার দূষিত বাতাস দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে, যার ফলে বিদেশি বিনিয়োগ ও পর্যটনের সম্ভাবনাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
এই ভয়াবহ বায়ুদূষণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে ঢাকার বাতাসকে পুনরায় নির্মল করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার, জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে। প্রথমত, যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে আনতে পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি সড়ক থেকে অপসারণ, উন্নতমানের জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত ইঞ্জিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে গণপরিবহনব্যবস্থা আধুনিক ও কার্যকর করে ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে—মেট্রোরেল ও বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, শিল্পকারখানা ও ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ এবং দূষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃতীয়ত, নির্মাণকাজের সময় ধুলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নিয়মকানুন প্রণয়ন ও তার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে—যেমন নির্মাণস্থলে পানি ছিটানো, কাপড়ে ঢেকে রাখা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করতে হবে। চতুর্থত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিও অত্যন্ত জরুরি; বর্জ্য পৃথক্করণ, সঠিক প্রক্রিয়াকরণ এবং যত্রতত্র ফেলা ও পোড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পঞ্চমত, শহরের চারপাশে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, যা বায়ু পরিশোধনের প্রাকৃতিক উপায়। এ ছাড়া বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে হবে। একই সঙ্গে, বায়ুমানের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তা জনগণের সামনে উপস্থাপনের জন্য উন্নত বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সবাই সচেতন হয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে পারে। সবশেষে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক চুক্তি ও প্রটোকলগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এই সব উদ্যোগ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই ঢাকার বাতাস আবার স্বচ্ছ ও সুস্থ করা সম্ভব হবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে বলেছিলেন একদা। তাঁর এই পরামর্শ কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে আর মন্তব্য না করাই ভালো। ন্যূনতম সহনশীলতারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও ভাবছে মানুষ। রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি...
২০ ঘণ্টা আগে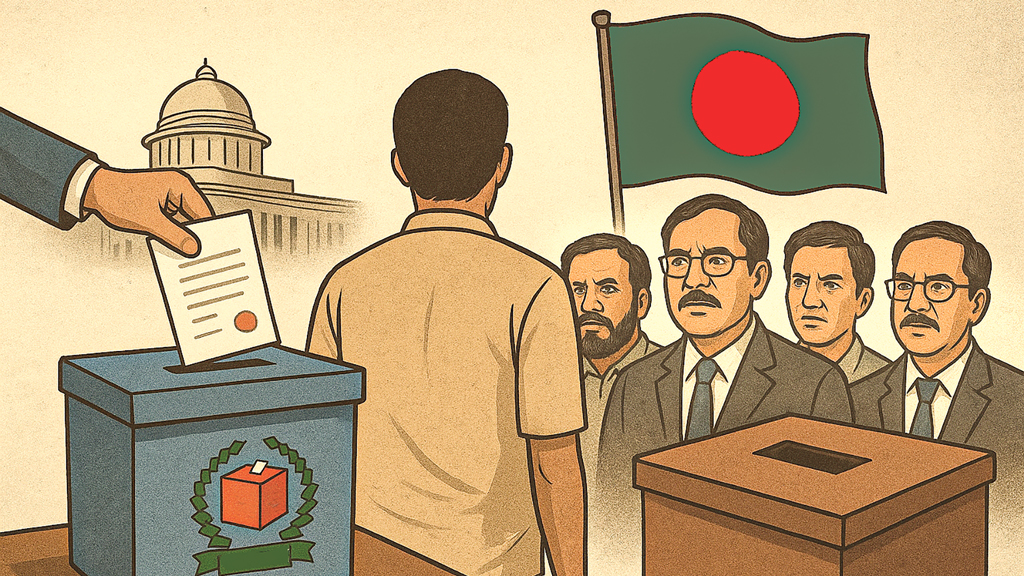
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
২০ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভালো নয়। বিশেষ করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশ হতাশাজনক ও বেদনাদায়ক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ দুরবস্থা দূরীকরণে কোনো সরকারই কোনো আন্তরিকতা দেখায়নি।
২০ ঘণ্টা আগে
সমাজের অলিগলি, শহর থেকে প্রান্তরে আজ যেন একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে—‘জিপিএ-৫ পেলেই জীবন সফল’। অভিভাবকের চোখে সন্তানের সফলতা মাপা হয় সেই একটিমাত্র অঙ্কে। কিন্তু প্রশ্ন, একটি ফলাফল, একটি সংখ্যাই কি সত্যিই নির্ধারণ করতে পারে একজন মানুষের মেধা, মানসিকতা কিংবা ভবিষ্যৎ? মানুষের জীবনের গল্প কখনোই...
২০ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে বলেছিলেন একদা। তাঁর এই পরামর্শ কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে আর মন্তব্য না করাই ভালো। ন্যূনতম সহনশীলতারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও ভাবছে মানুষ। রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেওয়া হচ্ছে এবং গালি দেওয়াই উচিত বলে বয়ান তৈরি করা হচ্ছে। উত্তেজিত হলে নাকি ইচ্ছেমতো গাল দেওয়া যায়।
আজকের পত্রিকার ফিচার বিভাগ থেকে একটি বিচিত্র লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাটির শিরোনাম ‘অনলাইন গালির সংস্কৃতি: ইংরেজিতে কীভাবে গালি দেন আপনি’। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ইন্টারনেটের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হচ্ছে ইংরেজি। পৃথিবীজুড়ে এই ভাষায় কে কাকে কতটা গালাগাল করে, তা নিয়েই ফিচারটি। যাঁরা সভ্য-ভব্য ইংরেজির চর্চা করে এসেছেন সারা জীবন, শেক্সপিয়ার, চার্লস ডিকেন্সের ভাষাকে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা কিন্তু এই ভার্চুয়াল ইংরেজির কাছে এসে বিপাকে পড়বেন। কারণ, এই ইংরেজিটা বইয়ের ইংরেজি থেকে অনেক দূরের ইংরেজি। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ ইংরেজিতে ভার্চুয়াল জগতে যা লেখেন, তাতে গালাগালের প্রবণতা বাড়ছে।
এ ব্যাপারে ফিচারটিতে বেঞ্জামিন বার্গেনের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। লেখক বলছেন, ‘আগে আপনি যে মিডিয়া দেখতেন, তা ছিল অত্যন্ত সম্পাদিত। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে হঠাৎ আমরা মানুষের ঘরোয়া ভাষা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। যখন আমরা মানুষের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ দেখি এবং তাতে গালিগালাজ বেশি থাকে। এর মানে হলো, আমরা সেগুলোর সঙ্গে আরও বেশি পরিচিত হচ্ছি, যা এটিকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। ফলে মানুষজন এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।’
এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়, যে রুচির আবহ তৈরি হয় আনুষ্ঠানিক ভাষায়, তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবাই বক্তা, তাই যে যার রুচির প্রকাশ ঘটাতে পারছে সেখানে। তাই ভাষার শালীনতা রক্ষা করার চেষ্টাও কেউ করে না।
বাস্তবজীবনে ক্ষমতাবান ও দুর্বলদের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে, তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় ভার্চুয়াল জগতে। তখন আক্রমণাত্মক ভাষাকে মোক্ষম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই গালাগালই তাকে ‘ক্ষমতার স্বাদ’ দেয়। ভার্চুয়াল জগতে মন্তব্য, লাইক, শেয়ার ইত্যাদি ‘মব মেন্টালিটি’ তৈরি করে। একদল মানুষ গালাগাল শুরু করলে অন্যরাও তা দলগতভাবে সমর্থন দিতে থাকে। ফলে এই দলবদ্ধ আবেগ তাদের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর অ্যালগরিদমের উসকানি তো আছেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যালগরিদম এমন পোস্টকে সামনে নিয়ে আসে, যেগুলোতে বিতর্ক, উত্তেজনা বা রাগের প্রকাশ রয়েছে। ‘মনোযোগ’ আকর্ষণই পুঁজিবাজারের পণ্য হয়ে উঠেছে।
পুরোনো মূল্যবোধগুলো আক্রমণের শিকার হচ্ছে এখন। পাল্টে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতিতে স্ল্যাং বা গালাগাল ‘স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যাবে কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। আনুষ্ঠানিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা থাকবে কি না, সেটাও সময়ই বলে দেবে। সুতরাং বলতেই হয়, দেখার অনেক বাকি আছে। দেখা যাক পানি কোন দিকে গড়ায়।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে বলেছিলেন একদা। তাঁর এই পরামর্শ কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে আর মন্তব্য না করাই ভালো। ন্যূনতম সহনশীলতারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও ভাবছে মানুষ। রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেওয়া হচ্ছে এবং গালি দেওয়াই উচিত বলে বয়ান তৈরি করা হচ্ছে। উত্তেজিত হলে নাকি ইচ্ছেমতো গাল দেওয়া যায়।
আজকের পত্রিকার ফিচার বিভাগ থেকে একটি বিচিত্র লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাটির শিরোনাম ‘অনলাইন গালির সংস্কৃতি: ইংরেজিতে কীভাবে গালি দেন আপনি’। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ইন্টারনেটের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হচ্ছে ইংরেজি। পৃথিবীজুড়ে এই ভাষায় কে কাকে কতটা গালাগাল করে, তা নিয়েই ফিচারটি। যাঁরা সভ্য-ভব্য ইংরেজির চর্চা করে এসেছেন সারা জীবন, শেক্সপিয়ার, চার্লস ডিকেন্সের ভাষাকে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা কিন্তু এই ভার্চুয়াল ইংরেজির কাছে এসে বিপাকে পড়বেন। কারণ, এই ইংরেজিটা বইয়ের ইংরেজি থেকে অনেক দূরের ইংরেজি। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ ইংরেজিতে ভার্চুয়াল জগতে যা লেখেন, তাতে গালাগালের প্রবণতা বাড়ছে।
এ ব্যাপারে ফিচারটিতে বেঞ্জামিন বার্গেনের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। লেখক বলছেন, ‘আগে আপনি যে মিডিয়া দেখতেন, তা ছিল অত্যন্ত সম্পাদিত। সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে হঠাৎ আমরা মানুষের ঘরোয়া ভাষা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। যখন আমরা মানুষের অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ দেখি এবং তাতে গালিগালাজ বেশি থাকে। এর মানে হলো, আমরা সেগুলোর সঙ্গে আরও বেশি পরিচিত হচ্ছি, যা এটিকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। ফলে মানুষজন এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।’
এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়, যে রুচির আবহ তৈরি হয় আনুষ্ঠানিক ভাষায়, তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবাই বক্তা, তাই যে যার রুচির প্রকাশ ঘটাতে পারছে সেখানে। তাই ভাষার শালীনতা রক্ষা করার চেষ্টাও কেউ করে না।
বাস্তবজীবনে ক্ষমতাবান ও দুর্বলদের মধ্যে যে দূরত্ব থাকে, তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় ভার্চুয়াল জগতে। তখন আক্রমণাত্মক ভাষাকে মোক্ষম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই গালাগালই তাকে ‘ক্ষমতার স্বাদ’ দেয়। ভার্চুয়াল জগতে মন্তব্য, লাইক, শেয়ার ইত্যাদি ‘মব মেন্টালিটি’ তৈরি করে। একদল মানুষ গালাগাল শুরু করলে অন্যরাও তা দলগতভাবে সমর্থন দিতে থাকে। ফলে এই দলবদ্ধ আবেগ তাদের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর অ্যালগরিদমের উসকানি তো আছেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যালগরিদম এমন পোস্টকে সামনে নিয়ে আসে, যেগুলোতে বিতর্ক, উত্তেজনা বা রাগের প্রকাশ রয়েছে। ‘মনোযোগ’ আকর্ষণই পুঁজিবাজারের পণ্য হয়ে উঠেছে।
পুরোনো মূল্যবোধগুলো আক্রমণের শিকার হচ্ছে এখন। পাল্টে যাওয়া বিশ্ব পরিস্থিতিতে স্ল্যাং বা গালাগাল ‘স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যাবে কি না, সে প্রশ্নও উঠছে। আনুষ্ঠানিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা থাকবে কি না, সেটাও সময়ই বলে দেবে। সুতরাং বলতেই হয়, দেখার অনেক বাকি আছে। দেখা যাক পানি কোন দিকে গড়ায়।

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য...
০২ আগস্ট ২০২৫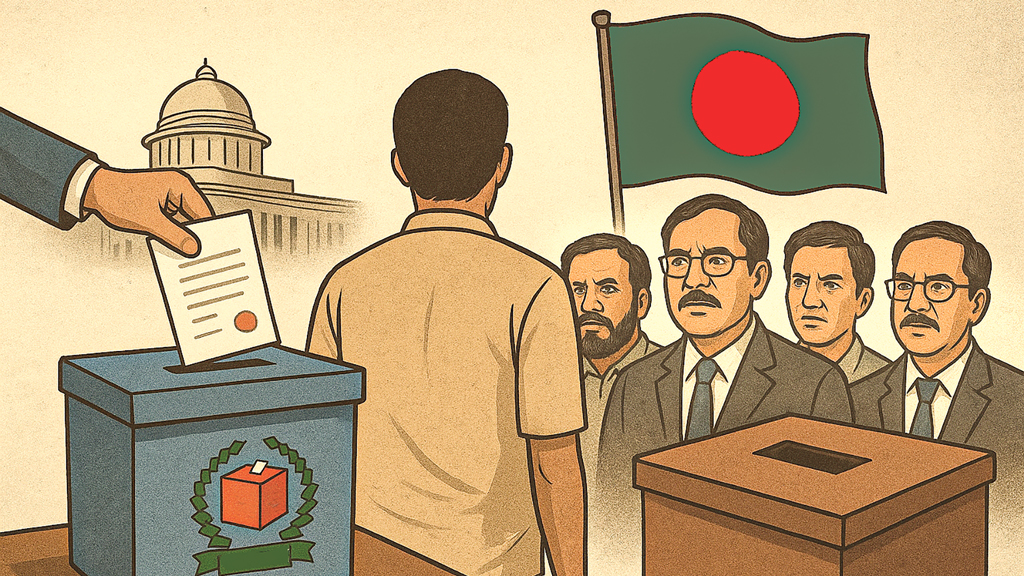
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
২০ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভালো নয়। বিশেষ করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশ হতাশাজনক ও বেদনাদায়ক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ দুরবস্থা দূরীকরণে কোনো সরকারই কোনো আন্তরিকতা দেখায়নি।
২০ ঘণ্টা আগে
সমাজের অলিগলি, শহর থেকে প্রান্তরে আজ যেন একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে—‘জিপিএ-৫ পেলেই জীবন সফল’। অভিভাবকের চোখে সন্তানের সফলতা মাপা হয় সেই একটিমাত্র অঙ্কে। কিন্তু প্রশ্ন, একটি ফলাফল, একটি সংখ্যাই কি সত্যিই নির্ধারণ করতে পারে একজন মানুষের মেধা, মানসিকতা কিংবা ভবিষ্যৎ? মানুষের জীবনের গল্প কখনোই...
২০ ঘণ্টা আগেঅরুণ কর্মকার
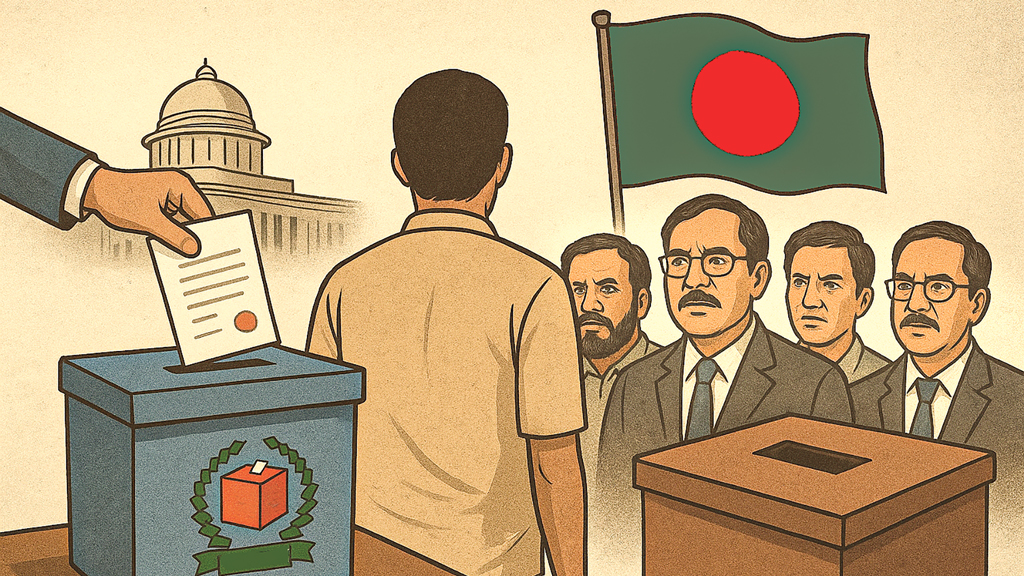
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই কথাটি সত্য যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথযাত্রায়, আগামী চার মাসে অনেকগুলো স্পর্শকাতর ইস্যুর মীমাংসা হতে হবে। তাহলেই কেবল নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ উন্নয়ন অপরিহার্য। কিন্তু সে বিষয়টি এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবেই আছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও একাধিকবার সে কথা বলা হয়েছে। তবে এখানে যে স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো অন্যতর কিছু। প্রধানত রাজনৈতিক ইস্যু।
এর মধ্যে প্রথমেই বলা যায় জুলাই সনদের প্রসঙ্গ। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া ৩০টি রাজনৈতিক দলের সবাই তো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করল না। এ ছাড়া জুলাই অভ্যুত্থানের স্ট্রাইকিং ফোর্স ছাত্রদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ না নিয়ে সনদের প্রতি একপ্রকার অনাস্থাই প্রকাশ করেছে। ফলে এই প্রশ্ন ওঠা খুবই সংগত যে এই সনদ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারল কি না এবং ভবিষ্যতে এই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কি না? আরও একটু বৃহত্তর পরিসরে ভাবতে গেলে দেখা যায়, আরও অনেক জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল সনদ স্বাক্ষর এবং জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে।
তার মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের শরিক অন্যান্য দলের কথা বাদ দিলেও জাতীয় পার্টি এবং আরও কিছু দলের কথা বলা যায়। যেখানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোকেই এই সনদ একসূত্রে গ্রথিত করতে পারল না, সেখানে ভবিষ্যতে এই সনদ এসব দলকে কীভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে? অবশ্য অনেকে ভাবতে পারেন বা অনেকের পরিকল্পনাও থাকতে পারে যে ওইসব দল আর কখনোই দেশের রাজনীতির মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না। কিংবা প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এই ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।
দ্বিতীয় ইস্যুটি হলো নির্বাচনের ধরন। কী পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে—সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি নাকি প্রচলিত পদ্ধতিতে। নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে, তা কি এক কক্ষবিশিষ্ট নাকি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে উচ্চকক্ষে কি পিআর পদ্ধতিতে সদস্য নিয়োগ হবে, নাকি প্রচলিত যে পদ্ধতিতে নারী সংসদ সদস্য নিয়োগ করা হয় সেই পদ্ধতিতে হবে? এসব বিষয় কিন্তু এখন পর্যন্ত ফয়সালা হয়নি। এ রকম আরও কয়েকটি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়া রয়েছে। এই নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে রাখা বিষয়গুলোর মীমাংসা কীভাবে করা হবে? পরবর্তী সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে করবে, নাকি অন্য কোনোভাবে?
তৃতীয় যে ইস্যুটির ফয়সালা হয়নি তা হলো গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হবে, নাকি একই দিনে দুটি আলাদা ব্যালটে হবে। জামায়াত নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের একই দিনে গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারণাকে ‘উদ্ভট’ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বিএনপি চায় একই দিনে দুটি নির্বাচন। এনসিপিরও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু জামায়াতের ঘোর আপত্তি আছে। তারা নভেম্বরে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবিতে দৃঢ় এবং অনড় অবস্থান নিয়ে আছে। সংলাপে অংশ নেওয়া কোনো কোনো দল জামায়াতের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। কোনো কোনো দল বিএনপি-এনসিপির প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের ফয়সালা হওয়া দরকার। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটা!
আরেকটি ইস্যু হলো, আগামী জাতীয় নির্বাচন কি অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) হবে, নাকি অংশগ্রহণমূলক (পার্টিসিপেটরি) হবে? আওয়ামী লীগের দাবি, তাদের অধীনে সব নির্বাচনই ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। কারণ ওই সব নির্বাচনের কোনো দলকেই জোরপূর্বক নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে তাদের অধীনে সব নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি। কারণ, বিএনপিসহ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ, বিএনপিসহ অধিকাংশ দলের দাবি ছিল, তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। সবশেষ তারা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ কারণে অংশগ্রহণ করেনি। তবে প্রশ্ন হলো, আগামী নির্বাচনে কি জোরপূর্বক কোনো দলকে বাদ দেওয়া হবে? নাকি যেকোনো দল ইচ্ছা করলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে? যদি জোর করে কোনো কোনো দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেই নির্বাচন কি সর্বজনীন হিসেবে স্বীকৃত হবে? বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে?
এনসিপির কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী প্রতীক (শাপলা) বরাদ্দ করা না-করাও একটি ইস্যু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এনসিপি একটি প্রতীক চেয়েছে আর নির্বাচন কমিশন সেটি বরাদ্দ না করার বা করতে না পারার কথা বলেছে, এটা যেন এনসিপি কোনোভাবেই মানতে পারছে না। তাই নির্বাচন কমিশন প্রতীক বরাদ্দসংক্রান্ত আইনকানুন, আরপিও সংশোধন প্রভৃতি যা কিছুই বলুক না কেন, এনসিপির অবস্থান অনড়। শাপলা প্রতীক তাদের দিতেই হবে। এটি একটি ছোট বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী পথযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। জামায়াতের আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট করেই এসব অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া এসব অভিযোগ তোলেননি। প্রবাসী ইউটিউবারদের কাছ থেকেও অনেক কথা মানুষ জানতে পারছে। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে—ষড়যন্ত্রকারী উপদেষ্টাদের বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, তাহলে সেটাও নির্বাচনের পথযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
সর্বোপরি আবারও সেই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রসঙ্গ চলে আসে। জুলাই অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ঐক্য তো অনেক আগেই ভেঙে গেছে। এরপর দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পরও জুলাই সনদকে কেন্দ্র করেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হলো না। ফলে রাজনীতি কিন্তু রাজপথে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচনী যাত্রাপথে এই ইস্যুগুলো মীমাংসা করতে হবে।
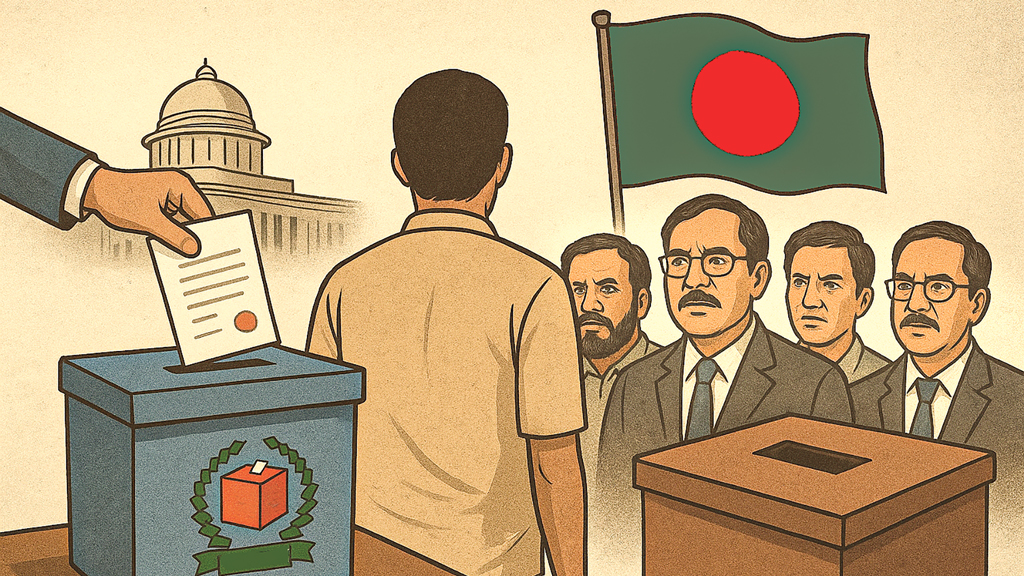
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই কথাটি সত্য যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথযাত্রায়, আগামী চার মাসে অনেকগুলো স্পর্শকাতর ইস্যুর মীমাংসা হতে হবে। তাহলেই কেবল নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ উন্নয়ন অপরিহার্য। কিন্তু সে বিষয়টি এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবেই আছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও একাধিকবার সে কথা বলা হয়েছে। তবে এখানে যে স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো অন্যতর কিছু। প্রধানত রাজনৈতিক ইস্যু।
এর মধ্যে প্রথমেই বলা যায় জুলাই সনদের প্রসঙ্গ। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া ৩০টি রাজনৈতিক দলের সবাই তো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করল না। এ ছাড়া জুলাই অভ্যুত্থানের স্ট্রাইকিং ফোর্স ছাত্রদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ না নিয়ে সনদের প্রতি একপ্রকার অনাস্থাই প্রকাশ করেছে। ফলে এই প্রশ্ন ওঠা খুবই সংগত যে এই সনদ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারল কি না এবং ভবিষ্যতে এই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কি না? আরও একটু বৃহত্তর পরিসরে ভাবতে গেলে দেখা যায়, আরও অনেক জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল সনদ স্বাক্ষর এবং জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে।
তার মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের শরিক অন্যান্য দলের কথা বাদ দিলেও জাতীয় পার্টি এবং আরও কিছু দলের কথা বলা যায়। যেখানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোকেই এই সনদ একসূত্রে গ্রথিত করতে পারল না, সেখানে ভবিষ্যতে এই সনদ এসব দলকে কীভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে? অবশ্য অনেকে ভাবতে পারেন বা অনেকের পরিকল্পনাও থাকতে পারে যে ওইসব দল আর কখনোই দেশের রাজনীতির মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না। কিংবা প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এই ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।
দ্বিতীয় ইস্যুটি হলো নির্বাচনের ধরন। কী পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে—সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি নাকি প্রচলিত পদ্ধতিতে। নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে, তা কি এক কক্ষবিশিষ্ট নাকি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে উচ্চকক্ষে কি পিআর পদ্ধতিতে সদস্য নিয়োগ হবে, নাকি প্রচলিত যে পদ্ধতিতে নারী সংসদ সদস্য নিয়োগ করা হয় সেই পদ্ধতিতে হবে? এসব বিষয় কিন্তু এখন পর্যন্ত ফয়সালা হয়নি। এ রকম আরও কয়েকটি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়া রয়েছে। এই নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে রাখা বিষয়গুলোর মীমাংসা কীভাবে করা হবে? পরবর্তী সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে করবে, নাকি অন্য কোনোভাবে?
তৃতীয় যে ইস্যুটির ফয়সালা হয়নি তা হলো গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হবে, নাকি একই দিনে দুটি আলাদা ব্যালটে হবে। জামায়াত নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের একই দিনে গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারণাকে ‘উদ্ভট’ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বিএনপি চায় একই দিনে দুটি নির্বাচন। এনসিপিরও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু জামায়াতের ঘোর আপত্তি আছে। তারা নভেম্বরে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবিতে দৃঢ় এবং অনড় অবস্থান নিয়ে আছে। সংলাপে অংশ নেওয়া কোনো কোনো দল জামায়াতের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। কোনো কোনো দল বিএনপি-এনসিপির প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের ফয়সালা হওয়া দরকার। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটা!
আরেকটি ইস্যু হলো, আগামী জাতীয় নির্বাচন কি অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) হবে, নাকি অংশগ্রহণমূলক (পার্টিসিপেটরি) হবে? আওয়ামী লীগের দাবি, তাদের অধীনে সব নির্বাচনই ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। কারণ ওই সব নির্বাচনের কোনো দলকেই জোরপূর্বক নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে তাদের অধীনে সব নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি। কারণ, বিএনপিসহ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ, বিএনপিসহ অধিকাংশ দলের দাবি ছিল, তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। সবশেষ তারা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ কারণে অংশগ্রহণ করেনি। তবে প্রশ্ন হলো, আগামী নির্বাচনে কি জোরপূর্বক কোনো দলকে বাদ দেওয়া হবে? নাকি যেকোনো দল ইচ্ছা করলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে? যদি জোর করে কোনো কোনো দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেই নির্বাচন কি সর্বজনীন হিসেবে স্বীকৃত হবে? বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে?
এনসিপির কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী প্রতীক (শাপলা) বরাদ্দ করা না-করাও একটি ইস্যু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এনসিপি একটি প্রতীক চেয়েছে আর নির্বাচন কমিশন সেটি বরাদ্দ না করার বা করতে না পারার কথা বলেছে, এটা যেন এনসিপি কোনোভাবেই মানতে পারছে না। তাই নির্বাচন কমিশন প্রতীক বরাদ্দসংক্রান্ত আইনকানুন, আরপিও সংশোধন প্রভৃতি যা কিছুই বলুক না কেন, এনসিপির অবস্থান অনড়। শাপলা প্রতীক তাদের দিতেই হবে। এটি একটি ছোট বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী পথযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। জামায়াতের আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট করেই এসব অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া এসব অভিযোগ তোলেননি। প্রবাসী ইউটিউবারদের কাছ থেকেও অনেক কথা মানুষ জানতে পারছে। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে—ষড়যন্ত্রকারী উপদেষ্টাদের বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, তাহলে সেটাও নির্বাচনের পথযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
সর্বোপরি আবারও সেই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রসঙ্গ চলে আসে। জুলাই অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ঐক্য তো অনেক আগেই ভেঙে গেছে। এরপর দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পরও জুলাই সনদকে কেন্দ্র করেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হলো না। ফলে রাজনীতি কিন্তু রাজপথে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচনী যাত্রাপথে এই ইস্যুগুলো মীমাংসা করতে হবে।

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য...
০২ আগস্ট ২০২৫
আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে বলেছিলেন একদা। তাঁর এই পরামর্শ কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে আর মন্তব্য না করাই ভালো। ন্যূনতম সহনশীলতারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও ভাবছে মানুষ। রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি...
২০ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভালো নয়। বিশেষ করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশ হতাশাজনক ও বেদনাদায়ক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ দুরবস্থা দূরীকরণে কোনো সরকারই কোনো আন্তরিকতা দেখায়নি।
২০ ঘণ্টা আগে
সমাজের অলিগলি, শহর থেকে প্রান্তরে আজ যেন একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে—‘জিপিএ-৫ পেলেই জীবন সফল’। অভিভাবকের চোখে সন্তানের সফলতা মাপা হয় সেই একটিমাত্র অঙ্কে। কিন্তু প্রশ্ন, একটি ফলাফল, একটি সংখ্যাই কি সত্যিই নির্ধারণ করতে পারে একজন মানুষের মেধা, মানসিকতা কিংবা ভবিষ্যৎ? মানুষের জীবনের গল্প কখনোই...
২০ ঘণ্টা আগেকাজী মাসুদুর রহমান

পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভালো নয়। বিশেষ করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশ হতাশাজনক ও বেদনাদায়ক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ দুরবস্থা দূরীকরণে কোনো সরকারই কোনো আন্তরিকতা দেখায়নি।
আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, দেশের উৎপাদনশীল শিক্ষার সবচেয়ে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো মাধ্যমিক। কেননা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। আবার উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও এ স্তরটি ট্রানজিট স্তর হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। অথচ এই স্তরের প্রায় ৯৭ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। ফলে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মেটাতে হয় ‘অনুদানভিত্তিক’ মান্থলি পেমেন্ট অর্ডারের (এমপিও) মাধ্যমে। তাঁদের বেতন-ভাতাও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অপ্রতুল ও যথেষ্ট বৈষম্যপূর্ণ। বিশেষ করে চিকিৎসা ভাতা, বাড়িভাড়া ও উৎসব ভাতার খাতে এই বৈষম্য খুবই প্রকট। যেমন বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা ভাতা, ঘরভাড়া ও উৎসব ভাতা দেওয়া হয় যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা ও মূল বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ। অথচ সরকারি মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের (যার সংখ্যা মাত্র ৩-৪ শতাংশ) শিক্ষকদের এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা ১৫০০ টাকা; ঘরভাড়া মূল বেতনের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ (উপজেলা ও সিটি করপোরেশনভিত্তিক)। একই সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের আওতায় শিক্ষাদানরত শিক্ষকদের মাঝে এ রকম আর্থিক বৈষম্য খুবই অযৌক্তিক। ২০১৫ সাল থেকে এনটিআরসির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে, যা বিসিএসের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। বিসিএসের মতো তাঁদেরও প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভার মাধ্যমে প্রখর মেধাভিত্তিক যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে।
এর আগে সরকারি শিক্ষকদের ৫ শতাংশ বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হলেও এ থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দীর্ঘদিন বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এমনকি বৈশাখী ভাতা সরকারি সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেওয়া হলেও তাঁদেরকে এ সুবিধার বাইরে রাখা হয়েছিল। ফলে সামাজিকভাবে তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে বেশ হীনম্মন্যতার মধ্যে বাস করতেন। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর তাঁরা ২০১৮ সাল থেকে এই সুবিধার আওতায় এসেছেন।
এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা ২০ শতাংশ ঘরভাড়া, ১৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ও ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন, যা জাতীয় ও বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির প্রতাপের তুলনায় যৎসামান্য। সবশেষ গত ১৩ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে তাঁরা উল্লিখিত দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদযাত্রা করে দাবি মানতে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তাঁদের দাবি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যথেষ্ট গড়িমসি লক্ষ করা যায়। সবশেষ ৫ অক্টোবর ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’- এর বিশেষ দিনে শিক্ষকদের বাড়িভাড়া মাত্র ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। এর প্রতিবাদে তাঁরা আবারও আন্দোলনে নামলে ১৩ অক্টোবর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টিয়ার গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেডের মতো ভয়াবহ অস্ত্র ব্যবহার করে। এমনকি বেধড়ক লাঠিপেটা করে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা হয়। সচেতন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, এ রাষ্ট্র কি তবে শিক্ষকদেরকে অবলা প্রাণী মনে করে? দাবি বাস্তবায়নে ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৪ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পুরো দেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তদানুযায়ী তা পালিত হচ্ছে।
বছর শেষের এই সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন শিক্ষার্থীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনবে। কেননা, আর মাত্র কয়েক মাস পর ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মতো দেশের বৃহত্তম দুই পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিকের প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। মাধ্যমিকের নির্বাচনী পরীক্ষাও অত্যাসন্ন। এ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা আগামী মাস থেকে শুরু হবে। এ রকম পরিস্থিতিতে দেশের তাবৎ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।
সচেতন মানুষও শিক্ষকদের দাবির পক্ষে সংহতি প্রকাশ করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। তাই কালক্ষেপণ না করে শিগগিরই সৃষ্ট সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান করে শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভালো নয়। বিশেষ করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশ হতাশাজনক ও বেদনাদায়ক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ দুরবস্থা দূরীকরণে কোনো সরকারই কোনো আন্তরিকতা দেখায়নি।
আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, দেশের উৎপাদনশীল শিক্ষার সবচেয়ে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো মাধ্যমিক। কেননা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। আবার উচ্চশিক্ষা স্তরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও এ স্তরটি ট্রানজিট স্তর হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। অথচ এই স্তরের প্রায় ৯৭ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। ফলে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মেটাতে হয় ‘অনুদানভিত্তিক’ মান্থলি পেমেন্ট অর্ডারের (এমপিও) মাধ্যমে। তাঁদের বেতন-ভাতাও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অপ্রতুল ও যথেষ্ট বৈষম্যপূর্ণ। বিশেষ করে চিকিৎসা ভাতা, বাড়িভাড়া ও উৎসব ভাতার খাতে এই বৈষম্য খুবই প্রকট। যেমন বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা ভাতা, ঘরভাড়া ও উৎসব ভাতা দেওয়া হয় যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা ও মূল বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ। অথচ সরকারি মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের (যার সংখ্যা মাত্র ৩-৪ শতাংশ) শিক্ষকদের এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতা ১৫০০ টাকা; ঘরভাড়া মূল বেতনের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ (উপজেলা ও সিটি করপোরেশনভিত্তিক)। একই সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের আওতায় শিক্ষাদানরত শিক্ষকদের মাঝে এ রকম আর্থিক বৈষম্য খুবই অযৌক্তিক। ২০১৫ সাল থেকে এনটিআরসির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে, যা বিসিএসের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। বিসিএসের মতো তাঁদেরও প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভার মাধ্যমে প্রখর মেধাভিত্তিক যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে।
এর আগে সরকারি শিক্ষকদের ৫ শতাংশ বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হলেও এ থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দীর্ঘদিন বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এমনকি বৈশাখী ভাতা সরকারি সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেওয়া হলেও তাঁদেরকে এ সুবিধার বাইরে রাখা হয়েছিল। ফলে সামাজিকভাবে তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে বেশ হীনম্মন্যতার মধ্যে বাস করতেন। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর তাঁরা ২০১৮ সাল থেকে এই সুবিধার আওতায় এসেছেন।
এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা ২০ শতাংশ ঘরভাড়া, ১৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ও ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন, যা জাতীয় ও বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির প্রতাপের তুলনায় যৎসামান্য। সবশেষ গত ১৩ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে তাঁরা উল্লিখিত দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদযাত্রা করে দাবি মানতে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তাঁদের দাবি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যথেষ্ট গড়িমসি লক্ষ করা যায়। সবশেষ ৫ অক্টোবর ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’- এর বিশেষ দিনে শিক্ষকদের বাড়িভাড়া মাত্র ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। এর প্রতিবাদে তাঁরা আবারও আন্দোলনে নামলে ১৩ অক্টোবর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টিয়ার গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেডের মতো ভয়াবহ অস্ত্র ব্যবহার করে। এমনকি বেধড়ক লাঠিপেটা করে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা হয়। সচেতন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, এ রাষ্ট্র কি তবে শিক্ষকদেরকে অবলা প্রাণী মনে করে? দাবি বাস্তবায়নে ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৪ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পুরো দেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তদানুযায়ী তা পালিত হচ্ছে।
বছর শেষের এই সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন শিক্ষার্থীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনবে। কেননা, আর মাত্র কয়েক মাস পর ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মতো দেশের বৃহত্তম দুই পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানের উচ্চমাধ্যমিকের প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। মাধ্যমিকের নির্বাচনী পরীক্ষাও অত্যাসন্ন। এ ছাড়া অন্যান্য শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা আগামী মাস থেকে শুরু হবে। এ রকম পরিস্থিতিতে দেশের তাবৎ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।
সচেতন মানুষও শিক্ষকদের দাবির পক্ষে সংহতি প্রকাশ করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। তাই কালক্ষেপণ না করে শিগগিরই সৃষ্ট সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান করে শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য...
০২ আগস্ট ২০২৫
আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে বলেছিলেন একদা। তাঁর এই পরামর্শ কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে আর মন্তব্য না করাই ভালো। ন্যূনতম সহনশীলতারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও ভাবছে মানুষ। রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি...
২০ ঘণ্টা আগে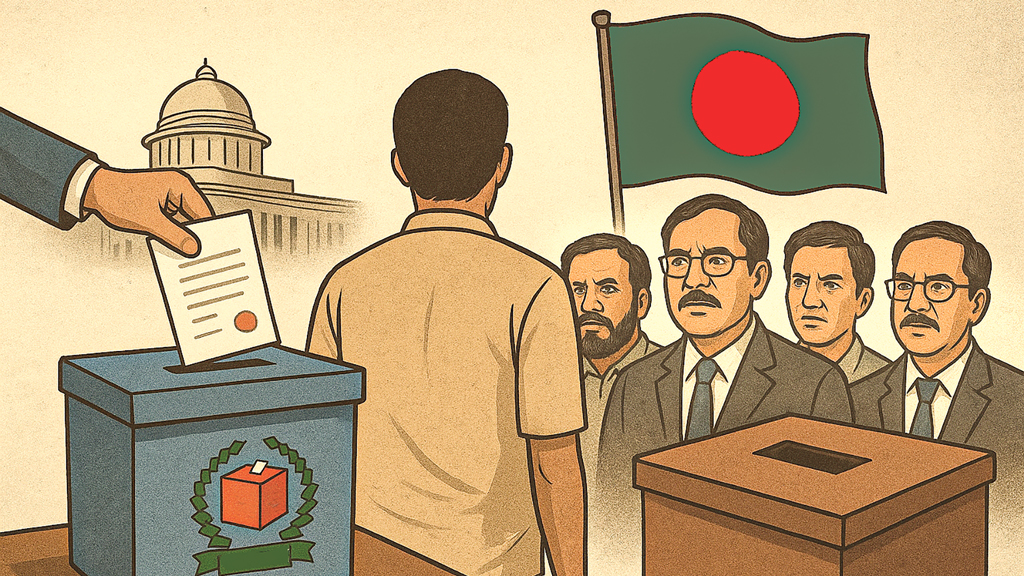
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
২০ ঘণ্টা আগে
সমাজের অলিগলি, শহর থেকে প্রান্তরে আজ যেন একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে—‘জিপিএ-৫ পেলেই জীবন সফল’। অভিভাবকের চোখে সন্তানের সফলতা মাপা হয় সেই একটিমাত্র অঙ্কে। কিন্তু প্রশ্ন, একটি ফলাফল, একটি সংখ্যাই কি সত্যিই নির্ধারণ করতে পারে একজন মানুষের মেধা, মানসিকতা কিংবা ভবিষ্যৎ? মানুষের জীবনের গল্প কখনোই...
২০ ঘণ্টা আগেজুবায়েদ মোস্তফা

সমাজের অলিগলি, শহর থেকে প্রান্তরে আজ যেন একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে—‘জিপিএ-৫ পেলেই জীবন সফল’। অভিভাবকের চোখে সন্তানের সফলতা মাপা হয় সেই একটিমাত্র অঙ্কে। কিন্তু প্রশ্ন, একটি ফলাফল, একটি সংখ্যাই কি সত্যিই নির্ধারণ করতে পারে একজন মানুষের মেধা, মানসিকতা কিংবা ভবিষ্যৎ? মানুষের জীবনের গল্প কখনোই কেবল একটি রেজাল্ট শিটে সীমাবদ্ধ থাকে না। জীবন হচ্ছে এক বহুমাত্রিক অভিযাত্রা—যেখানে সৃজনশীলতা, মনন, দক্ষতা, মূল্যবোধ, পরিশ্রম এবং মানবিকতা মিলেই গড়ে ওঠে প্রকৃত সফলতা।
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ‘জিপিএ-৫’ যেন এক পৌরাণিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। পত্রিকার প্রথম পাতায়, ব্যানার, পোস্টারে, সামাজিক মাধ্যমে দেখা যায়—‘অমুক বোর্ডে সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্তির রেকর্ড’! অথচ এর আড়ালে থেকে যায় হাজারো কিশোর-কিশোরীর চাপ, দুশ্চিন্তা, হতাশা এবং আত্মবিশ্বাস হারানোর গল্প।
শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার সারা দেশে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন। সেই হিসাবে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৭৬ হাজার ৮১৪ জন।
অথচ পরিতাপের বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁদের অনেকেই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। এই পরিসংখ্যান একটাই কথা বলে—আমরা সংখ্যার পেছনে ছুটেছি, জ্ঞানের নয়।
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সময় শেখার চেয়ে মুখস্থ করার নীরব প্রতিযোগিতা চলছে। শিক্ষার্থী জানে না কেন এই সূত্র, কীভাবে এই তত্ত্ব উদ্ভাবন হয়েছে—তবু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য মুখস্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে ফলাফলও আসে চমকপ্রদ জিপিএ-৫। কিন্তু যখন বাস্তবজীবনের চ্যালেঞ্জ আসে—সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যার সমাধান, সৃজনশীল চিন্তায়—তখন সেই জিপিএ-৫ তার দীপ্তি হারায়।
একবার ভেবে দেখুন—স্টিভ জবস, বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ তাঁদের সাফল্যের পথ কোথায় জিপি-৫ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? স্টিভ জবস কলেজও শেষ করেননি, অথচ তাঁর সৃষ্ট ‘এপেল’ আজ প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রতীক। অন্যদিকে, আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁরা হয়তো জিপিএ-৫ পাননি, কিন্তু তাঁদের দক্ষতা, সততা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারায় কর্মক্ষেত্রে অর্জন করেছেন অসাধারণ সাফল্য।
একজন মাঝারি ফলাফলের শিক্ষার্থী ব্যাংকার হয়েছেন, কেউ উদ্যোক্তা হয়ে শত মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন, কেউ হয়তো শিল্পী হয়ে ছুঁয়ে গেছেন মানুষের হৃদয়।
এ কথা মানতেই হবে যে জিপিএ-৫ পাওয়া সহজ নয়। এটি পরিশ্রমের প্রতিফলন, শৃঙ্খলার প্রতীক। কিন্তু এটিকে জীবনের শেষ সীমা ভেবে নেওয়াই ভুল। কারণ, জীবন কোনো গাণিতিক সমীকরণ নয়—এটি অনুভূতির, অভিজ্ঞতার এবং সিদ্ধান্তের সমষ্টি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়—যেসব শিক্ষার্থী জিপিএ-৪.৫ পেয়েছেন, তাঁরাই টিকে যান সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগিতায়। কারণ, তাঁরা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নয়, বাস্তবজীবনের বিশ্লেষণ, যুক্তি ও প্রয়োগে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলেন।
আমরা এমন এক সমাজ তৈরি করছি, যেখানে জিপিএ-৫ না পাওয়া মানেই ব্যর্থতা। অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, এমনকি প্রতিবেশীরাও একজন শিক্ষার্থীকে বিচার করেন কেবল একটি রেজাল্ট দিয়ে। ফলে শিক্ষার্থীটি নিজের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। অনেক সময় এ চাপ থেকে জন্ম নেয় মানসিক অবসাদ, এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে।
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নম্বরের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব মানুষকে মানসিকভাবে অপরিপক্ব করে তোলে। এ জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবল নম্বর নয়, মানুষ তৈরি করা। শিক্ষার্থী যেন বুঝতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে, প্রশ্ন করতে শেখে। শিক্ষা যদি হয়ে ওঠে জীবনের প্রয়োগের হাতিয়ার, তবে জিপিএ-৫ না পেলেও একজন শিক্ষার্থী তার স্বপ্নের দিগন্ত ছুঁতে পারবে।
ফিনল্যান্ড বা জাপানের মতো দেশে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় সৃজনশীলতা, দলগত কাজ, সমস্যা সমাধানের দক্ষতার ওপর। আমাদেরও সেই পথে হাঁটতে হবে। কারণ, ভবিষ্যৎ সেই প্রজন্মের—যারা কেবল প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে না, বরং নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়।
জিপিএ-৫ পেলে অভিনন্দন প্রাপ্য—এটি নিশ্চয়ই অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে সে ব্যর্থ নয়। ভবিষ্যৎ গড়ার মাপকাঠি কখনোই কেবল একটি গ্রেড হতে পারে না। সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব প্রতিভা ও গুণ অনুযায়ী মূল্যায়ন করা। কেউ বিজ্ঞানী হবেন, কেউ লেখক, কেউ উদ্যোক্তা, কেউ শিক্ষক—সবাই মিলে গড়ে তোলে একটি দেশ, একটি সমাজ।
শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজের অলিগলি, শহর থেকে প্রান্তরে আজ যেন একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে—‘জিপিএ-৫ পেলেই জীবন সফল’। অভিভাবকের চোখে সন্তানের সফলতা মাপা হয় সেই একটিমাত্র অঙ্কে। কিন্তু প্রশ্ন, একটি ফলাফল, একটি সংখ্যাই কি সত্যিই নির্ধারণ করতে পারে একজন মানুষের মেধা, মানসিকতা কিংবা ভবিষ্যৎ? মানুষের জীবনের গল্প কখনোই কেবল একটি রেজাল্ট শিটে সীমাবদ্ধ থাকে না। জীবন হচ্ছে এক বহুমাত্রিক অভিযাত্রা—যেখানে সৃজনশীলতা, মনন, দক্ষতা, মূল্যবোধ, পরিশ্রম এবং মানবিকতা মিলেই গড়ে ওঠে প্রকৃত সফলতা।
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ‘জিপিএ-৫’ যেন এক পৌরাণিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। পত্রিকার প্রথম পাতায়, ব্যানার, পোস্টারে, সামাজিক মাধ্যমে দেখা যায়—‘অমুক বোর্ডে সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্তির রেকর্ড’! অথচ এর আড়ালে থেকে যায় হাজারো কিশোর-কিশোরীর চাপ, দুশ্চিন্তা, হতাশা এবং আত্মবিশ্বাস হারানোর গল্প।
শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার সারা দেশে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন। সেই হিসাবে এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৭৬ হাজার ৮১৪ জন।
অথচ পরিতাপের বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁদের অনেকেই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। এই পরিসংখ্যান একটাই কথা বলে—আমরা সংখ্যার পেছনে ছুটেছি, জ্ঞানের নয়।
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সময় শেখার চেয়ে মুখস্থ করার নীরব প্রতিযোগিতা চলছে। শিক্ষার্থী জানে না কেন এই সূত্র, কীভাবে এই তত্ত্ব উদ্ভাবন হয়েছে—তবু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য মুখস্থ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে ফলাফলও আসে চমকপ্রদ জিপিএ-৫। কিন্তু যখন বাস্তবজীবনের চ্যালেঞ্জ আসে—সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যার সমাধান, সৃজনশীল চিন্তায়—তখন সেই জিপিএ-৫ তার দীপ্তি হারায়।
একবার ভেবে দেখুন—স্টিভ জবস, বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ তাঁদের সাফল্যের পথ কোথায় জিপি-৫ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? স্টিভ জবস কলেজও শেষ করেননি, অথচ তাঁর সৃষ্ট ‘এপেল’ আজ প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রতীক। অন্যদিকে, আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁরা হয়তো জিপিএ-৫ পাননি, কিন্তু তাঁদের দক্ষতা, সততা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারায় কর্মক্ষেত্রে অর্জন করেছেন অসাধারণ সাফল্য।
একজন মাঝারি ফলাফলের শিক্ষার্থী ব্যাংকার হয়েছেন, কেউ উদ্যোক্তা হয়ে শত মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছেন, কেউ হয়তো শিল্পী হয়ে ছুঁয়ে গেছেন মানুষের হৃদয়।
এ কথা মানতেই হবে যে জিপিএ-৫ পাওয়া সহজ নয়। এটি পরিশ্রমের প্রতিফলন, শৃঙ্খলার প্রতীক। কিন্তু এটিকে জীবনের শেষ সীমা ভেবে নেওয়াই ভুল। কারণ, জীবন কোনো গাণিতিক সমীকরণ নয়—এটি অনুভূতির, অভিজ্ঞতার এবং সিদ্ধান্তের সমষ্টি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায়—যেসব শিক্ষার্থী জিপিএ-৪.৫ পেয়েছেন, তাঁরাই টিকে যান সবচেয়ে কঠিন প্রতিযোগিতায়। কারণ, তাঁরা শুধু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান নয়, বাস্তবজীবনের বিশ্লেষণ, যুক্তি ও প্রয়োগে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলেন।
আমরা এমন এক সমাজ তৈরি করছি, যেখানে জিপিএ-৫ না পাওয়া মানেই ব্যর্থতা। অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, এমনকি প্রতিবেশীরাও একজন শিক্ষার্থীকে বিচার করেন কেবল একটি রেজাল্ট দিয়ে। ফলে শিক্ষার্থীটি নিজের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে, আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। অনেক সময় এ চাপ থেকে জন্ম নেয় মানসিক অবসাদ, এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে।
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নম্বরের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব মানুষকে মানসিকভাবে অপরিপক্ব করে তোলে। এ জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবল নম্বর নয়, মানুষ তৈরি করা। শিক্ষার্থী যেন বুঝতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে, প্রশ্ন করতে শেখে। শিক্ষা যদি হয়ে ওঠে জীবনের প্রয়োগের হাতিয়ার, তবে জিপিএ-৫ না পেলেও একজন শিক্ষার্থী তার স্বপ্নের দিগন্ত ছুঁতে পারবে।
ফিনল্যান্ড বা জাপানের মতো দেশে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় সৃজনশীলতা, দলগত কাজ, সমস্যা সমাধানের দক্ষতার ওপর। আমাদেরও সেই পথে হাঁটতে হবে। কারণ, ভবিষ্যৎ সেই প্রজন্মের—যারা কেবল প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে না, বরং নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়।
জিপিএ-৫ পেলে অভিনন্দন প্রাপ্য—এটি নিশ্চয়ই অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে সে ব্যর্থ নয়। ভবিষ্যৎ গড়ার মাপকাঠি কখনোই কেবল একটি গ্রেড হতে পারে না। সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব প্রতিভা ও গুণ অনুযায়ী মূল্যায়ন করা। কেউ বিজ্ঞানী হবেন, কেউ লেখক, কেউ উদ্যোক্তা, কেউ শিক্ষক—সবাই মিলে গড়ে তোলে একটি দেশ, একটি সমাজ।
শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকায় প্রতিদিন আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি, তার প্রতিটি কণায় লুকিয়ে আছে অদৃশ্য বিষ, যা নিঃশব্দে আমাদের দেহকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে সুস্থতার অধিকার। একসময় যাকে বলা হতো প্রাণের শহর, আজ তা যেন বিষে ভরা এক মৃত্যুপুরী। ঢাকার বাতাস আর নিছক বাতাস নয়—এ যেন নিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য...
০২ আগস্ট ২০২৫
আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে গালাগালিকে গলাগলিতে রূপান্তরিত করতে বলেছিলেন একদা। তাঁর এই পরামর্শ কতটা কাজে লেগেছে, তা নিয়ে আর মন্তব্য না করাই ভালো। ন্যূনতম সহনশীলতারও মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়েও ভাবছে মানুষ। রাজনীতির মাঠে প্রতিপক্ষকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি...
২০ ঘণ্টা আগে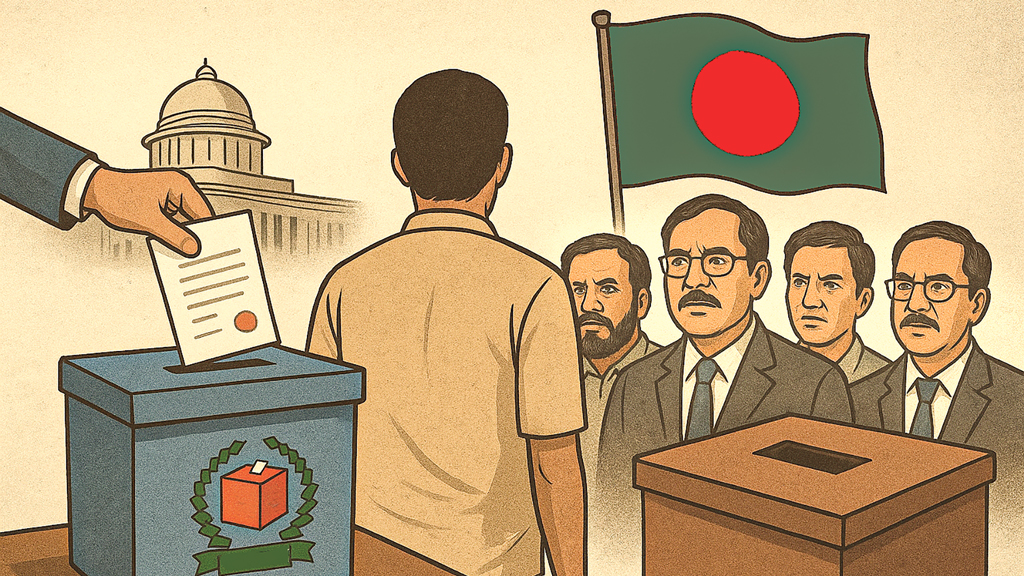
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
২০ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর বহু দেশে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা উচ্চতর হলেও, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভালো নয়। বিশেষ করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ চিত্র বেশ হতাশাজনক ও বেদনাদায়ক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে দীর্ঘদিন ধরে চলমান এ দুরবস্থা দূরীকরণে কোনো সরকারই কোনো আন্তরিকতা দেখায়নি।
২০ ঘণ্টা আগে