অরুণ কর্মকার
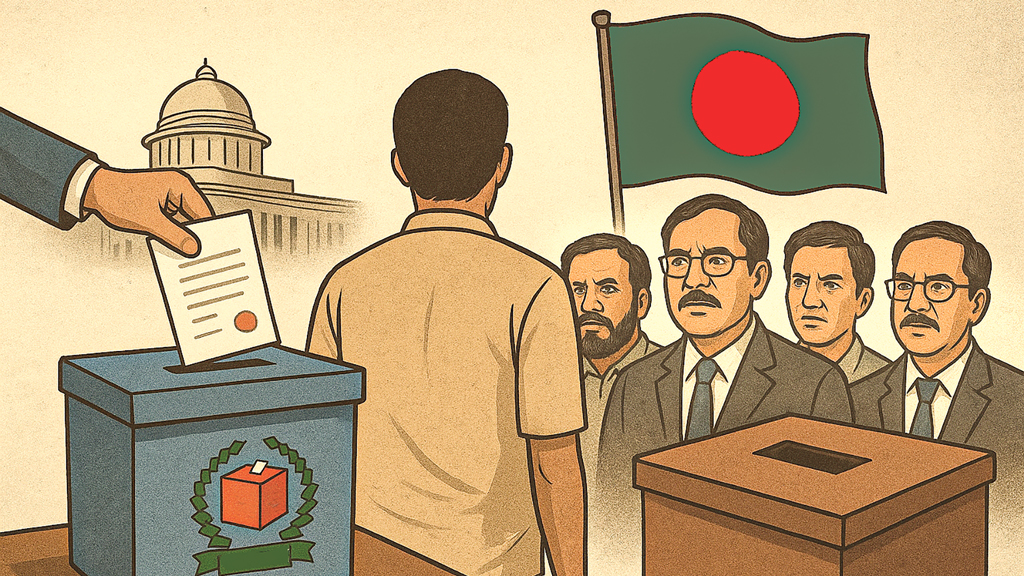
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই কথাটি সত্য যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথযাত্রায়, আগামী চার মাসে অনেকগুলো স্পর্শকাতর ইস্যুর মীমাংসা হতে হবে। তাহলেই কেবল নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ উন্নয়ন অপরিহার্য। কিন্তু সে বিষয়টি এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবেই আছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও একাধিকবার সে কথা বলা হয়েছে। তবে এখানে যে স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো অন্যতর কিছু। প্রধানত রাজনৈতিক ইস্যু।
এর মধ্যে প্রথমেই বলা যায় জুলাই সনদের প্রসঙ্গ। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া ৩০টি রাজনৈতিক দলের সবাই তো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করল না। এ ছাড়া জুলাই অভ্যুত্থানের স্ট্রাইকিং ফোর্স ছাত্রদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ না নিয়ে সনদের প্রতি একপ্রকার অনাস্থাই প্রকাশ করেছে। ফলে এই প্রশ্ন ওঠা খুবই সংগত যে এই সনদ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারল কি না এবং ভবিষ্যতে এই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কি না? আরও একটু বৃহত্তর পরিসরে ভাবতে গেলে দেখা যায়, আরও অনেক জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল সনদ স্বাক্ষর এবং জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে।
তার মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের শরিক অন্যান্য দলের কথা বাদ দিলেও জাতীয় পার্টি এবং আরও কিছু দলের কথা বলা যায়। যেখানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোকেই এই সনদ একসূত্রে গ্রথিত করতে পারল না, সেখানে ভবিষ্যতে এই সনদ এসব দলকে কীভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে? অবশ্য অনেকে ভাবতে পারেন বা অনেকের পরিকল্পনাও থাকতে পারে যে ওইসব দল আর কখনোই দেশের রাজনীতির মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না। কিংবা প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এই ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।
দ্বিতীয় ইস্যুটি হলো নির্বাচনের ধরন। কী পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে—সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি নাকি প্রচলিত পদ্ধতিতে। নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে, তা কি এক কক্ষবিশিষ্ট নাকি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে উচ্চকক্ষে কি পিআর পদ্ধতিতে সদস্য নিয়োগ হবে, নাকি প্রচলিত যে পদ্ধতিতে নারী সংসদ সদস্য নিয়োগ করা হয় সেই পদ্ধতিতে হবে? এসব বিষয় কিন্তু এখন পর্যন্ত ফয়সালা হয়নি। এ রকম আরও কয়েকটি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়া রয়েছে। এই নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে রাখা বিষয়গুলোর মীমাংসা কীভাবে করা হবে? পরবর্তী সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে করবে, নাকি অন্য কোনোভাবে?
তৃতীয় যে ইস্যুটির ফয়সালা হয়নি তা হলো গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হবে, নাকি একই দিনে দুটি আলাদা ব্যালটে হবে। জামায়াত নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের একই দিনে গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারণাকে ‘উদ্ভট’ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বিএনপি চায় একই দিনে দুটি নির্বাচন। এনসিপিরও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু জামায়াতের ঘোর আপত্তি আছে। তারা নভেম্বরে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবিতে দৃঢ় এবং অনড় অবস্থান নিয়ে আছে। সংলাপে অংশ নেওয়া কোনো কোনো দল জামায়াতের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। কোনো কোনো দল বিএনপি-এনসিপির প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের ফয়সালা হওয়া দরকার। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটা!
আরেকটি ইস্যু হলো, আগামী জাতীয় নির্বাচন কি অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) হবে, নাকি অংশগ্রহণমূলক (পার্টিসিপেটরি) হবে? আওয়ামী লীগের দাবি, তাদের অধীনে সব নির্বাচনই ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। কারণ ওই সব নির্বাচনের কোনো দলকেই জোরপূর্বক নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে তাদের অধীনে সব নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি। কারণ, বিএনপিসহ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ, বিএনপিসহ অধিকাংশ দলের দাবি ছিল, তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। সবশেষ তারা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ কারণে অংশগ্রহণ করেনি। তবে প্রশ্ন হলো, আগামী নির্বাচনে কি জোরপূর্বক কোনো দলকে বাদ দেওয়া হবে? নাকি যেকোনো দল ইচ্ছা করলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে? যদি জোর করে কোনো কোনো দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেই নির্বাচন কি সর্বজনীন হিসেবে স্বীকৃত হবে? বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে?
এনসিপির কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী প্রতীক (শাপলা) বরাদ্দ করা না-করাও একটি ইস্যু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এনসিপি একটি প্রতীক চেয়েছে আর নির্বাচন কমিশন সেটি বরাদ্দ না করার বা করতে না পারার কথা বলেছে, এটা যেন এনসিপি কোনোভাবেই মানতে পারছে না। তাই নির্বাচন কমিশন প্রতীক বরাদ্দসংক্রান্ত আইনকানুন, আরপিও সংশোধন প্রভৃতি যা কিছুই বলুক না কেন, এনসিপির অবস্থান অনড়। শাপলা প্রতীক তাদের দিতেই হবে। এটি একটি ছোট বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী পথযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। জামায়াতের আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট করেই এসব অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া এসব অভিযোগ তোলেননি। প্রবাসী ইউটিউবারদের কাছ থেকেও অনেক কথা মানুষ জানতে পারছে। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে—ষড়যন্ত্রকারী উপদেষ্টাদের বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, তাহলে সেটাও নির্বাচনের পথযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
সর্বোপরি আবারও সেই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রসঙ্গ চলে আসে। জুলাই অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ঐক্য তো অনেক আগেই ভেঙে গেছে। এরপর দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পরও জুলাই সনদকে কেন্দ্র করেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হলো না। ফলে রাজনীতি কিন্তু রাজপথে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচনী যাত্রাপথে এই ইস্যুগুলো মীমাংসা করতে হবে।
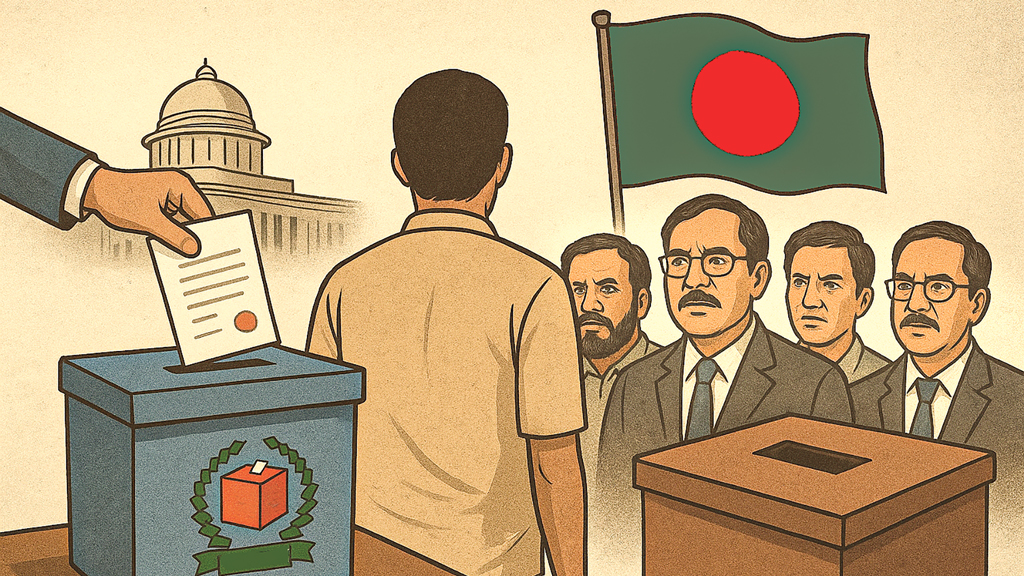
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই কথাটি সত্য যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথযাত্রায়, আগামী চার মাসে অনেকগুলো স্পর্শকাতর ইস্যুর মীমাংসা হতে হবে। তাহলেই কেবল নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ উন্নয়ন অপরিহার্য। কিন্তু সে বিষয়টি এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবেই আছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও একাধিকবার সে কথা বলা হয়েছে। তবে এখানে যে স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো অন্যতর কিছু। প্রধানত রাজনৈতিক ইস্যু।
এর মধ্যে প্রথমেই বলা যায় জুলাই সনদের প্রসঙ্গ। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া ৩০টি রাজনৈতিক দলের সবাই তো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করল না। এ ছাড়া জুলাই অভ্যুত্থানের স্ট্রাইকিং ফোর্স ছাত্রদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ না নিয়ে সনদের প্রতি একপ্রকার অনাস্থাই প্রকাশ করেছে। ফলে এই প্রশ্ন ওঠা খুবই সংগত যে এই সনদ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারল কি না এবং ভবিষ্যতে এই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কি না? আরও একটু বৃহত্তর পরিসরে ভাবতে গেলে দেখা যায়, আরও অনেক জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দল সনদ স্বাক্ষর এবং জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে।
তার মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের শরিক অন্যান্য দলের কথা বাদ দিলেও জাতীয় পার্টি এবং আরও কিছু দলের কথা বলা যায়। যেখানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলোকেই এই সনদ একসূত্রে গ্রথিত করতে পারল না, সেখানে ভবিষ্যতে এই সনদ এসব দলকে কীভাবে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবে? অবশ্য অনেকে ভাবতে পারেন বা অনেকের পরিকল্পনাও থাকতে পারে যে ওইসব দল আর কখনোই দেশের রাজনীতির মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না। কিংবা প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এই ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।
দ্বিতীয় ইস্যুটি হলো নির্বাচনের ধরন। কী পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে—সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি নাকি প্রচলিত পদ্ধতিতে। নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে, তা কি এক কক্ষবিশিষ্ট নাকি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে উচ্চকক্ষে কি পিআর পদ্ধতিতে সদস্য নিয়োগ হবে, নাকি প্রচলিত যে পদ্ধতিতে নারী সংসদ সদস্য নিয়োগ করা হয় সেই পদ্ধতিতে হবে? এসব বিষয় কিন্তু এখন পর্যন্ত ফয়সালা হয়নি। এ রকম আরও কয়েকটি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়া রয়েছে। এই নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে রাখা বিষয়গুলোর মীমাংসা কীভাবে করা হবে? পরবর্তী সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে করবে, নাকি অন্য কোনোভাবে?
তৃতীয় যে ইস্যুটির ফয়সালা হয়নি তা হলো গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হবে, নাকি একই দিনে দুটি আলাদা ব্যালটে হবে। জামায়াত নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের একই দিনে গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারণাকে ‘উদ্ভট’ বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বিএনপি চায় একই দিনে দুটি নির্বাচন। এনসিপিরও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু জামায়াতের ঘোর আপত্তি আছে। তারা নভেম্বরে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবিতে দৃঢ় এবং অনড় অবস্থান নিয়ে আছে। সংলাপে অংশ নেওয়া কোনো কোনো দল জামায়াতের দাবির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। কোনো কোনো দল বিএনপি-এনসিপির প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের ফয়সালা হওয়া দরকার। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটা!
আরেকটি ইস্যু হলো, আগামী জাতীয় নির্বাচন কি অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) হবে, নাকি অংশগ্রহণমূলক (পার্টিসিপেটরি) হবে? আওয়ামী লীগের দাবি, তাদের অধীনে সব নির্বাচনই ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। কারণ ওই সব নির্বাচনের কোনো দলকেই জোরপূর্বক নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তবে তাদের অধীনে সব নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়নি। কারণ, বিএনপিসহ কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ, বিএনপিসহ অধিকাংশ দলের দাবি ছিল, তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। সবশেষ তারা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ কারণে অংশগ্রহণ করেনি। তবে প্রশ্ন হলো, আগামী নির্বাচনে কি জোরপূর্বক কোনো দলকে বাদ দেওয়া হবে? নাকি যেকোনো দল ইচ্ছা করলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে? যদি জোর করে কোনো কোনো দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সেই নির্বাচন কি সর্বজনীন হিসেবে স্বীকৃত হবে? বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে?
এনসিপির কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী প্রতীক (শাপলা) বরাদ্দ করা না-করাও একটি ইস্যু। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, এনসিপি একটি প্রতীক চেয়েছে আর নির্বাচন কমিশন সেটি বরাদ্দ না করার বা করতে না পারার কথা বলেছে, এটা যেন এনসিপি কোনোভাবেই মানতে পারছে না। তাই নির্বাচন কমিশন প্রতীক বরাদ্দসংক্রান্ত আইনকানুন, আরপিও সংশোধন প্রভৃতি যা কিছুই বলুক না কেন, এনসিপির অবস্থান অনড়। শাপলা প্রতীক তাদের দিতেই হবে। এটি একটি ছোট বিষয় মনে হতে পারে। কিন্তু নির্বাচনী পথযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টার দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে, সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। জামায়াতের আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এবং এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট করেই এসব অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়া এসব অভিযোগ তোলেননি। প্রবাসী ইউটিউবারদের কাছ থেকেও অনেক কথা মানুষ জানতে পারছে। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে—ষড়যন্ত্রকারী উপদেষ্টাদের বহাল রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়, তাহলে সেটাও নির্বাচনের পথযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।
সর্বোপরি আবারও সেই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রসঙ্গ চলে আসে। জুলাই অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ঐক্য তো অনেক আগেই ভেঙে গেছে। এরপর দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পরও জুলাই সনদকে কেন্দ্র করেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হলো না। ফলে রাজনীতি কিন্তু রাজপথে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচনী যাত্রাপথে এই ইস্যুগুলো মীমাংসা করতে হবে।

জুলাই সনদ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা, জোট রাজনীতি, নারীনীতি, নির্বাচনী প্রতীক ইস্যু থেকে শুরু করে ফান্ডিং ও ‘মেধা বনাম কোটার’ বিতর্ক—এসব বিষয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা..
২ ঘণ্টা আগে
হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।
৪ ঘণ্টা আগে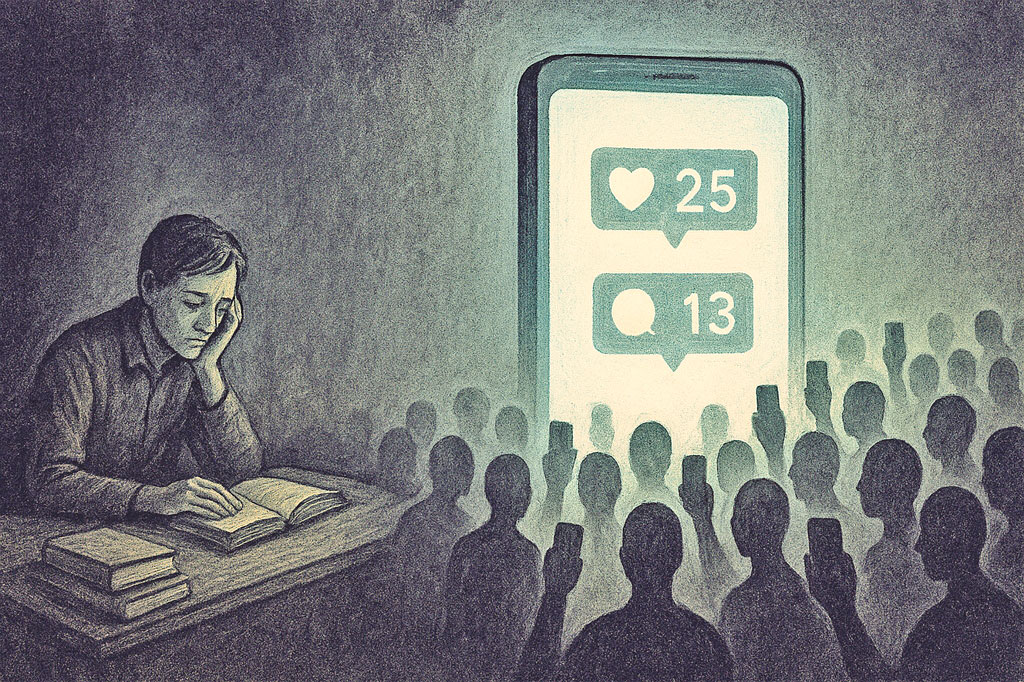
আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে মানুষের মূল্য আর তার চিন্তার গভীরতা, সততা বা মেধার ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে সে কতটা ‘ভাইরাল’ হতে পারে তার ওপর। ‘ভাইরাল’ এখন শুধু একটি শব্দ নয়, এটি এক প্রজন্মের মানদণ্ড, এক সমাজের সফলতার পরিমাপক।
৫ ঘণ্টা আগে
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য ও বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী এক নেতার একটি ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর তা ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যদিও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভিডিওটি এডিট করা, তবু যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে এই নেতাকে...
৫ ঘণ্টা আগে
জুলাই সনদ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা, জোট রাজনীতি, নারীনীতি, নির্বাচনী প্রতীক ইস্যু থেকে শুরু করে ফান্ডিং ও ‘মেধা বনাম কোটার’ বিতর্ক—এসব বিষয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন খোলাখুলি কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার সঙ্গে। আসন্ন নির্বাচনে এনসিপির কৌশল এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও উঠে এসেছে এই দীর্ঘ আলাপচারিতায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অর্চি হক।
অর্চি হক

আজকের পত্রিকা: জুলাই সনদকে অনেকে বাংলাদেশের নতুন ‘রাজনৈতিক চুক্তি’ বলে অভিহিত করছেন। আপনি কি মনে করেন, এই সনদ বাস্তবায়নযোগ্য?
সামান্তা শারমিন: বাস্তবায়ন তো সেটা করবেন, যেটা বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে সকলে একমত এবং সকলে ইচ্ছুক, উদ্গ্রীব। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি নিয়ে সকলেরই কমবেশি কনফিউশন আছে এবং নিজস্ব মতামত আছে, যেটা হয়তো অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলছে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা বলতে হবে, জুলাই সনদের সঙ্গে মানুষের সংযোগের জায়গা খুব একটা নেই। জুলাই সনদকে শ্রেণি-পেশার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জায়গা তৈরি করা হয়নি। ঐকমত্য কমিশনের যে আলাপগুলো হয়েছে, সেগুলো মোটাদাগে রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক। বাংলাদেশ এমন এক সিস্টেমে এসে দাঁড়িয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো ধারণা করে, বাংলাদেশের জনগণ তাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে যেকোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পরে আমাদের এইটুকু রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন—শুধু রাজনৈতিক দল সকল জনগণের মতামত গ্রহণ করতে পারে না; ধারণ করতে পারে না। আমার কাছে মনে হয়, জুলাই সনদের যে বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সেটার বিষয়ে যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, এই মতপার্থক্য কমিয়ে আনার জন্য ঐকমত্য কমিশন যে ধরনের ভূমিকা নিয়েছে, এই ভূমিকার চেয়ে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, আমূল পরিবর্তন এবং গুণগত পরিবর্তনের দিকে ঐকমত্য কমিশনের একধরনের ঝোঁক থাকবে। সেটার বদলে আমরা দেখতে পেয়েছি, বাহাত্তরের সংবিধানকে অবিকল রেখে গণ-অভ্যুত্থানকে বাহাত্তরের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার একধরনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই গণ-অভ্যুত্থান বাহাত্তরের সংবিধানকে অমান্য করে করা হয়েছে। সেই জায়গা থেকে অবশ্যই এই গণ-অভ্যুত্থানকে যেকোনো সংবিধানের ঊর্ধ্বে গণমানুষের চাওয়া, গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে স্থায়ীকরণ করা প্রয়োজন।
আজকের পত্রিকা: জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসেবে আপনি জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী সহিংসতা ও অস্থিরতার জন্য রাজনৈতিকভাবে কতটা দায় অনুভব করেন?
সামান্তা শারমিন: গত দুই মাসে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের, বিএনপির নিজস্ব নেতা-কর্মীর অন্তঃকোন্দলে নিহত হয়েছে ২০০ জন। আমি প্রতিটি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। কিন্তু বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক বাস্তবতা পরিবর্তনের জন্য এই রাজনৈতিক দলগুলো কোনো লড়াই করছে না। বারবার আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের কথা বলেছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, দলগুলো তাদের পুরাতন যে ব্যবস্থা, সেটার মধ্যেই কমফোর্ট ফিল করছে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যা কিছু করা লাগে, যে ধরনের ষড়যন্ত্র করা লাগে, সেগুলোতে লিপ্ত থাকতে তারা দ্বিধাবোধ করছে না। সেই জায়গা থেকে প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর যে ধরনের মতবাদ এবং তাদের যে অ্যাকশনগুলো আমরা দেখে থাকি, সেই জায়গা থেকে অবশ্যই পুরাতন রাজনৈতিক দলগুলোকে দায় নিতে হবে।
আজকের পত্রিকা: আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটের বিষয়ে কিছু ভাবছেন?
সামান্তা শারমিন: বিএনপি ও জামায়াত—দুটিই পুরোনো রাজনৈতিক দল। দুটিই এর আগে ক্ষমতায় ছিল। বাংলাদেশের মানুষ এই দুটি পার্টির শাসনামল দেখেছে। কী অস্থিরতার মধ্যে, কী পরিমাণ আইনশৃঙ্খলার অবনতির মধ্যে, কী ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্য দিয়ে সেই দিনগুলো পার করতে হয়েছে, সেই ইতিহাস কারও অজানা নয়। বিএনপি-জামায়াতের যদি কোনো রিফর্ম হতো, রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের কোনো রিফর্ম আমরা দেখতাম, তাহলে হয়তো ভাবা যেত। কিন্তু পুরোনো রাজনৈতিক ধারায় দালালি, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি এবং দখলদারির যে ব্যবস্থা আছে, এই ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন তারা করেনি। আপনারা এটাও দেখেছেন, বিএনপি কখনোই এককভাবে সরকারে যেতে পারেনি। তাদের সব সময় জোট গঠন করতে হয়েছে। এটা তাদের রাজনৈতিক ঐক্যের একটা বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি। একই সঙ্গে, জামায়াত আসলে কোনো ধরনের গণমানুষের দল নয়। গণমানুষের মধ্যে তার যে এক্সেপটেন্স, সেটা যথেষ্টই প্রশ্নবিদ্ধ। এবং এটাও প্রশ্ন থেকে যায়, জামায়াত যদি ক্ষমতায় আসে, জামায়াত যদি এটা মনে করে, তারা ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য ভালো, তাহলে তারা ভুল করছে। কারণ, জামায়াত এবং আওয়ামী লীগকে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবেই আমরা দেখে এসেছি। নিজেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কখনো কখনো জামায়াত আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগ জামায়াতকে ব্যবহার করেছে। আর এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, জামায়াত আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রসঙ্গটা এখানেই যে যদি জামায়াত ক্ষমতায় আসে, তাহলে আওয়ামী লীগ ফিরে আসার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে। বাংলাদেশের এবং বাইরের অনেক শক্তি এটা দেখানোর চেষ্টা করবে, বাংলাদেশ ইসলামিস্টের হাতে চলে যাচ্ছে। এভাবে আওয়ামী লীগ তার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করবে। সিভিল সোসাইটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষের অনেকে সোচ্চার, আওয়ামী লীগের পক্ষের ভোট কোথায় যাবে। জামায়াত চেষ্টা করে যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের ভোটারদের অ্যাট্রাক্ট করতে, আওয়ামী লীগের ভোটটা যাতে তাদের থাকে। আমি মনে করি, এই দুটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের কোনোটির সঙ্গেই এনসিপির যে রাষ্ট্রকল্প, এনসিপির যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সেটার কোনো মিল নেই। এ কারণে এনসিপি এই পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে কোনোভাবে কমপ্লাই করতে বাধ্য নয়। আমরা নিজেদের জোট গঠনের চেষ্টা করব অথবা আমরা নিজেদের সক্ষমতা এই নির্বাচনেই পরখ করে দেখতে চাই।
আজকের পত্রিকা: গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে আপনাদের একীভূত হওয়ার আলোচনাটা কি একেবারেই ভেস্তে গেছে?
সামান্তা শারমিন: আমরা তরুণদের রাজনীতিটা ওউন করি। আমরা মনে করি, এটা বাংলাদেশের জন্য পজিটিভ একটা এনফোর্সমেন্ট। তরুণেরা যদি সংসদে না যায়, এটা কোনো ভারসাম্য বা স্থিতিশীল সংসদ হবে না। সেই সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সাবেক অনেক কর্মী কিন্তু আমাদের দলে আছেন। তাঁরা কাজ করছেন। তাঁরা এনসিপির যে রাজনৈতিক প্রকল্প রাষ্ট্রকল্প, সেটাকে ওউন করে নিয়ে কাজ করছেন। গণঅধিকার পরিষদ একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল। তাদের সঙ্গে আমাদের নানান ফরমেটে আলাপ হয়েছে, কিন্তু একীভূত হওয়ার সুযোগটা আর নেই। তবে আমরা রাজনৈতিকভাবে একসঙ্গে কাজ করতে উদ্যমী আছি এবং সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে।
আজকের পত্রিকা: নির্বাচনী প্রতীকের প্রশ্নে আপনারা শাপলা প্রতীকের ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? আপনাদের দ্বিতীয় পছন্দ ছিল কলম। এখন কলম প্রতীক না নিয়ে শুধু শাপলাতে অনড় থেকে আপনারা আসলে কী বার্তা দিতে চাচ্ছেন?
সামান্তা শারমিন: আমরা বার্তা দিতে চাচ্ছি না; বরং শাপলা প্রতীকটা এনসিপিকে না দিয়ে ইসি (নির্বাচন কমিশন) একটা বার্তা দিতে চাচ্ছে। বার্তাটা এই যে এনসিপির যে তরুণদের রাজনৈতিক শক্তি, সেটা তাদের মনে একটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের যেই পক্ষ পরিবর্তন চায় না, মৌলিক পরিবর্তন চায় না, তারা তরুণদেরকে কোনোভাবেই একটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে আসা দল এবং যেটা অর্গানিকভাবে উঠে আসছে, সে রকম একটা পরিস্থিতিতে দেখতে চায় না। শাপলার ব্যাপারে প্রথম দিকে যখন ইসির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সিইসির (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, তখন কোনো মিটিংয়েই তাঁরা আপত্তি জানাননি। প্রথম দিকে শাপলা প্রতীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল লিস্টে। তখন তাঁরা আপত্তি জানাননি। বলেছেন, এটা কোনো সমস্যা নয়। এখন কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, প্রতীকের লিস্টে নেই। আমরা যখন জুলাই পদযাত্রায় ছিলাম, আমরা দেখেছি, পুরো বাংলাদেশে মানুষের উচ্ছ্বাস। তার আগেও আমরা পার্টি গঠনের আগে যে মতামত গ্রহণ করেছি, যে জরিপ চালিয়েছিলাম, সেখানেও শাপলা প্রতীক নিয়ে মানুষের উচ্ছ্বাস দেখেছি। এই যে দেশব্যাপী একটি অর্গানিক উচ্ছ্বাস, যেটার ব্যাপারে এনসিপি ক্যাম্পেইন আকারে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেয়নি, তারপরও মানুষের যে উচ্ছ্বাস—এটা অনেকের মনে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করছে, এই প্রতীক যদি এই দল পায়, তাহলে সে প্রথম অবস্থাতে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এটা অনেকে ফেস করতে চাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক দলগুলো, প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, তারা চায়, তাদের নিজেদের যে সক্ষমতা এবং তাদের যে কর্তৃত্ব, সেটা বজায় থাকুক। কোনো রাজনৈতিক দল সেই কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করবে, সে অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে, এটা তারা চাচ্ছে না।
আমরা কলম প্রতীক দ্বিতীয় ভাগে রেখেছিলাম। কিন্তু যেহেতু মানুষের কাছ থেকে আমরা রেসপন্স পেয়েছি, আমাদের সেই গুরুত্বটা দিতে হবে। আমরা যদি সেই গুরুত্বটা না দিই, তাহলে গণমানুষের এবং জনতার রাজনীতির দল হিসেবে নিজেদের দাবি করার কোনো জায়গা নেই। তাঁরা যে বক্তব্য দিয়েছেন, মানে মানুষের যে আগ্রহ শাপলা নিয়ে, তাদের যে এক্সেপটেন্স শাপলার প্রতি—সেটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমরা সেটা গ্রহণ করেছিলাম এবং এ কারণেই আমরা শাপলার যেকোনো ধরনের ফরমেশনের ব্যাপারে আপত্তি জানাইনি। আমরা লাল শাপলাও বলেছি। আপনি শুধু শাপলা দিতে পারেন। সাদা শাপলাও দিতে পারেন। কিংবা শাপলার যে ডিজাইন, সেটা পরিবর্তন করেও দেওয়া সম্ভব। কোনো যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে ইসি তার পজিশন নিয়েছে। একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এভাবে রাজনৈতিক পজিশন নিতে পারে কি না, এটা আমার প্রশ্ন। শাপলা প্রতীক আমাদের প্রাপ্য। সেই লড়াইটা আমরা জারি রাখব।
আজকের পত্রিকা: এনসিপির নারীনীতি কী? আপনারা সরকারে গেলে নারীরা কী ধরনের স্বাধীনতা পাবে? সবক্ষেত্রে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা কি তারা পাবে?
সামান্তা শারমিন: বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, আমি মনে করি, বাংলাদেশের নারীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে—চাকরি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পড়াশোনা, তার সামাজিক অবস্থান—সব জায়গায় অনিরাপত্তার বলয় আছে। এই বলয়টাকে আমরা মনে করি, বাংলাদেশের নারীদের রাজনীতিতে আসা, সক্রিয় ভূমিকা পালন করা, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা—এই বিষয়গুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় অনেক সময়। আমরা সে ক্ষেত্রে মনে করি, বাংলাদেশের রাজনীতির যদি মৌলিক পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে নারীদের অংশগ্রহণ কোনোভাবে বাদ দিয়ে এটা করা যাবে না। ঐকমত্য কমিশনে আমরা দেখলাম, নারীদের আসন নিয়ে সেই ৫ পারসেন্ট সংরক্ষিত বলয়ে আটকে থাকতে বাধ্য হলাম। এখান থেকে অনেক রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের বলা হলো, দেখানো হলো। কিন্তু এই রাজনৈতিক বাস্তবতাগুলো কারা তৈরি করেছে? এই রাজনৈতিক বাস্তবতাগুলো তৈরি করেছে পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো। এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো যেভাবে শক্তি প্রদর্শনের যে প্রক্রিয়া আছে, সে প্রক্রিয়ায় অর্থ এবং অস্ত্র—দুটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামনের নির্বাচনে আমরা অস্ত্রকে কী ভূমিকায় দেখতে পাব, অর্থকে কী ভূমিকায় দেখতে পাব—এগুলো পরিষ্কার নয়। এ রকম একটি অনিরাপদ রাজনৈতিক পরিসরে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এনসিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যপরিধির অংশ। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে অধিকাংশই নারী, সেই প্রতিফলনটা আমরা রাজনীতিতে দেখতে পাব, ক্লাসরুমে দেখতে পাব, যেকোনো করপোরেট প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাব, সেটা আমরা আশা করি।
আজকের পত্রিকা: ক্লাসরুম, রাজনীতি বা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিফলন দেখতে আরও কত বছর লাগতে পারে? তত দিন পর্যন্ত নারীদের কোটা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন কি?
সামান্তা শারমিন: নারীদের কোটা ব্যবস্থা তুলে দেওয়া তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। তারা যতটুকু কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে আসতে পারছে, কোটা তুলে দিলে তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। অনিরাপত্তা, সামাজিক পরিস্থিতিসহ নানা কারণে উঠে আসতে তারা বাধার সম্মুখীন হয়। আমি মনে করি, নারীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোটা ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে করে তাদেরকে আমরা নিয়ে আসতে পারি সামনের দিকে বা চাকরির ক্ষেত্রে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা, যেটাকে আমরা টোকেনিজম বলি, নারীদের শুধু সামনে রেখে শো করা যে আমাদের সঙ্গে ফোরামে এতজন নারী আছে। এটার পরিবর্তন দরকার।
আজকের পত্রিকা: অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমরা নারী ফুটবল দলের একাধিক ম্যাচ স্থগিত হতে দেখেছি। প্রকাশ্যে নারীদের হেনস্তার শিকার হতে দেখেছি। হেনস্তাকারীদের থানা থেকে সংবর্ধনা দিয়ে বের করে আনতে দেখেছি। এসব ঘটনায় এনসিপিকে সক্রিয় অবস্থানে দেখা যায়নি কেন?
সামান্তা শারমিন: আমার ধারণা, আপনার তথ্যে কিছুটা ঘাটতি আছে। যখন আক্রমণ করে মেয়েদের ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমাদের পার্টি হয়েছে কি না, মনে পড়ছে না। সম্ভবত নাগরিক কমিটি ছিল সে সময়। আমাদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন আমাদের নেতারা। ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন। একই সঙ্গে আমরা সংগঠনগত জায়গা থেকে প্রেস রিলিজ দিয়েছি। আমরা পার্টিগত জায়গা থেকে মনে করি, মেয়েদের খেলার স্বাধীনতা আছে, মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা আছে এবং তার যে স্বাভাবিক অভিগমন, এটাকে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
আজকের পত্রিকা: আপনাদের দলের ফান্ডিং বা অর্থায়নের উৎস কীভাবে পরিচালিত হয়? কারা এখানে অর্থ দেয়? কীভাবে এখানে স্বচ্ছতা বজায় রাখেন?
সামান্তা শারমিন: একটা রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি (জবাবদিহি) এবং জনগণের কাছে তার অর্থের উৎস সম্পর্কে পরিষ্কার মনোভাব থাকা। এটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে মানুষ আসলে কিছু আশা করে না, আমাদের কাছ থেকে করে। এই কারণে এই প্রশ্নগুলো এনসিপির কাছে বেশি আসে, যেটাকে আমরা খুবই ইতিবাচকভাবে দেখি। আমরা একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ করেছি। কীভাবে আমাদের অর্থায়ন হয়, সেটার একটা পরিষ্কার নীতিমালা আমরা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেছিলাম। সে সময় অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা জনতার কাছে সেটা উন্মুক্ত করেছি। আমাদের ডোনেশনগুলো এই মারফতই হয়ে থাকে এবং আমরা অর্থের উৎস এবং অর্থের যে জবাবদিহি, সেটার ক্ষেত্রে চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব একটা নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিষ্কার করতে। আমাদের অনেক ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করতে হচ্ছে। সেটার জায়গা থেকে আমরা গ্রোয়িং একটা জায়গায় আছি। আমরা মনে করি না, এটাই সর্বোচ্চ জবাবদিহি। মনে করি, প্রতিটি পয়সা কীভাবে খরচ হচ্ছে, এটা জানার অধিকার মানুষের আছে। আমরা আমাদের দলের ফান্ডিং, ওয়েবসাইট এবং আমাদের নানা ধরনের প্রসেস আছে—বিদেশ থেকে পাঠালে এক রকমের প্রসেস, দেশের অভ্যন্তরে নানা রকমের প্রসেস আছে। এগুলো উন্মুক্ত করা আছে। এই মোতাবেকই আপাতত এই দলটা চলছে।
আজকের পত্রিকা: এনসিপি কবে নাগরিকদের সামনে আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ করবে?
সামান্তা শারমিন: ইনশা আল্লাহ, আমরা ইলেকশনের আগেই আমাদের দলের এখন পর্যন্ত যত খরচ হয়েছে এবং প্রোগ্রামে আমাদের খরচ কীভাবে হয়েছে—এসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট, একই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থ জোগানের নিয়মটা প্রকাশ করতে পারব।
আজকের পত্রিকা: কোটা সংস্কার আন্দোলনের পর থেকে ‘মেধা বনাম কোটার’ প্রশ্নে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। আপনি কি মনে করেন, বর্তমানে চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে?
সামান্তা শারমিন: না, এটা হচ্ছে না। বাংলাদেশে এই সিস্টেমটাই নেই। আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতি, এমনকি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ। চাকরির ব্যবস্থাও ধ্বংস করেছে। চাকরির ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো, যেভাবে যেভাবে নিয়োগ হয়, এটা পুরোপুরি প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, বাবর সাহেব (বিএনপি নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর) রিসেন্টলি একটা বক্তব্যে বলেছেন, ‘ভালো করে পড়াশোনা করেন। পরীক্ষাটা দেন। ভাইভাটা ফেস করেন। তারপরে আমার যতটুকু সম্ভব, আমি দেখব।’ এটা লাস্ট কে বলেছিল, আপনার মনে আছে? জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। উনি বলেছিলেন, ‘আওয়ামী লীগ যারা করবে, যুবলীগ যারা করবে, তারাই চাকরি পাবে, আর কে চাকরি পাবে?’ আমরা এত দিন বলে আসছি, বিএনপি আওয়ামী লীগের রাস্তায় হাঁটছে; বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো করে কথা বলছে; ভারতপন্থী কথা বলছে। চাকরির ক্ষেত্রে ছোট একটা বিষয়ের মন্তব্য এভাবে মিলে যাচ্ছে! বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আপনি তাদের (বিএনপি) ওপর কীভাবে ডিপেন্ড করবেন?
আজকের পত্রিকা: আপনি নির্বাচনে অংশ নেবেন? যদি নেন, তাহলে কোন আসন থেকে?
সামান্তা শারমিন: কী ধরনের সংস্কার হচ্ছে এবং কী ধরনের রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা নির্বাচন করতে যাচ্ছি, এটা আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি। আসলে আসনকেন্দ্রিক কখনোই কাজ করিনি। আমি সংগঠনকে বিস্তৃত করার জন্য বাংলাদেশের সব জায়গায় কাজ করতে আগ্রহী এবং করেছিও। সংগঠন আমাকে যেভাবে কাজ করতে দিতে চায়, আমি সেটা কমপ্লাই করব। আসনভিত্তিক যে একধরনের কামড়াকামড়ি আছে, একধরনের টেনশন আছে এবং অস্থিরতা আছে, এটা আমি মনে করি না, আমার নিজেরও করা দরকার।
আজকের পত্রিকা: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
সামান্তা শারমিন: আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকা: জুলাই সনদকে অনেকে বাংলাদেশের নতুন ‘রাজনৈতিক চুক্তি’ বলে অভিহিত করছেন। আপনি কি মনে করেন, এই সনদ বাস্তবায়নযোগ্য?
সামান্তা শারমিন: বাস্তবায়ন তো সেটা করবেন, যেটা বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে সকলে একমত এবং সকলে ইচ্ছুক, উদ্গ্রীব। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি নিয়ে সকলেরই কমবেশি কনফিউশন আছে এবং নিজস্ব মতামত আছে, যেটা হয়তো অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলছে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা বলতে হবে, জুলাই সনদের সঙ্গে মানুষের সংযোগের জায়গা খুব একটা নেই। জুলাই সনদকে শ্রেণি-পেশার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জায়গা তৈরি করা হয়নি। ঐকমত্য কমিশনের যে আলাপগুলো হয়েছে, সেগুলো মোটাদাগে রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক। বাংলাদেশ এমন এক সিস্টেমে এসে দাঁড়িয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো ধারণা করে, বাংলাদেশের জনগণ তাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে যেকোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পরে আমাদের এইটুকু রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন—শুধু রাজনৈতিক দল সকল জনগণের মতামত গ্রহণ করতে পারে না; ধারণ করতে পারে না। আমার কাছে মনে হয়, জুলাই সনদের যে বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সেটার বিষয়ে যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, এই মতপার্থক্য কমিয়ে আনার জন্য ঐকমত্য কমিশন যে ধরনের ভূমিকা নিয়েছে, এই ভূমিকার চেয়ে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, আমূল পরিবর্তন এবং গুণগত পরিবর্তনের দিকে ঐকমত্য কমিশনের একধরনের ঝোঁক থাকবে। সেটার বদলে আমরা দেখতে পেয়েছি, বাহাত্তরের সংবিধানকে অবিকল রেখে গণ-অভ্যুত্থানকে বাহাত্তরের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার একধরনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই গণ-অভ্যুত্থান বাহাত্তরের সংবিধানকে অমান্য করে করা হয়েছে। সেই জায়গা থেকে অবশ্যই এই গণ-অভ্যুত্থানকে যেকোনো সংবিধানের ঊর্ধ্বে গণমানুষের চাওয়া, গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে স্থায়ীকরণ করা প্রয়োজন।
আজকের পত্রিকা: জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসেবে আপনি জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী সহিংসতা ও অস্থিরতার জন্য রাজনৈতিকভাবে কতটা দায় অনুভব করেন?
সামান্তা শারমিন: গত দুই মাসে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের, বিএনপির নিজস্ব নেতা-কর্মীর অন্তঃকোন্দলে নিহত হয়েছে ২০০ জন। আমি প্রতিটি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। কিন্তু বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক বাস্তবতা পরিবর্তনের জন্য এই রাজনৈতিক দলগুলো কোনো লড়াই করছে না। বারবার আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের কথা বলেছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, দলগুলো তাদের পুরাতন যে ব্যবস্থা, সেটার মধ্যেই কমফোর্ট ফিল করছে। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যা কিছু করা লাগে, যে ধরনের ষড়যন্ত্র করা লাগে, সেগুলোতে লিপ্ত থাকতে তারা দ্বিধাবোধ করছে না। সেই জায়গা থেকে প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর যে ধরনের মতবাদ এবং তাদের যে অ্যাকশনগুলো আমরা দেখে থাকি, সেই জায়গা থেকে অবশ্যই পুরাতন রাজনৈতিক দলগুলোকে দায় নিতে হবে।
আজকের পত্রিকা: আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটের বিষয়ে কিছু ভাবছেন?
সামান্তা শারমিন: বিএনপি ও জামায়াত—দুটিই পুরোনো রাজনৈতিক দল। দুটিই এর আগে ক্ষমতায় ছিল। বাংলাদেশের মানুষ এই দুটি পার্টির শাসনামল দেখেছে। কী অস্থিরতার মধ্যে, কী পরিমাণ আইনশৃঙ্খলার অবনতির মধ্যে, কী ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্য দিয়ে সেই দিনগুলো পার করতে হয়েছে, সেই ইতিহাস কারও অজানা নয়। বিএনপি-জামায়াতের যদি কোনো রিফর্ম হতো, রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের কোনো রিফর্ম আমরা দেখতাম, তাহলে হয়তো ভাবা যেত। কিন্তু পুরোনো রাজনৈতিক ধারায় দালালি, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি এবং দখলদারির যে ব্যবস্থা আছে, এই ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন তারা করেনি। আপনারা এটাও দেখেছেন, বিএনপি কখনোই এককভাবে সরকারে যেতে পারেনি। তাদের সব সময় জোট গঠন করতে হয়েছে। এটা তাদের রাজনৈতিক ঐক্যের একটা বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি। একই সঙ্গে, জামায়াত আসলে কোনো ধরনের গণমানুষের দল নয়। গণমানুষের মধ্যে তার যে এক্সেপটেন্স, সেটা যথেষ্টই প্রশ্নবিদ্ধ। এবং এটাও প্রশ্ন থেকে যায়, জামায়াত যদি ক্ষমতায় আসে, জামায়াত যদি এটা মনে করে, তারা ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য ভালো, তাহলে তারা ভুল করছে। কারণ, জামায়াত এবং আওয়ামী লীগকে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হিসেবেই আমরা দেখে এসেছি। নিজেরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কখনো কখনো জামায়াত আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগ জামায়াতকে ব্যবহার করেছে। আর এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, জামায়াত আওয়ামী লীগকে ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রসঙ্গটা এখানেই যে যদি জামায়াত ক্ষমতায় আসে, তাহলে আওয়ামী লীগ ফিরে আসার একটা সম্ভাবনা তৈরি হবে। বাংলাদেশের এবং বাইরের অনেক শক্তি এটা দেখানোর চেষ্টা করবে, বাংলাদেশ ইসলামিস্টের হাতে চলে যাচ্ছে। এভাবে আওয়ামী লীগ তার প্রাসঙ্গিকতা তৈরি করবে। সিভিল সোসাইটিতে আওয়ামী লীগের পক্ষের অনেকে সোচ্চার, আওয়ামী লীগের পক্ষের ভোট কোথায় যাবে। জামায়াত চেষ্টা করে যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের ভোটারদের অ্যাট্রাক্ট করতে, আওয়ামী লীগের ভোটটা যাতে তাদের থাকে। আমি মনে করি, এই দুটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের কোনোটির সঙ্গেই এনসিপির যে রাষ্ট্রকল্প, এনসিপির যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সেটার কোনো মিল নেই। এ কারণে এনসিপি এই পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে কোনোভাবে কমপ্লাই করতে বাধ্য নয়। আমরা নিজেদের জোট গঠনের চেষ্টা করব অথবা আমরা নিজেদের সক্ষমতা এই নির্বাচনেই পরখ করে দেখতে চাই।
আজকের পত্রিকা: গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে আপনাদের একীভূত হওয়ার আলোচনাটা কি একেবারেই ভেস্তে গেছে?
সামান্তা শারমিন: আমরা তরুণদের রাজনীতিটা ওউন করি। আমরা মনে করি, এটা বাংলাদেশের জন্য পজিটিভ একটা এনফোর্সমেন্ট। তরুণেরা যদি সংসদে না যায়, এটা কোনো ভারসাম্য বা স্থিতিশীল সংসদ হবে না। সেই সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সাবেক অনেক কর্মী কিন্তু আমাদের দলে আছেন। তাঁরা কাজ করছেন। তাঁরা এনসিপির যে রাজনৈতিক প্রকল্প রাষ্ট্রকল্প, সেটাকে ওউন করে নিয়ে কাজ করছেন। গণঅধিকার পরিষদ একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল। তাদের সঙ্গে আমাদের নানান ফরমেটে আলাপ হয়েছে, কিন্তু একীভূত হওয়ার সুযোগটা আর নেই। তবে আমরা রাজনৈতিকভাবে একসঙ্গে কাজ করতে উদ্যমী আছি এবং সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে।
আজকের পত্রিকা: নির্বাচনী প্রতীকের প্রশ্নে আপনারা শাপলা প্রতীকের ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? আপনাদের দ্বিতীয় পছন্দ ছিল কলম। এখন কলম প্রতীক না নিয়ে শুধু শাপলাতে অনড় থেকে আপনারা আসলে কী বার্তা দিতে চাচ্ছেন?
সামান্তা শারমিন: আমরা বার্তা দিতে চাচ্ছি না; বরং শাপলা প্রতীকটা এনসিপিকে না দিয়ে ইসি (নির্বাচন কমিশন) একটা বার্তা দিতে চাচ্ছে। বার্তাটা এই যে এনসিপির যে তরুণদের রাজনৈতিক শক্তি, সেটা তাদের মনে একটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের যেই পক্ষ পরিবর্তন চায় না, মৌলিক পরিবর্তন চায় না, তারা তরুণদেরকে কোনোভাবেই একটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে আসা দল এবং যেটা অর্গানিকভাবে উঠে আসছে, সে রকম একটা পরিস্থিতিতে দেখতে চায় না। শাপলার ব্যাপারে প্রথম দিকে যখন ইসির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সিইসির (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, তখন কোনো মিটিংয়েই তাঁরা আপত্তি জানাননি। প্রথম দিকে শাপলা প্রতীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল লিস্টে। তখন তাঁরা আপত্তি জানাননি। বলেছেন, এটা কোনো সমস্যা নয়। এখন কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, প্রতীকের লিস্টে নেই। আমরা যখন জুলাই পদযাত্রায় ছিলাম, আমরা দেখেছি, পুরো বাংলাদেশে মানুষের উচ্ছ্বাস। তার আগেও আমরা পার্টি গঠনের আগে যে মতামত গ্রহণ করেছি, যে জরিপ চালিয়েছিলাম, সেখানেও শাপলা প্রতীক নিয়ে মানুষের উচ্ছ্বাস দেখেছি। এই যে দেশব্যাপী একটি অর্গানিক উচ্ছ্বাস, যেটার ব্যাপারে এনসিপি ক্যাম্পেইন আকারে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেয়নি, তারপরও মানুষের যে উচ্ছ্বাস—এটা অনেকের মনে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। তারা মনে করছে, এই প্রতীক যদি এই দল পায়, তাহলে সে প্রথম অবস্থাতে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এটা অনেকে ফেস করতে চাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক দলগুলো, প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, তারা চায়, তাদের নিজেদের যে সক্ষমতা এবং তাদের যে কর্তৃত্ব, সেটা বজায় থাকুক। কোনো রাজনৈতিক দল সেই কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করবে, সে অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে, এটা তারা চাচ্ছে না।
আমরা কলম প্রতীক দ্বিতীয় ভাগে রেখেছিলাম। কিন্তু যেহেতু মানুষের কাছ থেকে আমরা রেসপন্স পেয়েছি, আমাদের সেই গুরুত্বটা দিতে হবে। আমরা যদি সেই গুরুত্বটা না দিই, তাহলে গণমানুষের এবং জনতার রাজনীতির দল হিসেবে নিজেদের দাবি করার কোনো জায়গা নেই। তাঁরা যে বক্তব্য দিয়েছেন, মানে মানুষের যে আগ্রহ শাপলা নিয়ে, তাদের যে এক্সেপটেন্স শাপলার প্রতি—সেটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমরা সেটা গ্রহণ করেছিলাম এবং এ কারণেই আমরা শাপলার যেকোনো ধরনের ফরমেশনের ব্যাপারে আপত্তি জানাইনি। আমরা লাল শাপলাও বলেছি। আপনি শুধু শাপলা দিতে পারেন। সাদা শাপলাও দিতে পারেন। কিংবা শাপলার যে ডিজাইন, সেটা পরিবর্তন করেও দেওয়া সম্ভব। কোনো যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে ইসি তার পজিশন নিয়েছে। একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এভাবে রাজনৈতিক পজিশন নিতে পারে কি না, এটা আমার প্রশ্ন। শাপলা প্রতীক আমাদের প্রাপ্য। সেই লড়াইটা আমরা জারি রাখব।
আজকের পত্রিকা: এনসিপির নারীনীতি কী? আপনারা সরকারে গেলে নারীরা কী ধরনের স্বাধীনতা পাবে? সবক্ষেত্রে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা কি তারা পাবে?
সামান্তা শারমিন: বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, আমি মনে করি, বাংলাদেশের নারীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে—চাকরি ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পড়াশোনা, তার সামাজিক অবস্থান—সব জায়গায় অনিরাপত্তার বলয় আছে। এই বলয়টাকে আমরা মনে করি, বাংলাদেশের নারীদের রাজনীতিতে আসা, সক্রিয় ভূমিকা পালন করা, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা—এই বিষয়গুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় অনেক সময়। আমরা সে ক্ষেত্রে মনে করি, বাংলাদেশের রাজনীতির যদি মৌলিক পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে নারীদের অংশগ্রহণ কোনোভাবে বাদ দিয়ে এটা করা যাবে না। ঐকমত্য কমিশনে আমরা দেখলাম, নারীদের আসন নিয়ে সেই ৫ পারসেন্ট সংরক্ষিত বলয়ে আটকে থাকতে বাধ্য হলাম। এখান থেকে অনেক রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের বলা হলো, দেখানো হলো। কিন্তু এই রাজনৈতিক বাস্তবতাগুলো কারা তৈরি করেছে? এই রাজনৈতিক বাস্তবতাগুলো তৈরি করেছে পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো। এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো যেভাবে শক্তি প্রদর্শনের যে প্রক্রিয়া আছে, সে প্রক্রিয়ায় অর্থ এবং অস্ত্র—দুটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামনের নির্বাচনে আমরা অস্ত্রকে কী ভূমিকায় দেখতে পাব, অর্থকে কী ভূমিকায় দেখতে পাব—এগুলো পরিষ্কার নয়। এ রকম একটি অনিরাপদ রাজনৈতিক পরিসরে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এনসিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যপরিধির অংশ। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের জনসংখ্যার যে অধিকাংশই নারী, সেই প্রতিফলনটা আমরা রাজনীতিতে দেখতে পাব, ক্লাসরুমে দেখতে পাব, যেকোনো করপোরেট প্রতিষ্ঠানে দেখতে পাব, সেটা আমরা আশা করি।
আজকের পত্রিকা: ক্লাসরুম, রাজনীতি বা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিফলন দেখতে আরও কত বছর লাগতে পারে? তত দিন পর্যন্ত নারীদের কোটা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন কি?
সামান্তা শারমিন: নারীদের কোটা ব্যবস্থা তুলে দেওয়া তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। তারা যতটুকু কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে আসতে পারছে, কোটা তুলে দিলে তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। অনিরাপত্তা, সামাজিক পরিস্থিতিসহ নানা কারণে উঠে আসতে তারা বাধার সম্মুখীন হয়। আমি মনে করি, নারীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোটা ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে করে তাদেরকে আমরা নিয়ে আসতে পারি সামনের দিকে বা চাকরির ক্ষেত্রে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা, যেটাকে আমরা টোকেনিজম বলি, নারীদের শুধু সামনে রেখে শো করা যে আমাদের সঙ্গে ফোরামে এতজন নারী আছে। এটার পরিবর্তন দরকার।
আজকের পত্রিকা: অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমরা নারী ফুটবল দলের একাধিক ম্যাচ স্থগিত হতে দেখেছি। প্রকাশ্যে নারীদের হেনস্তার শিকার হতে দেখেছি। হেনস্তাকারীদের থানা থেকে সংবর্ধনা দিয়ে বের করে আনতে দেখেছি। এসব ঘটনায় এনসিপিকে সক্রিয় অবস্থানে দেখা যায়নি কেন?
সামান্তা শারমিন: আমার ধারণা, আপনার তথ্যে কিছুটা ঘাটতি আছে। যখন আক্রমণ করে মেয়েদের ম্যাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমাদের পার্টি হয়েছে কি না, মনে পড়ছে না। সম্ভবত নাগরিক কমিটি ছিল সে সময়। আমাদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন আমাদের নেতারা। ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন। একই সঙ্গে আমরা সংগঠনগত জায়গা থেকে প্রেস রিলিজ দিয়েছি। আমরা পার্টিগত জায়গা থেকে মনে করি, মেয়েদের খেলার স্বাধীনতা আছে, মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা আছে এবং তার যে স্বাভাবিক অভিগমন, এটাকে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
আজকের পত্রিকা: আপনাদের দলের ফান্ডিং বা অর্থায়নের উৎস কীভাবে পরিচালিত হয়? কারা এখানে অর্থ দেয়? কীভাবে এখানে স্বচ্ছতা বজায় রাখেন?
সামান্তা শারমিন: একটা রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি (জবাবদিহি) এবং জনগণের কাছে তার অর্থের উৎস সম্পর্কে পরিষ্কার মনোভাব থাকা। এটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে মানুষ আসলে কিছু আশা করে না, আমাদের কাছ থেকে করে। এই কারণে এই প্রশ্নগুলো এনসিপির কাছে বেশি আসে, যেটাকে আমরা খুবই ইতিবাচকভাবে দেখি। আমরা একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ করেছি। কীভাবে আমাদের অর্থায়ন হয়, সেটার একটা পরিষ্কার নীতিমালা আমরা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেছিলাম। সে সময় অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা জনতার কাছে সেটা উন্মুক্ত করেছি। আমাদের ডোনেশনগুলো এই মারফতই হয়ে থাকে এবং আমরা অর্থের উৎস এবং অর্থের যে জবাবদিহি, সেটার ক্ষেত্রে চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব একটা নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিষ্কার করতে। আমাদের অনেক ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করতে হচ্ছে। সেটার জায়গা থেকে আমরা গ্রোয়িং একটা জায়গায় আছি। আমরা মনে করি না, এটাই সর্বোচ্চ জবাবদিহি। মনে করি, প্রতিটি পয়সা কীভাবে খরচ হচ্ছে, এটা জানার অধিকার মানুষের আছে। আমরা আমাদের দলের ফান্ডিং, ওয়েবসাইট এবং আমাদের নানা ধরনের প্রসেস আছে—বিদেশ থেকে পাঠালে এক রকমের প্রসেস, দেশের অভ্যন্তরে নানা রকমের প্রসেস আছে। এগুলো উন্মুক্ত করা আছে। এই মোতাবেকই আপাতত এই দলটা চলছে।
আজকের পত্রিকা: এনসিপি কবে নাগরিকদের সামনে আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ করবে?
সামান্তা শারমিন: ইনশা আল্লাহ, আমরা ইলেকশনের আগেই আমাদের দলের এখন পর্যন্ত যত খরচ হয়েছে এবং প্রোগ্রামে আমাদের খরচ কীভাবে হয়েছে—এসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট, একই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থ জোগানের নিয়মটা প্রকাশ করতে পারব।
আজকের পত্রিকা: কোটা সংস্কার আন্দোলনের পর থেকে ‘মেধা বনাম কোটার’ প্রশ্নে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। আপনি কি মনে করেন, বর্তমানে চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে?
সামান্তা শারমিন: না, এটা হচ্ছে না। বাংলাদেশে এই সিস্টেমটাই নেই। আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতি, এমনকি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ। চাকরির ব্যবস্থাও ধ্বংস করেছে। চাকরির ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো, যেভাবে যেভাবে নিয়োগ হয়, এটা পুরোপুরি প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, বাবর সাহেব (বিএনপি নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর) রিসেন্টলি একটা বক্তব্যে বলেছেন, ‘ভালো করে পড়াশোনা করেন। পরীক্ষাটা দেন। ভাইভাটা ফেস করেন। তারপরে আমার যতটুকু সম্ভব, আমি দেখব।’ এটা লাস্ট কে বলেছিল, আপনার মনে আছে? জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। উনি বলেছিলেন, ‘আওয়ামী লীগ যারা করবে, যুবলীগ যারা করবে, তারাই চাকরি পাবে, আর কে চাকরি পাবে?’ আমরা এত দিন বলে আসছি, বিএনপি আওয়ামী লীগের রাস্তায় হাঁটছে; বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো করে কথা বলছে; ভারতপন্থী কথা বলছে। চাকরির ক্ষেত্রে ছোট একটা বিষয়ের মন্তব্য এভাবে মিলে যাচ্ছে! বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে আপনি তাদের (বিএনপি) ওপর কীভাবে ডিপেন্ড করবেন?
আজকের পত্রিকা: আপনি নির্বাচনে অংশ নেবেন? যদি নেন, তাহলে কোন আসন থেকে?
সামান্তা শারমিন: কী ধরনের সংস্কার হচ্ছে এবং কী ধরনের রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা নির্বাচন করতে যাচ্ছি, এটা আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি। আসলে আসনকেন্দ্রিক কখনোই কাজ করিনি। আমি সংগঠনকে বিস্তৃত করার জন্য বাংলাদেশের সব জায়গায় কাজ করতে আগ্রহী এবং করেছিও। সংগঠন আমাকে যেভাবে কাজ করতে দিতে চায়, আমি সেটা কমপ্লাই করব। আসনভিত্তিক যে একধরনের কামড়াকামড়ি আছে, একধরনের টেনশন আছে এবং অস্থিরতা আছে, এটা আমি মনে করি না, আমার নিজেরও করা দরকার।
আজকের পত্রিকা: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
সামান্তা শারমিন: আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।
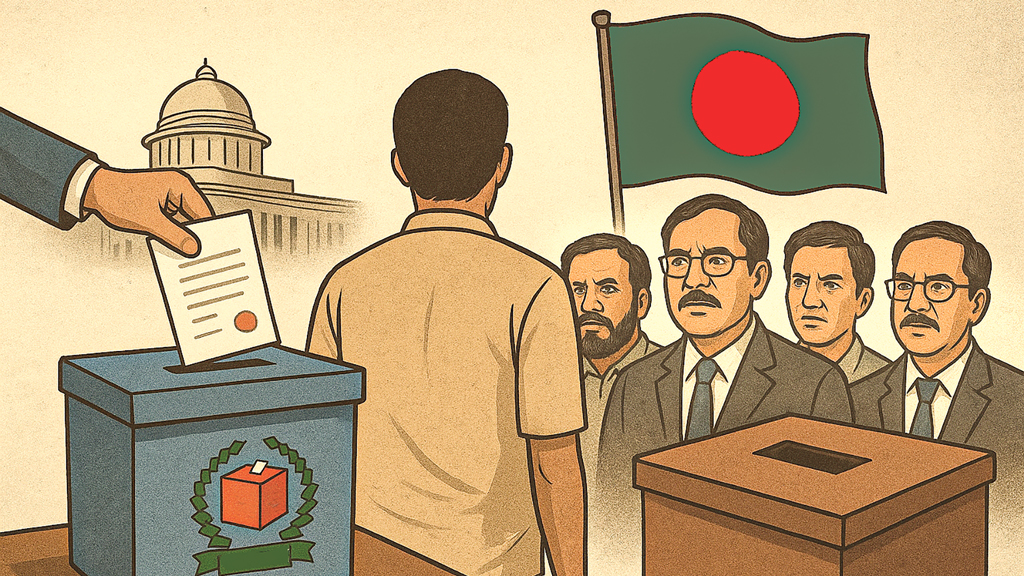
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
১ দিন আগে
হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।
৪ ঘণ্টা আগে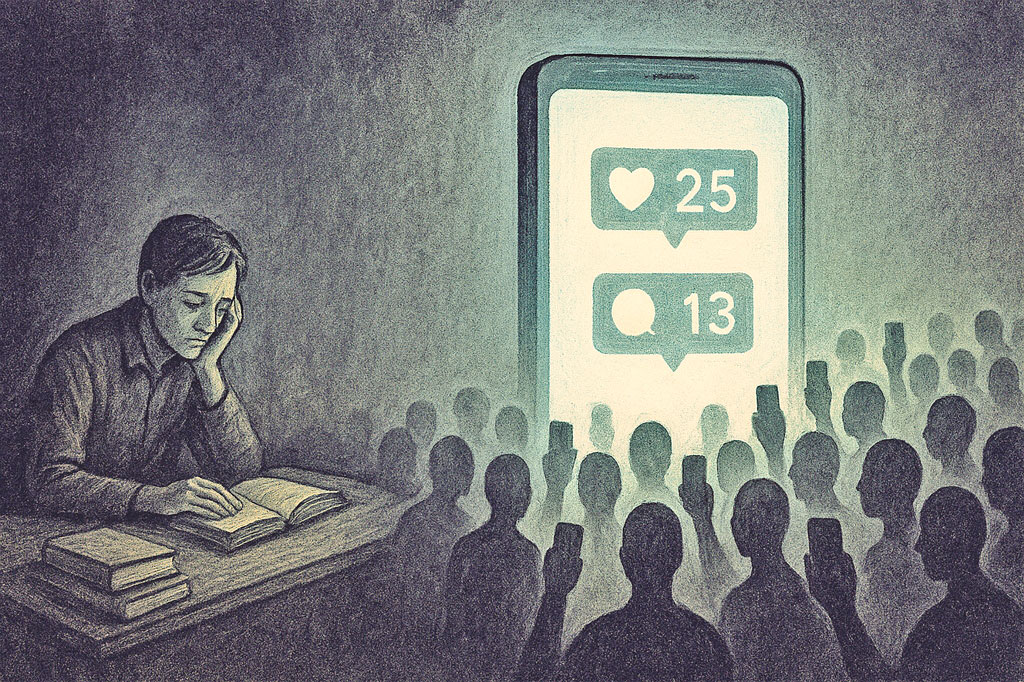
আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে মানুষের মূল্য আর তার চিন্তার গভীরতা, সততা বা মেধার ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে সে কতটা ‘ভাইরাল’ হতে পারে তার ওপর। ‘ভাইরাল’ এখন শুধু একটি শব্দ নয়, এটি এক প্রজন্মের মানদণ্ড, এক সমাজের সফলতার পরিমাপক।
৫ ঘণ্টা আগে
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য ও বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী এক নেতার একটি ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর তা ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যদিও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভিডিওটি এডিট করা, তবু যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে এই নেতাকে...
৫ ঘণ্টা আগে
হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার মাসুদ রানা।
মাসুদ রানা

সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে নতুন করে দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ তুলেছে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বক্তব্যের অনেকাংশের সত্যতা আছে। আবার তারা কোন মানদণ্ডে ব্যাপারগুলোকে দেখছে, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার না। তবে এটা সত্য যে দুই ধরনের অভিযোগ এই সরকারের বিরুদ্ধে তোলা যায়। একটা হলো, অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয়তার জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যাচ্ছে। যেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সরকারের সক্রিয়তা থাকা দরকার, সেখানে কোনো ধরনের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আবার অন্য ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিযোগ অনুযায়ী, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কি এমন কোনো অস্পষ্টতা আছে, যা এর অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করছে?
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কোনো অস্পষ্টতা বলে কিছু নেই। এই আইনটা নিজেই এমন যে এর অপব্যবহার করা সহজ। উল্টোভাবে বললে এ আইনটি অব্যবহার না করলেই নয়। বরং এর ব্যবহার করে রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। কারণ, এই আইনটা করা হয়েছিল রাজনৈতিক পরিসরে মানুষ যখন ক্ষোভ থেকে আন্দোলন করে এবং নিজ অভিব্যক্তির জায়গা থেকে প্রতিবাদ করে, তখন আইনশৃঙ্খলাবিরোধী এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। এ আইনটাকে এখনো অগণতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আইনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এইচআরডব্লিউর এই অভিযোগ সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় কি?
সেটা তো অবশ্যই সাংঘর্ষিক। কারণ, সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি যেভাবে হামলা করা হলো এবং শিক্ষকদের সঙ্গে যে আচরণটা করা হলো, মিছিলে যেভাবে জলকামান ব্যবহার করা হলো এবং তাঁদের ওপর পুলিশ যেভাবে চড়াও হয়েছে, নির্যাতন করেছে, যেভাবে শিক্ষকদের টেনেহিঁচড়ে আটক করেছে, সেটাকে কী বলা যায়? কোনো মানুষ এ ধরনের আচরণকে সমর্থন করতে পারে না।
এই সরকার যে মানবিক মর্যাদা, মানবাধিকার কিংবা আইনের শাসনের ক্ষেত্রে আগের সরকারের মতো হবে না—এই অঙ্গীকার করেছিল। সেটা তো শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেই বোঝা গেল। এগুলো তো হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ব্যাপার না শুধু। আমরা তো সবাই এসব দেখছি। এই সরকারের প্রধান সমস্যা, যেটা আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, যেখানে যেটা করার কথা না, সেখানে সেটাই করা হচ্ছে। শিক্ষকদের ওপর বলপ্রয়োগের কথা না, কিন্তু সেটাই করা হলো। যখন রাষ্ট্রের যেকোনো সেক্টরের পেশাজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে উত্থাপন করার জন্য আসছে, তাদের ওপরই বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে।
আর যারা মানুষের জান-মালের ক্ষতি করছে, মানুষের নিরাপত্তা নষ্ট করছে, তাদের বেলায় পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এখন পুলিশকে ন্যায়ের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হতে আর অন্যায়ের পক্ষে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পর অন্তর্বর্তী সরকার যে অঙ্গীকার করেছিল, সেটার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
এর কারণ কী?
প্রধানত তিনটা কারণে এসব হচ্ছে। প্রথমত, এ সরকারের অদক্ষতা। দেশ আসলে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং এর জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়—এসব তারা জানে না। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে যে বাহিনী ছিল তাদের কোনো ধরনের সংস্কার না করে এবং তাদের কোনো ধরনের সংস্কারের আওতায় না এনে, সেই বাহিনীর মনোবল ফেরানোর কথা বলা হচ্ছে। তার মানে দাঁড়ায়, এই বাহিনীকে আগের মতোই আচরণ করার কথা বলা হচ্ছে। এ কারণেই তারা অনেক ক্ষেত্রে আগের মতোই আচরণ করছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও গাইড করা হয়নি। এ কারণে তারা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের যে জনগণের প্রতি মানবিক হওয়া দরকার, সে বিষয়ে কোনো ধরনের জ্ঞান, ধারণা ও ট্রেনিং নেই। যখন আবার এই বাহিনীকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, তখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটছে মূলত সরকারের অদক্ষতা এবং এই বাহিনীর সদস্যদের চরিত্রের অসংগতির কারণে। আর এই বাহিনী হলো চরিত্রগতভাবেই স্বৈরাচার।
সরকার তো পুলিশ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল।
অন্তর্বর্তী সরকারের পরবর্তী সময়ে অপরাধ হিসেবে সামনে আসবে পুলিশের সংস্কার ঠিকমতো না করা। আমাদের দেশে সবচেয়ে জটিল হলো পুলিশের সংস্কার। কিন্তু এবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এর সংস্কার করার। এর আগে সব সময় পুলিশকে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের পর পুলিশের সাধারণ সদস্যরা দাবি তুলেছিলেন এ বাহিনীর সংস্কার করার জন্য। পুলিশ যেন আর কোনো সরকারের বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে। কিন্তু এ সরকার কোনোভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল না। এই দায়িত্ব পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হলো। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী যে নতুন বাংলাদেশ হওয়ার কথা ছিল, সেই ব্যর্থতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো পুলিশ বাহিনীকে ঠিকমতো সংস্কার করতে না পারা।
অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের অনেকের বিরুদ্ধেই শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। তাহলে এ সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কী থাকল?
সত্যি সত্যি যেটা দরকার ছিল—যাকে যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করা। ধরুন, কেউ একজন ছিলেন ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, অর্থ আত্মসাৎকারী, অন্য দলের প্রতি বা অন্য ব্যক্তির প্রতি জুলুমকারী—এখন তাঁদের যদি খুনের মামলার আসামি করা হয়, তখন বুঝতে হবে তাঁদের ভুল মামলার আসামি করা হয়েছে। যদিও তাঁরা খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পুলিশ ও আইন সরকারের নিয়ন্ত্রণে না থাকার কারণে গড়ে সব ধরনের আসামিকে গ্রেপ্তার করার জন্য হত্যা মামলা ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তাতে সরকার নিজেই ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেখানো গেছে, যারা নির্দিষ্ট কোনো অপরাধে অপরাধী না, সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নির্দোষ বলা হচ্ছে। ধরেন, একজন খুনের মামলার আসামি না, কিন্তু তিনি চুরি মামলার আসামি। যখন এক মামলার অপরাধে অন্য মামলায় আসামি করা হচ্ছে, তখন কিন্তু চুরির অপরাধটাও নাই হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন। এই ধরনের একটা প্রক্রিয়া এখানে শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার কারণে প্রকৃত অপরাধীর যেমন বিচার হবে না, তেমনি খুনের মামলারও ঠিকমতো বিচার হবে না। জনগণও ঠিকমতো বিচার পাবে না। কিন্তু এ সরকারকে একধরনের অবিচারের দায় নিয়ে বিদায় নিতে হবে।
অন্তর্বর্তী সরকার যদি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করার সাহস দেখাতে পারে, সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল তবিয়তে রেখেছে কেন?
সন্ত্রাসবিরোধী আইন যখন করা হয়, তখন এ আইন বাতিলের দাবিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে। এ আইন করার জন্য মামলা হয়েছে। ওই সময় এ আইনের মেয়াদ দুই বছর পরপর বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এখন এটা স্থায়ী করা হয়েছে। এখানে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নামে একটা আইন আছে। এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কালাকানুন নাম দিয়ে তা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এই সরকার তো এই আইনগুলো বাতিল করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কোন কোন আইন বাতিল করতে হবে, তার জন্য তারা তো কোনো আইন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আইন বাতিলের কোনো তালিকাও করেনি।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ঘাড়ের ওপর দাঁড়ানো ছিল। কারণ, আন্দোলনকারীরা কম-বেশি এ আইন দিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন অথবা এ আইনের কারণে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন—এসব কারণে এই আইন বাতিলের চাপ ছিল। সে কারণে সরকার এটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ আইনটাকে ধরে এখন সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকেও অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। অহিংস গণ-অভ্যুত্থান নামে একটা সংগঠন আছে। তারা দেশের লুটপাট, পাচারের টাকা ফেরত এনে সাধারণ মানুষকে যেন বিনা সুদে দেওয়া হয়, সে জন্য আন্দোলন করেছে। সেই আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে। এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে?
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু রক্ত ঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত এ সরকার কি সেই দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে?
এটা তো আসলে আন্দোলনকারীদেরও ব্যর্থতা। আবার এই সরকার তো অসম্ভব রকমের অদক্ষ সরকার। তারা কী কারণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা আমিও বুঝতে পারি না। এই সরকার তো কোনো কেয়ারটেকার সরকার না। এ সরকারের তিন মাসের মধ্যে একটা নির্বাচন দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। এ সরকারের দায়িত্ব ছিল স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা। সেসবের হোমওয়ার্ক নেই, তারা বাংলাদেশের আইনকানুন, সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা না রেখেই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে।
এই সরকারের অদক্ষতার জায়গা হলো, কারা এসব নিয়ে কাজ করেছে, সেটা তারা জানে না। জানলেও তারা তাদের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে সরকার যখন বেকায়দায় পড়েছে, তখন সবাইকে ডেকেছে। তারা বলতে চেয়েছে, সব রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে আছে। যদিও এই অভ্যুত্থানের পরাজিত শক্তি যদি ফিরে এসে আরও ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য এ সরকারকে আমরা এখনো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।
সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে নতুন করে দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ তুলেছে। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বক্তব্যের অনেকাংশের সত্যতা আছে। আবার তারা কোন মানদণ্ডে ব্যাপারগুলোকে দেখছে, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার না। তবে এটা সত্য যে দুই ধরনের অভিযোগ এই সরকারের বিরুদ্ধে তোলা যায়। একটা হলো, অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয়তার জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যাচ্ছে। যেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সরকারের সক্রিয়তা থাকা দরকার, সেখানে কোনো ধরনের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আবার অন্য ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার মতো করে ব্যবহার করা হচ্ছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের অভিযোগ অনুযায়ী, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কি এমন কোনো অস্পষ্টতা আছে, যা এর অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করছে?
সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কোনো অস্পষ্টতা বলে কিছু নেই। এই আইনটা নিজেই এমন যে এর অপব্যবহার করা সহজ। উল্টোভাবে বললে এ আইনটি অব্যবহার না করলেই নয়। বরং এর ব্যবহার করে রাজনৈতিক আলোচনা সভা বা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। কারণ, এই আইনটা করা হয়েছিল রাজনৈতিক পরিসরে মানুষ যখন ক্ষোভ থেকে আন্দোলন করে এবং নিজ অভিব্যক্তির জায়গা থেকে প্রতিবাদ করে, তখন আইনশৃঙ্খলাবিরোধী এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। এ আইনটাকে এখনো অগণতান্ত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য আইনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এইচআরডব্লিউর এই অভিযোগ সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় কি?
সেটা তো অবশ্যই সাংঘর্ষিক। কারণ, সম্প্রতি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রতি যেভাবে হামলা করা হলো এবং শিক্ষকদের সঙ্গে যে আচরণটা করা হলো, মিছিলে যেভাবে জলকামান ব্যবহার করা হলো এবং তাঁদের ওপর পুলিশ যেভাবে চড়াও হয়েছে, নির্যাতন করেছে, যেভাবে শিক্ষকদের টেনেহিঁচড়ে আটক করেছে, সেটাকে কী বলা যায়? কোনো মানুষ এ ধরনের আচরণকে সমর্থন করতে পারে না।
এই সরকার যে মানবিক মর্যাদা, মানবাধিকার কিংবা আইনের শাসনের ক্ষেত্রে আগের সরকারের মতো হবে না—এই অঙ্গীকার করেছিল। সেটা তো শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেই বোঝা গেল। এগুলো তো হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ব্যাপার না শুধু। আমরা তো সবাই এসব দেখছি। এই সরকারের প্রধান সমস্যা, যেটা আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, যেখানে যেটা করার কথা না, সেখানে সেটাই করা হচ্ছে। শিক্ষকদের ওপর বলপ্রয়োগের কথা না, কিন্তু সেটাই করা হলো। যখন রাষ্ট্রের যেকোনো সেক্টরের পেশাজীবী মানুষ তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে উত্থাপন করার জন্য আসছে, তাদের ওপরই বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে।
আর যারা মানুষের জান-মালের ক্ষতি করছে, মানুষের নিরাপত্তা নষ্ট করছে, তাদের বেলায় পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। এখন পুলিশকে ন্যায়ের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হতে আর অন্যায়ের পক্ষে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পর অন্তর্বর্তী সরকার যে অঙ্গীকার করেছিল, সেটার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
এর কারণ কী?
প্রধানত তিনটা কারণে এসব হচ্ছে। প্রথমত, এ সরকারের অদক্ষতা। দেশ আসলে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং এর জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়—এসব তারা জানে না। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে যে বাহিনী ছিল তাদের কোনো ধরনের সংস্কার না করে এবং তাদের কোনো ধরনের সংস্কারের আওতায় না এনে, সেই বাহিনীর মনোবল ফেরানোর কথা বলা হচ্ছে। তার মানে দাঁড়ায়, এই বাহিনীকে আগের মতোই আচরণ করার কথা বলা হচ্ছে। এ কারণেই তারা অনেক ক্ষেত্রে আগের মতোই আচরণ করছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নতুনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও গাইড করা হয়নি। এ কারণে তারা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের যে জনগণের প্রতি মানবিক হওয়া দরকার, সে বিষয়ে কোনো ধরনের জ্ঞান, ধারণা ও ট্রেনিং নেই। যখন আবার এই বাহিনীকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, তখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটছে মূলত সরকারের অদক্ষতা এবং এই বাহিনীর সদস্যদের চরিত্রের অসংগতির কারণে। আর এই বাহিনী হলো চরিত্রগতভাবেই স্বৈরাচার।
সরকার তো পুলিশ সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল।
অন্তর্বর্তী সরকারের পরবর্তী সময়ে অপরাধ হিসেবে সামনে আসবে পুলিশের সংস্কার ঠিকমতো না করা। আমাদের দেশে সবচেয়ে জটিল হলো পুলিশের সংস্কার। কিন্তু এবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এর সংস্কার করার। এর আগে সব সময় পুলিশকে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের পর পুলিশের সাধারণ সদস্যরা দাবি তুলেছিলেন এ বাহিনীর সংস্কার করার জন্য। পুলিশ যেন আর কোনো সরকারের বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে। কিন্তু এ সরকার কোনোভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল না। এই দায়িত্ব পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হলো। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী যে নতুন বাংলাদেশ হওয়ার কথা ছিল, সেই ব্যর্থতার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো পুলিশ বাহিনীকে ঠিকমতো সংস্কার করতে না পারা।
অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের অনেকের বিরুদ্ধেই শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। তাহলে এ সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কী থাকল?
সত্যি সত্যি যেটা দরকার ছিল—যাকে যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত করা। ধরুন, কেউ একজন ছিলেন ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, অর্থ আত্মসাৎকারী, অন্য দলের প্রতি বা অন্য ব্যক্তির প্রতি জুলুমকারী—এখন তাঁদের যদি খুনের মামলার আসামি করা হয়, তখন বুঝতে হবে তাঁদের ভুল মামলার আসামি করা হয়েছে। যদিও তাঁরা খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পুলিশ ও আইন সরকারের নিয়ন্ত্রণে না থাকার কারণে গড়ে সব ধরনের আসামিকে গ্রেপ্তার করার জন্য হত্যা মামলা ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তাতে সরকার নিজেই ন্যায়বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেখানো গেছে, যারা নির্দিষ্ট কোনো অপরাধে অপরাধী না, সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নির্দোষ বলা হচ্ছে। ধরেন, একজন খুনের মামলার আসামি না, কিন্তু তিনি চুরি মামলার আসামি। যখন এক মামলার অপরাধে অন্য মামলায় আসামি করা হচ্ছে, তখন কিন্তু চুরির অপরাধটাও নাই হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছেন। এই ধরনের একটা প্রক্রিয়া এখানে শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার কারণে প্রকৃত অপরাধীর যেমন বিচার হবে না, তেমনি খুনের মামলারও ঠিকমতো বিচার হবে না। জনগণও ঠিকমতো বিচার পাবে না। কিন্তু এ সরকারকে একধরনের অবিচারের দায় নিয়ে বিদায় নিতে হবে।
অন্তর্বর্তী সরকার যদি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করার সাহস দেখাতে পারে, সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল তবিয়তে রেখেছে কেন?
সন্ত্রাসবিরোধী আইন যখন করা হয়, তখন এ আইন বাতিলের দাবিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে। এ আইন করার জন্য মামলা হয়েছে। ওই সময় এ আইনের মেয়াদ দুই বছর পরপর বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এখন এটা স্থায়ী করা হয়েছে। এখানে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নামে একটা আইন আছে। এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কালাকানুন নাম দিয়ে তা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এই সরকার তো এই আইনগুলো বাতিল করার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কোন কোন আইন বাতিল করতে হবে, তার জন্য তারা তো কোনো আইন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আইন বাতিলের কোনো তালিকাও করেনি।
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ঘাড়ের ওপর দাঁড়ানো ছিল। কারণ, আন্দোলনকারীরা কম-বেশি এ আইন দিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন অথবা এ আইনের কারণে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছেন—এসব কারণে এই আইন বাতিলের চাপ ছিল। সে কারণে সরকার এটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ আইনটাকে ধরে এখন সন্ত্রাসবিরোধী আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনকেও অপব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। অহিংস গণ-অভ্যুত্থান নামে একটা সংগঠন আছে। তারা দেশের লুটপাট, পাচারের টাকা ফেরত এনে সাধারণ মানুষকে যেন বিনা সুদে দেওয়া হয়, সে জন্য আন্দোলন করেছে। সেই আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে। এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী হতে পারে?
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। কিন্তু রক্ত ঝরা আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত এ সরকার কি সেই দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে?
এটা তো আসলে আন্দোলনকারীদেরও ব্যর্থতা। আবার এই সরকার তো অসম্ভব রকমের অদক্ষ সরকার। তারা কী কারণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছে, সেটা আমিও বুঝতে পারি না। এই সরকার তো কোনো কেয়ারটেকার সরকার না। এ সরকারের তিন মাসের মধ্যে একটা নির্বাচন দিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। এ সরকারের দায়িত্ব ছিল স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা। সেসবের হোমওয়ার্ক নেই, তারা বাংলাদেশের আইনকানুন, সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা না রেখেই কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে।
এই সরকারের অদক্ষতার জায়গা হলো, কারা এসব নিয়ে কাজ করেছে, সেটা তারা জানে না। জানলেও তারা তাদের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে সরকার যখন বেকায়দায় পড়েছে, তখন সবাইকে ডেকেছে। তারা বলতে চেয়েছে, সব রাজনৈতিক দল আমাদের সঙ্গে আছে। যদিও এই অভ্যুত্থানের পরাজিত শক্তি যদি ফিরে এসে আরও ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য এ সরকারকে আমরা এখনো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি।
সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আজকের পত্রিকাকেও ধন্যবাদ।
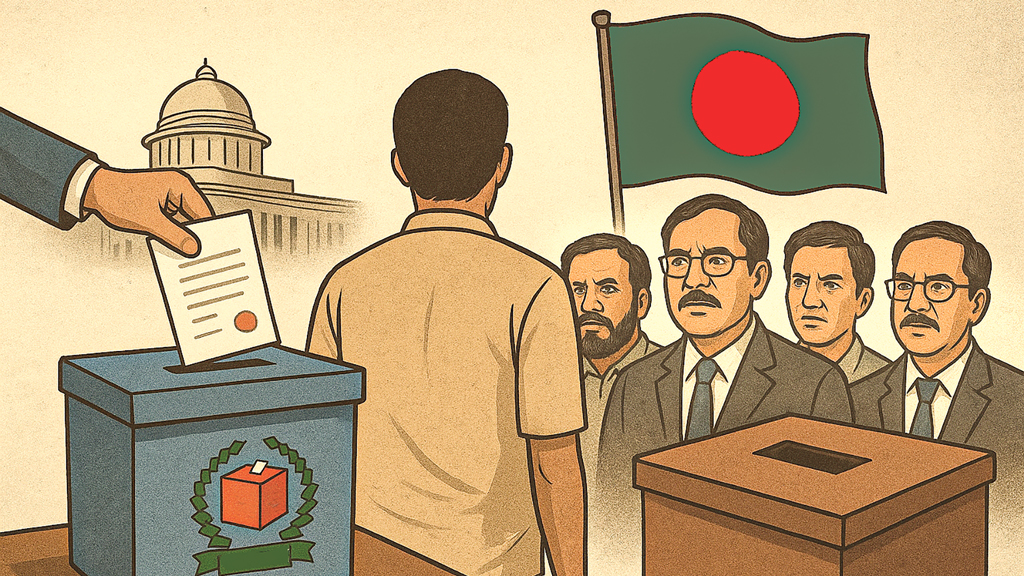
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
১ দিন আগে
জুলাই সনদ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা, জোট রাজনীতি, নারীনীতি, নির্বাচনী প্রতীক ইস্যু থেকে শুরু করে ফান্ডিং ও ‘মেধা বনাম কোটার’ বিতর্ক—এসব বিষয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা..
২ ঘণ্টা আগে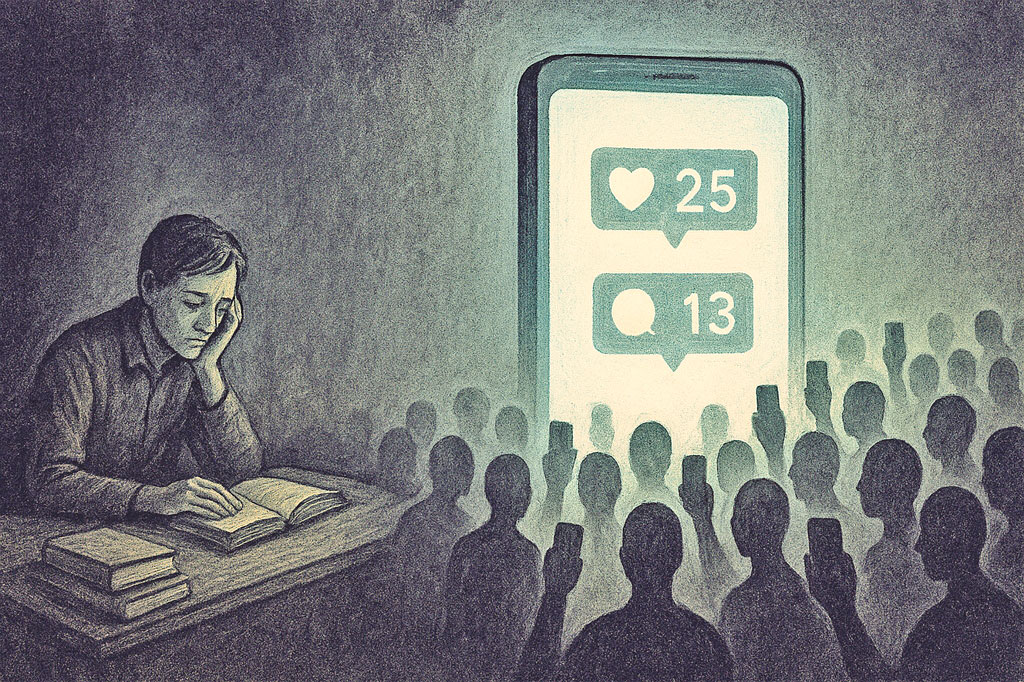
আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে মানুষের মূল্য আর তার চিন্তার গভীরতা, সততা বা মেধার ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে সে কতটা ‘ভাইরাল’ হতে পারে তার ওপর। ‘ভাইরাল’ এখন শুধু একটি শব্দ নয়, এটি এক প্রজন্মের মানদণ্ড, এক সমাজের সফলতার পরিমাপক।
৫ ঘণ্টা আগে
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য ও বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী এক নেতার একটি ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর তা ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যদিও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভিডিওটি এডিট করা, তবু যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে এই নেতাকে...
৫ ঘণ্টা আগেমো. শামীম মিয়া
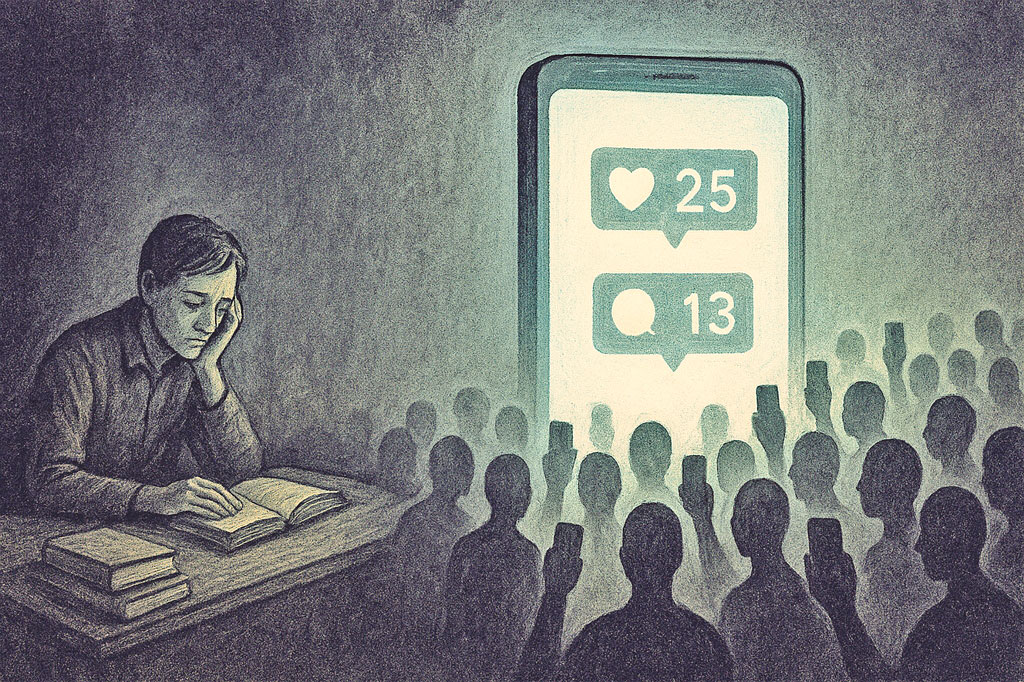
আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে মানুষের মূল্য আর তার চিন্তার গভীরতা, সততা বা মেধার ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে সে কতটা ‘ভাইরাল’ হতে পারে তার ওপর। ‘ভাইরাল’ এখন শুধু একটি শব্দ নয়, এটি এক প্রজন্মের মানদণ্ড, এক সমাজের সফলতার পরিমাপক। একসময়ের আদর্শনিষ্ঠ সমাজ আজ ক্লিক, ভিউ, লাইক আর ফলোয়ারের সংখ্যায় বিচার করছে মানুষকে। এই নতুন সংস্কৃতিতে মেধা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ যেন হারিয়ে যাচ্ছে একদম নিঃশব্দে—যেভাবে গোধূলির আলো হারিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে।
একসময় মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করত জ্ঞান, পরিশ্রম, সততা এবং নৈতিকতার মাধ্যমে। একজন শিক্ষক, গবেষক বা চিন্তাবিদ সমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসতেন। এখন সে জায়গা দখল করে নিয়েছে এক মিনিটের ভিডিও নির্মাতা, নাটকীয় মুখভঙ্গির ইনফ্লুয়েন্সার কিংবা বিতর্ক সৃষ্টিকারী মুখোশধারী ব্যক্তিত্ব। সমাজে এখন আর প্রশ্ন হয় না—‘সে মানুষটা কেমন?’ বরং প্রশ্ন হয়—‘তার কত ফলোয়ার?’ আর এই প্রশ্নই আসলে আমাদের পতনের সবচেয়ে বড় সূচক।
আজকে একজন তরুণ তাঁর দিনরাতের পরিশ্রম দিয়ে যদি একটি গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন, কেউ তা দেখে না। কিন্তু কেউ যদি কোনো চমকপ্রদ ভিডিও বানিয়ে কিছু নাটকীয় সংলাপ বলে, মুহূর্তেই সে ‘স্টার’। আমরা এখন এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে প্রচারণা সত্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে গেছে, আর জনপ্রিয়তা মেধার স্থান দখল করেছে।
এই ভাইরাল সংস্কৃতি আসলে কেবল একটি বিনোদন নয়, এটি সমাজের চিন্তা, নীতি ও নৈতিকতার মূলভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এখন মানুষ জ্ঞান বা মূল্যবোধ নয়, বরং ‘দেখানোর’ প্রতিযোগিতায় নামছে। আমরা তথ্যের চেয়ে ‘ইমপ্রেশন’ খুঁজি, চিন্তার চেয়ে ‘রিঅ্যাকশন’ চাই, যুক্তির চেয়ে ‘ভিউ’ দেখি। এই পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটেছে যে আমরা বুঝতেই পারিনি একটা গোটা প্রজন্ম ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে চিন্তা করার ক্ষমতা।
মানুষ এখন আর জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট নয়, বরং বিনোদনের প্রতি আসক্ত। সমাজে যে জায়গায় একসময় গুরুজনদের বক্তব্য, পণ্ডিতদের চিন্তা বা লেখকদের কলাম আলোচনার বিষয় হতো, এখন সেখানে স্থান পেয়েছে মেকি হাসি, সাজানো ঝগড়া আর মনগড়া কাহিনি। একজন মেধাবী মানুষ হয়তো সারা জীবন পরিশ্রম করে সমাজে ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ চাপা পড়ে যায় জনপ্রিয়তার কোলাহলে।
এই ভাইরাল সংস্কৃতির পেছনে তিনটি বড় শক্তি কাজ করছে—প্রযুক্তির অ্যালগরিদম, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা এবং সমাজে গভীর চিন্তার অভাব। সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম এমনভাবে কাজ করে যে যেসব বিষয় মানুষকে আবেগপ্রবণ করে, তা-ই বেশি প্রচার পায়। যত বেশি উত্তেজনাপূর্ণ, বিতর্কিত বা নাটকীয় কোনো কনটেন্ট, তত বেশি ‘রিচ’। ফলে মানুষ এখন বিষয়বস্তুর সত্যতা নয়, বরং তার ‘প্রভাব’ দেখেই প্রতিক্রিয়া দেয়।
অন্যদিকে, দর্শক এখন চিন্তা করতে চায় না, তারা চায় সহজ বিনোদন। একটা মজার ভিডিও দেখা বা কারও চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, কারণ এতে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রম লাগে না। এই সহজ আনন্দের চাহিদাই ‘ভাইরাল অর্থনীতি’ তৈরি করেছে, যেখানে মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও নাটকই আসল পণ্য। এই পরিবেশে সৎ ও মেধাবী মানুষেরা হয়ে পড়ছেন একেবারে নিঃসঙ্গ। তাঁদের কথা কেউ শুনতে চায় না, তাঁদের লেখা কেউ পড়ে না, কারণ তাঁরা ট্রেন্ডে নেই। সমাজে এখন নীরব হয়ে যাচ্ছে সেইসব মানুষ, যাঁদের সততা একসময় ছিল সমাজের নৈতিক শক্তি। তাঁরা আজ কোণঠাসা, কেউ কেউ হয়তো হতাশ। তাঁরা জানে, সত্য কথায় কেউ করতালি দেয় না; বরং তুচ্ছ, হাস্যকর কিংবা অশালীন কিছু বললে মুহূর্তেই হাজারো শেয়ার হয়।
ফলাফল হিসেবে জন্ম নিচ্ছে একধরনের সাংস্কৃতিক শূন্যতা। সততার জায়গায় এসেছে মুখোশ, মেধার জায়গায় এসেছে কৌশল এবং সত্যের জায়গায় এসেছে প্রচারণা। সমাজ এখন যেন এক বড় মঞ্চ, যেখানে সবাই অভিনয় করছে, কিন্তু কেউ নিজের চরিত্রে নেই। সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো, এই ভাইরাল সংস্কৃতি এখন আমাদের তরুণ প্রজন্মের চেতনায় প্রভাব ফেলছে। আজকের যুবক-যুবতীরা মনে করছে জীবনে সফলতা মানে জনপ্রিয়তা, আর জনপ্রিয়তা মানে ভাইরাল হওয়া। তাই তারা নিজেদের গড়ার চেয়ে, নিজেদের ‘দেখানোর’ প্রতিযোগিতায় নামছে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী আলো নিভে গেলে তারা যে শূন্যতা অনুভব করবে, তার জন্য কেউ প্রস্তুত নয়। ভাইরাল সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই, এটি ছুঁয়ে ফেলেছে আমাদের রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, এমনকি মানবিক সম্পর্ককেও। এখন ভালো কাজ করলেও সেটি পোস্ট না দিলে যেন তার কোনো মূল্য নেই। আমরা মানুষকে সাহায্য করি ক্যামেরার সামনে, কান্না করি লাইভে, আর প্রার্থনা করি দর্শকের লাইক পাওয়ার আশায়। মানবিকতা এখন যেন একপ্রকার অভিনয়ের অংশ, আর নৈতিকতা কেবল কনটেন্টের উপকরণ।
আমাদের রাজনীতিতেও দেখা যাচ্ছে এই সংস্কৃতির ছায়া। যোগ্যতা, চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ‘চমক’। একজন রাজনীতিকের বক্তব্য ভাইরাল হলেই তিনি আলোচনায় আসেন, নীতিনিষ্ঠ বক্তব্য দিলে নয়। ফলে রাজনীতি থেকেও হারিয়ে যাচ্ছে যুক্তি ও সততার জায়গা।
এই ভাইরাল মানসিকতা একপ্রকার বিষক্রিয়া, যা ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তা ও বিবেককে অবশ করে ফেলছে। আমরা এখন এমন এক সমাজে রূপ নিচ্ছি, যেখানে মানুষকে বিচার করা হয় তার ‘লাইক’ সংখ্যায়, তার কাজের প্রভাবে নয়। এই বিচারের মানদণ্ড যত বাড়ছে, ততই মেধাবীরা পিছিয়ে পড়ছে। কারণ তারা জানে, তাদের কাছে প্রচার নয়, সত্যটাই বড়। আর সেই সত্যই আজ সবচেয়ে কম বিক্রীত জিনিস।
তবে সব অন্ধকারের মাঝেও একটুখানি আলো এখনো আছে। কারণ ইতিহাস সাক্ষী, প্রচারণা কখনো চিরস্থায়ী হয়নি। সত্যই টিকে থেকেছে। সময়ের আবর্তে মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের জোয়ার একদিন নিজেই থেমে যাবে, কিন্তু সত্য, মেধা ও সততা তখনো থাকবে। শুধু দরকার সমাজের মানুষকে নতুন করে ভাবানো—আমরা কাকে মূল্য দিচ্ছি, কাকে অনুসরণ করছি, কাকে রোল মডেল বানাচ্ছি।
আজ প্রয়োজন এক নতুন সামাজিক আন্দোলনের, যেখানে ভাইরাল হওয়া নয়, মূল্যবোধই হবে নেতৃত্বের মাপকাঠি। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে—সাফল্য মানে কেবল খ্যাতি নয়, বরং দায়িত্ববোধ, জ্ঞান ও নৈতিক সাহস। তাদের বোঝাতে হবে, জীবনের আসল জয় ভিউ দিয়ে হয় না, হয় সম্মান দিয়ে; প্রচারণা দিয়ে নয়, হয় চরিত্র দিয়ে। যদি আমরা এই পরিবর্তন আনতে পারি, তবে হয়তো সমাজ আবার ফিরে পাবে সেই হারানো ভারসাম্য, যেখানে মানুষকে মাপা হবে তার সততা ও মেধায়—জনপ্রিয়তায় নয়। আজ মেধাবীরা হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা মরে যায়নি। সততার আলো হয়তো ক্ষীণ, কিন্তু নিভে যায়নি। সেই আলো একদিন আবার ছড়িয়ে পড়বে, যদি কেউ একজন সাহস করে সেটি জ্বালিয়ে রাখে। আমাদের দায়িত্ব সেই সাহস দেখানো। কারণ, ভাইরাল নয়, মূল্যবোধই একদিন হবে মানুষের সত্যিকারের পরিচয়।
লেখক: শিক্ষার্থী, ফুলছড়ি সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা
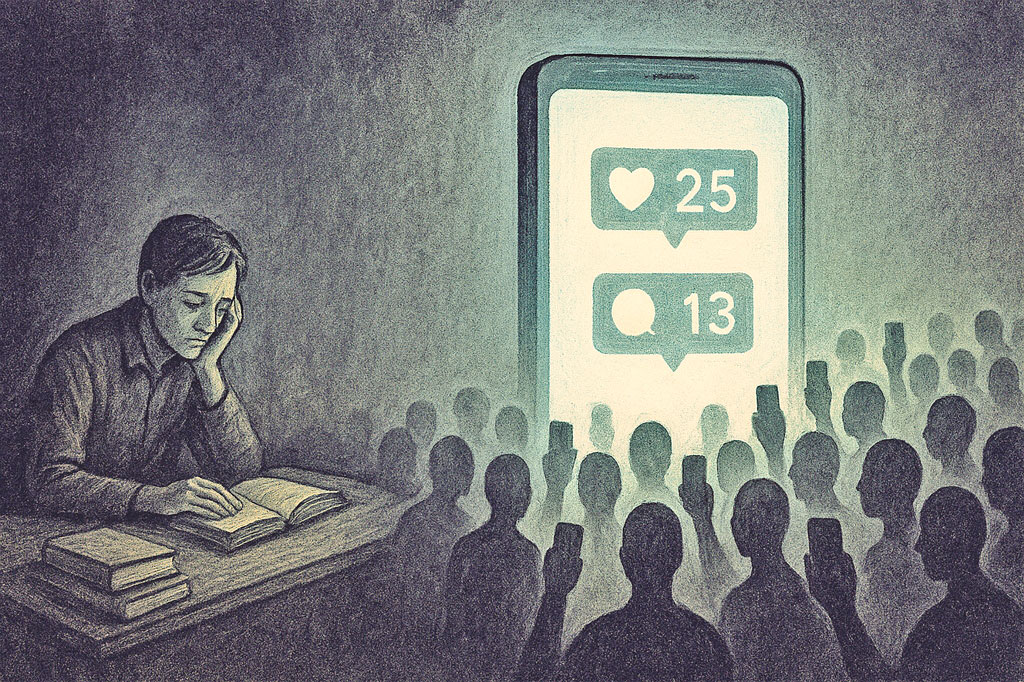
আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে মানুষের মূল্য আর তার চিন্তার গভীরতা, সততা বা মেধার ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে সে কতটা ‘ভাইরাল’ হতে পারে তার ওপর। ‘ভাইরাল’ এখন শুধু একটি শব্দ নয়, এটি এক প্রজন্মের মানদণ্ড, এক সমাজের সফলতার পরিমাপক। একসময়ের আদর্শনিষ্ঠ সমাজ আজ ক্লিক, ভিউ, লাইক আর ফলোয়ারের সংখ্যায় বিচার করছে মানুষকে। এই নতুন সংস্কৃতিতে মেধা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ যেন হারিয়ে যাচ্ছে একদম নিঃশব্দে—যেভাবে গোধূলির আলো হারিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে।
একসময় মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করত জ্ঞান, পরিশ্রম, সততা এবং নৈতিকতার মাধ্যমে। একজন শিক্ষক, গবেষক বা চিন্তাবিদ সমাজে শ্রদ্ধার আসনে বসতেন। এখন সে জায়গা দখল করে নিয়েছে এক মিনিটের ভিডিও নির্মাতা, নাটকীয় মুখভঙ্গির ইনফ্লুয়েন্সার কিংবা বিতর্ক সৃষ্টিকারী মুখোশধারী ব্যক্তিত্ব। সমাজে এখন আর প্রশ্ন হয় না—‘সে মানুষটা কেমন?’ বরং প্রশ্ন হয়—‘তার কত ফলোয়ার?’ আর এই প্রশ্নই আসলে আমাদের পতনের সবচেয়ে বড় সূচক।
আজকে একজন তরুণ তাঁর দিনরাতের পরিশ্রম দিয়ে যদি একটি গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন, কেউ তা দেখে না। কিন্তু কেউ যদি কোনো চমকপ্রদ ভিডিও বানিয়ে কিছু নাটকীয় সংলাপ বলে, মুহূর্তেই সে ‘স্টার’। আমরা এখন এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে প্রচারণা সত্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে গেছে, আর জনপ্রিয়তা মেধার স্থান দখল করেছে।
এই ভাইরাল সংস্কৃতি আসলে কেবল একটি বিনোদন নয়, এটি সমাজের চিন্তা, নীতি ও নৈতিকতার মূলভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এখন মানুষ জ্ঞান বা মূল্যবোধ নয়, বরং ‘দেখানোর’ প্রতিযোগিতায় নামছে। আমরা তথ্যের চেয়ে ‘ইমপ্রেশন’ খুঁজি, চিন্তার চেয়ে ‘রিঅ্যাকশন’ চাই, যুক্তির চেয়ে ‘ভিউ’ দেখি। এই পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটেছে যে আমরা বুঝতেই পারিনি একটা গোটা প্রজন্ম ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে চিন্তা করার ক্ষমতা।
মানুষ এখন আর জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট নয়, বরং বিনোদনের প্রতি আসক্ত। সমাজে যে জায়গায় একসময় গুরুজনদের বক্তব্য, পণ্ডিতদের চিন্তা বা লেখকদের কলাম আলোচনার বিষয় হতো, এখন সেখানে স্থান পেয়েছে মেকি হাসি, সাজানো ঝগড়া আর মনগড়া কাহিনি। একজন মেধাবী মানুষ হয়তো সারা জীবন পরিশ্রম করে সমাজে ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ চাপা পড়ে যায় জনপ্রিয়তার কোলাহলে।
এই ভাইরাল সংস্কৃতির পেছনে তিনটি বড় শক্তি কাজ করছে—প্রযুক্তির অ্যালগরিদম, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা এবং সমাজে গভীর চিন্তার অভাব। সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম এমনভাবে কাজ করে যে যেসব বিষয় মানুষকে আবেগপ্রবণ করে, তা-ই বেশি প্রচার পায়। যত বেশি উত্তেজনাপূর্ণ, বিতর্কিত বা নাটকীয় কোনো কনটেন্ট, তত বেশি ‘রিচ’। ফলে মানুষ এখন বিষয়বস্তুর সত্যতা নয়, বরং তার ‘প্রভাব’ দেখেই প্রতিক্রিয়া দেয়।
অন্যদিকে, দর্শক এখন চিন্তা করতে চায় না, তারা চায় সহজ বিনোদন। একটা মজার ভিডিও দেখা বা কারও চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়, কারণ এতে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রম লাগে না। এই সহজ আনন্দের চাহিদাই ‘ভাইরাল অর্থনীতি’ তৈরি করেছে, যেখানে মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও নাটকই আসল পণ্য। এই পরিবেশে সৎ ও মেধাবী মানুষেরা হয়ে পড়ছেন একেবারে নিঃসঙ্গ। তাঁদের কথা কেউ শুনতে চায় না, তাঁদের লেখা কেউ পড়ে না, কারণ তাঁরা ট্রেন্ডে নেই। সমাজে এখন নীরব হয়ে যাচ্ছে সেইসব মানুষ, যাঁদের সততা একসময় ছিল সমাজের নৈতিক শক্তি। তাঁরা আজ কোণঠাসা, কেউ কেউ হয়তো হতাশ। তাঁরা জানে, সত্য কথায় কেউ করতালি দেয় না; বরং তুচ্ছ, হাস্যকর কিংবা অশালীন কিছু বললে মুহূর্তেই হাজারো শেয়ার হয়।
ফলাফল হিসেবে জন্ম নিচ্ছে একধরনের সাংস্কৃতিক শূন্যতা। সততার জায়গায় এসেছে মুখোশ, মেধার জায়গায় এসেছে কৌশল এবং সত্যের জায়গায় এসেছে প্রচারণা। সমাজ এখন যেন এক বড় মঞ্চ, যেখানে সবাই অভিনয় করছে, কিন্তু কেউ নিজের চরিত্রে নেই। সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো, এই ভাইরাল সংস্কৃতি এখন আমাদের তরুণ প্রজন্মের চেতনায় প্রভাব ফেলছে। আজকের যুবক-যুবতীরা মনে করছে জীবনে সফলতা মানে জনপ্রিয়তা, আর জনপ্রিয়তা মানে ভাইরাল হওয়া। তাই তারা নিজেদের গড়ার চেয়ে, নিজেদের ‘দেখানোর’ প্রতিযোগিতায় নামছে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী আলো নিভে গেলে তারা যে শূন্যতা অনুভব করবে, তার জন্য কেউ প্রস্তুত নয়। ভাইরাল সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই, এটি ছুঁয়ে ফেলেছে আমাদের রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, এমনকি মানবিক সম্পর্ককেও। এখন ভালো কাজ করলেও সেটি পোস্ট না দিলে যেন তার কোনো মূল্য নেই। আমরা মানুষকে সাহায্য করি ক্যামেরার সামনে, কান্না করি লাইভে, আর প্রার্থনা করি দর্শকের লাইক পাওয়ার আশায়। মানবিকতা এখন যেন একপ্রকার অভিনয়ের অংশ, আর নৈতিকতা কেবল কনটেন্টের উপকরণ।
আমাদের রাজনীতিতেও দেখা যাচ্ছে এই সংস্কৃতির ছায়া। যোগ্যতা, চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ‘চমক’। একজন রাজনীতিকের বক্তব্য ভাইরাল হলেই তিনি আলোচনায় আসেন, নীতিনিষ্ঠ বক্তব্য দিলে নয়। ফলে রাজনীতি থেকেও হারিয়ে যাচ্ছে যুক্তি ও সততার জায়গা।
এই ভাইরাল মানসিকতা একপ্রকার বিষক্রিয়া, যা ধীরে ধীরে আমাদের চিন্তা ও বিবেককে অবশ করে ফেলছে। আমরা এখন এমন এক সমাজে রূপ নিচ্ছি, যেখানে মানুষকে বিচার করা হয় তার ‘লাইক’ সংখ্যায়, তার কাজের প্রভাবে নয়। এই বিচারের মানদণ্ড যত বাড়ছে, ততই মেধাবীরা পিছিয়ে পড়ছে। কারণ তারা জানে, তাদের কাছে প্রচার নয়, সত্যটাই বড়। আর সেই সত্যই আজ সবচেয়ে কম বিক্রীত জিনিস।
তবে সব অন্ধকারের মাঝেও একটুখানি আলো এখনো আছে। কারণ ইতিহাস সাক্ষী, প্রচারণা কখনো চিরস্থায়ী হয়নি। সত্যই টিকে থেকেছে। সময়ের আবর্তে মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের জোয়ার একদিন নিজেই থেমে যাবে, কিন্তু সত্য, মেধা ও সততা তখনো থাকবে। শুধু দরকার সমাজের মানুষকে নতুন করে ভাবানো—আমরা কাকে মূল্য দিচ্ছি, কাকে অনুসরণ করছি, কাকে রোল মডেল বানাচ্ছি।
আজ প্রয়োজন এক নতুন সামাজিক আন্দোলনের, যেখানে ভাইরাল হওয়া নয়, মূল্যবোধই হবে নেতৃত্বের মাপকাঠি। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে—সাফল্য মানে কেবল খ্যাতি নয়, বরং দায়িত্ববোধ, জ্ঞান ও নৈতিক সাহস। তাদের বোঝাতে হবে, জীবনের আসল জয় ভিউ দিয়ে হয় না, হয় সম্মান দিয়ে; প্রচারণা দিয়ে নয়, হয় চরিত্র দিয়ে। যদি আমরা এই পরিবর্তন আনতে পারি, তবে হয়তো সমাজ আবার ফিরে পাবে সেই হারানো ভারসাম্য, যেখানে মানুষকে মাপা হবে তার সততা ও মেধায়—জনপ্রিয়তায় নয়। আজ মেধাবীরা হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা মরে যায়নি। সততার আলো হয়তো ক্ষীণ, কিন্তু নিভে যায়নি। সেই আলো একদিন আবার ছড়িয়ে পড়বে, যদি কেউ একজন সাহস করে সেটি জ্বালিয়ে রাখে। আমাদের দায়িত্ব সেই সাহস দেখানো। কারণ, ভাইরাল নয়, মূল্যবোধই একদিন হবে মানুষের সত্যিকারের পরিচয়।
লেখক: শিক্ষার্থী, ফুলছড়ি সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা
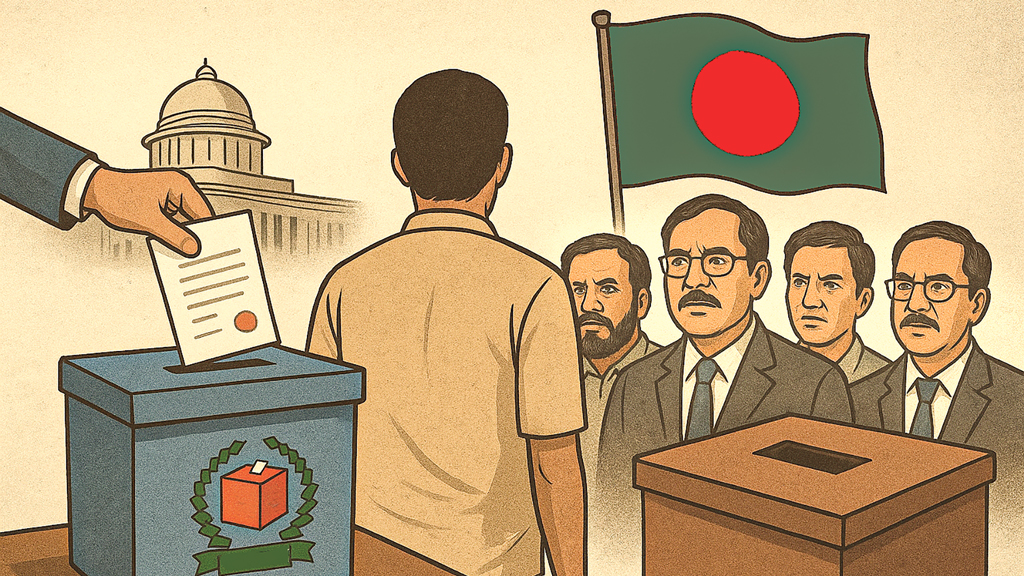
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
১ দিন আগে
জুলাই সনদ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা, জোট রাজনীতি, নারীনীতি, নির্বাচনী প্রতীক ইস্যু থেকে শুরু করে ফান্ডিং ও ‘মেধা বনাম কোটার’ বিতর্ক—এসব বিষয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা..
২ ঘণ্টা আগে
হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।
৪ ঘণ্টা আগে
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য ও বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী এক নেতার একটি ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর তা ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যদিও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভিডিওটি এডিট করা, তবু যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে এই নেতাকে...
৫ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য ও বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী এক নেতার একটি ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর তা ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যদিও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভিডিওটি এডিট করা, তবু যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে এই নেতাকে, তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে।
প্রথমেই বলতে হবে, ১৭ বছরের খিদে নিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের কথাবার্তায় এ ধরনের বেফাঁস শব্দাবলি উচ্চারিত হতেই পারে। কারণ, রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য কী, সেটা জেনে রাজনীতি করার মানুষ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ‘ধান্দাবাজি’র সঙ্গে রাজনীতিকে মিলিয়ে ফেলা হলে কেউ আর এখন শাসন করতে আসেন না। দেশ ও দশের সেবা করার যে প্রতিজ্ঞা ছিল রাজনীতির মধ্যে, তা এখন আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, সে অর্থ তুলে এনে নিজের পকেট ভর্তি করার নজির তো কম নেই। ক্ষমতায় আসার আগে ও পরে সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার নজির খুব কম। খোদ এই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার উদাহরণ খুবই দুর্বল। তাই, ক্ষমতায় থাকলে আচরণ একরকম, ক্ষমতার বাইরে গেলে আচরণ অন্য রকম হওয়ার ঘটনা দুর্লক্ষ্য নয়।
আলোচিত এই নেতা বলেছেন, ‘আমি থাকি আর না থাকি, আপনারা এক থাকেন। দল ক্ষমতায় না গেলে কিচ্ছু পাবেন না। এই কয় দিনে, এক বছরে ছোট ছোট চান্দাবাজি যা হইছে, এইটা আমি হইতে দিছি। আমি কেন হইতে দিছি? এই জন্য দিছি যে ১৭ বছর আমার নেতা-কর্মী কিছু খায় নাই।’
রাজনীতি কোন পর্যায়ে চলে গেলে ক্ষমতার সঙ্গে ‘খাওয়াদাওয়া’র সম্পর্কটা এত প্রগাঢ় হয়ে ওঠে? তার মানে দাঁড়ায়, রাজনৈতিক নেতারা বেঁচে থাকেন ক্ষমতার স্পর্শ পেলে। তখনই তাঁদের পেট ভরার মতো টাকাপয়সার আমদানি হতে পারে। ক্ষমতায় না থাকলে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত কি উপোস করে থাকেন তাঁরা? তাঁদের
কি বেঁচে থাকার মতো কোনো পেশা নেই? যে দল ক্ষমতায় যাবে, সে দল চাঁদাবাজি করে আখের গুছিয়ে নেবে—রাজনীতির আদর্শ কি শেষ পর্যন্ত এ রকম এক জায়গায় এসে ঠেকেছে?
যে প্রত্যাশার মুখোমুখি হয়েছিল দেশের সর্বস্তরের জনগণ, তা ক্রমেই ফিকে হয়ে এসেছে। বড় কোনো স্বপ্ন দেখে প্রতারিত হতে ভয় পায় দেশের মানুষ। বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর স্বপ্ন দেখিয়ে জনগণকে প্রত্যাশার মুখোমুখি দাঁড় করাল এবং তারপর সে স্বপ্ন ভেঙে গেলে, সে যাতনা জনগণই ভোগ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনতার নাম ভাঙিয়ে নিজের আসন পোক্ত করতে চায় বটে, কিন্তু আদতে কি জনতা তাদের যা ইচ্ছে তা করার ম্যান্ডেট দিয়েছে? জনগণ খাওয়াদাওয়ার রাজনীতি চায় না, এ কথা কবে বুঝবে রাজনৈতিক দলগুলো?

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির একজন সদস্য ও বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর) আসনে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী এক নেতার একটি ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ার পর তা ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। যদিও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভিডিওটি এডিট করা, তবু যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে শোনা গেছে এই নেতাকে, তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে।
প্রথমেই বলতে হবে, ১৭ বছরের খিদে নিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের কথাবার্তায় এ ধরনের বেফাঁস শব্দাবলি উচ্চারিত হতেই পারে। কারণ, রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য কী, সেটা জেনে রাজনীতি করার মানুষ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ‘ধান্দাবাজি’র সঙ্গে রাজনীতিকে মিলিয়ে ফেলা হলে কেউ আর এখন শাসন করতে আসেন না। দেশ ও দশের সেবা করার যে প্রতিজ্ঞা ছিল রাজনীতির মধ্যে, তা এখন আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, সে অর্থ তুলে এনে নিজের পকেট ভর্তি করার নজির তো কম নেই। ক্ষমতায় আসার আগে ও পরে সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার নজির খুব কম। খোদ এই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার উদাহরণ খুবই দুর্বল। তাই, ক্ষমতায় থাকলে আচরণ একরকম, ক্ষমতার বাইরে গেলে আচরণ অন্য রকম হওয়ার ঘটনা দুর্লক্ষ্য নয়।
আলোচিত এই নেতা বলেছেন, ‘আমি থাকি আর না থাকি, আপনারা এক থাকেন। দল ক্ষমতায় না গেলে কিচ্ছু পাবেন না। এই কয় দিনে, এক বছরে ছোট ছোট চান্দাবাজি যা হইছে, এইটা আমি হইতে দিছি। আমি কেন হইতে দিছি? এই জন্য দিছি যে ১৭ বছর আমার নেতা-কর্মী কিছু খায় নাই।’
রাজনীতি কোন পর্যায়ে চলে গেলে ক্ষমতার সঙ্গে ‘খাওয়াদাওয়া’র সম্পর্কটা এত প্রগাঢ় হয়ে ওঠে? তার মানে দাঁড়ায়, রাজনৈতিক নেতারা বেঁচে থাকেন ক্ষমতার স্পর্শ পেলে। তখনই তাঁদের পেট ভরার মতো টাকাপয়সার আমদানি হতে পারে। ক্ষমতায় না থাকলে খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত কি উপোস করে থাকেন তাঁরা? তাঁদের
কি বেঁচে থাকার মতো কোনো পেশা নেই? যে দল ক্ষমতায় যাবে, সে দল চাঁদাবাজি করে আখের গুছিয়ে নেবে—রাজনীতির আদর্শ কি শেষ পর্যন্ত এ রকম এক জায়গায় এসে ঠেকেছে?
যে প্রত্যাশার মুখোমুখি হয়েছিল দেশের সর্বস্তরের জনগণ, তা ক্রমেই ফিকে হয়ে এসেছে। বড় কোনো স্বপ্ন দেখে প্রতারিত হতে ভয় পায় দেশের মানুষ। বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর স্বপ্ন দেখিয়ে জনগণকে প্রত্যাশার মুখোমুখি দাঁড় করাল এবং তারপর সে স্বপ্ন ভেঙে গেলে, সে যাতনা জনগণই ভোগ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনতার নাম ভাঙিয়ে নিজের আসন পোক্ত করতে চায় বটে, কিন্তু আদতে কি জনতা তাদের যা ইচ্ছে তা করার ম্যান্ডেট দিয়েছে? জনগণ খাওয়াদাওয়ার রাজনীতি চায় না, এ কথা কবে বুঝবে রাজনৈতিক দলগুলো?
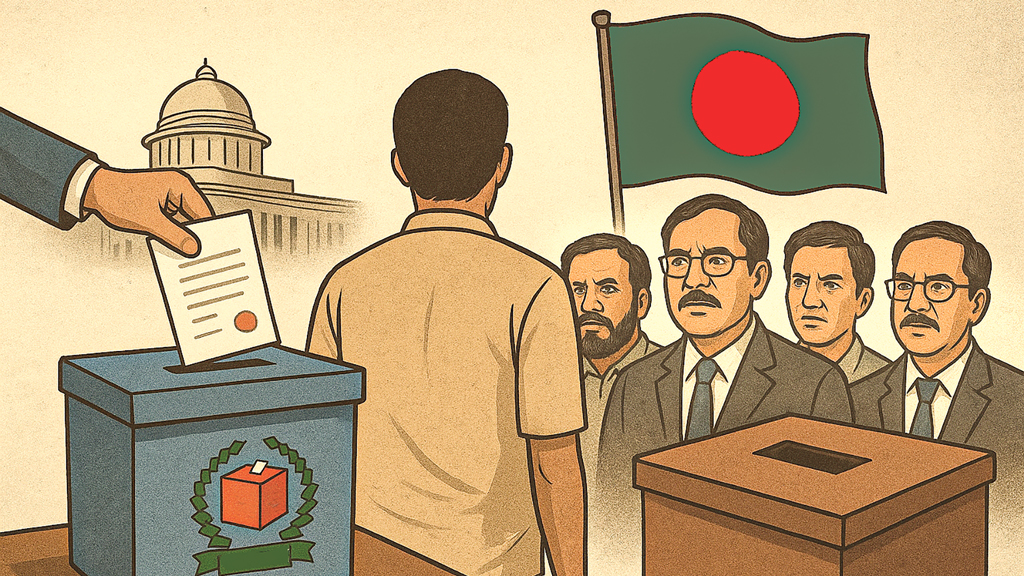
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে, পবিত্র রমজানের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। যদিও দেশে-বিদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্নতর জল্পনাও আছে। বিশেষ করে প্রবাসী কয়েকজন ইউটিউবার নানাভাবে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে নিশ্চিত নির্বাচনের বিষয়ে জনপরিসরে একটি সংশয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।
১ দিন আগে
জুলাই সনদ ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভূমিকা, জোট রাজনীতি, নারীনীতি, নির্বাচনী প্রতীক ইস্যু থেকে শুরু করে ফান্ডিং ও ‘মেধা বনাম কোটার’ বিতর্ক—এসব বিষয়ে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা..
২ ঘণ্টা আগে
হাসনাত কাইয়ুম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি। হাওরের মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে কারাভোগ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন।
৪ ঘণ্টা আগে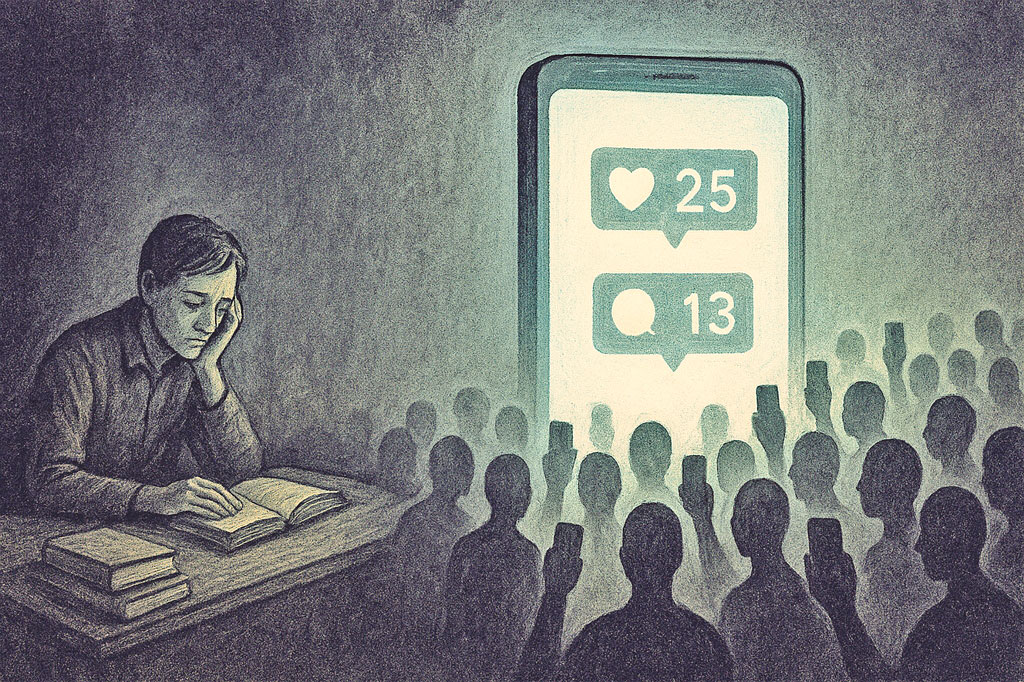
আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যেখানে মানুষের মূল্য আর তার চিন্তার গভীরতা, সততা বা মেধার ওপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে সে কতটা ‘ভাইরাল’ হতে পারে তার ওপর। ‘ভাইরাল’ এখন শুধু একটি শব্দ নয়, এটি এক প্রজন্মের মানদণ্ড, এক সমাজের সফলতার পরিমাপক।
৫ ঘণ্টা আগে