নাজমুল ইসলাম

কোভিড মহামারির নেতিবাচক প্রভাব বিশ্বের সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরই কম–বেশি পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। একটানা সাড়ে ১৭ মাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে সবচেয়ে নিরীহ অনুমানও ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু দেশের নীতিপ্রণেতা পর্যায়ে তেমনটি দেখা যাচ্ছে না। তারা এক রকম নির্বিকার বলা যায়।
গত মার্চে ইউনিসেফ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিশ্বের ১৪৭টি দেশের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সংস্থাটি জানায়, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের মতো এত দীর্ঘ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে বিশ্বের আর মাত্র ১৩টি দেশ। আর দক্ষিণ এশিয়ায় আর কেউ এমনটা করেনি। দীর্ঘ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বিশ্বের ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে বাংলাদেশেরই ৩ কোটি ৭০ লাখ।
এ তো গেল সংখ্যার হিসাব। এই প্রায় ৪ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে কারও কারও অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে, তারা আর শিক্ষাজীবনে ফিরতে পারবে কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। কারণ, মহামারির বড় প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির ওপর। বিশেষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত ব্যক্তিরা কাজ হারিয়েছে ব্যাপক হারে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় মন্দা চরম আকার নিয়েছে। কাজ, তথা আয়ের উৎস হারানো এই মানুষদের পরিবারের শিক্ষার্থীরা তাই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া নিয়েই সংশয়ে রয়েছে। কিশোর বা তরুণ বয়সী তো বটেই, বহু শিশুকেও এমনকি কর্মজীবনে ঢুকে পড়তে হয়েছে।
অর্থনৈতিক কারণেই অনেক শিশু কাজে যুক্ত হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের বড় অংশ চলে যায় খাবার ও বাসা ভাড়ায়। নাইজেরিয়ায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানকার নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের অর্ধেক বা তিন–চতুর্থাংশ ব্যয় হয় খাদ্যের পেছনে। বাংলাদেশেও দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ অসংখ্য। এই দরিদ্র মানুষদের সন্তানদের পুষ্টি নিরাপত্তাও এমনকি পড়েছে হুমকির মুখে। কারণ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলে দুপুরের খাবারের একটি নিশ্চয়তা থাকে। বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ওপর এর প্রভাব পড়েছে ভয়াবহভাবে। ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষ কীভাবে তাদের সন্তানের লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন এই মহামারির মধ্যে? বাধ্য হয়েই হয়তো মা–বাবা তাঁর সন্তানের শিক্ষার সমাপ্তি টানবেন।
দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। সেই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভাব্য একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু সেখানেও ব্যাপক অ-ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপের তথ্যমতে, ‘৭১ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তি নিরাপত্তাবেষ্টনীর বাইরে রয়েছেন। যারা বেষ্টনীর মধ্যে আছেন, তাঁদের ৪৭ শতাংশেরই সাহায্য পাওয়া উচিত নয়।’ (এম এ রাজ্জাক, প্রথম আলো, ৩১ মে,২০২০)
 শিক্ষকতা পেশাটা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কোনো চাকরি না পেয়ে শেষে শিক্ষকতায় যুক্ত হওয়ার সংখ্যা কম নয়। কারণ, এ পেশায় না আছে তেমন সম্মান, না আছে আর্থিক সুবিধা। যে অর্থ আসে, তাতে অনেকের সংসার চালাতেই কষ্ট হয়। ফলে পেশা বদলের প্রবণতা এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি। যাদের সেই সুযোগ মেলে না, তাঁরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদ্যালয়ের আঙিনায় পায়চারি করে যান। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তখন এই ভগ্ন হৃদয়ের মানুষগুলোর ওপর। শিক্ষার্থীদের একটা বড় সময় কাটে এই হতাশ মানুষদের সঙ্গে। এমন হতাশাগ্রস্ত ও আর্থিক সংকটে জর্জরিত জনবল দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ভালোভাবে চলতে পারে না। কোভিড এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এই সময়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিজীবনে সংকট বেড়েছে। অথচ কোভিডের এই সময় যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদানের বিষয়টি বেশ আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু যার জীবনেই সংকটের অন্ত নেই, তিনি কী করে যত্ন নিয়ে শিক্ষা দেবেন? অথচ এ নিয়ে নীতিপ্রণেতা পর্যায়ের কোনো হেলদোলও নেই।
শিক্ষকতা পেশাটা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কোনো চাকরি না পেয়ে শেষে শিক্ষকতায় যুক্ত হওয়ার সংখ্যা কম নয়। কারণ, এ পেশায় না আছে তেমন সম্মান, না আছে আর্থিক সুবিধা। যে অর্থ আসে, তাতে অনেকের সংসার চালাতেই কষ্ট হয়। ফলে পেশা বদলের প্রবণতা এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি। যাদের সেই সুযোগ মেলে না, তাঁরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদ্যালয়ের আঙিনায় পায়চারি করে যান। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তখন এই ভগ্ন হৃদয়ের মানুষগুলোর ওপর। শিক্ষার্থীদের একটা বড় সময় কাটে এই হতাশ মানুষদের সঙ্গে। এমন হতাশাগ্রস্ত ও আর্থিক সংকটে জর্জরিত জনবল দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ভালোভাবে চলতে পারে না। কোভিড এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এই সময়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিজীবনে সংকট বেড়েছে। অথচ কোভিডের এই সময় যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদানের বিষয়টি বেশ আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু যার জীবনেই সংকটের অন্ত নেই, তিনি কী করে যত্ন নিয়ে শিক্ষা দেবেন? অথচ এ নিয়ে নীতিপ্রণেতা পর্যায়ের কোনো হেলদোলও নেই।
এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও শিক্ষা বাজেট আগের মতোই আছে। বরং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির) বিপরীতে কমছে বলা যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিক্ষা বাজেট ছিল জিডিপির ২ দশমিক ১ শতাংশ। পরের বছর তা কমে ২ দশমিক শূন্য ৯ এবং এ অর্থবছরে তা আরও কমে ২ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ হয়েছে। এটি যেন এক ধ্রুব সংখ্যা হয়ে আছে, যা একটু এদিক–ওদিক করে দিলেই হয়। বাকি থাকল প্রণোদনা। মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাত হলেও শিক্ষা এখানে নিখোঁজ। উৎপাদন ও রপ্তানি খাত প্রণোদনার নামে সরকারি সহায়তা পেয়েছে। অথচ হাজার হাজার শিক্ষক এই সময়ে বেকার, অগণিত শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার শঙ্কা মাথায় নিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে।
জাতিসংঘের মতে, শিক্ষা খাতে কমপক্ষে জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয় করা উচিত। সেখানে এই মহামারির মধ্যে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির ২ শতাংশের আশপাশে। বাজেট বাড়ানো দূরের কথা শিক্ষা খাতে ব্যয় বেশি দেখাতে অনেক সময় অন্য খাতকে এর সঙ্গে একীভূত করা হয়।
সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বা বই উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে একটা অনুরণন উঠেছিল। কিন্তু মানের প্রশ্নে তা বিতর্কিত থেকে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে গুরুত্ব দেওয়া, না দেওয়া নিয়ে। এখন এই কোভিডকালে সার্বিক শিক্ষা খাত নিয়ে যে পরিকল্পনার অভাব দৃশ্যমান হলো, তা এই প্রশ্নকে ন্যায্যতা দিয়েছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমরা আদতে গোটা শিক্ষা খাতকেই যেন দৈবের হাওলা করে দিয়েছি। করোনা মোকাবিলা বা টিকা কর্মসূচি কোনো পর্যায়েই এখন পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়নি। বলা হচ্ছে, সেপ্টেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে। কিন্তু এই ঘোষণায় কেউ আস্থা পাচ্ছে বলে মনে হয় না।
বলা হতে পারে, করোনার এই সময়ে তো শিক্ষার্থীদের জন্য বিটিভিতে দৈনিক ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিবিএস বলছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের অর্ধেকের মতো শিশু টিভি সুবিধার আওতায় আছে। অর্থাৎ, বাকি অর্ধেক শিক্ষার্থী আওতার বাইরে। সেখানে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সুবিধার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।
বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে। অবকাঠামোর দিকে তাকালেই বিষয়টি টের পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হলো—পাটখড়ির মতো ভঙ্গুর মেরুদণ্ড কী করে এই অবকাঠামো ও উন্নয়নের ভার বহন করবে? শিক্ষাহীন একটি জাতি এই এত উন্নত অবকাঠামোকেই–বা কীভাবে ব্যবহার করবে?
আরও পড়ুন:

কোভিড মহামারির নেতিবাচক প্রভাব বিশ্বের সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরই কম–বেশি পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। একটানা সাড়ে ১৭ মাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে সবচেয়ে নিরীহ অনুমানও ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু দেশের নীতিপ্রণেতা পর্যায়ে তেমনটি দেখা যাচ্ছে না। তারা এক রকম নির্বিকার বলা যায়।
গত মার্চে ইউনিসেফ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিশ্বের ১৪৭টি দেশের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সংস্থাটি জানায়, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের মতো এত দীর্ঘ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে বিশ্বের আর মাত্র ১৩টি দেশ। আর দক্ষিণ এশিয়ায় আর কেউ এমনটা করেনি। দীর্ঘ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বিশ্বের ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে বাংলাদেশেরই ৩ কোটি ৭০ লাখ।
এ তো গেল সংখ্যার হিসাব। এই প্রায় ৪ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে কারও কারও অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে, তারা আর শিক্ষাজীবনে ফিরতে পারবে কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। কারণ, মহামারির বড় প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির ওপর। বিশেষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত ব্যক্তিরা কাজ হারিয়েছে ব্যাপক হারে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় মন্দা চরম আকার নিয়েছে। কাজ, তথা আয়ের উৎস হারানো এই মানুষদের পরিবারের শিক্ষার্থীরা তাই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া নিয়েই সংশয়ে রয়েছে। কিশোর বা তরুণ বয়সী তো বটেই, বহু শিশুকেও এমনকি কর্মজীবনে ঢুকে পড়তে হয়েছে।
অর্থনৈতিক কারণেই অনেক শিশু কাজে যুক্ত হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের বড় অংশ চলে যায় খাবার ও বাসা ভাড়ায়। নাইজেরিয়ায় পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানকার নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের অর্ধেক বা তিন–চতুর্থাংশ ব্যয় হয় খাদ্যের পেছনে। বাংলাদেশেও দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ অসংখ্য। এই দরিদ্র মানুষদের সন্তানদের পুষ্টি নিরাপত্তাও এমনকি পড়েছে হুমকির মুখে। কারণ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলে দুপুরের খাবারের একটি নিশ্চয়তা থাকে। বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ওপর এর প্রভাব পড়েছে ভয়াবহভাবে। ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষ কীভাবে তাদের সন্তানের লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন এই মহামারির মধ্যে? বাধ্য হয়েই হয়তো মা–বাবা তাঁর সন্তানের শিক্ষার সমাপ্তি টানবেন।
দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। সেই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভাব্য একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু সেখানেও ব্যাপক অ-ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা জরিপের তথ্যমতে, ‘৭১ শতাংশ যোগ্য ব্যক্তি নিরাপত্তাবেষ্টনীর বাইরে রয়েছেন। যারা বেষ্টনীর মধ্যে আছেন, তাঁদের ৪৭ শতাংশেরই সাহায্য পাওয়া উচিত নয়।’ (এম এ রাজ্জাক, প্রথম আলো, ৩১ মে,২০২০)
 শিক্ষকতা পেশাটা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কোনো চাকরি না পেয়ে শেষে শিক্ষকতায় যুক্ত হওয়ার সংখ্যা কম নয়। কারণ, এ পেশায় না আছে তেমন সম্মান, না আছে আর্থিক সুবিধা। যে অর্থ আসে, তাতে অনেকের সংসার চালাতেই কষ্ট হয়। ফলে পেশা বদলের প্রবণতা এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি। যাদের সেই সুযোগ মেলে না, তাঁরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদ্যালয়ের আঙিনায় পায়চারি করে যান। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তখন এই ভগ্ন হৃদয়ের মানুষগুলোর ওপর। শিক্ষার্থীদের একটা বড় সময় কাটে এই হতাশ মানুষদের সঙ্গে। এমন হতাশাগ্রস্ত ও আর্থিক সংকটে জর্জরিত জনবল দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ভালোভাবে চলতে পারে না। কোভিড এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এই সময়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিজীবনে সংকট বেড়েছে। অথচ কোভিডের এই সময় যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদানের বিষয়টি বেশ আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু যার জীবনেই সংকটের অন্ত নেই, তিনি কী করে যত্ন নিয়ে শিক্ষা দেবেন? অথচ এ নিয়ে নীতিপ্রণেতা পর্যায়ের কোনো হেলদোলও নেই।
শিক্ষকতা পেশাটা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কোনো চাকরি না পেয়ে শেষে শিক্ষকতায় যুক্ত হওয়ার সংখ্যা কম নয়। কারণ, এ পেশায় না আছে তেমন সম্মান, না আছে আর্থিক সুবিধা। যে অর্থ আসে, তাতে অনেকের সংসার চালাতেই কষ্ট হয়। ফলে পেশা বদলের প্রবণতা এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি। যাদের সেই সুযোগ মেলে না, তাঁরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদ্যালয়ের আঙিনায় পায়চারি করে যান। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তখন এই ভগ্ন হৃদয়ের মানুষগুলোর ওপর। শিক্ষার্থীদের একটা বড় সময় কাটে এই হতাশ মানুষদের সঙ্গে। এমন হতাশাগ্রস্ত ও আর্থিক সংকটে জর্জরিত জনবল দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ভালোভাবে চলতে পারে না। কোভিড এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এই সময়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিজীবনে সংকট বেড়েছে। অথচ কোভিডের এই সময় যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদানের বিষয়টি বেশ আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু যার জীবনেই সংকটের অন্ত নেই, তিনি কী করে যত্ন নিয়ে শিক্ষা দেবেন? অথচ এ নিয়ে নীতিপ্রণেতা পর্যায়ের কোনো হেলদোলও নেই।
এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও শিক্ষা বাজেট আগের মতোই আছে। বরং মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির) বিপরীতে কমছে বলা যায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিক্ষা বাজেট ছিল জিডিপির ২ দশমিক ১ শতাংশ। পরের বছর তা কমে ২ দশমিক শূন্য ৯ এবং এ অর্থবছরে তা আরও কমে ২ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ হয়েছে। এটি যেন এক ধ্রুব সংখ্যা হয়ে আছে, যা একটু এদিক–ওদিক করে দিলেই হয়। বাকি থাকল প্রণোদনা। মহামারিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাত হলেও শিক্ষা এখানে নিখোঁজ। উৎপাদন ও রপ্তানি খাত প্রণোদনার নামে সরকারি সহায়তা পেয়েছে। অথচ হাজার হাজার শিক্ষক এই সময়ে বেকার, অগণিত শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার শঙ্কা মাথায় নিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে।
জাতিসংঘের মতে, শিক্ষা খাতে কমপক্ষে জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয় করা উচিত। সেখানে এই মহামারির মধ্যে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির ২ শতাংশের আশপাশে। বাজেট বাড়ানো দূরের কথা শিক্ষা খাতে ব্যয় বেশি দেখাতে অনেক সময় অন্য খাতকে এর সঙ্গে একীভূত করা হয়।
সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বা বই উৎসবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে একটা অনুরণন উঠেছিল। কিন্তু মানের প্রশ্নে তা বিতর্কিত থেকে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে গুরুত্ব দেওয়া, না দেওয়া নিয়ে। এখন এই কোভিডকালে সার্বিক শিক্ষা খাত নিয়ে যে পরিকল্পনার অভাব দৃশ্যমান হলো, তা এই প্রশ্নকে ন্যায্যতা দিয়েছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমরা আদতে গোটা শিক্ষা খাতকেই যেন দৈবের হাওলা করে দিয়েছি। করোনা মোকাবিলা বা টিকা কর্মসূচি কোনো পর্যায়েই এখন পর্যন্ত কোনো পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়নি। বলা হচ্ছে, সেপ্টেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে। কিন্তু এই ঘোষণায় কেউ আস্থা পাচ্ছে বলে মনে হয় না।
বলা হতে পারে, করোনার এই সময়ে তো শিক্ষার্থীদের জন্য বিটিভিতে দৈনিক ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিবিএস বলছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের অর্ধেকের মতো শিশু টিভি সুবিধার আওতায় আছে। অর্থাৎ, বাকি অর্ধেক শিক্ষার্থী আওতার বাইরে। সেখানে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট সুবিধার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।
বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে। অবকাঠামোর দিকে তাকালেই বিষয়টি টের পাওয়া যাবে। প্রশ্ন হলো—পাটখড়ির মতো ভঙ্গুর মেরুদণ্ড কী করে এই অবকাঠামো ও উন্নয়নের ভার বহন করবে? শিক্ষাহীন একটি জাতি এই এত উন্নত অবকাঠামোকেই–বা কীভাবে ব্যবহার করবে?
আরও পড়ুন:

কিন্তু আরাকান আর্মি এখনো সেই অর্থে সিতওয়ে ও কায়াকফিউতে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ চালায়নি। কিন্তু কেন? এর পেছনে রয়েছে তিনটি কৌশলগত কারণ—কায়াকফিউতে চীনের বড় বিনিয়োগ, সিতওয়েতে ভারতের বিনিয়োগ এবং স্থানীয় জনগণের কাছে রাজনৈতিক বৈধতা ও শাসন কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এএ–এর অগ্রাধিকার।
২০ ঘণ্টা আগে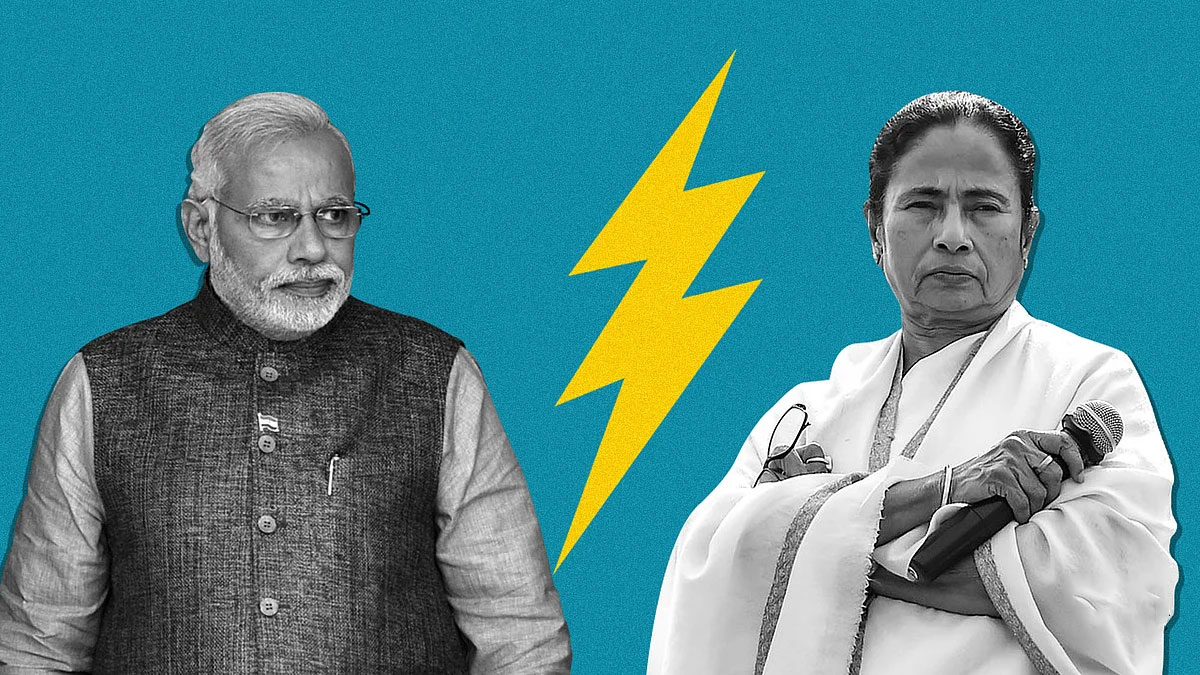
আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের আগেই নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোতে নীরবে বড়সড় পরিবর্তন এনেছেন। আগের তুলনায় বিজেপির নির্বাচনী রণনীতি এবার অনেকটাই ভিন্ন।
১ দিন আগে
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...
১ দিন আগে
বিগত পাঁচ বছর চীনকে প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখেছে ভারত। এমনকি গত মে মাস পর্যন্ত চীনকে কার্যত প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেছে। কারণ, ভারতনিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পর চার দিনের যুদ্ধে পাকিস্তান চীনা প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল।
১ দিন আগে