
তবে কি আরও একটি স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছে। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ঘটনার দ্বিতীয় দিনে উভয় পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, খুব শিগগিরই, যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের নিরাপত্তার বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের যে দ্বন্দ্ব ও রাশিয়ার ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ তা যদি প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও বিদ্যমান যে বৈরিতা তা কি আদৌ কমবে। নাকি আরও একটি স্নায়ু যুদ্ধ দেখতে যাচ্ছে বিশ্ব? রুশ হামলা ইউক্রেনের ওপর হলেও প্রকৃতপক্ষে তা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক হামলা। এই হামলা একাধিক বৈশ্বিক প্রভাব নিয়ে হাজির হয়েছে।
বিগত দুই দশকের মধ্যে রাশিয়া এই প্রথম সমরশক্তি প্রদর্শন করল। ১৯৮৯ সালে রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগের পর দেশটি সেভাবে সমরশক্তি প্রদর্শন করেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা বিগত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে যেসব হামলা চালিয়েছে তা থেকে ভিন্ন নয়।
তবে ইউক্রেন হামলা স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার রাশিয়ার আচরণের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল এখনো একই কায়দায় ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে, এটা কেবল শুরু।
সাম্প্রতিক বক্তব্যের মাধ্যমে পুতিন ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে দেশটিতে রুশ হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করেছেন। গত সপ্তাহে পূর্ব ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও স্বঘোষিত স্বাধীন দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর পুতিন দেশটির সেনাবাহিনীকে ওই দুই অঞ্চলে ‘শান্তিরক্ষী’ হিসেবে মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানেই থেমে থাকেননি। তার পরপরই তিনি ইউক্রেন সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। সর্বশেষ খবর অনুসারে রুশ বাহিনী ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে প্রবেশ করেছে। এমনকি রাজধানী কিয়েভের প্রশাসনিক এলাকায়ও প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে।
প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমা শক্তিগুলো এই হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন হিসেবে আখ্যা দিয়ে রাশিয়ার ওপর একাধিক অবরোধ আরোপ করেছে। এসব অবরোধকে প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় বলে ভাবা হচ্ছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিম হয়তো রাশিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।
 তবে এসবে ভড়কে না গিয়ে ক্রেমলিনকে বরং প্রস্তুত বলেই মনে হচ্ছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এসব নিষেধাজ্ঞা যতটাই কঠোর হোক না কেন রাশিয়ার মতো আচরণের দেশগুলো খুব একটা নিরুৎসাহিত হয় না। বিশেষ করে যখন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ সামনে আসে। তুলনা করতে গেলে দেখা যাবে, রাশিয়ার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম শক্তির দেশগুলো যেমন, ইরানের ওপর পশ্চিমা অবরোধ কিছু ক্ষতি করতে পারলেও তা কখনোই আলোচনার টেবিলে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া ভুগতে শুরু করলে দেশটি এমন কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে যা কেবল ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।
তবে এসবে ভড়কে না গিয়ে ক্রেমলিনকে বরং প্রস্তুত বলেই মনে হচ্ছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এসব নিষেধাজ্ঞা যতটাই কঠোর হোক না কেন রাশিয়ার মতো আচরণের দেশগুলো খুব একটা নিরুৎসাহিত হয় না। বিশেষ করে যখন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ সামনে আসে। তুলনা করতে গেলে দেখা যাবে, রাশিয়ার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম শক্তির দেশগুলো যেমন, ইরানের ওপর পশ্চিমা অবরোধ কিছু ক্ষতি করতে পারলেও তা কখনোই আলোচনার টেবিলে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া ভুগতে শুরু করলে দেশটি এমন কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে যা কেবল ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।
তবে পশ্চিমা অবরোধ কতটা অকার্যকর হবে তা অনেকখানি নির্ভর করবে চীনের ওপর। বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চীন রাশিয়াকে সাহায্য করতে কতটা প্রস্তুত তার ওপর। যেমন সহায়তা চীন ইরানকে করেছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতে বেইজিং সফরের সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ন্যাটো সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে একটি যৌথ বিবৃতি দেন। সম্প্রতি রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পর চীন সরকার এই হামলাকে ‘আগ্রাসন’ হিসেবে অভিহিত না করে উভয় পক্ষকে ‘সংযম’ প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে।
পুতিন হয়তো ইচ্ছে করেই ‘ভূ-কৌশলগত ট্রল’ হিসেবে ওয়াশিংটনের অতীত কর্মকাণ্ড টেনে যুক্তরাষ্ট্রকে খোঁচা দিয়েছেন ইউক্রেনে হামলাকে ন্যায্য বলে উপস্থাপন করতে। ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চলগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেমলিনের দাবি, তাঁরা ওই সব এলাকার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছে। ঠিক যেমনটা পশ্চিমারা করেছিল ১৯৯০-এর দশকে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া ও বসনিয়া গঠনের সময়।
কেবল তাই নয় যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর ইউরোপীয় মিত্ররা জাতিসংঘের ‘রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট’ ম্যান্ডেট বা ‘নিরাপত্তা দানের দায়িত্বে’র দোহাই দিয়ে লিবিয়ায় ‘মানবতার প্রয়োজনে’ হস্তক্ষেপ করেছিল রাশিয়াও ঠিক একইরকম অজুহাতে ইউক্রেন আক্রমণকে ন্যায্য বলে দাবি করছে। বলা হচ্ছে ইউক্রেনে রুশ হস্তক্ষেপ এলে সেখানে চলমান ‘গণহত্যা’ বন্ধেই করা। রুশ সমর্থকদের দাবি, এই ‘রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট’ ম্যান্ডেট যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কার এবং রাশিয়া কেবল নিজেকে রক্ষায় এই ম্যান্ডেট ব্যবহার করছে।
পুতিনের দাবি, ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং তা রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকি। বিষয়টি অনেকটা ইরাক আগ্রাসনের আগে সাদ্দাম হোসেন ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করেছেন এমন অভিযোগের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। প্রহসনমূলক এই অজুহাতটি সে সময়ের মার্কিন প্রশাসন ইরাক আক্রমণে ব্যবহার করেছিল। সে সময়ে সিনেটর ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনিও অজুহাতটি সমর্থন করেছিলেন।
 এ ছাড়া পূর্ব ইউক্রেনের দুই অঞ্চলকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে রাশিয়ার স্বীকৃতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক সিরিয়ার গোলান মালভূমির ও পূর্ব জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের ‘অবৈধ স্বীকৃতির’ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যা বাইডেন প্রশাসনও অব্যাহত রেখেছে। কেবল তাই নয়, ইউক্রেনের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে রাশিয়ার যে প্রচেষ্টা, তা সম্প্রতি ভেনেজুয়েলাসহ কয়েকটি দেশে মার্কিন প্রশাসন যেভাবে পট পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়।
এ ছাড়া পূর্ব ইউক্রেনের দুই অঞ্চলকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে রাশিয়ার স্বীকৃতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক সিরিয়ার গোলান মালভূমির ও পূর্ব জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের ‘অবৈধ স্বীকৃতির’ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যা বাইডেন প্রশাসনও অব্যাহত রেখেছে। কেবল তাই নয়, ইউক্রেনের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে রাশিয়ার যে প্রচেষ্টা, তা সম্প্রতি ভেনেজুয়েলাসহ কয়েকটি দেশে মার্কিন প্রশাসন যেভাবে পট পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়।
স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, রাশিয়া কেবল ওয়াশিংটনের মিথ্যাচার ও চাতুর্যকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে রাশিয়া তার প্রতিপক্ষের করা ভুল থেকে কোনো শিক্ষাই নেয়নি। পক্ষান্তরে, রাশিয়ার প্রতিপক্ষও আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়ায় করা ভুল থেকেও কোনো শিক্ষা নেয়নি।
পুরোনো অভ্যাস দূর করা কঠিন। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাধর দেশগুলো তাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কোনো পদক্ষেপকে আটকে দিতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় জুয়া খেলতে, ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক—যতক্ষণ না তারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।
অনেকে দাবি করেন, মার্কিন গণতন্ত্র ও রাশিয়ার স্বৈরাচারকে এক কাতারে বিবেচনা করা ঠিক নয়। তবে এটা সত্য যে, স্বৈরাচারী শাসনের চেয়ে গণতন্ত্রে জবাবদিহি বেশি। কিন্তু সত্য হলো, বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি সামনে এলে প্রধান শক্তিগুলোর আচরণ ভূ-রাজনৈতিক, কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিচালিত হয়, শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি এখানে কিছু নয়।
আবার অনেকেই যুক্তি দেন, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো বিগত দুই শতাব্দী ধরেই ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আচরণ করেছে। আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার উত্তরসূরি রাশিয়ান ফেডারেশনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সহিংস আচরণ করেছে। তবে রাশিয়া নিজের এই আচরণকে ‘আগ্রাসী’ বলে মানতে নারাজ। দেশটির এক মুখপাত্র বলেছেন, এটি পশ্চিম উদ্ভাবিত একটি শব্দ ‘যারা নিজেরাই রক্তের সাগরে ডুবে আছে’।
দুঃখজনকভাবে, স্নায়ুযুদ্ধের শেষের পর থেকে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই গায়ের জোরে নেতৃত্ব দিয়েছে। খুব কম সময়ই তারা তাদের শক্তি ব্যবহার করে কোনো ইতিবাচক উদাহরণ তৈরি করতে পেরেছে। ফলে তাদের এমন কার্যক্রম বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তাকেই কেবল ক্ষুণ্ন করেছে। তারা সঠিক স্থানে ভুল পদ্ধতি এবং ভুল স্থানে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে, দরিদ্র দেশগুলোতে স্বৈরশাসকদের টিকিয়ে রাখতে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিয়েছে।
দেশ দুটি বিগত তিনটি দশক নষ্ট করেছে কেবল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, ঠিক যেমনটি করেছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়। এই প্রক্রিয়া কেবল আরেকটি স্নায়ু যুদ্ধেরই পথ প্রশস্ত করেছে। এটি ইউরোপ এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের জন্য একটি অন্ধকার সময় হবে।
আল জাজিরার জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মারওয়ান বিশারার নিবন্ধ। ভাষান্তর: আব্দুর রহমান

তবে কি আরও একটি স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছে। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ঘটনার দ্বিতীয় দিনে উভয় পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, খুব শিগগিরই, যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের নিরাপত্তার বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের যে দ্বন্দ্ব ও রাশিয়ার ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ তা যদি প্রত্যাহার করা না হয়, তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও বিদ্যমান যে বৈরিতা তা কি আদৌ কমবে। নাকি আরও একটি স্নায়ু যুদ্ধ দেখতে যাচ্ছে বিশ্ব? রুশ হামলা ইউক্রেনের ওপর হলেও প্রকৃতপক্ষে তা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক হামলা। এই হামলা একাধিক বৈশ্বিক প্রভাব নিয়ে হাজির হয়েছে।
বিগত দুই দশকের মধ্যে রাশিয়া এই প্রথম সমরশক্তি প্রদর্শন করল। ১৯৮৯ সালে রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগের পর দেশটি সেভাবে সমরশক্তি প্রদর্শন করেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা বিগত কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে যেসব হামলা চালিয়েছে তা থেকে ভিন্ন নয়।
তবে ইউক্রেন হামলা স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার রাশিয়ার আচরণের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল এখনো একই কায়দায় ইউক্রেনে হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে, এটা কেবল শুরু।
সাম্প্রতিক বক্তব্যের মাধ্যমে পুতিন ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে দেশটিতে রুশ হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করেছেন। গত সপ্তাহে পূর্ব ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও স্বঘোষিত স্বাধীন দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর পুতিন দেশটির সেনাবাহিনীকে ওই দুই অঞ্চলে ‘শান্তিরক্ষী’ হিসেবে মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানেই থেমে থাকেননি। তার পরপরই তিনি ইউক্রেন সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন। সর্বশেষ খবর অনুসারে রুশ বাহিনী ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে প্রবেশ করেছে। এমনকি রাজধানী কিয়েভের প্রশাসনিক এলাকায়ও প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে।
প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমা শক্তিগুলো এই হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন হিসেবে আখ্যা দিয়ে রাশিয়ার ওপর একাধিক অবরোধ আরোপ করেছে। এসব অবরোধকে প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় বলে ভাবা হচ্ছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিম হয়তো রাশিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।
 তবে এসবে ভড়কে না গিয়ে ক্রেমলিনকে বরং প্রস্তুত বলেই মনে হচ্ছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এসব নিষেধাজ্ঞা যতটাই কঠোর হোক না কেন রাশিয়ার মতো আচরণের দেশগুলো খুব একটা নিরুৎসাহিত হয় না। বিশেষ করে যখন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ সামনে আসে। তুলনা করতে গেলে দেখা যাবে, রাশিয়ার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম শক্তির দেশগুলো যেমন, ইরানের ওপর পশ্চিমা অবরোধ কিছু ক্ষতি করতে পারলেও তা কখনোই আলোচনার টেবিলে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া ভুগতে শুরু করলে দেশটি এমন কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে যা কেবল ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।
তবে এসবে ভড়কে না গিয়ে ক্রেমলিনকে বরং প্রস্তুত বলেই মনে হচ্ছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এসব নিষেধাজ্ঞা যতটাই কঠোর হোক না কেন রাশিয়ার মতো আচরণের দেশগুলো খুব একটা নিরুৎসাহিত হয় না। বিশেষ করে যখন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ সামনে আসে। তুলনা করতে গেলে দেখা যাবে, রাশিয়ার চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম শক্তির দেশগুলো যেমন, ইরানের ওপর পশ্চিমা অবরোধ কিছু ক্ষতি করতে পারলেও তা কখনোই আলোচনার টেবিলে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া ভুগতে শুরু করলে দেশটি এমন কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে যা কেবল ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।
তবে পশ্চিমা অবরোধ কতটা অকার্যকর হবে তা অনেকখানি নির্ভর করবে চীনের ওপর। বিশেষ করে নিষেধাজ্ঞার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চীন রাশিয়াকে সাহায্য করতে কতটা প্রস্তুত তার ওপর। যেমন সহায়তা চীন ইরানকে করেছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতে বেইজিং সফরের সময় রুশ প্রেসিডেন্ট ও চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ন্যাটো সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে একটি যৌথ বিবৃতি দেন। সম্প্রতি রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পর চীন সরকার এই হামলাকে ‘আগ্রাসন’ হিসেবে অভিহিত না করে উভয় পক্ষকে ‘সংযম’ প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে।
পুতিন হয়তো ইচ্ছে করেই ‘ভূ-কৌশলগত ট্রল’ হিসেবে ওয়াশিংটনের অতীত কর্মকাণ্ড টেনে যুক্তরাষ্ট্রকে খোঁচা দিয়েছেন ইউক্রেনে হামলাকে ন্যায্য বলে উপস্থাপন করতে। ইউক্রেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চলগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেমলিনের দাবি, তাঁরা ওই সব এলাকার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছে। ঠিক যেমনটা পশ্চিমারা করেছিল ১৯৯০-এর দশকে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মেসিডোনিয়া ও বসনিয়া গঠনের সময়।
কেবল তাই নয় যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর ইউরোপীয় মিত্ররা জাতিসংঘের ‘রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট’ ম্যান্ডেট বা ‘নিরাপত্তা দানের দায়িত্বে’র দোহাই দিয়ে লিবিয়ায় ‘মানবতার প্রয়োজনে’ হস্তক্ষেপ করেছিল রাশিয়াও ঠিক একইরকম অজুহাতে ইউক্রেন আক্রমণকে ন্যায্য বলে দাবি করছে। বলা হচ্ছে ইউক্রেনে রুশ হস্তক্ষেপ এলে সেখানে চলমান ‘গণহত্যা’ বন্ধেই করা। রুশ সমর্থকদের দাবি, এই ‘রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট’ ম্যান্ডেট যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কার এবং রাশিয়া কেবল নিজেকে রক্ষায় এই ম্যান্ডেট ব্যবহার করছে।
পুতিনের দাবি, ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং তা রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকি। বিষয়টি অনেকটা ইরাক আগ্রাসনের আগে সাদ্দাম হোসেন ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি করেছেন এমন অভিযোগের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। প্রহসনমূলক এই অজুহাতটি সে সময়ের মার্কিন প্রশাসন ইরাক আক্রমণে ব্যবহার করেছিল। সে সময়ে সিনেটর ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনিও অজুহাতটি সমর্থন করেছিলেন।
 এ ছাড়া পূর্ব ইউক্রেনের দুই অঞ্চলকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে রাশিয়ার স্বীকৃতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক সিরিয়ার গোলান মালভূমির ও পূর্ব জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের ‘অবৈধ স্বীকৃতির’ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যা বাইডেন প্রশাসনও অব্যাহত রেখেছে। কেবল তাই নয়, ইউক্রেনের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে রাশিয়ার যে প্রচেষ্টা, তা সম্প্রতি ভেনেজুয়েলাসহ কয়েকটি দেশে মার্কিন প্রশাসন যেভাবে পট পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়।
এ ছাড়া পূর্ব ইউক্রেনের দুই অঞ্চলকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে রাশিয়ার স্বীকৃতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক সিরিয়ার গোলান মালভূমির ও পূর্ব জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের ‘অবৈধ স্বীকৃতির’ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যা বাইডেন প্রশাসনও অব্যাহত রেখেছে। কেবল তাই নয়, ইউক্রেনের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে রাশিয়ার যে প্রচেষ্টা, তা সম্প্রতি ভেনেজুয়েলাসহ কয়েকটি দেশে মার্কিন প্রশাসন যেভাবে পট পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা যায়।
স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, রাশিয়া কেবল ওয়াশিংটনের মিথ্যাচার ও চাতুর্যকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে রাশিয়া তার প্রতিপক্ষের করা ভুল থেকে কোনো শিক্ষাই নেয়নি। পক্ষান্তরে, রাশিয়ার প্রতিপক্ষও আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়ায় করা ভুল থেকেও কোনো শিক্ষা নেয়নি।
পুরোনো অভ্যাস দূর করা কঠিন। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাধর দেশগুলো তাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কোনো পদক্ষেপকে আটকে দিতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় জুয়া খেলতে, ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক—যতক্ষণ না তারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।
অনেকে দাবি করেন, মার্কিন গণতন্ত্র ও রাশিয়ার স্বৈরাচারকে এক কাতারে বিবেচনা করা ঠিক নয়। তবে এটা সত্য যে, স্বৈরাচারী শাসনের চেয়ে গণতন্ত্রে জবাবদিহি বেশি। কিন্তু সত্য হলো, বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি সামনে এলে প্রধান শক্তিগুলোর আচরণ ভূ-রাজনৈতিক, কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিচালিত হয়, শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি এখানে কিছু নয়।
আবার অনেকেই যুক্তি দেন, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো বিগত দুই শতাব্দী ধরেই ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আচরণ করেছে। আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার উত্তরসূরি রাশিয়ান ফেডারেশনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সহিংস আচরণ করেছে। তবে রাশিয়া নিজের এই আচরণকে ‘আগ্রাসী’ বলে মানতে নারাজ। দেশটির এক মুখপাত্র বলেছেন, এটি পশ্চিম উদ্ভাবিত একটি শব্দ ‘যারা নিজেরাই রক্তের সাগরে ডুবে আছে’।
দুঃখজনকভাবে, স্নায়ুযুদ্ধের শেষের পর থেকে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই গায়ের জোরে নেতৃত্ব দিয়েছে। খুব কম সময়ই তারা তাদের শক্তি ব্যবহার করে কোনো ইতিবাচক উদাহরণ তৈরি করতে পেরেছে। ফলে তাদের এমন কার্যক্রম বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তাকেই কেবল ক্ষুণ্ন করেছে। তারা সঠিক স্থানে ভুল পদ্ধতি এবং ভুল স্থানে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে, দরিদ্র দেশগুলোতে স্বৈরশাসকদের টিকিয়ে রাখতে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিয়েছে।
দেশ দুটি বিগত তিনটি দশক নষ্ট করেছে কেবল নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, ঠিক যেমনটি করেছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময়। এই প্রক্রিয়া কেবল আরেকটি স্নায়ু যুদ্ধেরই পথ প্রশস্ত করেছে। এটি ইউরোপ এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের জন্য একটি অন্ধকার সময় হবে।
আল জাজিরার জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মারওয়ান বিশারার নিবন্ধ। ভাষান্তর: আব্দুর রহমান

সাহারা মরুভূমির প্রান্তবর্তী ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ দেশ নাইজারে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে চায় রাশিয়া। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এরইমধ্যে এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিও হয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় জ্বালানি সংস্থা রোসাটম এবং নাইজার কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত ওই চুক্তি অনুযায়ী...
১ ঘণ্টা আগে
কিন্তু আরাকান আর্মি এখনো সেই অর্থে সিতওয়ে ও কায়াকফিউতে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ চালায়নি। কিন্তু কেন? এর পেছনে রয়েছে তিনটি কৌশলগত কারণ—কায়াকফিউতে চীনের বড় বিনিয়োগ, সিতওয়েতে ভারতের বিনিয়োগ এবং স্থানীয় জনগণের কাছে রাজনৈতিক বৈধতা ও শাসন কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এএ–এর অগ্রাধিকার।
২ দিন আগে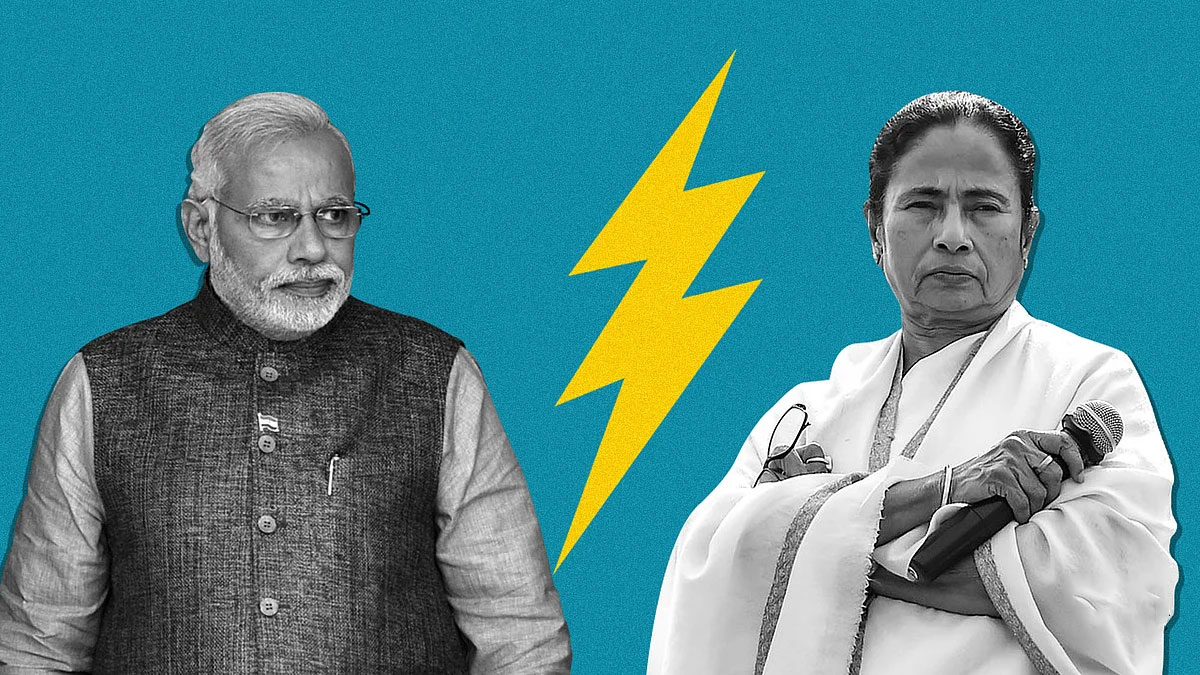
আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের আগেই নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোতে নীরবে বড়সড় পরিবর্তন এনেছেন। আগের তুলনায় বিজেপির নির্বাচনী রণনীতি এবার অনেকটাই ভিন্ন।
২ দিন আগে
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...
২ দিন আগে