আজকের পত্রিকা ডেস্ক

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়। এসব পাখির মধ্যে আর্কটিক টার্ন (Arctic tern বা Sterna paradisaea) নামের এক প্রজাতির পাখি পুরো জীবনে এত দূরত্ব অতিক্রম করে যে চাঁদ পর্যন্ত যাওয়া-আসার সমান হয়! মানুষের মতো জিপিএস বা কম্পাস না থাকলেও পরিযায়ী পাখিরা প্রতিবছর হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের পথ নির্ভুলভাবে পাড়ি দেয়। তাদের এই বিস্ময়কর দিক নির্ধারণ ক্ষমতা বরাবরই মানুষকে চমকে দেয়।
তাই পাখিদের দিক নির্ধারণের বিস্ময়কর ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে—সে বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে নানা গবেষণায় এই দক্ষতার পেছনে কিছু কারণও খুঁজে পেয়েছেন।
অদ্ভুত ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যবহার
জার্মানির ইনস্টিটিউট অব অ্যাভিয়ান রিসার্চের পরিচালক মিরিয়াম লিডভোগেল লাইভ সায়েন্সকে বলেন, ‘আমরা জানি, পাখিরা সঠিক দিক নির্ধারণে নানা রকম সংকেত ব্যবহার করে।’
সবচেয়ে সাধারণ সংকেত হলো—দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি। একবার মৌসুমি যাত্রায় অংশ নেওয়া পাখিরা নদী বা পর্বতের মতো পরিচিত ভূচিত্র মনে রাখতে পারে। তবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেসব পাখি উড়ে যায়, তাদের জন্য এ ধরনের চিহ্ন থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে, স্কোপোলির শিয়ারওয়াটার (Calonectris diomedea) নামের সামুদ্রিক পাখির নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দিলে তারা স্থলভাগের ওপর ঠিকঠাক উড়তে পারলেও পানির ওপর দিয়ে উড়ার সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে। অর্থাৎ, ঘ্রাণশক্তিও তাদের দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।
সূর্য-নক্ষত্রের দিকনির্দেশ
দিনের বেলা উড়তে থাকা পাখিরা সূর্য ব্যবহার করে দিক নির্ধারণ করে। এই ‘সূর্য কম্পাস’ কাজ করে সূর্যের অবস্থান এবং পাখির অভ্যন্তরীণ দেহঘড়ির (circadian rhythm) সময়জ্ঞান মিলিয়ে। কৃত্রিম আলো দিয়ে যদি পাখির সময়জ্ঞান বিঘ্নিত করা হয়, তবে তারা দিক হারিয়ে ফেলে।
তবে বেশির ভাগ পাখি রাতের বেলা উড়ে, ফলে সূর্য তাদের কাজে আসে না। তখন তারা নির্ভর করে আকাশের নক্ষত্রের অবস্থান ও ঘূর্ণনের ওপর। বিশেষভাবে, তারা ধ্রুবতারাকে ঘিরে থাকা নক্ষত্র মণ্ডল চিনে রাখে। এভাবেই তারা ব্যবহার করে ‘তারকা কম্পাস’।
চুম্বকীয় অনুভূতি: ম্যাগনেটোরিসেপশন
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে সূর্য ও নক্ষত্র দেখা না গেলেও পাখিরা দিক নির্ণয় করতে পারে। এ অবস্থায় কাজ করে পাখির এক আশ্চর্য ইন্দ্রিয়—ম্যাগনেটোরিসেপশন। এই শক্তি পাখিকে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করে।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ পিটার হোর মনে করেন, এই ইন্দ্রিয় ক্ষমতা কোনো এক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্ভর করে, যা চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি ও দিক বুঝে কাজ করে। তাঁর মতে, এতে ক্রিপ্টোক্রোম (cryptochrome) নামক একটি অণু ভূমিকা রাখতে পারে, যা পাখির চোখে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, নীল আলোতে এই অণুটি চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতি সংবেদনশীল হয়। তবে এত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে কীভাবে, তা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট নয়।
এ ছাড়া পাখির ঠোঁটেও চুম্বকীয় অনুভূতি থাকতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঠোঁটের ওপরের অংশে ম্যাগনেটাইট (লোহাজাতীয় খনিজ) গ্রহণকারী রিসেপ্টর রয়েছে, যা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংযুক্ত। এটি চৌম্বক শক্তি নিরূপণে সাহায্য করতে পারে।
মেঘলা দিনেও দিক বোঝে পাখি
চুম্বকশক্তির পাশাপাশি পাখি মেঘলা আকাশেও দিক নির্ধারণে সহায়তা পায় সূর্যের আলো থেকে বিকিরিত পোলারাইজড লাইট (সুসংগঠিত বিকিরিত তরঙ্গ) মাধ্যমে। পাখির চোখে থাকা বিশেষ কোষ এই আলো বুঝতে পারে, এমনকি সূর্য দেখা না গেলেও।
রাতে চোখে কম দেখলে আমরা হাত নাড়িয়ে পথ বুঝে নিই, তেমনি পাখিরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে।
লিডভোগেল বলেন, ‘পাখিরা তাদের সব সংকেতকে সমন্বয় করে দিক নির্ধারণ করে। যাত্রার বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন সংকেত বেশি কার্যকর হয়।’
পিটার হোর বলেন, ঝড় কিংবা সৌড়ঝড় তেজস্ক্রিয়তার সময় চৌম্বকক্ষেত্র বিঘ্নিত হয়, তখন পাখিরা হয়তো অন্য সংকেতে ভরসা করে।
সবশেষে, এই দুর্দান্ত দক্ষতার ভিত্তি হলো পাখির জিনগত অভিবাসন প্রবণতা। এই অভ্যাস পাখির পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। কত দূর যাবে, কোন দিকে যাবে—সবই জিনের মাধ্যমে নির্ধারিত। তবে ঠিক কোন জিনগুলো এ জন্য দায়ী, তা নিয়ে গবেষণা চলছে।
পাখি সংরক্ষণের জন্য তাদের এই রহস্যময় দক্ষতা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় পাখিদের নতুন পরিবেশে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বা পুনর্বাসনের চেষ্টা চলে। তবে একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পাখিরা নতুন জায়গা ছেড়ে চলে যায়।
হোর বলেন, ‘মানুষের চেষ্টায় পাখিদের পুনর্বাসন খুব সফল হয়নি। কারণ, তারা এতটাই দক্ষ পথপ্রদর্শক যে তাদের সরিয়ে নিলেও তারা আবার ফিরে আসে।’
তথ্যসূত্র: লাইভ সায়েন্স

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়। এসব পাখির মধ্যে আর্কটিক টার্ন (Arctic tern বা Sterna paradisaea) নামের এক প্রজাতির পাখি পুরো জীবনে এত দূরত্ব অতিক্রম করে যে চাঁদ পর্যন্ত যাওয়া-আসার সমান হয়! মানুষের মতো জিপিএস বা কম্পাস না থাকলেও পরিযায়ী পাখিরা প্রতিবছর হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের পথ নির্ভুলভাবে পাড়ি দেয়। তাদের এই বিস্ময়কর দিক নির্ধারণ ক্ষমতা বরাবরই মানুষকে চমকে দেয়।
তাই পাখিদের দিক নির্ধারণের বিস্ময়কর ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে—সে বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে নানা গবেষণায় এই দক্ষতার পেছনে কিছু কারণও খুঁজে পেয়েছেন।
অদ্ভুত ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যবহার
জার্মানির ইনস্টিটিউট অব অ্যাভিয়ান রিসার্চের পরিচালক মিরিয়াম লিডভোগেল লাইভ সায়েন্সকে বলেন, ‘আমরা জানি, পাখিরা সঠিক দিক নির্ধারণে নানা রকম সংকেত ব্যবহার করে।’
সবচেয়ে সাধারণ সংকেত হলো—দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি। একবার মৌসুমি যাত্রায় অংশ নেওয়া পাখিরা নদী বা পর্বতের মতো পরিচিত ভূচিত্র মনে রাখতে পারে। তবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেসব পাখি উড়ে যায়, তাদের জন্য এ ধরনের চিহ্ন থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে, স্কোপোলির শিয়ারওয়াটার (Calonectris diomedea) নামের সামুদ্রিক পাখির নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দিলে তারা স্থলভাগের ওপর ঠিকঠাক উড়তে পারলেও পানির ওপর দিয়ে উড়ার সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে। অর্থাৎ, ঘ্রাণশক্তিও তাদের দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।
সূর্য-নক্ষত্রের দিকনির্দেশ
দিনের বেলা উড়তে থাকা পাখিরা সূর্য ব্যবহার করে দিক নির্ধারণ করে। এই ‘সূর্য কম্পাস’ কাজ করে সূর্যের অবস্থান এবং পাখির অভ্যন্তরীণ দেহঘড়ির (circadian rhythm) সময়জ্ঞান মিলিয়ে। কৃত্রিম আলো দিয়ে যদি পাখির সময়জ্ঞান বিঘ্নিত করা হয়, তবে তারা দিক হারিয়ে ফেলে।
তবে বেশির ভাগ পাখি রাতের বেলা উড়ে, ফলে সূর্য তাদের কাজে আসে না। তখন তারা নির্ভর করে আকাশের নক্ষত্রের অবস্থান ও ঘূর্ণনের ওপর। বিশেষভাবে, তারা ধ্রুবতারাকে ঘিরে থাকা নক্ষত্র মণ্ডল চিনে রাখে। এভাবেই তারা ব্যবহার করে ‘তারকা কম্পাস’।
চুম্বকীয় অনুভূতি: ম্যাগনেটোরিসেপশন
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে সূর্য ও নক্ষত্র দেখা না গেলেও পাখিরা দিক নির্ণয় করতে পারে। এ অবস্থায় কাজ করে পাখির এক আশ্চর্য ইন্দ্রিয়—ম্যাগনেটোরিসেপশন। এই শক্তি পাখিকে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করে।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ পিটার হোর মনে করেন, এই ইন্দ্রিয় ক্ষমতা কোনো এক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্ভর করে, যা চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি ও দিক বুঝে কাজ করে। তাঁর মতে, এতে ক্রিপ্টোক্রোম (cryptochrome) নামক একটি অণু ভূমিকা রাখতে পারে, যা পাখির চোখে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, নীল আলোতে এই অণুটি চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতি সংবেদনশীল হয়। তবে এত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে কীভাবে, তা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট নয়।
এ ছাড়া পাখির ঠোঁটেও চুম্বকীয় অনুভূতি থাকতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঠোঁটের ওপরের অংশে ম্যাগনেটাইট (লোহাজাতীয় খনিজ) গ্রহণকারী রিসেপ্টর রয়েছে, যা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংযুক্ত। এটি চৌম্বক শক্তি নিরূপণে সাহায্য করতে পারে।
মেঘলা দিনেও দিক বোঝে পাখি
চুম্বকশক্তির পাশাপাশি পাখি মেঘলা আকাশেও দিক নির্ধারণে সহায়তা পায় সূর্যের আলো থেকে বিকিরিত পোলারাইজড লাইট (সুসংগঠিত বিকিরিত তরঙ্গ) মাধ্যমে। পাখির চোখে থাকা বিশেষ কোষ এই আলো বুঝতে পারে, এমনকি সূর্য দেখা না গেলেও।
রাতে চোখে কম দেখলে আমরা হাত নাড়িয়ে পথ বুঝে নিই, তেমনি পাখিরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে।
লিডভোগেল বলেন, ‘পাখিরা তাদের সব সংকেতকে সমন্বয় করে দিক নির্ধারণ করে। যাত্রার বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন সংকেত বেশি কার্যকর হয়।’
পিটার হোর বলেন, ঝড় কিংবা সৌড়ঝড় তেজস্ক্রিয়তার সময় চৌম্বকক্ষেত্র বিঘ্নিত হয়, তখন পাখিরা হয়তো অন্য সংকেতে ভরসা করে।
সবশেষে, এই দুর্দান্ত দক্ষতার ভিত্তি হলো পাখির জিনগত অভিবাসন প্রবণতা। এই অভ্যাস পাখির পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। কত দূর যাবে, কোন দিকে যাবে—সবই জিনের মাধ্যমে নির্ধারিত। তবে ঠিক কোন জিনগুলো এ জন্য দায়ী, তা নিয়ে গবেষণা চলছে।
পাখি সংরক্ষণের জন্য তাদের এই রহস্যময় দক্ষতা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় পাখিদের নতুন পরিবেশে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বা পুনর্বাসনের চেষ্টা চলে। তবে একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পাখিরা নতুন জায়গা ছেড়ে চলে যায়।
হোর বলেন, ‘মানুষের চেষ্টায় পাখিদের পুনর্বাসন খুব সফল হয়নি। কারণ, তারা এতটাই দক্ষ পথপ্রদর্শক যে তাদের সরিয়ে নিলেও তারা আবার ফিরে আসে।’
তথ্যসূত্র: লাইভ সায়েন্স
আজকের পত্রিকা ডেস্ক

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়। এসব পাখির মধ্যে আর্কটিক টার্ন (Arctic tern বা Sterna paradisaea) নামের এক প্রজাতির পাখি পুরো জীবনে এত দূরত্ব অতিক্রম করে যে চাঁদ পর্যন্ত যাওয়া-আসার সমান হয়! মানুষের মতো জিপিএস বা কম্পাস না থাকলেও পরিযায়ী পাখিরা প্রতিবছর হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের পথ নির্ভুলভাবে পাড়ি দেয়। তাদের এই বিস্ময়কর দিক নির্ধারণ ক্ষমতা বরাবরই মানুষকে চমকে দেয়।
তাই পাখিদের দিক নির্ধারণের বিস্ময়কর ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে—সে বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে নানা গবেষণায় এই দক্ষতার পেছনে কিছু কারণও খুঁজে পেয়েছেন।
অদ্ভুত ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যবহার
জার্মানির ইনস্টিটিউট অব অ্যাভিয়ান রিসার্চের পরিচালক মিরিয়াম লিডভোগেল লাইভ সায়েন্সকে বলেন, ‘আমরা জানি, পাখিরা সঠিক দিক নির্ধারণে নানা রকম সংকেত ব্যবহার করে।’
সবচেয়ে সাধারণ সংকেত হলো—দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি। একবার মৌসুমি যাত্রায় অংশ নেওয়া পাখিরা নদী বা পর্বতের মতো পরিচিত ভূচিত্র মনে রাখতে পারে। তবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেসব পাখি উড়ে যায়, তাদের জন্য এ ধরনের চিহ্ন থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে, স্কোপোলির শিয়ারওয়াটার (Calonectris diomedea) নামের সামুদ্রিক পাখির নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দিলে তারা স্থলভাগের ওপর ঠিকঠাক উড়তে পারলেও পানির ওপর দিয়ে উড়ার সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে। অর্থাৎ, ঘ্রাণশক্তিও তাদের দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।
সূর্য-নক্ষত্রের দিকনির্দেশ
দিনের বেলা উড়তে থাকা পাখিরা সূর্য ব্যবহার করে দিক নির্ধারণ করে। এই ‘সূর্য কম্পাস’ কাজ করে সূর্যের অবস্থান এবং পাখির অভ্যন্তরীণ দেহঘড়ির (circadian rhythm) সময়জ্ঞান মিলিয়ে। কৃত্রিম আলো দিয়ে যদি পাখির সময়জ্ঞান বিঘ্নিত করা হয়, তবে তারা দিক হারিয়ে ফেলে।
তবে বেশির ভাগ পাখি রাতের বেলা উড়ে, ফলে সূর্য তাদের কাজে আসে না। তখন তারা নির্ভর করে আকাশের নক্ষত্রের অবস্থান ও ঘূর্ণনের ওপর। বিশেষভাবে, তারা ধ্রুবতারাকে ঘিরে থাকা নক্ষত্র মণ্ডল চিনে রাখে। এভাবেই তারা ব্যবহার করে ‘তারকা কম্পাস’।
চুম্বকীয় অনুভূতি: ম্যাগনেটোরিসেপশন
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে সূর্য ও নক্ষত্র দেখা না গেলেও পাখিরা দিক নির্ণয় করতে পারে। এ অবস্থায় কাজ করে পাখির এক আশ্চর্য ইন্দ্রিয়—ম্যাগনেটোরিসেপশন। এই শক্তি পাখিকে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করে।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ পিটার হোর মনে করেন, এই ইন্দ্রিয় ক্ষমতা কোনো এক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্ভর করে, যা চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি ও দিক বুঝে কাজ করে। তাঁর মতে, এতে ক্রিপ্টোক্রোম (cryptochrome) নামক একটি অণু ভূমিকা রাখতে পারে, যা পাখির চোখে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, নীল আলোতে এই অণুটি চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতি সংবেদনশীল হয়। তবে এত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে কীভাবে, তা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট নয়।
এ ছাড়া পাখির ঠোঁটেও চুম্বকীয় অনুভূতি থাকতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঠোঁটের ওপরের অংশে ম্যাগনেটাইট (লোহাজাতীয় খনিজ) গ্রহণকারী রিসেপ্টর রয়েছে, যা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংযুক্ত। এটি চৌম্বক শক্তি নিরূপণে সাহায্য করতে পারে।
মেঘলা দিনেও দিক বোঝে পাখি
চুম্বকশক্তির পাশাপাশি পাখি মেঘলা আকাশেও দিক নির্ধারণে সহায়তা পায় সূর্যের আলো থেকে বিকিরিত পোলারাইজড লাইট (সুসংগঠিত বিকিরিত তরঙ্গ) মাধ্যমে। পাখির চোখে থাকা বিশেষ কোষ এই আলো বুঝতে পারে, এমনকি সূর্য দেখা না গেলেও।
রাতে চোখে কম দেখলে আমরা হাত নাড়িয়ে পথ বুঝে নিই, তেমনি পাখিরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে।
লিডভোগেল বলেন, ‘পাখিরা তাদের সব সংকেতকে সমন্বয় করে দিক নির্ধারণ করে। যাত্রার বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন সংকেত বেশি কার্যকর হয়।’
পিটার হোর বলেন, ঝড় কিংবা সৌড়ঝড় তেজস্ক্রিয়তার সময় চৌম্বকক্ষেত্র বিঘ্নিত হয়, তখন পাখিরা হয়তো অন্য সংকেতে ভরসা করে।
সবশেষে, এই দুর্দান্ত দক্ষতার ভিত্তি হলো পাখির জিনগত অভিবাসন প্রবণতা। এই অভ্যাস পাখির পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। কত দূর যাবে, কোন দিকে যাবে—সবই জিনের মাধ্যমে নির্ধারিত। তবে ঠিক কোন জিনগুলো এ জন্য দায়ী, তা নিয়ে গবেষণা চলছে।
পাখি সংরক্ষণের জন্য তাদের এই রহস্যময় দক্ষতা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় পাখিদের নতুন পরিবেশে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বা পুনর্বাসনের চেষ্টা চলে। তবে একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পাখিরা নতুন জায়গা ছেড়ে চলে যায়।
হোর বলেন, ‘মানুষের চেষ্টায় পাখিদের পুনর্বাসন খুব সফল হয়নি। কারণ, তারা এতটাই দক্ষ পথপ্রদর্শক যে তাদের সরিয়ে নিলেও তারা আবার ফিরে আসে।’
তথ্যসূত্র: লাইভ সায়েন্স

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়। এসব পাখির মধ্যে আর্কটিক টার্ন (Arctic tern বা Sterna paradisaea) নামের এক প্রজাতির পাখি পুরো জীবনে এত দূরত্ব অতিক্রম করে যে চাঁদ পর্যন্ত যাওয়া-আসার সমান হয়! মানুষের মতো জিপিএস বা কম্পাস না থাকলেও পরিযায়ী পাখিরা প্রতিবছর হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের পথ নির্ভুলভাবে পাড়ি দেয়। তাদের এই বিস্ময়কর দিক নির্ধারণ ক্ষমতা বরাবরই মানুষকে চমকে দেয়।
তাই পাখিদের দিক নির্ধারণের বিস্ময়কর ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে—সে বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ইতিমধ্যে নানা গবেষণায় এই দক্ষতার পেছনে কিছু কারণও খুঁজে পেয়েছেন।
অদ্ভুত ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যবহার
জার্মানির ইনস্টিটিউট অব অ্যাভিয়ান রিসার্চের পরিচালক মিরিয়াম লিডভোগেল লাইভ সায়েন্সকে বলেন, ‘আমরা জানি, পাখিরা সঠিক দিক নির্ধারণে নানা রকম সংকেত ব্যবহার করে।’
সবচেয়ে সাধারণ সংকেত হলো—দৃষ্টিশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি। একবার মৌসুমি যাত্রায় অংশ নেওয়া পাখিরা নদী বা পর্বতের মতো পরিচিত ভূচিত্র মনে রাখতে পারে। তবে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেসব পাখি উড়ে যায়, তাদের জন্য এ ধরনের চিহ্ন থাকে না। গবেষণায় দেখা গেছে, স্কোপোলির শিয়ারওয়াটার (Calonectris diomedea) নামের সামুদ্রিক পাখির নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দিলে তারা স্থলভাগের ওপর ঠিকঠাক উড়তে পারলেও পানির ওপর দিয়ে উড়ার সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে। অর্থাৎ, ঘ্রাণশক্তিও তাদের দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ।
সূর্য-নক্ষত্রের দিকনির্দেশ
দিনের বেলা উড়তে থাকা পাখিরা সূর্য ব্যবহার করে দিক নির্ধারণ করে। এই ‘সূর্য কম্পাস’ কাজ করে সূর্যের অবস্থান এবং পাখির অভ্যন্তরীণ দেহঘড়ির (circadian rhythm) সময়জ্ঞান মিলিয়ে। কৃত্রিম আলো দিয়ে যদি পাখির সময়জ্ঞান বিঘ্নিত করা হয়, তবে তারা দিক হারিয়ে ফেলে।
তবে বেশির ভাগ পাখি রাতের বেলা উড়ে, ফলে সূর্য তাদের কাজে আসে না। তখন তারা নির্ভর করে আকাশের নক্ষত্রের অবস্থান ও ঘূর্ণনের ওপর। বিশেষভাবে, তারা ধ্রুবতারাকে ঘিরে থাকা নক্ষত্র মণ্ডল চিনে রাখে। এভাবেই তারা ব্যবহার করে ‘তারকা কম্পাস’।
চুম্বকীয় অনুভূতি: ম্যাগনেটোরিসেপশন
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে সূর্য ও নক্ষত্র দেখা না গেলেও পাখিরা দিক নির্ণয় করতে পারে। এ অবস্থায় কাজ করে পাখির এক আশ্চর্য ইন্দ্রিয়—ম্যাগনেটোরিসেপশন। এই শক্তি পাখিকে পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করে।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ পিটার হোর মনে করেন, এই ইন্দ্রিয় ক্ষমতা কোনো এক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্ভর করে, যা চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি ও দিক বুঝে কাজ করে। তাঁর মতে, এতে ক্রিপ্টোক্রোম (cryptochrome) নামক একটি অণু ভূমিকা রাখতে পারে, যা পাখির চোখে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, নীল আলোতে এই অণুটি চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতি সংবেদনশীল হয়। তবে এত সূক্ষ্মভাবে কাজ করে কীভাবে, তা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট নয়।
এ ছাড়া পাখির ঠোঁটেও চুম্বকীয় অনুভূতি থাকতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঠোঁটের ওপরের অংশে ম্যাগনেটাইট (লোহাজাতীয় খনিজ) গ্রহণকারী রিসেপ্টর রয়েছে, যা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংযুক্ত। এটি চৌম্বক শক্তি নিরূপণে সাহায্য করতে পারে।
মেঘলা দিনেও দিক বোঝে পাখি
চুম্বকশক্তির পাশাপাশি পাখি মেঘলা আকাশেও দিক নির্ধারণে সহায়তা পায় সূর্যের আলো থেকে বিকিরিত পোলারাইজড লাইট (সুসংগঠিত বিকিরিত তরঙ্গ) মাধ্যমে। পাখির চোখে থাকা বিশেষ কোষ এই আলো বুঝতে পারে, এমনকি সূর্য দেখা না গেলেও।
রাতে চোখে কম দেখলে আমরা হাত নাড়িয়ে পথ বুঝে নিই, তেমনি পাখিরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে।
লিডভোগেল বলেন, ‘পাখিরা তাদের সব সংকেতকে সমন্বয় করে দিক নির্ধারণ করে। যাত্রার বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন সংকেত বেশি কার্যকর হয়।’
পিটার হোর বলেন, ঝড় কিংবা সৌড়ঝড় তেজস্ক্রিয়তার সময় চৌম্বকক্ষেত্র বিঘ্নিত হয়, তখন পাখিরা হয়তো অন্য সংকেতে ভরসা করে।
সবশেষে, এই দুর্দান্ত দক্ষতার ভিত্তি হলো পাখির জিনগত অভিবাসন প্রবণতা। এই অভ্যাস পাখির পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। কত দূর যাবে, কোন দিকে যাবে—সবই জিনের মাধ্যমে নির্ধারিত। তবে ঠিক কোন জিনগুলো এ জন্য দায়ী, তা নিয়ে গবেষণা চলছে।
পাখি সংরক্ষণের জন্য তাদের এই রহস্যময় দক্ষতা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় পাখিদের নতুন পরিবেশে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বা পুনর্বাসনের চেষ্টা চলে। তবে একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পাখিরা নতুন জায়গা ছেড়ে চলে যায়।
হোর বলেন, ‘মানুষের চেষ্টায় পাখিদের পুনর্বাসন খুব সফল হয়নি। কারণ, তারা এতটাই দক্ষ পথপ্রদর্শক যে তাদের সরিয়ে নিলেও তারা আবার ফিরে আসে।’
তথ্যসূত্র: লাইভ সায়েন্স

দশকের পর দশক কিংবা শতাব্দীকাল ধরে মানবসভ্যতার নানা অধ্যায়ে জমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বিশ্বজুড়ে এ বছর গবেষকেরা যেন গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব, জেনেটিক বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ২০২৫ সালে উন্মোচিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক রহস্য।
২ দিন আগে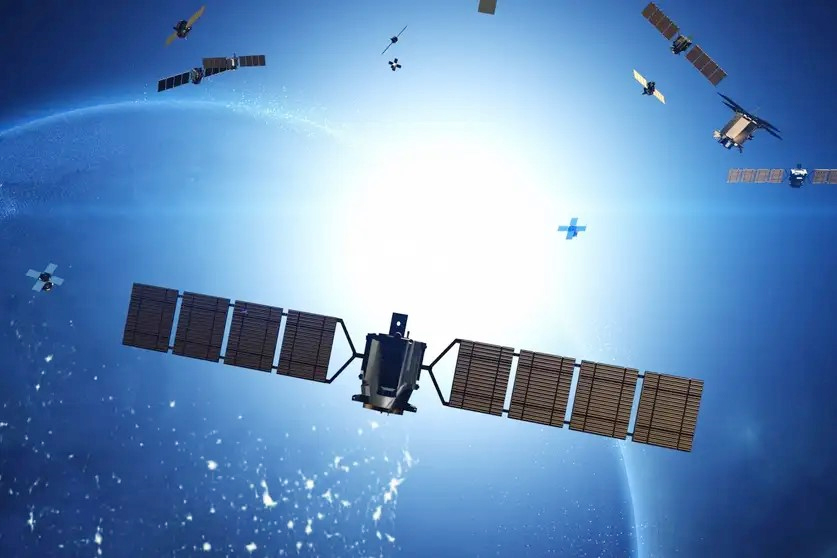
কোনো বড় ধরনের সৌরঝড় বা প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের কারণে যদি পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলো হঠাৎ নিজেদের গতিপথ পরিবর্তনের সক্ষমতা হারায়, তবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা।
৮ দিন আগে
উত্তর ইতালির একটি ন্যাশনাল পার্কে ২১ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। তাও আবার একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। এই পায়ের ছাপগুলোর কয়েকটির ব্যাস ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত। আর এগুলো সমান্তরাল সারিতে সাজানো। এসবের মধ্যে অনেকগুলোতে আঙুল ও নখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা গেছে
৮ দিন আগে
ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।
১১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

দশকের পর দশক কিংবা শতাব্দীকাল ধরে মানবসভ্যতার নানা অধ্যায়ে জমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বিশ্বজুড়ে এ বছর গবেষকেরা যেন গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব, জেনেটিক বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ২০২৫ সালে উন্মোচিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক রহস্য।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) এ বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানিয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বিদায়ী এই বছরটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইস্টার আইল্যান্ডের একটি খনিতে পড়ে থাকা অসমাপ্ত পাথরের মূর্তিগুলো বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা জানতে পেরেছেন, প্রাচীন পলিনেশীয়রা কীভাবে পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে বিশাল মোয়াই মূর্তি তৈরি করত।
এদিকে, ইতালির পম্পেই নগরীতে নতুন করে খননকাজ শুরু হওয়ার পর একটি পাথরের সিঁড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হওয়ার আগে শহরটি দেখতে কেমন ছিল তা জানতে সহায়তা করেছে।
পেরুর আন্দিজ পর্বতমালায় ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৫ হাজার ২০০টি গর্ত নিয়েও নতুন ধারণা দিয়েছেন গবেষকেরা। এই গর্তগুলোর নির্মাতা কারা এবং কেন এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল—ড্রোন ফুটেজ ও উদ্ভিদকণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেছে।
কিছু গবেষণা আবার নতুন প্রশ্নও উসকে দিয়েছে। যেমন—চিকিৎসা নথি না থাকায় বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের মৃত্যুর কারণ জানতে গবেষকেরা তাঁর লেখার ভাষা ও শব্দচয়ন বিশ্লেষণ করছেন।

এ বছর ঐতিহাসিক বিষয়ে আলোচিত আবিষ্কারগুলোর একটি হলো, অস্ট্রিয়ার প্রত্যন্ত গির্জায় সংরক্ষিত রহস্যময় একটি মমি। ১৭০০ সাল থেকে ‘বাতাসে শুকানো যাজক’ নামে পরিচিত এই দেহটির পরিচয় দীর্ঘদিন অজানা ছিল। আধুনিক স্ক্যান ও রেডিওকার্বন ডেটিংয়ের মাধ্যমে জানা গেছে, তিনি ছিলেন ফ্রাঞ্জ জাভের সিডলার ফন রোজেনেগ নামে একজন অভিজাত ব্যক্তি। পরবর্তীতে তিনি গির্জার যাজক হয়েছিলেন। গবেষকেরা তাঁর দেহ সংরক্ষণের এক অজানা পদ্ধতি ও মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণও চিহ্নিত করেছেন।
এদিকে ডেনমার্কে সংরক্ষিত হিয়র্টস্প্রিং নৌকাটির উৎস নিয়েও রহস্যের পর্দা উঠেছে। ২০০০ বছরেরও বেশি সময় আগের এই নৌকাটি অস্ত্রে ভরা ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় এটি দ্বীপে আক্রমণ করার উদ্দেশে যোদ্ধাদের বহন করছিল। বিশ্লেষণে একটি আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। এটিকে তৎকালীন কোনো নাবিকের সরাসরি প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রমাণ মিলেছে—অভিযাত্রী আর্নেস্ট শ্যাকলটনের জাহাজ এইচএমএস অ্যান্ডিউরেন্স ভাঙা স্টিয়ারিং নয়, বরং কাঠামোগত দুর্বলতার কারণেই ডুবে গিয়েছিল।

১৪ হাজার বছর আগে বরফ যুগের ‘টুমাট পাপিজ’ নামে পরিচিত দুটি সংরক্ষিত শাবককে এত দিন গৃহপালিত কুকুর মনে করা হলেও নতুন জেনেটিক গবেষণায় জানা গেছে, এগুলো আসলে নেকড়ে শাবক ছিল এবং মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।
এ ছাড়া ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান নিয়েও নতুন তথ্য মিলেছে। সেই সময়ে নিহত ফরাসি সেনাদের দাঁতের নমুনা বিশ্লেষণ করে টাইফাসের পাশাপাশি প্যারাটাইফয়েড ও রিল্যাপসিং ফিভারের জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা ওই বাহিনীর বিপুল প্রাণহানির অন্যতম কারণ হতে পারে।
সব মিলিয়ে, ২০২৫ সাল বিজ্ঞানের হাত ধরে ইতিহাসের বহু অন্ধকার কোণ আলোকিত করেছে এবং আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে মানবসভ্যতার দীর্ঘ ও জটিল পথচলা।

দশকের পর দশক কিংবা শতাব্দীকাল ধরে মানবসভ্যতার নানা অধ্যায়ে জমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বিশ্বজুড়ে এ বছর গবেষকেরা যেন গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব, জেনেটিক বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ২০২৫ সালে উন্মোচিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক রহস্য।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) এ বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানিয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বিদায়ী এই বছরটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইস্টার আইল্যান্ডের একটি খনিতে পড়ে থাকা অসমাপ্ত পাথরের মূর্তিগুলো বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা জানতে পেরেছেন, প্রাচীন পলিনেশীয়রা কীভাবে পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে বিশাল মোয়াই মূর্তি তৈরি করত।
এদিকে, ইতালির পম্পেই নগরীতে নতুন করে খননকাজ শুরু হওয়ার পর একটি পাথরের সিঁড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হওয়ার আগে শহরটি দেখতে কেমন ছিল তা জানতে সহায়তা করেছে।
পেরুর আন্দিজ পর্বতমালায় ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৫ হাজার ২০০টি গর্ত নিয়েও নতুন ধারণা দিয়েছেন গবেষকেরা। এই গর্তগুলোর নির্মাতা কারা এবং কেন এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল—ড্রোন ফুটেজ ও উদ্ভিদকণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেছে।
কিছু গবেষণা আবার নতুন প্রশ্নও উসকে দিয়েছে। যেমন—চিকিৎসা নথি না থাকায় বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের মৃত্যুর কারণ জানতে গবেষকেরা তাঁর লেখার ভাষা ও শব্দচয়ন বিশ্লেষণ করছেন।

এ বছর ঐতিহাসিক বিষয়ে আলোচিত আবিষ্কারগুলোর একটি হলো, অস্ট্রিয়ার প্রত্যন্ত গির্জায় সংরক্ষিত রহস্যময় একটি মমি। ১৭০০ সাল থেকে ‘বাতাসে শুকানো যাজক’ নামে পরিচিত এই দেহটির পরিচয় দীর্ঘদিন অজানা ছিল। আধুনিক স্ক্যান ও রেডিওকার্বন ডেটিংয়ের মাধ্যমে জানা গেছে, তিনি ছিলেন ফ্রাঞ্জ জাভের সিডলার ফন রোজেনেগ নামে একজন অভিজাত ব্যক্তি। পরবর্তীতে তিনি গির্জার যাজক হয়েছিলেন। গবেষকেরা তাঁর দেহ সংরক্ষণের এক অজানা পদ্ধতি ও মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণও চিহ্নিত করেছেন।
এদিকে ডেনমার্কে সংরক্ষিত হিয়র্টস্প্রিং নৌকাটির উৎস নিয়েও রহস্যের পর্দা উঠেছে। ২০০০ বছরেরও বেশি সময় আগের এই নৌকাটি অস্ত্রে ভরা ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় এটি দ্বীপে আক্রমণ করার উদ্দেশে যোদ্ধাদের বহন করছিল। বিশ্লেষণে একটি আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। এটিকে তৎকালীন কোনো নাবিকের সরাসরি প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রমাণ মিলেছে—অভিযাত্রী আর্নেস্ট শ্যাকলটনের জাহাজ এইচএমএস অ্যান্ডিউরেন্স ভাঙা স্টিয়ারিং নয়, বরং কাঠামোগত দুর্বলতার কারণেই ডুবে গিয়েছিল।

১৪ হাজার বছর আগে বরফ যুগের ‘টুমাট পাপিজ’ নামে পরিচিত দুটি সংরক্ষিত শাবককে এত দিন গৃহপালিত কুকুর মনে করা হলেও নতুন জেনেটিক গবেষণায় জানা গেছে, এগুলো আসলে নেকড়ে শাবক ছিল এবং মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।
এ ছাড়া ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান নিয়েও নতুন তথ্য মিলেছে। সেই সময়ে নিহত ফরাসি সেনাদের দাঁতের নমুনা বিশ্লেষণ করে টাইফাসের পাশাপাশি প্যারাটাইফয়েড ও রিল্যাপসিং ফিভারের জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যা ওই বাহিনীর বিপুল প্রাণহানির অন্যতম কারণ হতে পারে।
সব মিলিয়ে, ২০২৫ সাল বিজ্ঞানের হাত ধরে ইতিহাসের বহু অন্ধকার কোণ আলোকিত করেছে এবং আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে মানবসভ্যতার দীর্ঘ ও জটিল পথচলা।

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়।
১৬ জুন ২০২৫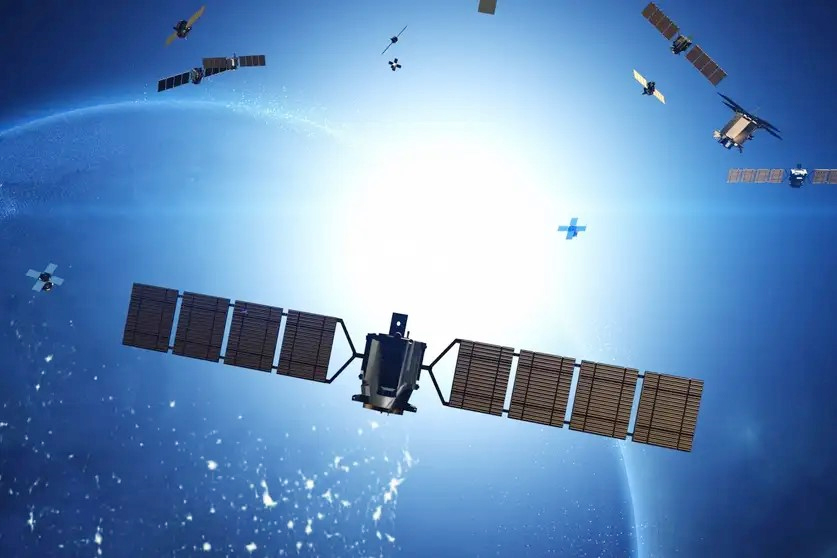
কোনো বড় ধরনের সৌরঝড় বা প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের কারণে যদি পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলো হঠাৎ নিজেদের গতিপথ পরিবর্তনের সক্ষমতা হারায়, তবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা।
৮ দিন আগে
উত্তর ইতালির একটি ন্যাশনাল পার্কে ২১ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। তাও আবার একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। এই পায়ের ছাপগুলোর কয়েকটির ব্যাস ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত। আর এগুলো সমান্তরাল সারিতে সাজানো। এসবের মধ্যে অনেকগুলোতে আঙুল ও নখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা গেছে
৮ দিন আগে
ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।
১১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক
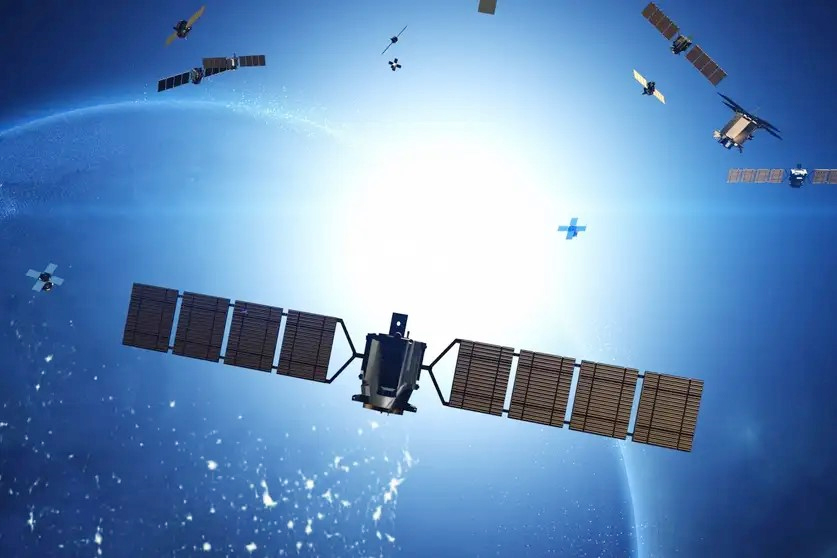
কোনো বড় ধরনের সৌরঝড় বা প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের কারণে যদি পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলো হঠাৎ নিজেদের গতিপথ পরিবর্তনের সক্ষমতা হারায়, তবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন এক গবেষণা বলছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সব স্যাটেলাইট একযোগে অচল হয়ে পড়লে প্রথম সংঘর্ষ ঘটতে সময় লাগবে গড়ে মাত্র ২.৮ দিন।
গত সাত বছরে পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইটের সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে প্রায় ৪ হাজার স্যাটেলাইট ছিল, এখন সেই সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজারে পৌঁছেছে। এই বিস্ফোরণধর্মী বৃদ্ধির পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে স্পেসএক্সের স্টারলিংক প্রকল্প। নিম্ন-পৃথিবী কক্ষপথে (৩৪০ থেকে ৫৫০ কিলোমিটার উচ্চতায়) বর্তমানে স্টারলিংকের স্যাটেলাইটই রয়েছে ৯ হাজারের বেশি।
কক্ষপথে এত বেশি স্যাটেলাইট থাকার কারণে নিয়মিত সংঘর্ষ এড়াতে ‘কলিশন অ্যাভয়ডেন্স ম্যানুভার’ বা গতিপথ পরিবর্তনের কৌশল নিতে হয়। স্পেসএক্স জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ৩১ মে পর্যন্ত মাত্র ছয় মাসে তারা ১ লাখ ৪৪ হাজারেরও বেশি সংঘর্ষ এড়ানোর কৌশল প্রয়োগ করেছে।
গত মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে নিও সায়েন্টিস্ট জানিয়েছে, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা থিয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা স্যাটেলাইটের অবস্থানসংক্রান্ত উন্মুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সংঘর্ষ ঝুঁকি পরিমাপের জন্য নতুন একটি সূচক তৈরি করেছেন। এই সূচকের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ক্র্যাশ ক্লক’।
গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৮ সালে যদি সব স্যাটেলাইট হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারাত, তবে প্রথম সংঘর্ষ হতে সময় লাগত প্রায় ১২১ দিন। কিন্তু বর্তমানে সেই সময় নেমে এসেছে মাত্র ২.৮ দিনে। এই তথ্য বিজ্ঞানীদেরও বিস্মিত করেছে।
সব স্যাটেলাইট একসঙ্গে অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম হলেও ২০২৪ সালের মে মাসে শক্তিশালী সৌরঝড়ে স্টারলিংক স্যাটেলাইটগুলোতে অস্বাভাবিক ঢেউয়ের মতো প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী সৌরঝড় হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন—আগামী বছরগুলোতে স্পেসএক্স, অ্যামাজন ও চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আরও হাজার হাজার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে। ফলে কক্ষপথে ভিড় আরও বাড়বে, আর ‘ক্র্যাশ ক্লক’-এর সময়সীমা আরও এগিয়ে আসবে। এই পরিস্থিতি মহাকাশ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তা সামনে আনছে।
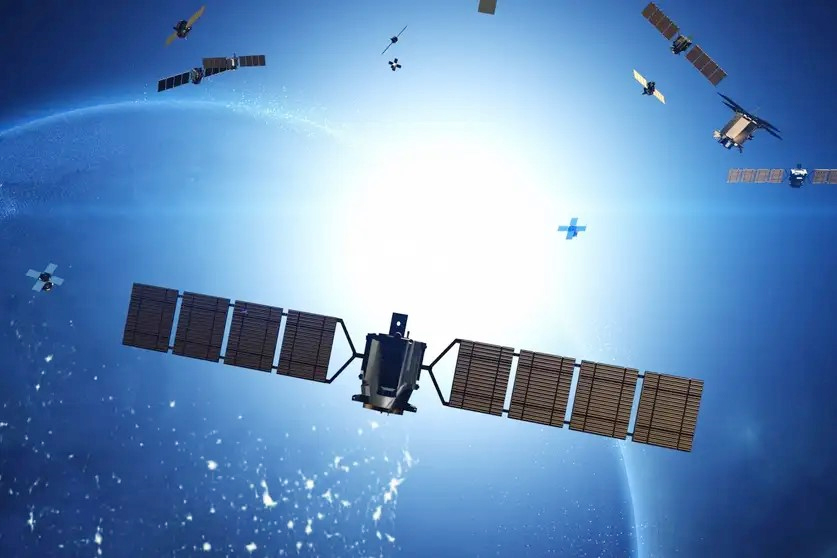
কোনো বড় ধরনের সৌরঝড় বা প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের কারণে যদি পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলো হঠাৎ নিজেদের গতিপথ পরিবর্তনের সক্ষমতা হারায়, তবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন এক গবেষণা বলছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সব স্যাটেলাইট একযোগে অচল হয়ে পড়লে প্রথম সংঘর্ষ ঘটতে সময় লাগবে গড়ে মাত্র ২.৮ দিন।
গত সাত বছরে পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইটের সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে প্রায় ৪ হাজার স্যাটেলাইট ছিল, এখন সেই সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজারে পৌঁছেছে। এই বিস্ফোরণধর্মী বৃদ্ধির পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে স্পেসএক্সের স্টারলিংক প্রকল্প। নিম্ন-পৃথিবী কক্ষপথে (৩৪০ থেকে ৫৫০ কিলোমিটার উচ্চতায়) বর্তমানে স্টারলিংকের স্যাটেলাইটই রয়েছে ৯ হাজারের বেশি।
কক্ষপথে এত বেশি স্যাটেলাইট থাকার কারণে নিয়মিত সংঘর্ষ এড়াতে ‘কলিশন অ্যাভয়ডেন্স ম্যানুভার’ বা গতিপথ পরিবর্তনের কৌশল নিতে হয়। স্পেসএক্স জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ৩১ মে পর্যন্ত মাত্র ছয় মাসে তারা ১ লাখ ৪৪ হাজারেরও বেশি সংঘর্ষ এড়ানোর কৌশল প্রয়োগ করেছে।
গত মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) এই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে নিও সায়েন্টিস্ট জানিয়েছে, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা থিয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা স্যাটেলাইটের অবস্থানসংক্রান্ত উন্মুক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সংঘর্ষ ঝুঁকি পরিমাপের জন্য নতুন একটি সূচক তৈরি করেছেন। এই সূচকের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ক্র্যাশ ক্লক’।
গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৮ সালে যদি সব স্যাটেলাইট হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারাত, তবে প্রথম সংঘর্ষ হতে সময় লাগত প্রায় ১২১ দিন। কিন্তু বর্তমানে সেই সময় নেমে এসেছে মাত্র ২.৮ দিনে। এই তথ্য বিজ্ঞানীদেরও বিস্মিত করেছে।
সব স্যাটেলাইট একসঙ্গে অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম হলেও ২০২৪ সালের মে মাসে শক্তিশালী সৌরঝড়ে স্টারলিংক স্যাটেলাইটগুলোতে অস্বাভাবিক ঢেউয়ের মতো প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী সৌরঝড় হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন—আগামী বছরগুলোতে স্পেসএক্স, অ্যামাজন ও চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আরও হাজার হাজার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে। ফলে কক্ষপথে ভিড় আরও বাড়বে, আর ‘ক্র্যাশ ক্লক’-এর সময়সীমা আরও এগিয়ে আসবে। এই পরিস্থিতি মহাকাশ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তা সামনে আনছে।

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়।
১৬ জুন ২০২৫
দশকের পর দশক কিংবা শতাব্দীকাল ধরে মানবসভ্যতার নানা অধ্যায়ে জমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বিশ্বজুড়ে এ বছর গবেষকেরা যেন গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব, জেনেটিক বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ২০২৫ সালে উন্মোচিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক রহস্য।
২ দিন আগে
উত্তর ইতালির একটি ন্যাশনাল পার্কে ২১ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। তাও আবার একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। এই পায়ের ছাপগুলোর কয়েকটির ব্যাস ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত। আর এগুলো সমান্তরাল সারিতে সাজানো। এসবের মধ্যে অনেকগুলোতে আঙুল ও নখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা গেছে
৮ দিন আগে
ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।
১১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

উত্তর ইতালির একটি ন্যাশনাল পার্কে ২১ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। তাও আবার একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। এই পায়ের ছাপগুলোর কয়েকটির ব্যাস ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত। আর এগুলো সমান্তরাল সারিতে সাজানো। এসবের মধ্যে অনেকগুলোতে আঙুল ও নখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা গেছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।
ধারণা করা হচ্ছে, এই ডাইনোসরগুলো ছিল ‘প্রোসাওরোপড’ (prosauropod) প্রজাতির। এ প্রজাতির ডাইনোসরের গলা লম্বা ও মাথা ছোট এবং ধারালো নখবিশিষ্ট তৃণভোজী প্রাণী ছিল।
মিলানভিত্তিক জীবাশ্মবিদ ক্রিস্টিয়ানো ডাল সাসো বলেন, ‘কখনো কল্পনাও করিনি, আমি যে অঞ্চলে বাস করি, সেখানেই এমন এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দেখা পাব।’
গত সেপ্টেম্বরে মিলানের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত স্টেলভিও ন্যাশনাল পার্কের একটি খাঁড়া পাহাড়ের গায়ে কয়েক শ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এই পায়ের ছাপগুলো একজন আলোকচিত্রীর চোখে ধরা পড়ে।
বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০ থেকে ২৫ কোটি বছর আগে ট্রায়াসিক যুগে এই পাহাড়ের অংশটি ছিল একটি সমুদ্র তীরবর্তী সমতল ভূমি, যা পরে আল্পাইন পর্বতমালায় রূপান্তরিত হয়।
ডাল সাসো আরও বলেন, এই জায়গা ডাইনোসরে পরিপূর্ণ ছিল; এটি একটি বিশাল বৈজ্ঞানিক সম্পদ।
ডাল সাসো আরও যোগ করেন, ডাইনোসরের দলগুলো সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল করত এবং সেখানে আরও কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে, যেগুলো থেকে মনে হয়, পশুরা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ হয়ে বৃত্তাকারে অবস্থান নিত।
আবিষ্কারকেরা বলছেন, প্রোসাওরোপডগুলো ১০ মিটার বা ৩৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারত। তারা সাধারণত দুই পায়ে হাঁটত, তবে কিছু ক্ষেত্রে পায়ের ছাপের সামনে হাতের ছাপও পাওয়া গেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, তারা সম্ভবত মাঝেমধ্যে থেমে বিশ্রাম নেওয়ার সময় তাদের সামনের পা মাটিতে রাখত।
আলোকচিত্রী এলিয়ো ডেলা ফেরেরা এই স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘এই আবিষ্কার আমাদের সবার মধ্যে ভাবনার খোরাক জোগাবে এবং আমরা যেখানে বাস করি, আমাদের ঘর, আমাদের পৃথিবী, এই জায়গাগুলো সম্পর্কে আমরা কতটা কম জানি, তা বোঝায়।’
ইতালির সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এলাকাটি অত্যন্ত দুর্গম এবং যাতায়াতের কোনো পথ নেই। তাই গবেষণার কাজে ড্রোনের পাশাপাশি রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
উল্লেখ্য, আগামী বছর ইতালিতে শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া স্টেলভিও ন্যাশনাল পার্কটি সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ইতালির সীমান্তবর্তী ফ্রায়েল উপত্যকায় অবস্থিত। মন্ত্রণালয় জানায়, এটি যেন অনেকটা এমন যে, স্বয়ং ইতিহাসই বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ক্রীড়া ইভেন্টকে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছে; প্রকৃতি ও ক্রীড়ার মধ্যে এক প্রতীকী সেতুবন্ধনের মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানকে এক সুতায় গেঁথেছে।

উত্তর ইতালির একটি ন্যাশনাল পার্কে ২১ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। তাও আবার একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। এই পায়ের ছাপগুলোর কয়েকটির ব্যাস ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত। আর এগুলো সমান্তরাল সারিতে সাজানো। এসবের মধ্যে অনেকগুলোতে আঙুল ও নখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা গেছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।
ধারণা করা হচ্ছে, এই ডাইনোসরগুলো ছিল ‘প্রোসাওরোপড’ (prosauropod) প্রজাতির। এ প্রজাতির ডাইনোসরের গলা লম্বা ও মাথা ছোট এবং ধারালো নখবিশিষ্ট তৃণভোজী প্রাণী ছিল।
মিলানভিত্তিক জীবাশ্মবিদ ক্রিস্টিয়ানো ডাল সাসো বলেন, ‘কখনো কল্পনাও করিনি, আমি যে অঞ্চলে বাস করি, সেখানেই এমন এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের দেখা পাব।’
গত সেপ্টেম্বরে মিলানের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত স্টেলভিও ন্যাশনাল পার্কের একটি খাঁড়া পাহাড়ের গায়ে কয়েক শ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এই পায়ের ছাপগুলো একজন আলোকচিত্রীর চোখে ধরা পড়ে।
বিবিসির প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০ থেকে ২৫ কোটি বছর আগে ট্রায়াসিক যুগে এই পাহাড়ের অংশটি ছিল একটি সমুদ্র তীরবর্তী সমতল ভূমি, যা পরে আল্পাইন পর্বতমালায় রূপান্তরিত হয়।
ডাল সাসো আরও বলেন, এই জায়গা ডাইনোসরে পরিপূর্ণ ছিল; এটি একটি বিশাল বৈজ্ঞানিক সম্পদ।
ডাল সাসো আরও যোগ করেন, ডাইনোসরের দলগুলো সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল করত এবং সেখানে আরও কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে, যেগুলো থেকে মনে হয়, পশুরা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধ হয়ে বৃত্তাকারে অবস্থান নিত।
আবিষ্কারকেরা বলছেন, প্রোসাওরোপডগুলো ১০ মিটার বা ৩৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারত। তারা সাধারণত দুই পায়ে হাঁটত, তবে কিছু ক্ষেত্রে পায়ের ছাপের সামনে হাতের ছাপও পাওয়া গেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, তারা সম্ভবত মাঝেমধ্যে থেমে বিশ্রাম নেওয়ার সময় তাদের সামনের পা মাটিতে রাখত।
আলোকচিত্রী এলিয়ো ডেলা ফেরেরা এই স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘এই আবিষ্কার আমাদের সবার মধ্যে ভাবনার খোরাক জোগাবে এবং আমরা যেখানে বাস করি, আমাদের ঘর, আমাদের পৃথিবী, এই জায়গাগুলো সম্পর্কে আমরা কতটা কম জানি, তা বোঝায়।’
ইতালির সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এলাকাটি অত্যন্ত দুর্গম এবং যাতায়াতের কোনো পথ নেই। তাই গবেষণার কাজে ড্রোনের পাশাপাশি রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।
উল্লেখ্য, আগামী বছর ইতালিতে শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া স্টেলভিও ন্যাশনাল পার্কটি সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে ইতালির সীমান্তবর্তী ফ্রায়েল উপত্যকায় অবস্থিত। মন্ত্রণালয় জানায়, এটি যেন অনেকটা এমন যে, স্বয়ং ইতিহাসই বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ক্রীড়া ইভেন্টকে শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছে; প্রকৃতি ও ক্রীড়ার মধ্যে এক প্রতীকী সেতুবন্ধনের মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানকে এক সুতায় গেঁথেছে।

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়।
১৬ জুন ২০২৫
দশকের পর দশক কিংবা শতাব্দীকাল ধরে মানবসভ্যতার নানা অধ্যায়ে জমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বিশ্বজুড়ে এ বছর গবেষকেরা যেন গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব, জেনেটিক বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ২০২৫ সালে উন্মোচিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক রহস্য।
২ দিন আগে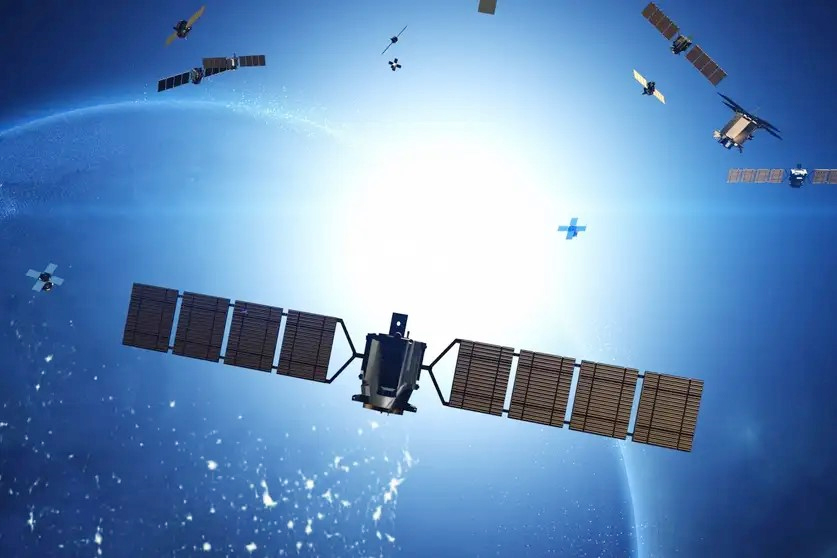
কোনো বড় ধরনের সৌরঝড় বা প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের কারণে যদি পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলো হঠাৎ নিজেদের গতিপথ পরিবর্তনের সক্ষমতা হারায়, তবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা।
৮ দিন আগে
ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা।
১১ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা। শিকার একই হওয়ায় দুই শিকারী জোট বেঁধেছে বলে মনে করছেন তাঁরা।
এ নিয়ে একটি গবেষণাও প্রকাশিত হয়েছে। সায়েন্টিফিক রিপোর্টস সাময়িকীতে প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই দুই শিকারি প্রাণীর মধ্যে হয়তো একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
গবেষকেরা বলছেন, ‘কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া উপকূলে প্যাসিফিক হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন ও নর্দার্ন রেসিডেন্ট কিলার হোয়েলের মধ্যে এ ধরনের একটি রহস্যজনক সম্পর্ক দেখা যায়, যেখানে এই দুই সিটাসিয়ান প্রজাতিকে প্রায়ই একে অপরের কয়েক মিটারের মধ্যেই দেখা যায়।’
ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লাইবনিজ ইনস্টিটিউট ও হাকাই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কাজ করা বিজ্ঞানীরা ড্রোন ভিডিও ও শব্দগত রেকর্ডিং সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে জানান, এই প্রথম অরকা ও ডলফিনের এভাবে খাদ্য চাহিদা পূরণে যৌথভাবে কাজ করতে দেখা গেল।
গবেষণার প্রধান লেখক সারা ফরচুন দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, ‘স্যামন শিকারের পারদর্শিতায় শীর্ষস্থানে রয়েছে এই তিমিগুলো। তারা অত্যন্ত দক্ষ ও বিশেষায়িত শিকারি। মনে হচ্ছিল ডলফিনগুলো তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অরকাদের এভাবে ডলফিনের অনুসরণ করতে দেখা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত আর ভীষণ রোমাঞ্চকর।’
দুই শিকারির মধ্যে সদ্য গড়ে ওঠা এই সম্পর্কের কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন। একটি সম্ভাবনা হলো ক্লেপ্টোপ্যারাসিটিজম, যেখানে ডলফিনেরা অরকার শিকার ছিনিয়ে নিতে পারে।
আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, ডলফিনেরা স্তন্যপায়ীভোজী ট্রানসিয়েন্ট কিলার হোয়েল এবং কিছুটা কম মাত্রায় বড় হাঙরের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই সম্পর্ক গড়ে তুলছে।
তবে সারা ফরচুনের মতে, যদি ডলফিনেরা পরজীবীর মতো আচরণ করত, তাহলে সদ্য ধরা শিকার নিয়ে সাধারণত অত্যন্ত রক্ষণশীল কিলার হোয়েলেরা এতটা শান্ত থাকত না, যেমনটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। এতে গবেষকদের সামনে সবচেয়ে জোরালো ব্যাখ্যাটি উঠে এসেছে, এই দুই শিকারি আসলে পরস্পরকে সহযোগিতা করছে।
সারা ফরচুন আরও বলেন, ‘অরকাগুলো নিজেদের অবস্থান এমনভাবে নিচ্ছিল, যেন তারা ডলফিনদের অনুসরণ করছে। ফলে ডলফিনদেরই নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল। বিষয়টি আমাদের আরও গভীরভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং আসলে কী ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করতে আগ্রহী করে তোলে।’
এই সহযোগিতা নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে, কারণ নর্দার্ন রেসিডেন্ট অরকারা মূলত স্যামন শিকারে বিশেষজ্ঞ আর হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন সাধারণত হেরিং ও অ্যাঙ্কোভির মতো ছোট মাছ খেয়ে থাকে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার উপকূলে একদিন। স্যামন মাছের ঝাঁক পড়িমড়ি করে ছুটতে দেখা গেল। তাদের পিছেই চোখে পড়ল কিলার হোয়েল নামে পরিচিত অরকা ও হোয়াইট–সাইডেড ডলফিনের দলকে। তাও আবার একসঙ্গে! এই দুই শিকারী প্রাণীকে জোটবেঁধে স্যামন শিকারে ছুটতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত বিজ্ঞানীরা। শিকার একই হওয়ায় দুই শিকারী জোট বেঁধেছে বলে মনে করছেন তাঁরা।
এ নিয়ে একটি গবেষণাও প্রকাশিত হয়েছে। সায়েন্টিফিক রিপোর্টস সাময়িকীতে প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই দুই শিকারি প্রাণীর মধ্যে হয়তো একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
গবেষকেরা বলছেন, ‘কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া উপকূলে প্যাসিফিক হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন ও নর্দার্ন রেসিডেন্ট কিলার হোয়েলের মধ্যে এ ধরনের একটি রহস্যজনক সম্পর্ক দেখা যায়, যেখানে এই দুই সিটাসিয়ান প্রজাতিকে প্রায়ই একে অপরের কয়েক মিটারের মধ্যেই দেখা যায়।’
ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লাইবনিজ ইনস্টিটিউট ও হাকাই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কাজ করা বিজ্ঞানীরা ড্রোন ভিডিও ও শব্দগত রেকর্ডিং সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে জানান, এই প্রথম অরকা ও ডলফিনের এভাবে খাদ্য চাহিদা পূরণে যৌথভাবে কাজ করতে দেখা গেল।
গবেষণার প্রধান লেখক সারা ফরচুন দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, ‘স্যামন শিকারের পারদর্শিতায় শীর্ষস্থানে রয়েছে এই তিমিগুলো। তারা অত্যন্ত দক্ষ ও বিশেষায়িত শিকারি। মনে হচ্ছিল ডলফিনগুলো তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অরকাদের এভাবে ডলফিনের অনুসরণ করতে দেখা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত আর ভীষণ রোমাঞ্চকর।’
দুই শিকারির মধ্যে সদ্য গড়ে ওঠা এই সম্পর্কের কারণ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন। একটি সম্ভাবনা হলো ক্লেপ্টোপ্যারাসিটিজম, যেখানে ডলফিনেরা অরকার শিকার ছিনিয়ে নিতে পারে।
আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, ডলফিনেরা স্তন্যপায়ীভোজী ট্রানসিয়েন্ট কিলার হোয়েল এবং কিছুটা কম মাত্রায় বড় হাঙরের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে এই সম্পর্ক গড়ে তুলছে।
তবে সারা ফরচুনের মতে, যদি ডলফিনেরা পরজীবীর মতো আচরণ করত, তাহলে সদ্য ধরা শিকার নিয়ে সাধারণত অত্যন্ত রক্ষণশীল কিলার হোয়েলেরা এতটা শান্ত থাকত না, যেমনটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। এতে গবেষকদের সামনে সবচেয়ে জোরালো ব্যাখ্যাটি উঠে এসেছে, এই দুই শিকারি আসলে পরস্পরকে সহযোগিতা করছে।
সারা ফরচুন আরও বলেন, ‘অরকাগুলো নিজেদের অবস্থান এমনভাবে নিচ্ছিল, যেন তারা ডলফিনদের অনুসরণ করছে। ফলে ডলফিনদেরই নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল। বিষয়টি আমাদের আরও গভীরভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং আসলে কী ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করতে আগ্রহী করে তোলে।’
এই সহযোগিতা নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে, কারণ নর্দার্ন রেসিডেন্ট অরকারা মূলত স্যামন শিকারে বিশেষজ্ঞ আর হোয়াইট–সাইডেড ডলফিন সাধারণত হেরিং ও অ্যাঙ্কোভির মতো ছোট মাছ খেয়ে থাকে।

প্রতিবছর শীত এলেই বাংলাদেশের আকাশে দেখা মেলে হাজার হাজার অতিথি বা পরিযায়ী পাখির। সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া কিংবা হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব পাখি উড়ে আসে দেশের হাওর-বাঁওড়, জলাশয় আর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। আবার গরম পড়লেই তারা পাড়ি জমায় হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের নিজের ঠিকানায়।
১৬ জুন ২০২৫
দশকের পর দশক কিংবা শতাব্দীকাল ধরে মানবসভ্যতার নানা অধ্যায়ে জমে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বিশ্বজুড়ে এ বছর গবেষকেরা যেন গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব, জেনেটিক বিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজি ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় ২০২৫ সালে উন্মোচিত হয়েছে বহু ঐতিহাসিক রহস্য।
২ দিন আগে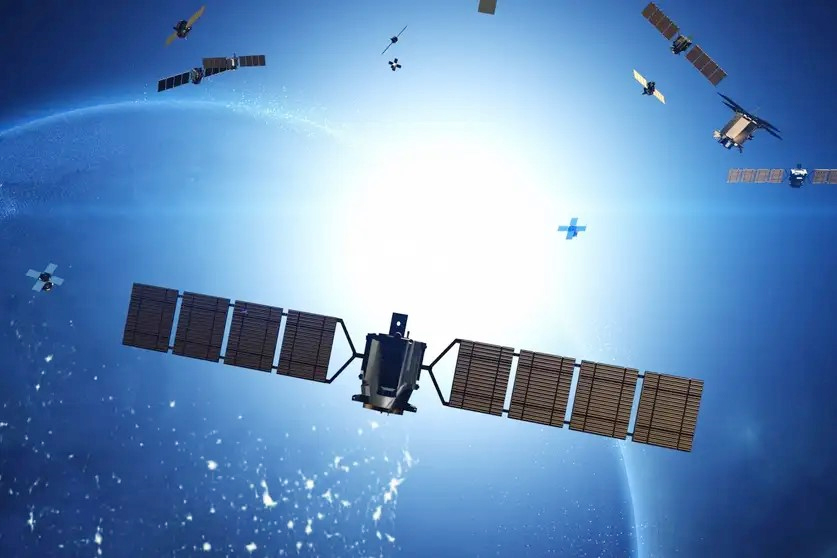
কোনো বড় ধরনের সৌরঝড় বা প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের কারণে যদি পৃথিবীর কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলো হঠাৎ নিজেদের গতিপথ পরিবর্তনের সক্ষমতা হারায়, তবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিজ্ঞানীরা।
৮ দিন আগে
উত্তর ইতালির একটি ন্যাশনাল পার্কে ২১ কোটি বছর আগের ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। তাও আবার একটি-দুটি নয়, হাজার হাজার। এই পায়ের ছাপগুলোর কয়েকটির ব্যাস ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত। আর এগুলো সমান্তরাল সারিতে সাজানো। এসবের মধ্যে অনেকগুলোতে আঙুল ও নখের ছাপ স্পষ্ট বোঝা গেছে
৮ দিন আগে