সাহস মোস্তাফিজ

গত ১০ দিনে চারজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। খবরটি উদ্বেগজনক। উদ্বেগ আরও বাড়ে, যখন জানা যায়—এর মধ্যে তিনজনই আলাদা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী।
কী চলছিল এই চার শিক্ষার্থীর মনে? এত কষ্টে গড়া একটা জীবন এক মুহূর্তে জলাঞ্জলি দিয়ে দিল তারা! তাদের মনোজগতে প্রবেশ দুঃসাধ্য হলেও সংকটটি অনুমান করা যায়, যায় অনুভব করা। আত্মহত্যার এই প্রবণতা তো আসলে দীর্ঘ সময়ের হতাশার ফল।
করোনাভাইরাসের তাৎক্ষণিক প্রভাব নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত ছিলাম। সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ছিল সর্বোচ্চ মনোযোগ। ধীরে ধীরে করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমছে। চলছে টিকা কার্যক্রম। অনেকেই এর মধ্যে টিকা নিয়েছেন। এই টিকা দিয়ে ভাইরাস নির্মূলের একটা আশা দেখা দিলেও দীর্ঘ করোনা পরিস্থিতির কারণে তীব্র হতাশা গ্রাস করেছে বিভিন্ন পেশার মানুষকে। পিছিয়ে পড়ার হতাশা, ভেঙে পড়ার হতাশা থেকে বাড়ছে মানসিক চাপ।
আশপাশ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ বর্ষে পড়তেন শিশির। ২০২০ সালের মার্চের শুরুতে তাঁর পরিকল্পনাটা ছিল—ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন, চাকরিতে ঢুকবেন, পরিবারের দুঃখের দিন ঘোচাবেন। মার্চের শেষে পুরো বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর স্বপ্নও ঘরবন্দী হয়ে পড়ল। এখনো বেকার শিশির। চাকরির জন্য যাকেই বলেন, তিনিই বলেন, ‘আর কয়েকটা দিন যাক।’ কিন্তু শিশিরের দিন তো যায় না।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমিতে গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসবে গিয়েছিলাম। প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় পর দর্শকদের উপস্থিতিতে এমন উৎসব হচ্ছে শিল্পকলায়। নাট্যকার আজাদ আবুল কালাম নাটকের শেষে আক্ষেপ করে বললেন, ‘আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি আসলে পাঁচ বছর পিছিয়ে গেছে।’
পরিচিত কয়েকটি উঠতি ব্যান্ডের খোঁজ নিলাম। করোনার আগে যে ব্যান্ডগুলো ব্যস্ত ছিল নতুন নতুন গান ও ভিডিও নির্মাণে। মঞ্চে গান করে চলে যেত ছয় বা আটজনের সংগীত-সংসার। ওই ব্যান্ডগুলোর প্রায় সবগুলোই এখন অর্ধমৃত। ব্যান্ডের সদস্যরা মনে করছেন, সংগীত পরিবেশন করে বাঁচার চেষ্টা করাই এখন বিলাসিতা। ব্যান্ডের কেউ ঢাকা ছেড়েছেন, কেউ পেশা বদলেছেন, কেউ একেবারে ভেঙে-মচকেই গেছেন।
কেউ কেউ যে নতুন করে শুরুর স্বপ্ন দেখছেন না, তা নয়। তবে আগের মতো সহজ নয়, স্বীকার করলেন কৃষ্ণপক্ষ ব্যান্ডের শিল্পী দেবাশীষ। বললেন, ‘ক্যাম্পাসে গান গেয়ে গেয়েই তো এ পর্যন্ত এসেছি ভাই, সেই ক্যাম্পাসই তো আর আগের মতো নাই। প্র্যাকটিস করতে টাকা লাগে, গান রেকর্ড করতে, ভিডিও করতে টাকা লাগে। শো ছাড়া একটা ব্যান্ড কেমন করে বাঁচবে?’
 মাসুদ আল মাহাদি অপুদের মতো বয়সের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পাস করেছেন চার বছর আগে। চার বছরের প্রথম দু বছর চাকরির প্রস্তুতি নিয়েছেন। চাকরি খুঁজেছেন। সরকারি চাকরিতে আবেদন করেছেন। পরীক্ষা দিয়েছেন। কোনো কোনো আবেদনের উত্তরই আসেনি।
মাসুদ আল মাহাদি অপুদের মতো বয়সের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পাস করেছেন চার বছর আগে। চার বছরের প্রথম দু বছর চাকরির প্রস্তুতি নিয়েছেন। চাকরি খুঁজেছেন। সরকারি চাকরিতে আবেদন করেছেন। পরীক্ষা দিয়েছেন। কোনো কোনো আবেদনের উত্তরই আসেনি।
চাকরির আবেদনে টাকা লাগে। কোথাও ৫০০, কোথাও ১ হাজার। কিন্তু এই আবেদনে সিঁকে ছেঁড়ে না অপুদের। তাঁদের এই হন্যে হয়ে চাকরি খোঁজাটা, সত্যজিৎ রায়ের ‘জনঅরণ্য’ সিনেমার দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয়, যেখানে মুখ্য চরিত্র ও তার বন্ধু একের পর এক আবেদন করতে থাকে। প্রতিবারই আশা—এবার হবে। কিন্তু শেষে সেই অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় জবাব আসে—হলো না। সেই জনঅরণ্যের শেষ দৃশ্যটির কথা আর না হয় না বলি।
এইসব বাস্তবতা এখনকার চাকরিপ্রার্থীরা জানেন না, তা নয়। তবু তাঁরা পত্রিকায় বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর চাকরির বিজ্ঞাপনে সাড়া দেন; আবেদন করেন। কিন্তু ওইটুকুই। কোনো কোনো জায়গায় চাকরিদাতারা নিজেদের লোকই নিয়ে নেয়। অপুর মতো ছেলেরা কখনো কখনো সুযোগ পান চাকরিদাতাদের প্রশ্ন করার। চাকরিদাতা উত্তর দেন, ‘তোমরা মেধাবী, এত ছোট চাকরি দিয়া তোমরা কী করবা! দুই দিন পর তো আবার অন্য চাকরিতে চইলা যাবা। তোমাদের আরও ভালো চাকরি হবে, লাইগা থাকো।’ এভাবেই বেকার হয়ে আরও ভালো চাকরির পেছনে ছুটতে থাকেন তথাকথিত মেধাবীরা।
‘তোমরা মেধাবী, এত ছোট চাকরি দিয়া তোমরা কী করবা! দুই দিন পর তো আবার অন্য চাকরিতে চইলা যাবা। তোমাদের আরও ভালো চাকরি হবে, লাইগা থাকো।’
চাকরি হয়ও কারও কারও, যাদের ফোন করার সামর্থওয়ালা বড় ভাই আছে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় মানা হয় না প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বয়সের সীমা। দেখানো হয় ‘মানবিক কারণ’।
অপু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। ভালো ফল করেছেন। তাঁর বিভাগের অনেকে বলেন, একজন শিক্ষক কয়েকটি কোর্সে ইচ্ছে করেই নম্বর কম দিতেন। ওই কয়েকটা কোর্সে সঠিক নম্বর পেলে অপু প্রথমই হতেন। সাম্প্রদায়িকতাকে যদি আমরা সমাজের বিষফোঁড়া মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকের এই রাজনৈতিক পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি, এলাকাপ্রীতিকেও বিষফোঁড়া গণ্য করা জরুরি।
অপুর জীবন কেটেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে উপাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে আন্দোলন করেছেন। আজকাল উপাচার্যরা অপুদের যুক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে পারেন না। তাঁরা মোকাবিলা করেন পেশিশক্তি কিংবা নিজস্ব বাহিনী দিয়ে। গল্প নয়, এমন ঘটনা সত্যিই ঘটেছে।
আরেকটা গল্প বলি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে চাকরি করছিলেন সানজাদ। প্রয়োজনীয় সব যোগ্যতা নিয়ে চার বছরেও সহকারী অধ্যাপক পদে আসীন হতে পারছিলেন না। করোনার আগে বোর্ড বসল। সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলেন। প্রমোশন হলে বেতনও বাড়বে। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। পরদিন সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। পরের মাস থেকে বেতন অর্ধেক। কোনো মাসে তাও নেই।
এখন সময় কিছুটা স্বাভাবিক। দু বছর পেরিয়েও সানজাদ এখনো আগের পদেই। প্রতি মুহূর্তে প্রশাসন চাপ দিচ্ছে, ‘ছাত্র ভর্তি করাও নইলে চাকরি ছাড়।’ সহকারী অধ্যাপকে পদোন্নতি না দিয়ে আরও কম বেতনে প্রভাষক নিলেই যে ওদের লাভ।
এখন সময় কিছুটা স্বাভাবিক। দু বছর পেরিয়েও সানজাদ এখনো আগের পদেই। প্রতি মুহূর্তে প্রশাসন চাপ দিচ্ছে, ‘ছাত্র ভর্তি করাও নইলে চাকরি ছাড়।’ সহকারী অধ্যাপকে পদোন্নতি না দিয়ে আরও কম বেতনে প্রভাষক নিলেই যে ওদের লাভ।
কত কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল। সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত খবর থেকে জানা যায়, শিক্ষকেরা কেউ সবজি বিক্রি করছেন, কেউ-বা গ্রামে ফিরে গেছেন।
ধরা যাক, করোনার আগে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের মাসিক খরচ ছিল ৫০ হাজার টাকা। করোনার পর সেই পরিবারের খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার টাকায়। সবকিছুর দাম বেড়েছে। কিন্তু আয়? বেশির ভাগেরই কমেছে। বেড়েছে নির্ভরশীল সদস্যের সংখ্যা। কেউ চাকরি হারিয়েছে, কারও বেতন কমেছে। মুখ তো কমেনি।
স্কুলের শিক্ষার্থীরা দু বছর ধরে ঘরবন্দী। এর মধ্যে অনেকে স্কুলে ভর্তি হলেও স্কুল দেখেনি। মাঠে খেলা নেই, পরিবারে আনন্দ নেই। অনেক পরিবারে তো নেমে এসেছে স্বজন হারানোর শোক। একটা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য এই সময়টা যে কী ভয়ানক!
যোগাযোগের বিকল্প হিসেবে যে অনলাইন প্রযুক্তি আমাদের হাতে এসেছে, সেখানে রয়েছে সহনশীলতা, মায়া, ভালোবাসার প্রবল ঘাটতি। ভার্চুয়াল জগৎ তো আর বাস্তব দুনিয়ার সবটা দিতে পারে না।
প্লিজ, আপনার পাশের মানুষটির দিকে তাকান। একটু গল্প করেন, দেখবেন রাজ্যের হতাশা তাঁর চোখে-মুখে। বৃষ্টির মতো ঝরছে চোখ বেয়ে। এমনই এক নিষ্ঠুর সময় চলছে।
তবে আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়। বীরত্ব তো নয়ই। কিন্তু এই প্রবণতার শেকড় সন্ধান জরুরি। এই ভয়ানক সামাজিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সবার অংশগ্রহণ জরুরি। এই ক্রান্তিকালে সমাজে সামগ্রিক সততার কোনো বিকল্প নেই।
সরকারের দায়িত্বটাও এখন বেড়ে গেছে। সরকার তো বাড়ি বাড়ি টাকা পৌঁছে দিতে পারবে না। ধরে ধরে মানসিক সেবাও দিতে পারবে না। সরকার পারে সমাজে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে। বিশেষ করে আর্থিক স্বচ্ছতা ও সেবার নিশ্চয়তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। এটিও এখন একটা যুদ্ধ।
এই যে প্রায়ই পত্রিকার পাতায় পড়ি ‘দেড় হাজার কোটি টাকা লোপাট’, ‘বালিশ-ভর্তি টাকা উদ্ধার’, ‘অমুক অফিসের কেরানির ঢাকায় দশটা বাড়ি’, ‘তমুক প্রজেক্টে একটা চেয়ারের দাম ৫০ হাজার টাকা’— এই ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও বোধ হয় এ দেশের তরুণেরা আবারও লড়াইয়ের রসদ ফিরে পাবে।

গত ১০ দিনে চারজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। খবরটি উদ্বেগজনক। উদ্বেগ আরও বাড়ে, যখন জানা যায়—এর মধ্যে তিনজনই আলাদা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী।
কী চলছিল এই চার শিক্ষার্থীর মনে? এত কষ্টে গড়া একটা জীবন এক মুহূর্তে জলাঞ্জলি দিয়ে দিল তারা! তাদের মনোজগতে প্রবেশ দুঃসাধ্য হলেও সংকটটি অনুমান করা যায়, যায় অনুভব করা। আত্মহত্যার এই প্রবণতা তো আসলে দীর্ঘ সময়ের হতাশার ফল।
করোনাভাইরাসের তাৎক্ষণিক প্রভাব নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত ছিলাম। সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ছিল সর্বোচ্চ মনোযোগ। ধীরে ধীরে করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমছে। চলছে টিকা কার্যক্রম। অনেকেই এর মধ্যে টিকা নিয়েছেন। এই টিকা দিয়ে ভাইরাস নির্মূলের একটা আশা দেখা দিলেও দীর্ঘ করোনা পরিস্থিতির কারণে তীব্র হতাশা গ্রাস করেছে বিভিন্ন পেশার মানুষকে। পিছিয়ে পড়ার হতাশা, ভেঙে পড়ার হতাশা থেকে বাড়ছে মানসিক চাপ।
আশপাশ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ বর্ষে পড়তেন শিশির। ২০২০ সালের মার্চের শুরুতে তাঁর পরিকল্পনাটা ছিল—ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন, চাকরিতে ঢুকবেন, পরিবারের দুঃখের দিন ঘোচাবেন। মার্চের শেষে পুরো বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর স্বপ্নও ঘরবন্দী হয়ে পড়ল। এখনো বেকার শিশির। চাকরির জন্য যাকেই বলেন, তিনিই বলেন, ‘আর কয়েকটা দিন যাক।’ কিন্তু শিশিরের দিন তো যায় না।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমিতে গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসবে গিয়েছিলাম। প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় পর দর্শকদের উপস্থিতিতে এমন উৎসব হচ্ছে শিল্পকলায়। নাট্যকার আজাদ আবুল কালাম নাটকের শেষে আক্ষেপ করে বললেন, ‘আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি আসলে পাঁচ বছর পিছিয়ে গেছে।’
পরিচিত কয়েকটি উঠতি ব্যান্ডের খোঁজ নিলাম। করোনার আগে যে ব্যান্ডগুলো ব্যস্ত ছিল নতুন নতুন গান ও ভিডিও নির্মাণে। মঞ্চে গান করে চলে যেত ছয় বা আটজনের সংগীত-সংসার। ওই ব্যান্ডগুলোর প্রায় সবগুলোই এখন অর্ধমৃত। ব্যান্ডের সদস্যরা মনে করছেন, সংগীত পরিবেশন করে বাঁচার চেষ্টা করাই এখন বিলাসিতা। ব্যান্ডের কেউ ঢাকা ছেড়েছেন, কেউ পেশা বদলেছেন, কেউ একেবারে ভেঙে-মচকেই গেছেন।
কেউ কেউ যে নতুন করে শুরুর স্বপ্ন দেখছেন না, তা নয়। তবে আগের মতো সহজ নয়, স্বীকার করলেন কৃষ্ণপক্ষ ব্যান্ডের শিল্পী দেবাশীষ। বললেন, ‘ক্যাম্পাসে গান গেয়ে গেয়েই তো এ পর্যন্ত এসেছি ভাই, সেই ক্যাম্পাসই তো আর আগের মতো নাই। প্র্যাকটিস করতে টাকা লাগে, গান রেকর্ড করতে, ভিডিও করতে টাকা লাগে। শো ছাড়া একটা ব্যান্ড কেমন করে বাঁচবে?’
 মাসুদ আল মাহাদি অপুদের মতো বয়সের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পাস করেছেন চার বছর আগে। চার বছরের প্রথম দু বছর চাকরির প্রস্তুতি নিয়েছেন। চাকরি খুঁজেছেন। সরকারি চাকরিতে আবেদন করেছেন। পরীক্ষা দিয়েছেন। কোনো কোনো আবেদনের উত্তরই আসেনি।
মাসুদ আল মাহাদি অপুদের মতো বয়সের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পাস করেছেন চার বছর আগে। চার বছরের প্রথম দু বছর চাকরির প্রস্তুতি নিয়েছেন। চাকরি খুঁজেছেন। সরকারি চাকরিতে আবেদন করেছেন। পরীক্ষা দিয়েছেন। কোনো কোনো আবেদনের উত্তরই আসেনি।
চাকরির আবেদনে টাকা লাগে। কোথাও ৫০০, কোথাও ১ হাজার। কিন্তু এই আবেদনে সিঁকে ছেঁড়ে না অপুদের। তাঁদের এই হন্যে হয়ে চাকরি খোঁজাটা, সত্যজিৎ রায়ের ‘জনঅরণ্য’ সিনেমার দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয়, যেখানে মুখ্য চরিত্র ও তার বন্ধু একের পর এক আবেদন করতে থাকে। প্রতিবারই আশা—এবার হবে। কিন্তু শেষে সেই অবধারিত ও অপরিবর্তনীয় জবাব আসে—হলো না। সেই জনঅরণ্যের শেষ দৃশ্যটির কথা আর না হয় না বলি।
এইসব বাস্তবতা এখনকার চাকরিপ্রার্থীরা জানেন না, তা নয়। তবু তাঁরা পত্রিকায় বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর চাকরির বিজ্ঞাপনে সাড়া দেন; আবেদন করেন। কিন্তু ওইটুকুই। কোনো কোনো জায়গায় চাকরিদাতারা নিজেদের লোকই নিয়ে নেয়। অপুর মতো ছেলেরা কখনো কখনো সুযোগ পান চাকরিদাতাদের প্রশ্ন করার। চাকরিদাতা উত্তর দেন, ‘তোমরা মেধাবী, এত ছোট চাকরি দিয়া তোমরা কী করবা! দুই দিন পর তো আবার অন্য চাকরিতে চইলা যাবা। তোমাদের আরও ভালো চাকরি হবে, লাইগা থাকো।’ এভাবেই বেকার হয়ে আরও ভালো চাকরির পেছনে ছুটতে থাকেন তথাকথিত মেধাবীরা।
‘তোমরা মেধাবী, এত ছোট চাকরি দিয়া তোমরা কী করবা! দুই দিন পর তো আবার অন্য চাকরিতে চইলা যাবা। তোমাদের আরও ভালো চাকরি হবে, লাইগা থাকো।’
চাকরি হয়ও কারও কারও, যাদের ফোন করার সামর্থওয়ালা বড় ভাই আছে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় মানা হয় না প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বয়সের সীমা। দেখানো হয় ‘মানবিক কারণ’।
অপু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। ভালো ফল করেছেন। তাঁর বিভাগের অনেকে বলেন, একজন শিক্ষক কয়েকটি কোর্সে ইচ্ছে করেই নম্বর কম দিতেন। ওই কয়েকটা কোর্সে সঠিক নম্বর পেলে অপু প্রথমই হতেন। সাম্প্রদায়িকতাকে যদি আমরা সমাজের বিষফোঁড়া মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকের এই রাজনৈতিক পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি, এলাকাপ্রীতিকেও বিষফোঁড়া গণ্য করা জরুরি।
অপুর জীবন কেটেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে উপাচার্যের সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তি উপস্থাপন করে আন্দোলন করেছেন। আজকাল উপাচার্যরা অপুদের যুক্তি দিয়ে মোকাবিলা করতে পারেন না। তাঁরা মোকাবিলা করেন পেশিশক্তি কিংবা নিজস্ব বাহিনী দিয়ে। গল্প নয়, এমন ঘটনা সত্যিই ঘটেছে।
আরেকটা গল্প বলি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে চাকরি করছিলেন সানজাদ। প্রয়োজনীয় সব যোগ্যতা নিয়ে চার বছরেও সহকারী অধ্যাপক পদে আসীন হতে পারছিলেন না। করোনার আগে বোর্ড বসল। সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলেন। প্রমোশন হলে বেতনও বাড়বে। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। পরদিন সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। পরের মাস থেকে বেতন অর্ধেক। কোনো মাসে তাও নেই।
এখন সময় কিছুটা স্বাভাবিক। দু বছর পেরিয়েও সানজাদ এখনো আগের পদেই। প্রতি মুহূর্তে প্রশাসন চাপ দিচ্ছে, ‘ছাত্র ভর্তি করাও নইলে চাকরি ছাড়।’ সহকারী অধ্যাপকে পদোন্নতি না দিয়ে আরও কম বেতনে প্রভাষক নিলেই যে ওদের লাভ।
এখন সময় কিছুটা স্বাভাবিক। দু বছর পেরিয়েও সানজাদ এখনো আগের পদেই। প্রতি মুহূর্তে প্রশাসন চাপ দিচ্ছে, ‘ছাত্র ভর্তি করাও নইলে চাকরি ছাড়।’ সহকারী অধ্যাপকে পদোন্নতি না দিয়ে আরও কম বেতনে প্রভাষক নিলেই যে ওদের লাভ।
কত কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল। সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত খবর থেকে জানা যায়, শিক্ষকেরা কেউ সবজি বিক্রি করছেন, কেউ-বা গ্রামে ফিরে গেছেন।
ধরা যাক, করোনার আগে মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের মাসিক খরচ ছিল ৫০ হাজার টাকা। করোনার পর সেই পরিবারের খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার টাকায়। সবকিছুর দাম বেড়েছে। কিন্তু আয়? বেশির ভাগেরই কমেছে। বেড়েছে নির্ভরশীল সদস্যের সংখ্যা। কেউ চাকরি হারিয়েছে, কারও বেতন কমেছে। মুখ তো কমেনি।
স্কুলের শিক্ষার্থীরা দু বছর ধরে ঘরবন্দী। এর মধ্যে অনেকে স্কুলে ভর্তি হলেও স্কুল দেখেনি। মাঠে খেলা নেই, পরিবারে আনন্দ নেই। অনেক পরিবারে তো নেমে এসেছে স্বজন হারানোর শোক। একটা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য এই সময়টা যে কী ভয়ানক!
যোগাযোগের বিকল্প হিসেবে যে অনলাইন প্রযুক্তি আমাদের হাতে এসেছে, সেখানে রয়েছে সহনশীলতা, মায়া, ভালোবাসার প্রবল ঘাটতি। ভার্চুয়াল জগৎ তো আর বাস্তব দুনিয়ার সবটা দিতে পারে না।
প্লিজ, আপনার পাশের মানুষটির দিকে তাকান। একটু গল্প করেন, দেখবেন রাজ্যের হতাশা তাঁর চোখে-মুখে। বৃষ্টির মতো ঝরছে চোখ বেয়ে। এমনই এক নিষ্ঠুর সময় চলছে।
তবে আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়। বীরত্ব তো নয়ই। কিন্তু এই প্রবণতার শেকড় সন্ধান জরুরি। এই ভয়ানক সামাজিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সবার অংশগ্রহণ জরুরি। এই ক্রান্তিকালে সমাজে সামগ্রিক সততার কোনো বিকল্প নেই।
সরকারের দায়িত্বটাও এখন বেড়ে গেছে। সরকার তো বাড়ি বাড়ি টাকা পৌঁছে দিতে পারবে না। ধরে ধরে মানসিক সেবাও দিতে পারবে না। সরকার পারে সমাজে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে। বিশেষ করে আর্থিক স্বচ্ছতা ও সেবার নিশ্চয়তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। এটিও এখন একটা যুদ্ধ।
এই যে প্রায়ই পত্রিকার পাতায় পড়ি ‘দেড় হাজার কোটি টাকা লোপাট’, ‘বালিশ-ভর্তি টাকা উদ্ধার’, ‘অমুক অফিসের কেরানির ঢাকায় দশটা বাড়ি’, ‘তমুক প্রজেক্টে একটা চেয়ারের দাম ৫০ হাজার টাকা’— এই ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও বোধ হয় এ দেশের তরুণেরা আবারও লড়াইয়ের রসদ ফিরে পাবে।

সাহারা মরুভূমির প্রান্তবর্তী ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ দেশ নাইজারে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়তে চায় রাশিয়া। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এরইমধ্যে এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিও হয়েছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় জ্বালানি সংস্থা রোসাটম এবং নাইজার কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত ওই চুক্তি অনুযায়ী...
২১ ঘণ্টা আগে
কিন্তু আরাকান আর্মি এখনো সেই অর্থে সিতওয়ে ও কায়াকফিউতে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ চালায়নি। কিন্তু কেন? এর পেছনে রয়েছে তিনটি কৌশলগত কারণ—কায়াকফিউতে চীনের বড় বিনিয়োগ, সিতওয়েতে ভারতের বিনিয়োগ এবং স্থানীয় জনগণের কাছে রাজনৈতিক বৈধতা ও শাসন কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এএ–এর অগ্রাধিকার।
৩ দিন আগে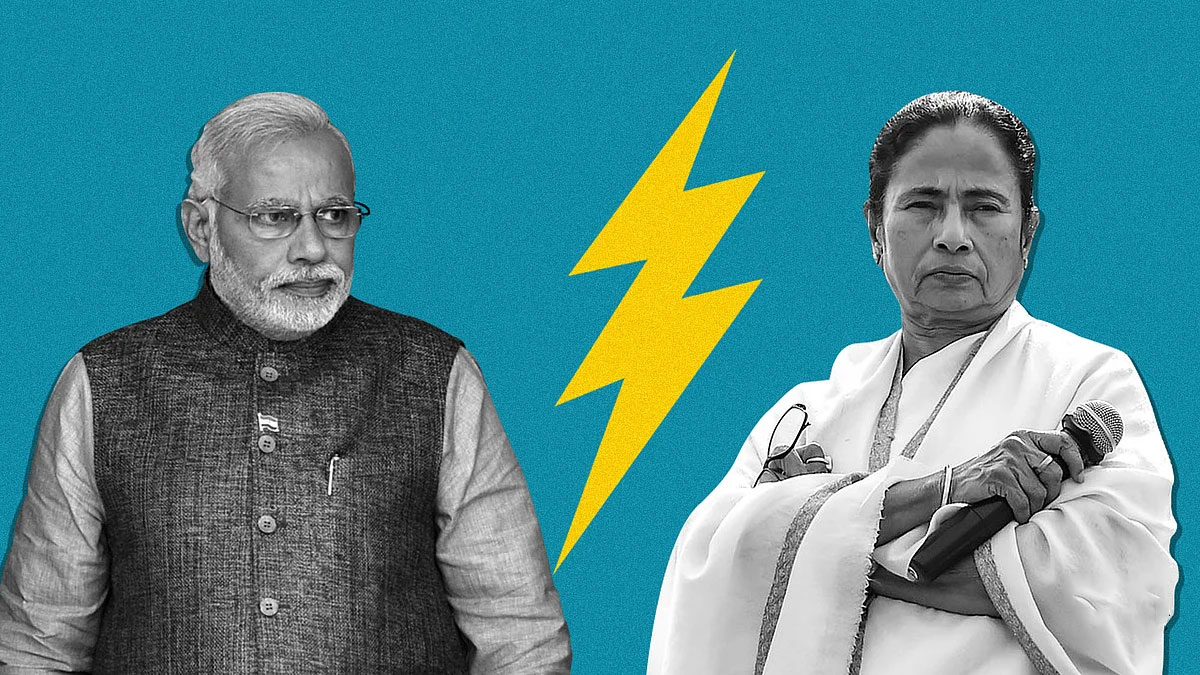
আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের আগেই নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোতে নীরবে বড়সড় পরিবর্তন এনেছেন। আগের তুলনায় বিজেপির নির্বাচনী রণনীতি এবার অনেকটাই ভিন্ন।
৩ দিন আগে
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশ্বে লবিস্ট নিয়োগের ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে বিশ্বের অন্য দেশগুলো নিজ স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে প্রায়ই লবিং ফার্ম নিয়োগ দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে খবর এসেছে, বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিপুল...
৩ দিন আগে