সৌভিক রেজা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের দ্বিশতবর্ষ আমরা পার করে এসেছি। এই কবির কৃতিত্ব ঠিক কোথায়? কবি-প্রসঙ্গে আলোচনায় আজ এই প্রশ্নটি আবারও জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬৯ বঙ্গাব্দে মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন, ‘ঋজু পরিপাটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মহতী কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন।’ তারই সূত্র ধরে এর অনেক বছর বাদে অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের মনে হয়েছিল, ‘যে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও পুরুষকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাবণ-চরিত্রে প্রথম প্রচণ্ড অভিব্যক্তি পেলো, তার উন্মেষ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই। সুন্দ-উপসুন্দ চরিত্রের ভেতরে বিদ্রোহের যে সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিলো, রাবণ চরিত্রে তারই পূর্ণতর বিকাশ।’ আর সেই কারণেই পুনরুক্তির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, ‘যে উন্নততর সৌন্দর্যবুদ্ধি, ভাষা-শিল্প ও নাটকীয়তা মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যের সম্পদ তার সূত্রপাত...তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ঘটেছিলো।’
আবার অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের কাছে মাইকেলের গোটা ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যটি একটি ‘কৃত্রিম মহাকাব্য’ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। তিনি বলছেন, ‘আমি মেঘনাদবধের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না। আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।’ শুধু মাইকেলই একা নন, বাংলার সমস্ত মহাকবির উদ্দেশে সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘হে বঙ্গমহাকবিগণ! লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভালো আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙালিদের মানুষ হইতে শিখাও।’ বুঝতে পারি যে, কাব্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে তিনি খানিকটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন।
মাইকেল মধুসূদনের প্রতি যে কজন সমালোচক কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগসহ সুবিচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মোহিতলাল মজুমদার। কবি-সমালোচক মোহিতলালের মতে, ‘সাহিত্যের রস ও সাহিত্যের রূপ এই দুই লইয়া সাহিত্যের স্বরূপ।’ তিনি মূলত সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে দিয়ে ‘কবি ও কাব্যের কার্য্যগত সম্বন্ধ’ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ‘কবিপ্রতিভা বলিতে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ বুঝায় না; কারণ, যাহাকে আমরা চিন্তাবৃত্তি বলি, কাব্য সেই চিন্তাবৃত্তির ফল নয়।’ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার রীতি-পদ্ধতিকে মোহিতলাল যে শতভাগ মান্যতা দেননি, এইটিও তার একটি নমুনা।
মর্মসন্ধানী সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে শিশিরকুমার দাশ তাঁর আলোচনায় মাইকেলের কথা বলতে গিয়ে উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসকে পটভূমি হিসেবে সামনে এনেছিলেন। কেননা, শিশিরকুমারের মতে ওই শতক হচ্ছে ‘ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচনের ইতিহাস’। যে কারণে তিনি এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধুসূদনের আবির্ভাবকে সূচনা-বিন্দু হিসেবে গণ্য করে সৃষ্টিশীল অজস্র প্রতিভার আবির্ভাব দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই দেখাটা যে একেবারেই অমূলক নয়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যালোচনার জায়গাজমির মধ্যে তার সন্ধান আমরা দেখতে পাই। মাইকেলের আত্মপ্রকাশের কাব্যিক যে সামর্থ্য, সেটির কথা বিবেচনা করেই দেবীপ্রসাদ বলেছিলেন, ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের পাঠকেরা জানেন আত্মপ্রকাশের একটি সমর্থ মাধ্যমের অনুসন্ধানে মধুসূদনের সারা জীবন কেটেছিল।’ মাইকেলের মধ্যে তিনি এমন একজন আত্মসচেতন কবিকে দেখতে পেয়েছিলেন, যে আত্মসচেতনতা তাঁকে রোমান্টিকতার বলয়ে ঠেলে দিয়েছিল।
অন্যদিকে আবার আবদুল মান্নান সৈয়দ মাইকেলের কাব্যের ‘নিহিতার্থ সন্ধান’ করতে গিয়ে বলেছিলেন—মধুসূদন একটি স্থির হ্রদ নন—এক প্রবহমান নদী, বদ্ধ মৃত ও কৃত্রিম জলাশয় নন—এক জীবিত প্রবাহ।’ মাইকেলের কবিতায় প্রবহমানতা তথা ছন্দোমুক্তিকে তিনি অশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন আর সেই বিষয়টিকে আরও বিস্তারে নিয়ে গিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘প্রসঙ্গের সাহসের সঙ্গেই প্রকরণের সাহস যুক্ত। মাইকেল যে নূতন প্রকরণের সমীপে গিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর ছিলো প্রসঙ্গেরও নবীনতা।’ সে কারণেই মান্নান সৈয়দের কাছে মধুসূদন হয়ে উঠেছিলেন ‘বাংলা সাহিত্যের দেশে প্রথম আধুনিক মানুষ।’
মান্নান সৈয়দের কথার সূত্র ধরে আমাদের মনে পড়ে যে মধুসূদনের মৃত্যুর পরে ‘বঙ্গদর্শন’ (ভাদ্র ১২৮০) পত্রিকায় বঙ্কিম লিখেছিলেন: ‘যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য।...এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা...জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূধন।’ সেই বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, ‘যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব...কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।’
২৫ জানুয়ারি মাইকেলের জন্মদিন। কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের দ্বিশতবর্ষ আমরা পার করে এসেছি। এই কবির কৃতিত্ব ঠিক কোথায়? কবি-প্রসঙ্গে আলোচনায় আজ এই প্রশ্নটি আবারও জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৬৯ বঙ্গাব্দে মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন, ‘ঋজু পরিপাটী প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মহতী কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছেন।’ তারই সূত্র ধরে এর অনেক বছর বাদে অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের মনে হয়েছিল, ‘যে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও পুরুষকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাবণ-চরিত্রে প্রথম প্রচণ্ড অভিব্যক্তি পেলো, তার উন্মেষ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই। সুন্দ-উপসুন্দ চরিত্রের ভেতরে বিদ্রোহের যে সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিলো, রাবণ চরিত্রে তারই পূর্ণতর বিকাশ।’ আর সেই কারণেই পুনরুক্তির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, ‘যে উন্নততর সৌন্দর্যবুদ্ধি, ভাষা-শিল্প ও নাটকীয়তা মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা কাব্যের সম্পদ তার সূত্রপাত...তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ঘটেছিলো।’
আবার অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথের কাছে মাইকেলের গোটা ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যটি একটি ‘কৃত্রিম মহাকাব্য’ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। তিনি বলছেন, ‘আমি মেঘনাদবধের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না। আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।’ শুধু মাইকেলই একা নন, বাংলার সমস্ত মহাকবির উদ্দেশে সেদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘হে বঙ্গমহাকবিগণ! লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভালো আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙালিদের মানুষ হইতে শিখাও।’ বুঝতে পারি যে, কাব্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে তিনি খানিকটা ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন।
মাইকেল মধুসূদনের প্রতি যে কজন সমালোচক কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগসহ সুবিচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মোহিতলাল মজুমদার। কবি-সমালোচক মোহিতলালের মতে, ‘সাহিত্যের রস ও সাহিত্যের রূপ এই দুই লইয়া সাহিত্যের স্বরূপ।’ তিনি মূলত সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে দিয়ে ‘কবি ও কাব্যের কার্য্যগত সম্বন্ধ’ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, ‘কবিপ্রতিভা বলিতে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ বুঝায় না; কারণ, যাহাকে আমরা চিন্তাবৃত্তি বলি, কাব্য সেই চিন্তাবৃত্তির ফল নয়।’ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার রীতি-পদ্ধতিকে মোহিতলাল যে শতভাগ মান্যতা দেননি, এইটিও তার একটি নমুনা।
মর্মসন্ধানী সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে শিশিরকুমার দাশ তাঁর আলোচনায় মাইকেলের কথা বলতে গিয়ে উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসকে পটভূমি হিসেবে সামনে এনেছিলেন। কেননা, শিশিরকুমারের মতে ওই শতক হচ্ছে ‘ব্যক্তিত্বের বন্ধন মোচনের ইতিহাস’। যে কারণে তিনি এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধুসূদনের আবির্ভাবকে সূচনা-বিন্দু হিসেবে গণ্য করে সৃষ্টিশীল অজস্র প্রতিভার আবির্ভাব দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই দেখাটা যে একেবারেই অমূলক নয়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যালোচনার জায়গাজমির মধ্যে তার সন্ধান আমরা দেখতে পাই। মাইকেলের আত্মপ্রকাশের কাব্যিক যে সামর্থ্য, সেটির কথা বিবেচনা করেই দেবীপ্রসাদ বলেছিলেন, ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের পাঠকেরা জানেন আত্মপ্রকাশের একটি সমর্থ মাধ্যমের অনুসন্ধানে মধুসূদনের সারা জীবন কেটেছিল।’ মাইকেলের মধ্যে তিনি এমন একজন আত্মসচেতন কবিকে দেখতে পেয়েছিলেন, যে আত্মসচেতনতা তাঁকে রোমান্টিকতার বলয়ে ঠেলে দিয়েছিল।
অন্যদিকে আবার আবদুল মান্নান সৈয়দ মাইকেলের কাব্যের ‘নিহিতার্থ সন্ধান’ করতে গিয়ে বলেছিলেন—মধুসূদন একটি স্থির হ্রদ নন—এক প্রবহমান নদী, বদ্ধ মৃত ও কৃত্রিম জলাশয় নন—এক জীবিত প্রবাহ।’ মাইকেলের কবিতায় প্রবহমানতা তথা ছন্দোমুক্তিকে তিনি অশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন আর সেই বিষয়টিকে আরও বিস্তারে নিয়ে গিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, ‘প্রসঙ্গের সাহসের সঙ্গেই প্রকরণের সাহস যুক্ত। মাইকেল যে নূতন প্রকরণের সমীপে গিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর ছিলো প্রসঙ্গেরও নবীনতা।’ সে কারণেই মান্নান সৈয়দের কাছে মধুসূদন হয়ে উঠেছিলেন ‘বাংলা সাহিত্যের দেশে প্রথম আধুনিক মানুষ।’
মান্নান সৈয়দের কথার সূত্র ধরে আমাদের মনে পড়ে যে মধুসূদনের মৃত্যুর পরে ‘বঙ্গদর্শন’ (ভাদ্র ১২৮০) পত্রিকায় বঙ্কিম লিখেছিলেন: ‘যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য।...এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা...জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূধন।’ সেই বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, ‘যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব...কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।’
২৫ জানুয়ারি মাইকেলের জন্মদিন। কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

যে সংবাদটি ছাপা হয়েছে গত বুধবারের আজকের পত্রিকার শেষের পাতায়, তা বেদনা দিয়ে ঘেরা। রাজশাহীর নিম্ন আয়ের মানুষ কীভাবে ঋণের ফাঁদে আটকে দিশেহারা হয়ে উঠছেন, তারই বিশদ বর্ণনা রয়েছে এই প্রতিবেদনে। সম্প্রতি ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে সপরিবারে আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে।
২ ঘণ্টা আগে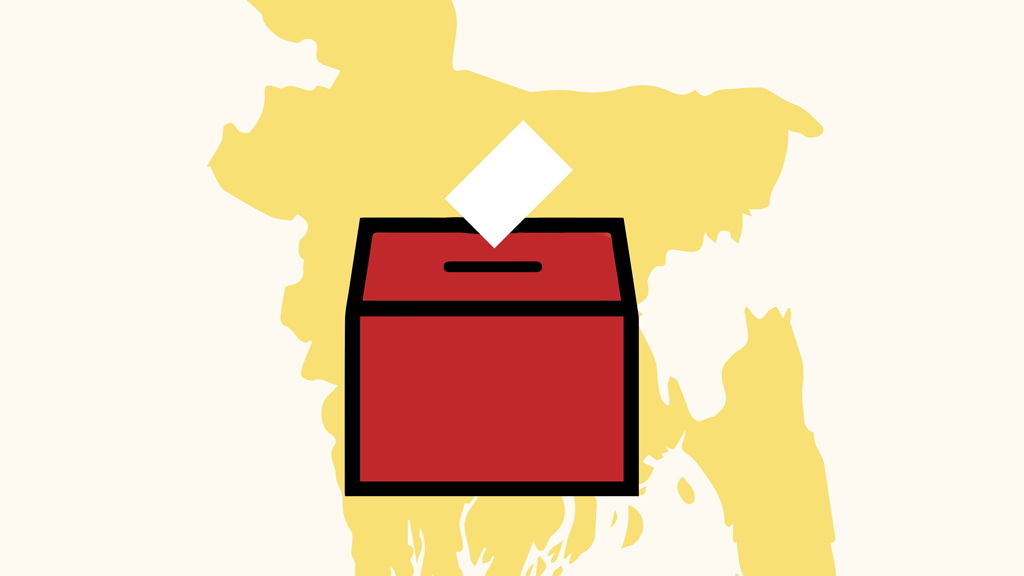
আপাতদৃষ্টিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যহীন। অর্থাৎ অভ্যুত্থান সফল হলে কী করা হবে, দেশে বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ইত্যাদি। কিন্তু অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর প্রধান দাবি ও করণীয় নির্ধারণ...
২ ঘণ্টা আগে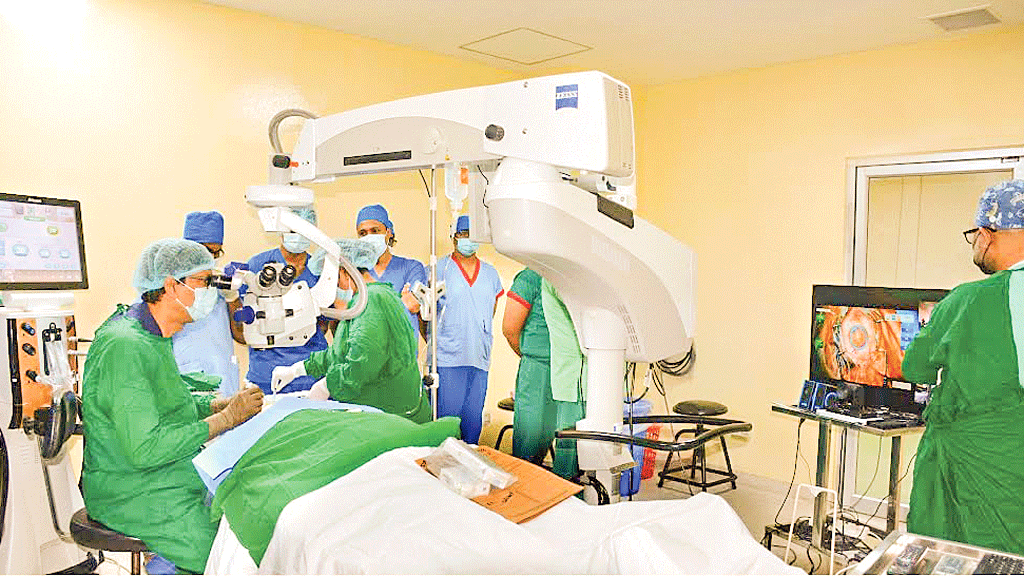
একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি উদ্যোগ এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি হাসপাতালের সংকট এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।
২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) পুরোনো দুর্নীতির একটি ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। আজকের পত্রিকায় ১৯ আগস্ট প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০১৬ সালে সোনামসজিদ স্থলবন্দরে প্রায় ৪৫০ টন জুয়েলারি (গয়না) আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু অসাধু আমদানিকারকেরা ‘কৃত্রিম মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ আমদানির ভুয়া ঘোষণা...
১ দিন আগে