জাহীদ রেজা নূর
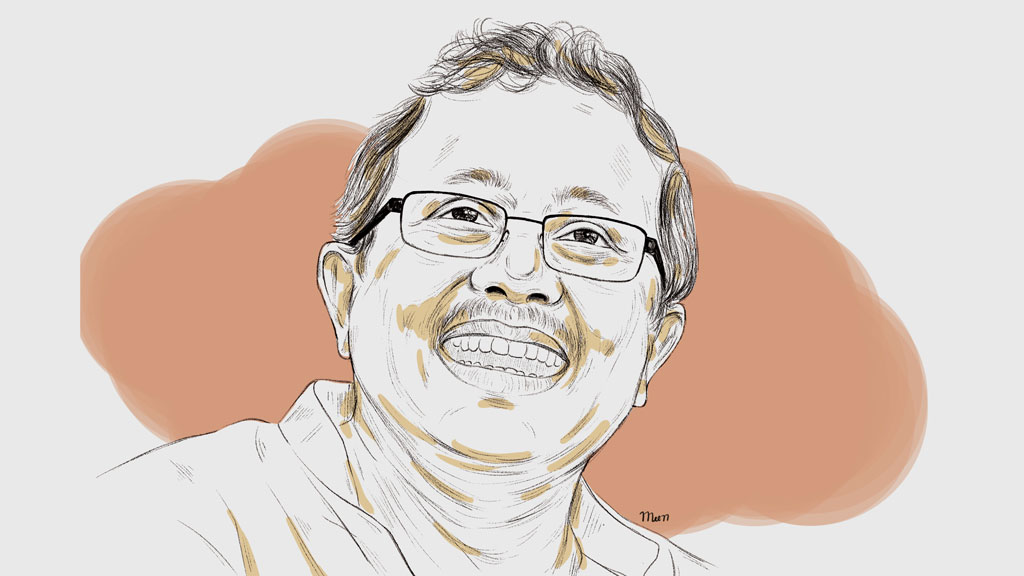
তালেবান ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ শঙ্কায় থাকবে বলে লিখেছেন পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মীর। লেখাটি বেরিয়েছে আজকের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। শুধু বাংলাদেশ নয়, সঙ্গে আরও ৯টি দেশ থাকবে হুমকির মুখে। ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতে তারা এমন কিছু কথা বলেছে, যার অর্থ দাঁড়ায়—নারী, শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়ে হয়তো তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন আনবে। কথাগুলো আন্তর্জাতিক মহল থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সাময়িক ফাঁকা বুলি কি না, তা নিয়েও ভাবছে বিশ্ব সম্প্রদায়। এখন সারা বিশ্বের চোখ আফগানিস্তানের দিকে। আফগানিস্তান বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের পরীক্ষা–নিরীক্ষা নিয়েও এখন বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো নতুন নতুন বিশ্লেষণ সামনে আনছে। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের ঘটনাবলির দিকে রাখতে হবে চোখ।
দুই. যুক্তরাষ্ট্র যখন আফগানিস্তানকে ভাগ্যের তথা তালেবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, তখন প্রশাসনকে সহায়তাকারী আফগানদের কথা একবারের জন্যও ভাবল না, এটা চরম স্বার্থপরতার নজির। আল-কায়েদা বা তালেবানকে শায়েস্তা করার কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র আদতে আফগানিস্তানে কোন পরিবর্তনটা আনতে পেরেছে? ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারা আফগান-হৃদয় অধিকার করে নিতে পারেনি। একটু নিকট অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ইরাকে সাদ্দাম হোসেনকে তৈরি করেছিল আমেরিকা, তারাই তাঁকে নিশ্চিহ্ন করেছে। তালেবানের সঙ্গে আঁতাত করেছিল মার্কিনরা, পরে তাদের শায়েস্তা করার জন্য এসেছে লড়তে। বিশ্ব রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে পড়ে আফগানিস্তানের জনগণ আসলে মুক্তভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেনি। এ কারণেই মার্কিন ঘোষণার পরপরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল তাদের গড়ে দিয়ে যাওয়া প্রশাসন। সরকারি বাহিনী কোথাও একটু প্রতিরোধ করল না, এমনকি প্রতিরোধের কথা ভাবলও না।
তিন. আরেকটি ব্যাপার তুলে ধরার পরই যাব মূল আলোচনায়। এই ভণিতাটুকু করা হলে পরের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তান সরকারকে সাহায্য করার জন্য সে দেশে সৈন্য পাঠাল, তখন অনেকেই ‘বিপ্লব রপ্তানি’ নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার কী ট্র্যাজিক পরিণতি হয়েছিল, সে কথা সবাই জানেন। গিরিখাত আর পাথুরে আফগানিস্তানে লুকিয়ে থাকার জায়গা রয়েছে অনেক। বাইরে থেকে এসে সেগুলো ধ্বংস করা ভৌগোলিকভাবেই সম্ভব নয়। আরেকটা ব্যাপার রয়ে গেছে আফগান মননে। তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনা, নিয়মকানুন, রীতি খুব একটা বদলায় না বা বদলায়নি। ভাবনার ধরনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা পশ্চিমা ভাবনার একেবারেই বিপরীত। ফলে চাইলেই আফগান মন জয় করা সম্ভব নয়। এ দুটো কারণ এড়িয়ে আফগানিস্তানকে বোঝা সম্ভব নয়।
আফগানদের সঙ্গে প্রথম বোঝাপড়া করেছিল ব্রিটেন। ১৮৩৮–১৮৪২ সালে আফগান-ইংল্যান্ড যুদ্ধ দিয়েই এর শুরু। রাশিয়ার সঙ্গে সরকারি সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছিল আফগানরা, এটা ব্রিটিশরা ভালোভাবে নেয়নি। তারা ভারত থেকে ২০ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিল কাবুল দখল করার জন্য। বাধা ছাড়াই কাবুলে পৌঁছেছিল তারা। কিন্তু সেই সুখ বেশি দিন ছিল না। প্রতিটা গ্রামের মানুষই রুখে দাঁড়িয়েছিল, যার ফল হিসেবে এই বিশাল সেনাবাহিনীকে কচুকাটা করল আফগানরা।
দ্বিতীয়বার ব্রিটিশ সেনারা আফগানিস্তানে ঢুকেছিল ১৮৭৮-১৮৮০ সময়ে। ১৮৮০ সালের ২৭ জুলাই ব্রিটিশ জেনারেল বেরোউজের বাহিনী পরাজিত হয় কান্দাহারে। অবশ্য তখন একটা দালাল সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল।
ব্রিটিশদের সঙ্গে তৃতীয় যুদ্ধ ছিল ১৯১৯ সালে। ব্রিটিশবিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন আমানুল্লাহ খান। এর পরের ইতিহাস অনেকের জানা। সৈয়দ মুজতবা আলীর অনবদ্য ‘দেশে বিদেশে’ রচনায় সেই সময়ের আফগানিস্তানের ইতিহাস পাওয়া যাবে।
এরপর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সবশেষে যুক্তরাষ্ট্র। সবার পরিণতি একই রকম। কেউ টিকতে পারেনি আফগানিস্তানে। টিকতে পারেনি সেটা বড় কথা নয়; ভাবনার দিক থেকেও খুব একটা পরিবর্তন আনতে পারেনি। বাংলাদেশসহ যে দেশগুলো শঙ্কায় থাকবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন হামিদ মীর, সেই আশঙ্কার একটা বড় কারণই হলো আফগান ভাবনার ধরনটি। সেখানেই প্রশ্ন ওঠে, আল-কায়েদা, তালেবানের দিকে কেন আকৃষ্ট হচ্ছে আমাদের মতো দেশগুলোর কেউ কেউ?
 চার. মাদ্রাসাপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাই আল-কায়েদা, তালেবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়—এমন ধারণা ভেঙে গেছে হোলি আর্টিজানে হামলার পর। বোঝা গেছে, যেকোনো সামাজিক স্তর ও শিক্ষার মানুষই এ ধরনের ‘জিহাদি’ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কেন তা ঘটে? এটা যদি জীবনবিচ্ছিন্ন পড়ালেখার ফল হতো, তাহলে একভাবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও আকৃষ্ট হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে। অবলীলায় মানুষ খুন করছে, অবলীলায় জীবন দিচ্ছে।
চার. মাদ্রাসাপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাই আল-কায়েদা, তালেবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়—এমন ধারণা ভেঙে গেছে হোলি আর্টিজানে হামলার পর। বোঝা গেছে, যেকোনো সামাজিক স্তর ও শিক্ষার মানুষই এ ধরনের ‘জিহাদি’ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কেন তা ঘটে? এটা যদি জীবনবিচ্ছিন্ন পড়ালেখার ফল হতো, তাহলে একভাবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও আকৃষ্ট হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে। অবলীলায় মানুষ খুন করছে, অবলীলায় জীবন দিচ্ছে।
দীর্ঘদিন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা একটি দেশের মানুষের মধ্যে তো এ ধরনের মনোভাব তৈরি হতে পারে না। তাহলে কী এমন ঘটনা ঘটে গেল, যার বোঝা বইতে হচ্ছে উদারপন্থী সমাজকে?
একটা হলো, শিক্ষাব্যবস্থাকে নানা মুখে ছুটতে দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা, বাংলা মিডিয়াম, ইংরেজি মিডিয়াম ইত্যাদিতে বিভক্ত করে শিক্ষায় ধনী-গরিব স্তর তৈরি করে ফেলা হয়েছে। কোনো কোনো মাদ্রাসায় যে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হতো না, সে রকম খবরও আমরা দেখেছি। সেই সব শিক্ষালয়ে দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হয় না। মাদ্রাসা নিয়ে আলোচনা থাক, স্কুলগুলোতেও কি দেশপ্রেমের শিক্ষা দেওয়া হয়? দেশের প্রতি মমত্ব আসে ভাবনাজুড়ে দেশ থাকলে। আমাদের এখানে দেশকে ভালোবাসার জন্য কি শিক্ষালয়ে কোনো পরিবেশ রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে তালেবানের প্রতি আকর্ষণের একটি সূত্র পাওয়া যাবে।
এখানেই বলে রাখা দরকার, ওয়াজের নামে অনেক ক্ষেত্রেই যে অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন, বিষোদ্গার, ঘৃণা প্রচার ইত্যাদি করা হয়, তা তথ্যের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা মানুষকে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। সাঈদীর চন্দ্রভ্রমণের কথা বিশ্বাস করা মানুষের সংখ্যা কম নয়।
দ্বিতীয় বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। ইরাকে যখন মার্কিন হামলা হয়েছিল, তখন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিল। মুসলিম দেশ হিসেবে ইরাক বাংলাদেশি মানুষের মনের কাছাকাছি ছিল। সাদ্দামকে সৃষ্টি করেছিল মার্কিনরা, তারাই তাঁকে ধ্বংস করছিল—এ কথা আমাদের দেশের মানুষকে ছোঁয়নি। হুজুগে মাতাল দেশবাসী সাদ্দামকেই নায়কের আসনে বসিয়েছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল ইরাকের ওপর মার্কিনদের হিংস্রতার কারণে। আরও বড় ব্যাপার, মার্কিনরা ইরাক আক্রমণের যে কারণ দেখিয়েছিল, পরে দেখা গেছে সে রকম কোনো কিছু ইরাক ঘটায়নি। ফলে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল। এ থেকে কারও মনে মার্কিন বিদ্বেষ চলে আসতেই পারে। ইরাকে মার্কিন হামলা ছিল অবৈধ এবং তা ছিল বিশ্বজুড়ে মার্কিন মোড়লিপনার এক নিকৃষ্ট উদাহরণ।
তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে সম্ভবত খুব কম ভাবা হয়েছে। হতাশা। হ্যাঁ, রাষ্ট্রভাবনায় হতাশা। পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে চাওয়া হয়েছিল, তা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এখনো। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পরমতসহিষ্ণুতা দিনে দিনে কমছে। তার চেয়ে বড় ব্যাপার, রাজনৈতিকভাবে এত দুর্নীতি, এত নিষ্ঠুরতার দেখা পাওয়া গেছে যে সাধারণ মানুষও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মুক্তির ঠিকানা দেখছে না। রাজনৈতিক নেতারা মুখে যা বলছেন, কাজে তার প্রতিফলন নেই। রাজনীতির সঙ্গে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। আইনসভায় আইনজীবীদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সেখানে ব্যবসায়ীরা ঢুকে পড়েছেন। ফলে দিগ্ভ্রান্ত মানুষের অনেকেই বিকল্প পথ খুঁজতে চাইছে। উদার, সহনশীল কোনো পথ দেখাতে পারছে না কেউ, তাই এমন সব পথের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তারা, যা গোটা দেশটাকেই বানিয়ে তুলতে পারে বর্বর।
পথ খুঁজে না পেয়ে অনেকে জঙ্গিবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ভালো বিকল্প পথ দেখাতে পারলে এমন হতো না।
পাঁচ. তালেবান ক্ষমতায় ফিরেছে বলে আমাদের দেশে যাঁরা উৎফুল্ল হয়েছেন কিংবা বলছেন, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ আফগানরাই গড়ে তুলুক, তারা তাদের মতো করেই বিষয়টি দেখছেন। এর সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক রয়েছে এবং সেটা মোটেই ঝুঁকিমুক্ত নয়, সেটা তাঁরা ভাবছেন না। কিন্তু তালেবান শাসনে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীকে দেখা হলে, শিক্ষার দিকে নজর না দিলে, পরমতসহিষ্ণু না হলে যে বিপদ ঘনিয়ে আসবে দেশটির সামনে, তা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লে সেটাকে অস্বাভাবিক ভাবা ঠিক হবে না। শিকড় থাকবে নিজ সংস্কৃতিতে প্রথিত, কিন্তু ডালপালা ছড়িয়ে যাবে সর্বদিকে, সবখানে। এটা না হলে বিপদ বাড়বে। আফগানরা এখন সেদিকে যাবে কি না, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা
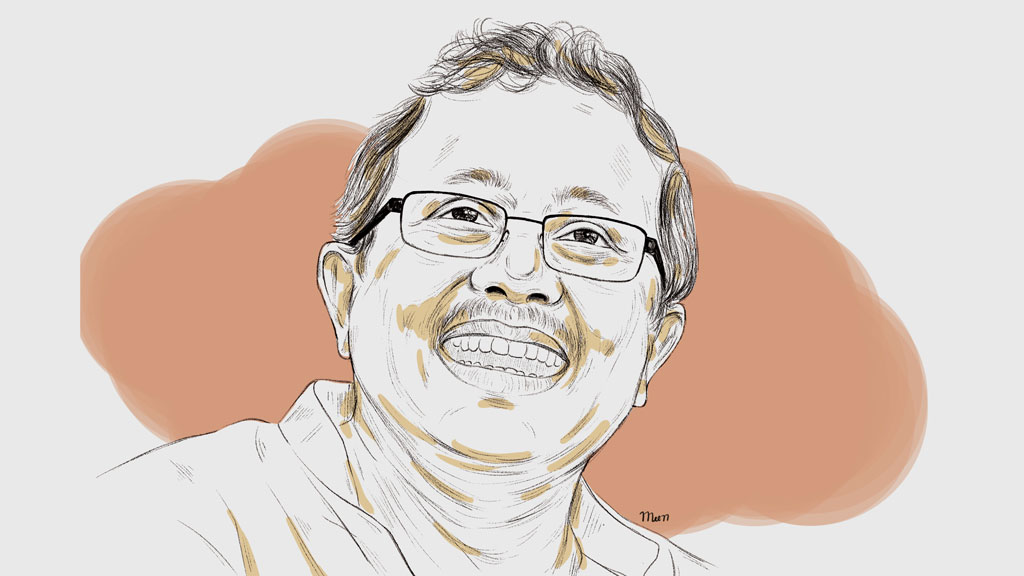
তালেবান ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশ শঙ্কায় থাকবে বলে লিখেছেন পাকিস্তানি সাংবাদিক হামিদ মীর। লেখাটি বেরিয়েছে আজকের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। শুধু বাংলাদেশ নয়, সঙ্গে আরও ৯টি দেশ থাকবে হুমকির মুখে। ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতে তারা এমন কিছু কথা বলেছে, যার অর্থ দাঁড়ায়—নারী, শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়ে হয়তো তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন আনবে। কথাগুলো আন্তর্জাতিক মহল থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সাময়িক ফাঁকা বুলি কি না, তা নিয়েও ভাবছে বিশ্ব সম্প্রদায়। এখন সারা বিশ্বের চোখ আফগানিস্তানের দিকে। আফগানিস্তান বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের পরীক্ষা–নিরীক্ষা নিয়েও এখন বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো নতুন নতুন বিশ্লেষণ সামনে আনছে। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের ঘটনাবলির দিকে রাখতে হবে চোখ।
দুই. যুক্তরাষ্ট্র যখন আফগানিস্তানকে ভাগ্যের তথা তালেবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, তখন প্রশাসনকে সহায়তাকারী আফগানদের কথা একবারের জন্যও ভাবল না, এটা চরম স্বার্থপরতার নজির। আল-কায়েদা বা তালেবানকে শায়েস্তা করার কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র আদতে আফগানিস্তানে কোন পরিবর্তনটা আনতে পেরেছে? ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তারা আফগান-হৃদয় অধিকার করে নিতে পারেনি। একটু নিকট অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ইরাকে সাদ্দাম হোসেনকে তৈরি করেছিল আমেরিকা, তারাই তাঁকে নিশ্চিহ্ন করেছে। তালেবানের সঙ্গে আঁতাত করেছিল মার্কিনরা, পরে তাদের শায়েস্তা করার জন্য এসেছে লড়তে। বিশ্ব রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে পড়ে আফগানিস্তানের জনগণ আসলে মুক্তভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেনি। এ কারণেই মার্কিন ঘোষণার পরপরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল তাদের গড়ে দিয়ে যাওয়া প্রশাসন। সরকারি বাহিনী কোথাও একটু প্রতিরোধ করল না, এমনকি প্রতিরোধের কথা ভাবলও না।
তিন. আরেকটি ব্যাপার তুলে ধরার পরই যাব মূল আলোচনায়। এই ভণিতাটুকু করা হলে পরের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার একটা ক্ষেত্র তৈরি হবে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তান সরকারকে সাহায্য করার জন্য সে দেশে সৈন্য পাঠাল, তখন অনেকেই ‘বিপ্লব রপ্তানি’ নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার কী ট্র্যাজিক পরিণতি হয়েছিল, সে কথা সবাই জানেন। গিরিখাত আর পাথুরে আফগানিস্তানে লুকিয়ে থাকার জায়গা রয়েছে অনেক। বাইরে থেকে এসে সেগুলো ধ্বংস করা ভৌগোলিকভাবেই সম্ভব নয়। আরেকটা ব্যাপার রয়ে গেছে আফগান মননে। তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবনা, নিয়মকানুন, রীতি খুব একটা বদলায় না বা বদলায়নি। ভাবনার ধরনে এমন অনেক কিছুই আছে, যা পশ্চিমা ভাবনার একেবারেই বিপরীত। ফলে চাইলেই আফগান মন জয় করা সম্ভব নয়। এ দুটো কারণ এড়িয়ে আফগানিস্তানকে বোঝা সম্ভব নয়।
আফগানদের সঙ্গে প্রথম বোঝাপড়া করেছিল ব্রিটেন। ১৮৩৮–১৮৪২ সালে আফগান-ইংল্যান্ড যুদ্ধ দিয়েই এর শুরু। রাশিয়ার সঙ্গে সরকারি সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছিল আফগানরা, এটা ব্রিটিশরা ভালোভাবে নেয়নি। তারা ভারত থেকে ২০ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিল কাবুল দখল করার জন্য। বাধা ছাড়াই কাবুলে পৌঁছেছিল তারা। কিন্তু সেই সুখ বেশি দিন ছিল না। প্রতিটা গ্রামের মানুষই রুখে দাঁড়িয়েছিল, যার ফল হিসেবে এই বিশাল সেনাবাহিনীকে কচুকাটা করল আফগানরা।
দ্বিতীয়বার ব্রিটিশ সেনারা আফগানিস্তানে ঢুকেছিল ১৮৭৮-১৮৮০ সময়ে। ১৮৮০ সালের ২৭ জুলাই ব্রিটিশ জেনারেল বেরোউজের বাহিনী পরাজিত হয় কান্দাহারে। অবশ্য তখন একটা দালাল সরকারকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল।
ব্রিটিশদের সঙ্গে তৃতীয় যুদ্ধ ছিল ১৯১৯ সালে। ব্রিটিশবিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন আমানুল্লাহ খান। এর পরের ইতিহাস অনেকের জানা। সৈয়দ মুজতবা আলীর অনবদ্য ‘দেশে বিদেশে’ রচনায় সেই সময়ের আফগানিস্তানের ইতিহাস পাওয়া যাবে।
এরপর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সবশেষে যুক্তরাষ্ট্র। সবার পরিণতি একই রকম। কেউ টিকতে পারেনি আফগানিস্তানে। টিকতে পারেনি সেটা বড় কথা নয়; ভাবনার দিক থেকেও খুব একটা পরিবর্তন আনতে পারেনি। বাংলাদেশসহ যে দেশগুলো শঙ্কায় থাকবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন হামিদ মীর, সেই আশঙ্কার একটা বড় কারণই হলো আফগান ভাবনার ধরনটি। সেখানেই প্রশ্ন ওঠে, আল-কায়েদা, তালেবানের দিকে কেন আকৃষ্ট হচ্ছে আমাদের মতো দেশগুলোর কেউ কেউ?
 চার. মাদ্রাসাপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাই আল-কায়েদা, তালেবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়—এমন ধারণা ভেঙে গেছে হোলি আর্টিজানে হামলার পর। বোঝা গেছে, যেকোনো সামাজিক স্তর ও শিক্ষার মানুষই এ ধরনের ‘জিহাদি’ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কেন তা ঘটে? এটা যদি জীবনবিচ্ছিন্ন পড়ালেখার ফল হতো, তাহলে একভাবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও আকৃষ্ট হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে। অবলীলায় মানুষ খুন করছে, অবলীলায় জীবন দিচ্ছে।
চার. মাদ্রাসাপড়ুয়া শিক্ষার্থীরাই আল-কায়েদা, তালেবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়—এমন ধারণা ভেঙে গেছে হোলি আর্টিজানে হামলার পর। বোঝা গেছে, যেকোনো সামাজিক স্তর ও শিক্ষার মানুষই এ ধরনের ‘জিহাদি’ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কেন তা ঘটে? এটা যদি জীবনবিচ্ছিন্ন পড়ালেখার ফল হতো, তাহলে একভাবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও আকৃষ্ট হচ্ছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে। অবলীলায় মানুষ খুন করছে, অবলীলায় জীবন দিচ্ছে।
দীর্ঘদিন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা একটি দেশের মানুষের মধ্যে তো এ ধরনের মনোভাব তৈরি হতে পারে না। তাহলে কী এমন ঘটনা ঘটে গেল, যার বোঝা বইতে হচ্ছে উদারপন্থী সমাজকে?
একটা হলো, শিক্ষাব্যবস্থাকে নানা মুখে ছুটতে দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা, বাংলা মিডিয়াম, ইংরেজি মিডিয়াম ইত্যাদিতে বিভক্ত করে শিক্ষায় ধনী-গরিব স্তর তৈরি করে ফেলা হয়েছে। কোনো কোনো মাদ্রাসায় যে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হতো না, সে রকম খবরও আমরা দেখেছি। সেই সব শিক্ষালয়ে দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হয় না। মাদ্রাসা নিয়ে আলোচনা থাক, স্কুলগুলোতেও কি দেশপ্রেমের শিক্ষা দেওয়া হয়? দেশের প্রতি মমত্ব আসে ভাবনাজুড়ে দেশ থাকলে। আমাদের এখানে দেশকে ভালোবাসার জন্য কি শিক্ষালয়ে কোনো পরিবেশ রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে তালেবানের প্রতি আকর্ষণের একটি সূত্র পাওয়া যাবে।
এখানেই বলে রাখা দরকার, ওয়াজের নামে অনেক ক্ষেত্রেই যে অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন, বিষোদ্গার, ঘৃণা প্রচার ইত্যাদি করা হয়, তা তথ্যের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা মানুষকে সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। সাঈদীর চন্দ্রভ্রমণের কথা বিশ্বাস করা মানুষের সংখ্যা কম নয়।
দ্বিতীয় বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। ইরাকে যখন মার্কিন হামলা হয়েছিল, তখন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিল। মুসলিম দেশ হিসেবে ইরাক বাংলাদেশি মানুষের মনের কাছাকাছি ছিল। সাদ্দামকে সৃষ্টি করেছিল মার্কিনরা, তারাই তাঁকে ধ্বংস করছিল—এ কথা আমাদের দেশের মানুষকে ছোঁয়নি। হুজুগে মাতাল দেশবাসী সাদ্দামকেই নায়কের আসনে বসিয়েছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল ইরাকের ওপর মার্কিনদের হিংস্রতার কারণে। আরও বড় ব্যাপার, মার্কিনরা ইরাক আক্রমণের যে কারণ দেখিয়েছিল, পরে দেখা গেছে সে রকম কোনো কিছু ইরাক ঘটায়নি। ফলে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল। এ থেকে কারও মনে মার্কিন বিদ্বেষ চলে আসতেই পারে। ইরাকে মার্কিন হামলা ছিল অবৈধ এবং তা ছিল বিশ্বজুড়ে মার্কিন মোড়লিপনার এক নিকৃষ্ট উদাহরণ।
তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে সম্ভবত খুব কম ভাবা হয়েছে। হতাশা। হ্যাঁ, রাষ্ট্রভাবনায় হতাশা। পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে চাওয়া হয়েছিল, তা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এখনো। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, পরমতসহিষ্ণুতা দিনে দিনে কমছে। তার চেয়ে বড় ব্যাপার, রাজনৈতিকভাবে এত দুর্নীতি, এত নিষ্ঠুরতার দেখা পাওয়া গেছে যে সাধারণ মানুষও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মুক্তির ঠিকানা দেখছে না। রাজনৈতিক নেতারা মুখে যা বলছেন, কাজে তার প্রতিফলন নেই। রাজনীতির সঙ্গে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। আইনসভায় আইনজীবীদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সেখানে ব্যবসায়ীরা ঢুকে পড়েছেন। ফলে দিগ্ভ্রান্ত মানুষের অনেকেই বিকল্প পথ খুঁজতে চাইছে। উদার, সহনশীল কোনো পথ দেখাতে পারছে না কেউ, তাই এমন সব পথের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তারা, যা গোটা দেশটাকেই বানিয়ে তুলতে পারে বর্বর।
পথ খুঁজে না পেয়ে অনেকে জঙ্গিবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। ভালো বিকল্প পথ দেখাতে পারলে এমন হতো না।
পাঁচ. তালেবান ক্ষমতায় ফিরেছে বলে আমাদের দেশে যাঁরা উৎফুল্ল হয়েছেন কিংবা বলছেন, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ আফগানরাই গড়ে তুলুক, তারা তাদের মতো করেই বিষয়টি দেখছেন। এর সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক রয়েছে এবং সেটা মোটেই ঝুঁকিমুক্ত নয়, সেটা তাঁরা ভাবছেন না। কিন্তু তালেবান শাসনে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীকে দেখা হলে, শিক্ষার দিকে নজর না দিলে, পরমতসহিষ্ণু না হলে যে বিপদ ঘনিয়ে আসবে দেশটির সামনে, তা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লে সেটাকে অস্বাভাবিক ভাবা ঠিক হবে না। শিকড় থাকবে নিজ সংস্কৃতিতে প্রথিত, কিন্তু ডালপালা ছড়িয়ে যাবে সর্বদিকে, সবখানে। এটা না হলে বিপদ বাড়বে। আফগানরা এখন সেদিকে যাবে কি না, সেটাই কোটি টাকার প্রশ্ন।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। অনেকের কাছে এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ওপর আস্থা রেখেছেন। নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল এবং নির্বাচনের পর ভোট গণনার সময় সারা রাত বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার, শুধু আমার নয় বরং অনেকেরই। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, পাশ্চাত্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, তখন প্রথম দিন বড় বোনের কাছ থেকে শাড়ি এনে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলাম। সেই দিনের শিহরণ, অনুভূতি এখনো শরীর-মনে দোলা দেয়।
৯ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের পরে যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। প্রস্তাব এসেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে। সমালোচনার মুখে সেই পথ থেকে সরে এসেছে সরকার। বাতিল করা হয়েছে গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। বহু দুঃসংবাদের মধ্যে এটি একটি সুসংবাদ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ধরনের এই কেনাকাটার বিষয়টি
৯ ঘণ্টা আগে
জাতীয় প্রেসক্লাবে ৭ সেপ্টেম্বর গণশক্তি আয়োজন করে ‘জুলাই সনদ ও নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা। সেই সভায় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না যে প্রশ্নটি করেছেন, তা কোটি টাকার সঙ্গে তুলনা করাই যায়। তাঁর সহজ জিজ্ঞাসা—‘ভোটের দিন যাঁর যেখানে শক্তি আছে, তাঁর যদি মনে হয় জিততে পারবেন না...
১ দিন আগে