মামুনুর রশীদ
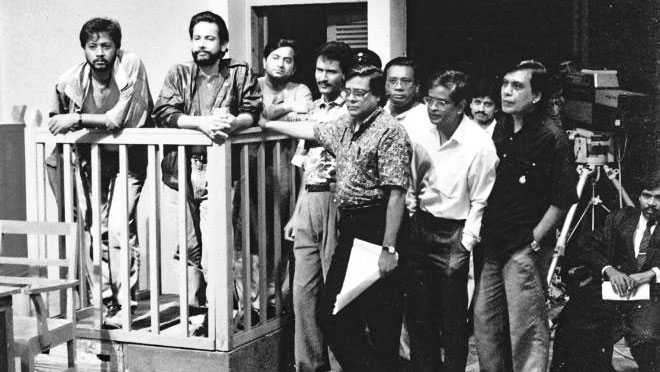
বহুদিন ধরেই বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল পণ্য হচ্ছে নাটক। নাটক, বিশেষ নাটক, ধারাবাহিক নাটক, টেলিফিল্ম—এমনি নানা শিরোনামে নাটক প্রচারিত হয়ে আসছে। মাঝেমধ্যেই নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে, প্রযোজনার দুর্বলতা নিয়ে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আচরণ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে নানা আলাপ–আলোচনা আমাদের পত্রপত্রিকায়, ফেসবুকে ও চায়ের আড্ডায় ঝড় তুলছে। টেলিভিশনের পর্দা ছাড়াও এখন এক অতি স্বাধীন মাধ্যম গড়ে উঠেছে, যার নাম ইউটিউব। এখানে যেকোনো বিষয় প্রচার করা যায়। সম্প্রতি এসেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম।
টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিদিন নাটকের প্রয়োজন হয় এবং শোনা যায়, নাটক ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠান স্পনসর হয় না। যদিও কিছুদিন ধরে সংবাদ স্পনসর হয়ে আসছে। চ্যানেলগুলো নাটক প্রচারের পর এগুলো ইউটিউবে দিয়ে থাকে এবং সেখান থেকে একটা ভালো অর্থ তারা পায়। কিছু কিছু চ্যানেলের আবার এমনই অবস্থা যে নিজেরা নাটক না কিনে ইউটিউবের একটি জনপ্রিয় নাটক কিনে থাকে এবং তা প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশে এখন বহু চ্যানেল, পাশাপাশি অজস্র ইউটিউব চ্যানেল। আবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও নাটক বানানো শুরু হয়েছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মও স্বাধীন। আর এই স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে নানান ধরনের আইনি জটিলতা হচ্ছে।
১৯৯৪ সালের আগে দেশে একটিই চ্যানেল ছিল, সেটি সরকারি। চ্যানেলটি নজরদারি করার জন্য সরকার সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকত। প্রযোজনার মান কমে গেলেও কিছু বলত না, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বিষয় হলে যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার পরেও বেশ কিছু ভালো প্রযোজক, বেশ কিছু নাট্যকারের ভালো ভালো কাজ করার সুযোগ হতো, নাটক নিয়ে মহড়া হতো, আলোচনা-সমালোচনা হতো ব্যাপক এবং সেই পাকিস্তান আমল থেকে প্রতিভাবান প্রযোজকদের হাতে ভালো নাটকও আসত এবং টেলিভিশনের জন্য, বিশেষ করে ভালো কিছু নাট্যকারেরও কাজ করার সুযোগ এসেছে।
এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে সত্তরের দশকের শেষ থেকে আশির দশক এবং নব্বইয়ের দশকের অর্ধেক পর্যন্ত টিভি নাটকের একটা স্বর্ণযুগ বিবেচিত হয়। নাটকে বিনোদন থাকত অবশ্যই, বিনোদন না থাকলে দর্শক নাটক দেখবে না—এ কথাও সত্য। ওই সময়ে যাঁরা নাটক লিখতেন, তাঁদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি থাকত। জনপ্রিয়তা একটা নিরিখ হলেও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই একটা বিষয় বারবার উচ্চারিত হতো, তা হলো নাটকটি দিয়ে কী বার্তা পৌঁছানো হলো সমাজে? যেহেতু এই মাধ্যম একটি পারিবারিক মাধ্যম, পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি থেকে শুরু করে একেবারে কনিষ্ঠ ব্যক্তিও নাটক বা টিভি অনুষ্ঠানের দর্শক। তাই এখানে কোন বিষয়টি দেখানো যাবে বা যাবে না, এর একটা হিসাব–নিকাশ সব সময়ই করতে হতো।
ওই সময়ে আমরা যাঁরা নাটক লিখতাম বা অভিনয় করতাম, তাঁদের নাটক শিশু-কিশোর থেকে সব বয়সী মানুষের একটা মানসভূমি তৈরি হওয়ার কাজে লাগত। নাটকগুলো নিয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে আলাপ-আলোচনা হতো। নাটকের কোনো চমৎকার সংলাপ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। কোনো একটি নাটকে ভুল কোনো বার্তা গেলে তা নিয়ে পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হতো। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, পশ্চিমা দেশগুলোতেও টেলিভিশন সামাজিকভাবে গুরুত্ব বহন করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো নাটক রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখত। আমাদের দেশেও সেই নজির আছে।
১৯৯৪ সালের পর যখন প্যাকেজ নাটক এল, তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে তা প্রচার করা হতো। ফলে নাটক বা অনুষ্ঠানকে একটা কঠিন প্রিভিউ বডির মাধ্যম দিয়ে যেতে হতো। কিন্তু প্রাইভেট চ্যানেলগুলোতে যখন নাটক প্রচার শুরু হলো, সেখানে প্রিভিউ কমিটি গৌণ হতে শুরু করল। দু-একটি চ্যানেলে প্রিভিউ হতো বটে, কিন্তু অধিকাংশ চ্যানেলেই বিষয়টির গুরুত্ব কমে যেতে লাগল। বাংলাদেশ টেলিভিশন যখন একমাত্র চ্যানেল ছিল, তখন পরিচালক, অভিনেতাদের সুযোগের একটা সংকোচন ছিল, যার কারণে প্রতিভাবান অনেকেই সুযোগ পাননি। নাটকের প্রযোজনা যখন উন্মুক্ত হলো, তখন বেশ কিছু পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা সুযোগ পেয়ে তাঁদের প্রতিভারও স্বাক্ষর রাখতে শুরু করলেন। এর মধ্যে চলে এল লগ্নিকারক। টেলিভিশন নাটকে চলচ্চিত্রের মতো লগ্নি লাগে না বলে দলে দলে খুদে লগ্নিকারক এই শিল্পে আসতে শুরু করলেন। যেখানে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মার্কেটিং বিভাগ ছিল একটি গৌণ জায়গা, এখানে এসে সেই জায়গা কালে কালে মুখ্য হয়ে উঠল। মূলত টেলিভিশন নাটক স্পনসর হওয়ার ওপর নির্ভর করছে একটি চ্যানেলের বাঁচা-মরা।
তাই অনুষ্ঠান বিভাগ মুখ্য নয়, মুখ্য হয়ে উঠল মার্কেটিং। মার্কেটিংয়ের লোকেরাও যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের মুখাপেক্ষী, তাঁদের ভালো লাগা ও মন্দ লাগার ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে কোথা থেকে জুটে গেল টিআরপি নামে একটি বিষয়। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এই টিআরপির খবরদারি করে। বহুবারই ভ্রান্ত টিআরপি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত শক্তিতে তারা অনুষ্ঠান বিপণনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। এর মধ্যে হুজুগপ্রিয় বাঙালি শত শত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যার অধিকাংশ ক্ষুদ্র বা স্বল্প পুঁজি নিয়ে। এবং উৎসাহিত করে চলেছে হাজার হাজার নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলী।
খুব দ্রুত এই ক্ষুদ্র শিল্প একটা বিশাল শিল্পের রূপ ধারণ করেছে। একজন পরিচালকের, নাট্যকারের, অভিনেতা-অভিনেত্রীর যে কিছু একটা যোগ্যতা থাকা দরকার, তা যেন কালে কালে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। শত শত নাটকের ওপর কোনো ধরনের অভিভাবকত্ব রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ওপর। কিন্তু সেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও আর টিকে থাকতে পারছে না। একদল ব্যবসায়ী এজেন্সি তৈরি করে টেলিভিশনের সময় কিনে নিচ্ছে। সময় কিনে নেওয়ার পর ওই নাটকের ওপর চ্যানেলের কোনো কর্তৃত্বও থাকছে না। এই এজেন্সিগুলো একধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে।
বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে কিছু শিল্পীর সময় তারা আগেভাগেই কিনে নিচ্ছে। প্রতিটি ঈদে তাদের শতাধিক নাটক বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত হয়ে থাকে, যেগুলোর কোনো প্রিভিউ করা সম্ভব হয় না। নাটক লেখা এমন একটি সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে কথার পর কথা সাজালেই তা নাটক হয়ে যায় আর পরিচালকের অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ম্যানেজারের মতো একজন মোটামুটি ক্যামেরাম্যান নিয়ে গোটা দুই দক্ষ অভিনেতা দিয়ে কাজটা নামিয়ে ফেলে এবং টিআরপির লোকেরা এসব নাটক টিআরপির প্রথম সারিতে নিয়ে আসে।
একজন নাট্য পরিচালককে যে কতটা শিক্ষিত হতে হয়, একজন নাট্যকারকে কতটা সাহিত্য সম্পর্কে জানতে হয়, একজন শিল্পীরও কতটা জানাশোনা থাকা দরকার—এসব এখন আর আলোচনার বিষয়ে আসে না। এ যেন আমরা সবাই রাজা যে যার রাজত্বে।
আশির দশকে আমাদের চলচ্চিত্রের একটা দুর্দশা হয়েছিল। অনেক পরিচালককে বলা হতো কাটপিস ডিরেক্টর। টেলিভিশনের দুর্দশা দেখে আমাদেরও মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিকেই যাচ্ছে কি না! এই যাচ্ছে কি না ভাবতে ভাবতেই দেখা গেল চলে গেছে। আজকাল টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বিভাগকে বলতে শোনা যায় অদ্ভুত সব শব্দ, তার মধ্যে একটা হচ্ছে পরিচালকদের তারা বলেন, একটা কমেডি রোমান্টিক নাটক বানিয়ে নিয়ে আসেন। সেই কমেডি রোমান্টিকের হুজুগ চলছে সর্বত্র। আর চ্যানেল না নিলেই বা কি আসে-যায়? আমাদের হাতে তো আছে ইউটিউব। যত অশ্লীলতা আছে, ভাঁড়ামি আছে এগুলোই চলে।
একশ্রেণির দর্শকও তৈরি হয়েছে, যারা এগুলো ‘খায়’। এই নৈরাজ্যের কালে কিছু ভালো নাটক যে তৈরি হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু সেগুলোর টিআরপি অতটা ওঠে না। আশির দশক পর্যন্ত পরিচালক, নাট্যকার, শিল্পীরা একটা মধ্যবিত্তের জীবনযাপন করত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত। কিন্তু আজকে এখান থেকেই একটা বিত্তবান শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে। মিডিয়ার কোনো পিকনিকে গেলে বিলাসবহুল গাড়ির সংখ্যাও গুনে শেষ করা যায় না। এত বিত্তবান মানুষ তৈরি করেছে এই শিল্প। কিন্তু বিত্তবান সমৃদ্ধ শিক্ষিত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুম্বাইয়ে দিলীপ কুমারের পাঠাগারের মতো এত বড় ব্যক্তিগত পাঠাগার আর নেই। আমাদের দেশের কজন অভিনেতার বাড়িতে পাঠাগার খুঁজে পাওয়া যাবে? পৃথিবীতে অনেক অভিনেতাই লেখক-পরিচালকের চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত।
তাই বলে তাঁরা কখনো লেখেননি। অভিনয়টাই করে গেছেন, পরিচালকও হননি। আর পরিচালকেরা তো নিজেরাই একেকটা লাইব্রেরি। চরিত্র বোঝাতে গিয়ে অভিনেতাদের সম্মোহিত করার যোগ্যতা রাখেন। আমাদের জাতীয় সংগীতে আছে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। যদি সত্যি আমরা এ দেশকে ভালোবাসি, তার শিল্প-সাহিত্য-মিডিয়াকে ভালোবাসি, তাহলে নিজের যোগ্যতা নিয়ে, অতীত গৌরব নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কী ভাবব? ‘ঘটনা সত্য’ বলে একটা অসত্যকে চাপিয়ে দিয়ে একটা অমানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করব?
লেখক: নাট্যব্যক্তিত্ব
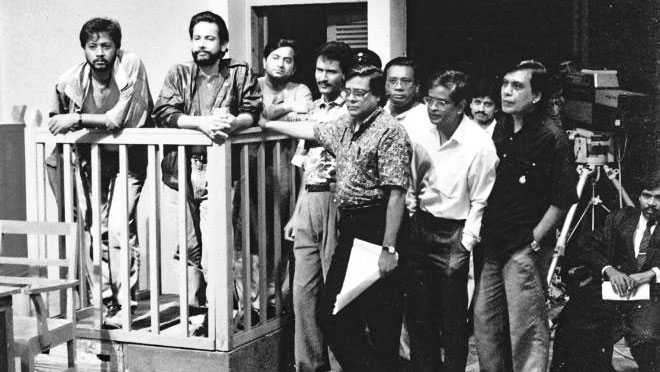
বহুদিন ধরেই বাংলাদেশের মিডিয়া জগতে সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল পণ্য হচ্ছে নাটক। নাটক, বিশেষ নাটক, ধারাবাহিক নাটক, টেলিফিল্ম—এমনি নানা শিরোনামে নাটক প্রচারিত হয়ে আসছে। মাঝেমধ্যেই নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে, প্রযোজনার দুর্বলতা নিয়ে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আচরণ ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে নানা আলাপ–আলোচনা আমাদের পত্রপত্রিকায়, ফেসবুকে ও চায়ের আড্ডায় ঝড় তুলছে। টেলিভিশনের পর্দা ছাড়াও এখন এক অতি স্বাধীন মাধ্যম গড়ে উঠেছে, যার নাম ইউটিউব। এখানে যেকোনো বিষয় প্রচার করা যায়। সম্প্রতি এসেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম।
টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিদিন নাটকের প্রয়োজন হয় এবং শোনা যায়, নাটক ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠান স্পনসর হয় না। যদিও কিছুদিন ধরে সংবাদ স্পনসর হয়ে আসছে। চ্যানেলগুলো নাটক প্রচারের পর এগুলো ইউটিউবে দিয়ে থাকে এবং সেখান থেকে একটা ভালো অর্থ তারা পায়। কিছু কিছু চ্যানেলের আবার এমনই অবস্থা যে নিজেরা নাটক না কিনে ইউটিউবের একটি জনপ্রিয় নাটক কিনে থাকে এবং তা প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশে এখন বহু চ্যানেল, পাশাপাশি অজস্র ইউটিউব চ্যানেল। আবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও নাটক বানানো শুরু হয়েছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মও স্বাধীন। আর এই স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে নানান ধরনের আইনি জটিলতা হচ্ছে।
১৯৯৪ সালের আগে দেশে একটিই চ্যানেল ছিল, সেটি সরকারি। চ্যানেলটি নজরদারি করার জন্য সরকার সব সময়ই উদ্বিগ্ন থাকত। প্রযোজনার মান কমে গেলেও কিছু বলত না, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বিষয় হলে যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার পরেও বেশ কিছু ভালো প্রযোজক, বেশ কিছু নাট্যকারের ভালো ভালো কাজ করার সুযোগ হতো, নাটক নিয়ে মহড়া হতো, আলোচনা-সমালোচনা হতো ব্যাপক এবং সেই পাকিস্তান আমল থেকে প্রতিভাবান প্রযোজকদের হাতে ভালো নাটকও আসত এবং টেলিভিশনের জন্য, বিশেষ করে ভালো কিছু নাট্যকারেরও কাজ করার সুযোগ এসেছে।
এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে সত্তরের দশকের শেষ থেকে আশির দশক এবং নব্বইয়ের দশকের অর্ধেক পর্যন্ত টিভি নাটকের একটা স্বর্ণযুগ বিবেচিত হয়। নাটকে বিনোদন থাকত অবশ্যই, বিনোদন না থাকলে দর্শক নাটক দেখবে না—এ কথাও সত্য। ওই সময়ে যাঁরা নাটক লিখতেন, তাঁদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি থাকত। জনপ্রিয়তা একটা নিরিখ হলেও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। টেলিভিশনের জন্মলগ্ন থেকেই একটা বিষয় বারবার উচ্চারিত হতো, তা হলো নাটকটি দিয়ে কী বার্তা পৌঁছানো হলো সমাজে? যেহেতু এই মাধ্যম একটি পারিবারিক মাধ্যম, পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি থেকে শুরু করে একেবারে কনিষ্ঠ ব্যক্তিও নাটক বা টিভি অনুষ্ঠানের দর্শক। তাই এখানে কোন বিষয়টি দেখানো যাবে বা যাবে না, এর একটা হিসাব–নিকাশ সব সময়ই করতে হতো।
ওই সময়ে আমরা যাঁরা নাটক লিখতাম বা অভিনয় করতাম, তাঁদের নাটক শিশু-কিশোর থেকে সব বয়সী মানুষের একটা মানসভূমি তৈরি হওয়ার কাজে লাগত। নাটকগুলো নিয়ে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে আলাপ-আলোচনা হতো। নাটকের কোনো চমৎকার সংলাপ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। কোনো একটি নাটকে ভুল কোনো বার্তা গেলে তা নিয়ে পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হতো। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, পশ্চিমা দেশগুলোতেও টেলিভিশন সামাজিকভাবে গুরুত্ব বহন করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো নাটক রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখত। আমাদের দেশেও সেই নজির আছে।
১৯৯৪ সালের পর যখন প্যাকেজ নাটক এল, তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে তা প্রচার করা হতো। ফলে নাটক বা অনুষ্ঠানকে একটা কঠিন প্রিভিউ বডির মাধ্যম দিয়ে যেতে হতো। কিন্তু প্রাইভেট চ্যানেলগুলোতে যখন নাটক প্রচার শুরু হলো, সেখানে প্রিভিউ কমিটি গৌণ হতে শুরু করল। দু-একটি চ্যানেলে প্রিভিউ হতো বটে, কিন্তু অধিকাংশ চ্যানেলেই বিষয়টির গুরুত্ব কমে যেতে লাগল। বাংলাদেশ টেলিভিশন যখন একমাত্র চ্যানেল ছিল, তখন পরিচালক, অভিনেতাদের সুযোগের একটা সংকোচন ছিল, যার কারণে প্রতিভাবান অনেকেই সুযোগ পাননি। নাটকের প্রযোজনা যখন উন্মুক্ত হলো, তখন বেশ কিছু পরিচালক, নাট্যকার, অভিনেতা সুযোগ পেয়ে তাঁদের প্রতিভারও স্বাক্ষর রাখতে শুরু করলেন। এর মধ্যে চলে এল লগ্নিকারক। টেলিভিশন নাটকে চলচ্চিত্রের মতো লগ্নি লাগে না বলে দলে দলে খুদে লগ্নিকারক এই শিল্পে আসতে শুরু করলেন। যেখানে বাংলাদেশ টেলিভিশনে মার্কেটিং বিভাগ ছিল একটি গৌণ জায়গা, এখানে এসে সেই জায়গা কালে কালে মুখ্য হয়ে উঠল। মূলত টেলিভিশন নাটক স্পনসর হওয়ার ওপর নির্ভর করছে একটি চ্যানেলের বাঁচা-মরা।
তাই অনুষ্ঠান বিভাগ মুখ্য নয়, মুখ্য হয়ে উঠল মার্কেটিং। মার্কেটিংয়ের লোকেরাও যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের মুখাপেক্ষী, তাঁদের ভালো লাগা ও মন্দ লাগার ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে কোথা থেকে জুটে গেল টিআরপি নামে একটি বিষয়। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এই টিআরপির খবরদারি করে। বহুবারই ভ্রান্ত টিআরপি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত শক্তিতে তারা অনুষ্ঠান বিপণনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। এর মধ্যে হুজুগপ্রিয় বাঙালি শত শত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যার অধিকাংশ ক্ষুদ্র বা স্বল্প পুঁজি নিয়ে। এবং উৎসাহিত করে চলেছে হাজার হাজার নাট্যকার, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলী।
খুব দ্রুত এই ক্ষুদ্র শিল্প একটা বিশাল শিল্পের রূপ ধারণ করেছে। একজন পরিচালকের, নাট্যকারের, অভিনেতা-অভিনেত্রীর যে কিছু একটা যোগ্যতা থাকা দরকার, তা যেন কালে কালে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। শত শত নাটকের ওপর কোনো ধরনের অভিভাবকত্ব রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ওপর। কিন্তু সেই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও আর টিকে থাকতে পারছে না। একদল ব্যবসায়ী এজেন্সি তৈরি করে টেলিভিশনের সময় কিনে নিচ্ছে। সময় কিনে নেওয়ার পর ওই নাটকের ওপর চ্যানেলের কোনো কর্তৃত্বও থাকছে না। এই এজেন্সিগুলো একধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে।
বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে কিছু শিল্পীর সময় তারা আগেভাগেই কিনে নিচ্ছে। প্রতিটি ঈদে তাদের শতাধিক নাটক বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত হয়ে থাকে, যেগুলোর কোনো প্রিভিউ করা সম্ভব হয় না। নাটক লেখা এমন একটি সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে কথার পর কথা সাজালেই তা নাটক হয়ে যায় আর পরিচালকের অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ম্যানেজারের মতো একজন মোটামুটি ক্যামেরাম্যান নিয়ে গোটা দুই দক্ষ অভিনেতা দিয়ে কাজটা নামিয়ে ফেলে এবং টিআরপির লোকেরা এসব নাটক টিআরপির প্রথম সারিতে নিয়ে আসে।
একজন নাট্য পরিচালককে যে কতটা শিক্ষিত হতে হয়, একজন নাট্যকারকে কতটা সাহিত্য সম্পর্কে জানতে হয়, একজন শিল্পীরও কতটা জানাশোনা থাকা দরকার—এসব এখন আর আলোচনার বিষয়ে আসে না। এ যেন আমরা সবাই রাজা যে যার রাজত্বে।
আশির দশকে আমাদের চলচ্চিত্রের একটা দুর্দশা হয়েছিল। অনেক পরিচালককে বলা হতো কাটপিস ডিরেক্টর। টেলিভিশনের দুর্দশা দেখে আমাদেরও মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিকেই যাচ্ছে কি না! এই যাচ্ছে কি না ভাবতে ভাবতেই দেখা গেল চলে গেছে। আজকাল টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বিভাগকে বলতে শোনা যায় অদ্ভুত সব শব্দ, তার মধ্যে একটা হচ্ছে পরিচালকদের তারা বলেন, একটা কমেডি রোমান্টিক নাটক বানিয়ে নিয়ে আসেন। সেই কমেডি রোমান্টিকের হুজুগ চলছে সর্বত্র। আর চ্যানেল না নিলেই বা কি আসে-যায়? আমাদের হাতে তো আছে ইউটিউব। যত অশ্লীলতা আছে, ভাঁড়ামি আছে এগুলোই চলে।
একশ্রেণির দর্শকও তৈরি হয়েছে, যারা এগুলো ‘খায়’। এই নৈরাজ্যের কালে কিছু ভালো নাটক যে তৈরি হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু সেগুলোর টিআরপি অতটা ওঠে না। আশির দশক পর্যন্ত পরিচালক, নাট্যকার, শিল্পীরা একটা মধ্যবিত্তের জীবনযাপন করত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত। কিন্তু আজকে এখান থেকেই একটা বিত্তবান শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে। মিডিয়ার কোনো পিকনিকে গেলে বিলাসবহুল গাড়ির সংখ্যাও গুনে শেষ করা যায় না। এত বিত্তবান মানুষ তৈরি করেছে এই শিল্প। কিন্তু বিত্তবান সমৃদ্ধ শিক্ষিত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুম্বাইয়ে দিলীপ কুমারের পাঠাগারের মতো এত বড় ব্যক্তিগত পাঠাগার আর নেই। আমাদের দেশের কজন অভিনেতার বাড়িতে পাঠাগার খুঁজে পাওয়া যাবে? পৃথিবীতে অনেক অভিনেতাই লেখক-পরিচালকের চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত।
তাই বলে তাঁরা কখনো লেখেননি। অভিনয়টাই করে গেছেন, পরিচালকও হননি। আর পরিচালকেরা তো নিজেরাই একেকটা লাইব্রেরি। চরিত্র বোঝাতে গিয়ে অভিনেতাদের সম্মোহিত করার যোগ্যতা রাখেন। আমাদের জাতীয় সংগীতে আছে ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। যদি সত্যি আমরা এ দেশকে ভালোবাসি, তার শিল্প-সাহিত্য-মিডিয়াকে ভালোবাসি, তাহলে নিজের যোগ্যতা নিয়ে, অতীত গৌরব নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা কী ভাবব? ‘ঘটনা সত্য’ বলে একটা অসত্যকে চাপিয়ে দিয়ে একটা অমানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করব?
লেখক: নাট্যব্যক্তিত্ব

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। অনেকের কাছে এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ওপর আস্থা রেখেছেন। নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল এবং নির্বাচনের পর ভোট গণনার সময় সারা রাত বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১ দিন আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার, শুধু আমার নয় বরং অনেকেরই। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, পাশ্চাত্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, তখন প্রথম দিন বড় বোনের কাছ থেকে শাড়ি এনে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলাম। সেই দিনের শিহরণ, অনুভূতি এখনো শরীর-মনে দোলা দেয়।
১ দিন আগে
নির্বাচনের পরে যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। প্রস্তাব এসেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে। সমালোচনার মুখে সেই পথ থেকে সরে এসেছে সরকার। বাতিল করা হয়েছে গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। বহু দুঃসংবাদের মধ্যে এটি একটি সুসংবাদ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ধরনের এই কেনাকাটার বিষয়টি
১ দিন আগে
জাতীয় প্রেসক্লাবে ৭ সেপ্টেম্বর গণশক্তি আয়োজন করে ‘জুলাই সনদ ও নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা। সেই সভায় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না যে প্রশ্নটি করেছেন, তা কোটি টাকার সঙ্গে তুলনা করাই যায়। তাঁর সহজ জিজ্ঞাসা—‘ভোটের দিন যাঁর যেখানে শক্তি আছে, তাঁর যদি মনে হয় জিততে পারবেন না...
২ দিন আগে