আবদুল্লাহ আল মোহন
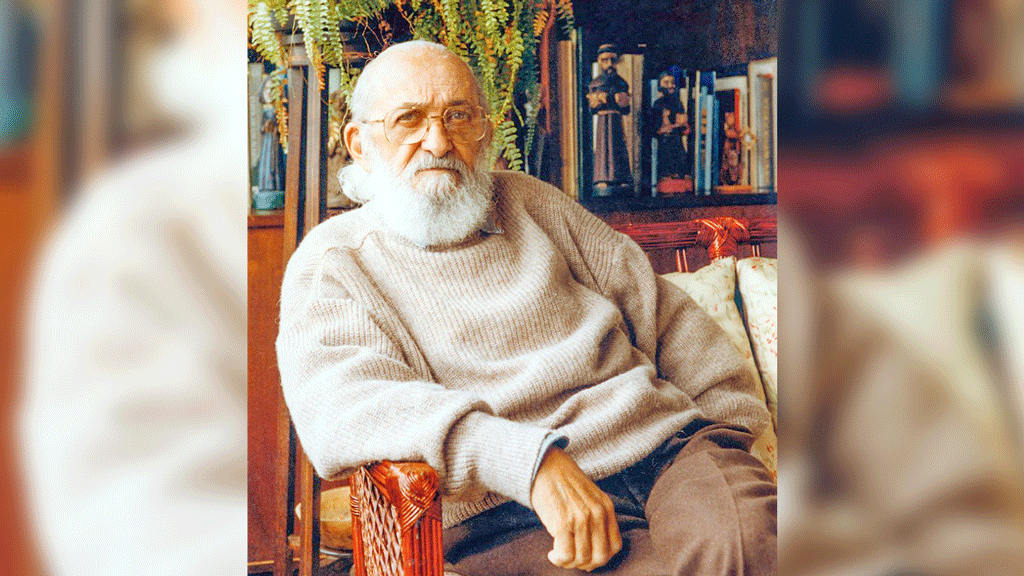
ব্রাজিলীয় বংশোদ্ভূত মানবতাবাদী শিক্ষক, শিক্ষা চিন্তক পাওলো ফ্রেইরের (মতান্তরে উচ্চারণ ‘ফ্রেইরি’) শিক্ষাভাবনা বিগত এবং চলমান শতাব্দীতে সারা দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মানবিক শিক্ষাপ্রেমী ফ্রেইরে মনে করতেন, শিক্ষা হবে মানুষের ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি, যার দ্বারা সে নিজেকে এবং সমাজকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কল্যাণধর্মী ও মানবিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হবে। আমাদের চরম জরাগ্রস্ত, অব্যবস্থাপনা, অরাজক ও পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থার এই অস্থির সময়ে তাঁকে খুব মনে পড়ে। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাচর্চা নয়, জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত থাকবে, সৃজনশীলতার বিকাশে আনন্দ-সহযোগে জীবনমুখী শিক্ষা লাভ করবে, জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার মানবিক মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা লাভ করবে।
ফ্রেইরে ১৯২১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ব্রাজিলের রেসিফ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৫ বছর বয়সে ১৯৯৭ সালের ২ মে মারা যান। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ফ্রেইরে একাডেমিক লেখালেখির পাশাপাশি শিক্ষকতা, শিক্ষকদের শিক্ষাদান, সাক্ষরতা কার্যক্রম ইত্যাদিতে জড়িত ছিলেন। তাঁর শিক্ষাভাবনার গভীরে বহমান রয়েছে মানবতাবাদ আর জনকল্যাণের দর্শন। তাঁর তত্ত্ব বিভিন্ন দেশে সফল এবং ভুল উভয়ভাবেই প্রয়োগ হয়েছে। মানুষের অসীম সম্ভাবনার প্রতি আস্থা থেকেই ফ্রেইরে লিখেছিলেন ‘অত্যাচারিতের শিক্ষা’। একজন সক্রিয় শিক্ষক হিসেবে প্রিয় এই বইটি নিত্য পাঠে নতুন নতুন ভাবনার খোরাক আজও খুঁজে পাই।
১৯৭০ সালে পর্তুগিজ ভাষায় ব্রাজিলের ধর্মযাজক ফ্রেইরের লেখা ‘অত্যাচারিতের শিক্ষা’ (Pedagogy of the oppressed) বইটিকে বৈপ্লবিক মনে করা হয়, কারণ বহু কালের পোষিত শিক্ষাভাবনার মূলে আঘাত করে তা একটা বাঁকবদল ঘটিয়েছিল। সেই প্রাচীন যুগ থেকে শিক্ষাকে মনে করা হয়েছে দানের বিষয়। শিক্ষক উঁচু বেদি থেকে শিক্ষা বা জ্ঞান প্রদান করবেন, আর শিক্ষার্থী নত হয়ে বিনা প্রশ্নে সেই জ্ঞানের খণ্ড দিয়ে মনের শূন্য পাত্র ভরে নেবে। আমাদের দেশে যেমন গুরুবাক্য ছিল আপ্তবাক্য। বেদ অপৌরুষেয়, স্মৃতিশাস্ত্র অবশ্যমান্য। ইউরোপের আঠারো শতকের জ্ঞানদীপ্তির পরেও মানুষের মনকে ফাঁকা স্লেটের মতো ভাবতে চাইতেন জন লক প্রমুখ দার্শনিক। পাওলো ফ্রেইরে এই ধারণাকে উল্টে দিয়ে বললেন, শিক্ষা জিনিসটা দান করা বা পুঁজি করে রাখার মতো বস্তু নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কথালাপ আর প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের ভেতর থেকেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে নতুন নতুন জ্ঞানের শিখা। প্রচলিত ভাবনার শিক্ষাকে তিনি বললেন আমানতি (ব্যাংকিং) ব্যবস্থা, আর তার বিপরীতে নিয়ে এলেন কথালাপী পদ্ধতি বা ‘ডায়ালজিক্যাল মেথড’। সক্রেটিসের স্মরণীয় ঐতিহ্য মনে রেখে আরও অনেকটা এগিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন, শিক্ষা মানে জ্ঞানের পিণ্ড পুঁজি করে রাখা নয়, বরং প্রতিটি শব্দের ভেতর দিয়ে এই বিশ্বের একটি খণ্ডকে হাতের মুঠোয় ধরতে পারা, যাকে চেতনার উন্মেষ বলা হয়। তাঁর আর একটি বইয়ের নাম, সাক্ষরতা: শব্দপাঠ ও বিশ্বপাঠ (লিটারেসি: রিডিং দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড), বেরিয়েছিল ১৯৮৭ সালে।
ফ্রেইরে মূলত জাঁ-পল সার্ত্র, এরিক ফ্রম, লুইস আলথুসার, হার্বাট মার্কুস, কার্ল মার্ক্সের চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর লেখনীতে। নিরক্ষরতা দূর করার প্রকল্প হাতে নিয়ে প্রচারাভিযানে ফ্রেইরে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং বিকাশ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কোনো শিক্ষা যদি কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগানো না যায় তাহলে দ্রুত সেই শিক্ষা পুরোপুরি ভুলে যাওয়া সম্ভব। শিক্ষা আমাদের এমন পথ দেখাবে, যেখানে একজন মানুষ তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। যদি তা না হয় তাহলে মানুষ পড়াশোনাকে গুরুত্ব দেবে না। পড়াশোনা থেকে নিজেরাই দূরে থাকবে।
ফ্রেইরে ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের শিক্ষাসচিব ছিলেন এবং পরবর্তীকালে পন্টিফিক্যাল ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব সাও পাওলোতে অধ্যাপনায় যুক্ত হন। তিনি ইউনেসকোর আন্তর্জাতিক জুরিবোর্ডেরও সদস্য ছিলেন এবং ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি ব্রাজিলে বয়স্ক শিক্ষার জাতীয় পরিকল্পনার সাধারণ সমন্বয়কও ছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে ১৫টি বই লিখেছেন। কয়েকটি বই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ‘অত্যাচারিতের শিক্ষা’ বইটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত।
ফ্রেইরের শৈশব কেটেছে ভীষণ কষ্টে। দারিদ্র্যের রুদ্ররূপ খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তিনি মানুষের দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব ইত্যাদির কারণ সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন আপন অতীত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই। পরে মার্ক্সের শ্রেণির ধারণা তাঁর শিক্ষাভাবনার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লেখকদের দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্যপূর্ণ ও রাজনীতিকৃত চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার উপায় নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল কথা হচ্ছে, শিক্ষাপ্রক্রিয়া হবে অংশগ্রহণমূলক, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচনা বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের এবং জগৎ সম্পর্কে জানবে অর্থাৎ জানার বিষয় নির্দিষ্ট করে পূর্বনির্ধারিত থাকবে না। এরপর তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে কাজ শুরু করবে। তিনি শিক্ষায়তনে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টি ও চর্চার ওপর জোর দিয়েছেন, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতপ্রকাশ করতে পারবে এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার প্রেরণা মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হবে বলে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।
আবদুল্লাহ আল মোহন, সহযোগী অধ্যাপক
ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা
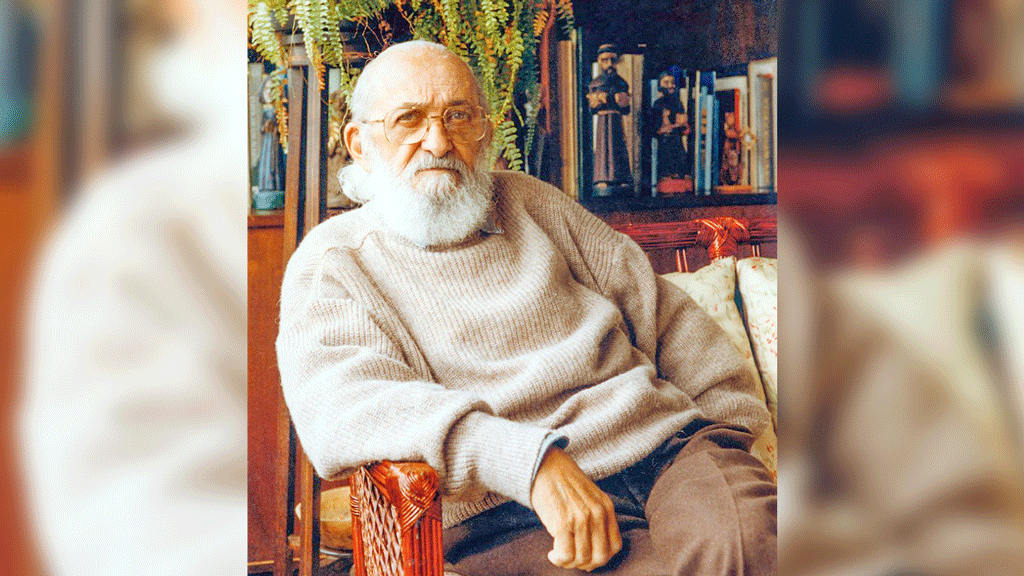
ব্রাজিলীয় বংশোদ্ভূত মানবতাবাদী শিক্ষক, শিক্ষা চিন্তক পাওলো ফ্রেইরের (মতান্তরে উচ্চারণ ‘ফ্রেইরি’) শিক্ষাভাবনা বিগত এবং চলমান শতাব্দীতে সারা দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মানবিক শিক্ষাপ্রেমী ফ্রেইরে মনে করতেন, শিক্ষা হবে মানুষের ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি, যার দ্বারা সে নিজেকে এবং সমাজকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কল্যাণধর্মী ও মানবিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হবে। আমাদের চরম জরাগ্রস্ত, অব্যবস্থাপনা, অরাজক ও পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থার এই অস্থির সময়ে তাঁকে খুব মনে পড়ে। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাচর্চা নয়, জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত থাকবে, সৃজনশীলতার বিকাশে আনন্দ-সহযোগে জীবনমুখী শিক্ষা লাভ করবে, জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার মানবিক মানুষ হওয়ার সুশিক্ষা লাভ করবে।
ফ্রেইরে ১৯২১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ব্রাজিলের রেসিফ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৫ বছর বয়সে ১৯৯৭ সালের ২ মে মারা যান। তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ফ্রেইরে একাডেমিক লেখালেখির পাশাপাশি শিক্ষকতা, শিক্ষকদের শিক্ষাদান, সাক্ষরতা কার্যক্রম ইত্যাদিতে জড়িত ছিলেন। তাঁর শিক্ষাভাবনার গভীরে বহমান রয়েছে মানবতাবাদ আর জনকল্যাণের দর্শন। তাঁর তত্ত্ব বিভিন্ন দেশে সফল এবং ভুল উভয়ভাবেই প্রয়োগ হয়েছে। মানুষের অসীম সম্ভাবনার প্রতি আস্থা থেকেই ফ্রেইরে লিখেছিলেন ‘অত্যাচারিতের শিক্ষা’। একজন সক্রিয় শিক্ষক হিসেবে প্রিয় এই বইটি নিত্য পাঠে নতুন নতুন ভাবনার খোরাক আজও খুঁজে পাই।
১৯৭০ সালে পর্তুগিজ ভাষায় ব্রাজিলের ধর্মযাজক ফ্রেইরের লেখা ‘অত্যাচারিতের শিক্ষা’ (Pedagogy of the oppressed) বইটিকে বৈপ্লবিক মনে করা হয়, কারণ বহু কালের পোষিত শিক্ষাভাবনার মূলে আঘাত করে তা একটা বাঁকবদল ঘটিয়েছিল। সেই প্রাচীন যুগ থেকে শিক্ষাকে মনে করা হয়েছে দানের বিষয়। শিক্ষক উঁচু বেদি থেকে শিক্ষা বা জ্ঞান প্রদান করবেন, আর শিক্ষার্থী নত হয়ে বিনা প্রশ্নে সেই জ্ঞানের খণ্ড দিয়ে মনের শূন্য পাত্র ভরে নেবে। আমাদের দেশে যেমন গুরুবাক্য ছিল আপ্তবাক্য। বেদ অপৌরুষেয়, স্মৃতিশাস্ত্র অবশ্যমান্য। ইউরোপের আঠারো শতকের জ্ঞানদীপ্তির পরেও মানুষের মনকে ফাঁকা স্লেটের মতো ভাবতে চাইতেন জন লক প্রমুখ দার্শনিক। পাওলো ফ্রেইরে এই ধারণাকে উল্টে দিয়ে বললেন, শিক্ষা জিনিসটা দান করা বা পুঁজি করে রাখার মতো বস্তু নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কথালাপ আর প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের ভেতর থেকেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে নতুন নতুন জ্ঞানের শিখা। প্রচলিত ভাবনার শিক্ষাকে তিনি বললেন আমানতি (ব্যাংকিং) ব্যবস্থা, আর তার বিপরীতে নিয়ে এলেন কথালাপী পদ্ধতি বা ‘ডায়ালজিক্যাল মেথড’। সক্রেটিসের স্মরণীয় ঐতিহ্য মনে রেখে আরও অনেকটা এগিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন, শিক্ষা মানে জ্ঞানের পিণ্ড পুঁজি করে রাখা নয়, বরং প্রতিটি শব্দের ভেতর দিয়ে এই বিশ্বের একটি খণ্ডকে হাতের মুঠোয় ধরতে পারা, যাকে চেতনার উন্মেষ বলা হয়। তাঁর আর একটি বইয়ের নাম, সাক্ষরতা: শব্দপাঠ ও বিশ্বপাঠ (লিটারেসি: রিডিং দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড), বেরিয়েছিল ১৯৮৭ সালে।
ফ্রেইরে মূলত জাঁ-পল সার্ত্র, এরিক ফ্রম, লুইস আলথুসার, হার্বাট মার্কুস, কার্ল মার্ক্সের চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর লেখনীতে। নিরক্ষরতা দূর করার প্রকল্প হাতে নিয়ে প্রচারাভিযানে ফ্রেইরে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং বিকাশ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কোনো শিক্ষা যদি কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগানো না যায় তাহলে দ্রুত সেই শিক্ষা পুরোপুরি ভুলে যাওয়া সম্ভব। শিক্ষা আমাদের এমন পথ দেখাবে, যেখানে একজন মানুষ তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। যদি তা না হয় তাহলে মানুষ পড়াশোনাকে গুরুত্ব দেবে না। পড়াশোনা থেকে নিজেরাই দূরে থাকবে।
ফ্রেইরে ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের শিক্ষাসচিব ছিলেন এবং পরবর্তীকালে পন্টিফিক্যাল ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব সাও পাওলোতে অধ্যাপনায় যুক্ত হন। তিনি ইউনেসকোর আন্তর্জাতিক জুরিবোর্ডেরও সদস্য ছিলেন এবং ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি ব্রাজিলে বয়স্ক শিক্ষার জাতীয় পরিকল্পনার সাধারণ সমন্বয়কও ছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে ১৫টি বই লিখেছেন। কয়েকটি বই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ‘অত্যাচারিতের শিক্ষা’ বইটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত।
ফ্রেইরের শৈশব কেটেছে ভীষণ কষ্টে। দারিদ্র্যের রুদ্ররূপ খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তিনি মানুষের দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব ইত্যাদির কারণ সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন আপন অতীত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই। পরে মার্ক্সের শ্রেণির ধারণা তাঁর শিক্ষাভাবনার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লেখকদের দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্যপূর্ণ ও রাজনীতিকৃত চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার উপায় নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল কথা হচ্ছে, শিক্ষাপ্রক্রিয়া হবে অংশগ্রহণমূলক, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচনা বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের এবং জগৎ সম্পর্কে জানবে অর্থাৎ জানার বিষয় নির্দিষ্ট করে পূর্বনির্ধারিত থাকবে না। এরপর তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে কাজ শুরু করবে। তিনি শিক্ষায়তনে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশ সৃষ্টি ও চর্চার ওপর জোর দিয়েছেন, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতপ্রকাশ করতে পারবে এবং অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার প্রেরণা মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হবে বলে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।
আবদুল্লাহ আল মোহন, সহযোগী অধ্যাপক
ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা
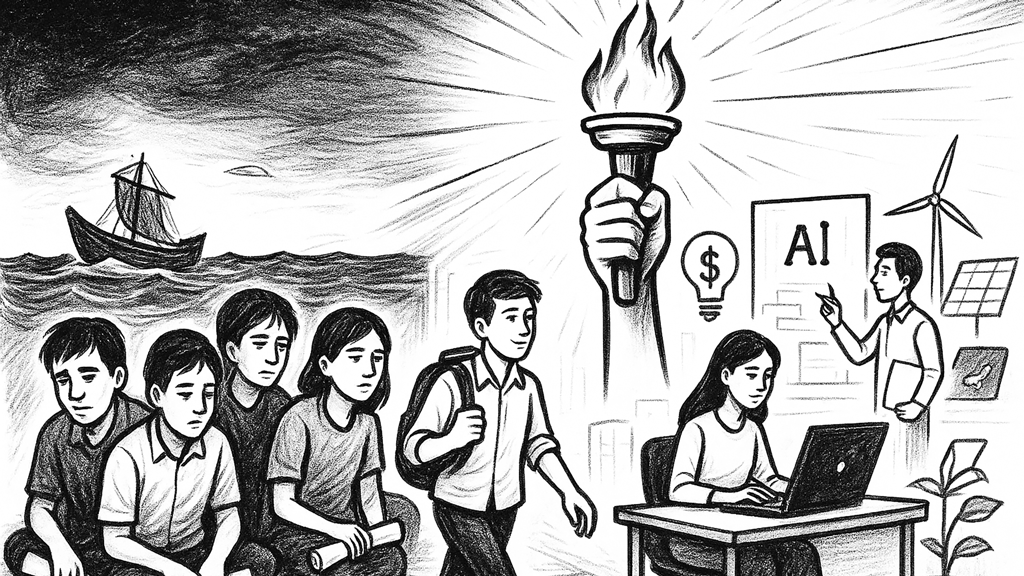
দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্সপ্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট এবং জানিয়েছেন—এ জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন।
৩ ঘণ্টা আগে
ছোট্ট একটা খবর ছাপা হয়েছে ১৮ সেপ্টেম্বরের আজকের পত্রিকার ৬ পৃষ্ঠায়। শিরোনাম, ‘১০ টাকায় ইলিশ বিক্রির ঘোষণা, না পেয়ে ঘেরাও’। খবরটি দেখে প্রথমেই চোখে ভেসে উঠল ক্ষুব্ধ হতদরিদ্র মানুষের অবয়ব। ইলিশ মাছ যে বহু আগেই সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে, সে কথা সবাই জানে।
৩ ঘণ্টা আগে
ডেঙ্গু হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্ত একটি নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিজ। অর্থাৎ সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, যারা বিশ্বপরিক্রমায় অনুমিত বাসস্থানের সুবিধায় নিজেদের উপনীত করতে ব্যর্থ, মূলত তাদের রোগ। মশা-মাছির জন্য যে পরিবেশ অনুকূল, নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মানুষের জন্য সেই পরিবেশ অনুপযুক্ত।
১০ ঘণ্টা আগে
হঠাৎ জ্বলে ওঠা নেপালের জেনারেশন জেড বিদ্রোহ যেমন দ্রুতই থেমে গেছে, তেমনি এটি একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং এর অভিঘাত ভবিষ্যতের রাজনীতিকে স্পষ্টভাবে প্রভাবিত করবে। নেপালের সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে, প্রতিটি আন্দোলনই রাষ্ট্রকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে।
১ দিন আগে