জাহীদ রেজা নূর
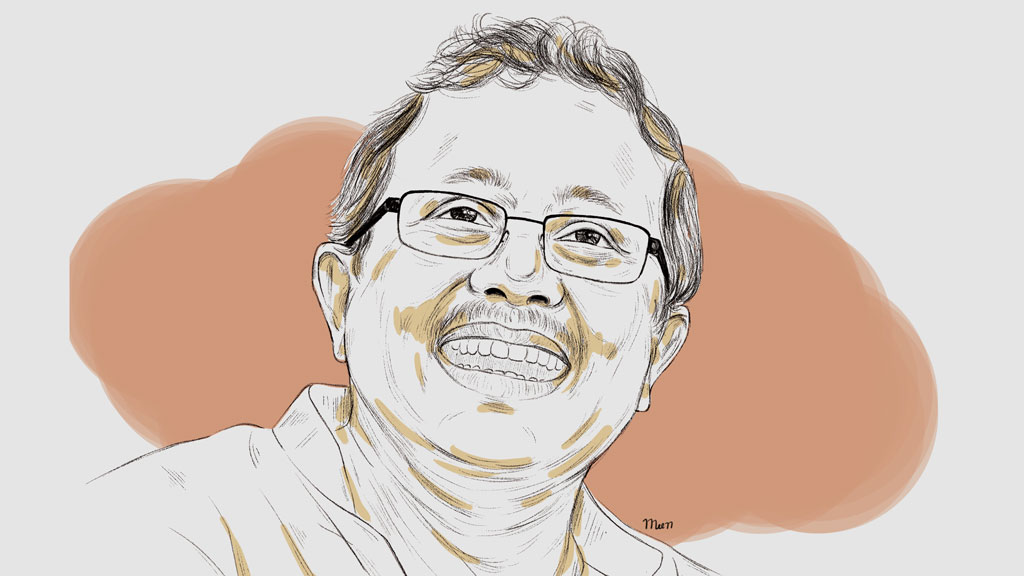
কাবুলের বিমানবন্দরে ভয়াবহ বোমা হামলার পর মনে হলো, লেখালেখির চোখ এখনো আফগানিস্তানে থাকা দরকার। আমাদের দেশে যাঁরা তালেবানের ক্ষমতায় আসা না-আসা নিয়ে খুব চিন্তিত, তাঁদের অনেকেই মনে করেন, মার্কিনদের হাত থেকে আফগানরা মুক্ত হলো, এটাই আসল বিজয়। কিন্তু এটা কার বিজয়, কেন বিজয়, আদতেই বিজয় কি না, আর বিজয় হয়ে থাকলে পরাজয়টা হলো কার, সে প্রশ্নগুলো নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। ভাবেন, সে প্রশ্নের উত্তর তাঁরা পেয়ে গেছেন।
আমাদের দেশে প্রধানত দুইভাবে এই বিজয়কে চিহ্নিত করা হয়। একটি হলো, আফগানিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতন হয়েছে। অন্যটি হলো, আফগানিস্তান নামক মুসলমানদের দেশে এখন ইসলামি হুকুমত কায়েম করবে তালেবান।
সত্যিকার অর্থে, এভাবে বিজয়ের স্বাদ নেওয়ার বাইরে যে বিশাল ক্ষেত্র রয়ে গেছে, তাতে ভাবনার চাষবাস কম। আফগানিস্তান কোন ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রয়েছে, সেটা এখনই বোঝা যাবে না। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও। আর এই ভবিষ্যতের নাগাল পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলোয়াড়েরা কে কোথায় কোন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, কে কতটা প্রস্তুত হয়ে আফগান স্টেডিয়ামে নামছেন, তার খোঁজও তো রাখতে হয়। এটা যে আফগানিস্তানে মার্কিন উপস্থিতির ২০ বছরের অবসান হয়েছে ভেবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার মতো ব্যাপার নয়, সে কথা বোঝা দরকার।
আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে মূলত সংকটটা কোথায়, সেটা বোঝার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আফগানিস্তানের প্রশস্ত মাঠে কে কোন জায়গার খেলোয়াড়, কে রক্ষণভাগ সামলাচ্ছেন, কে আক্রমণ শাণাচ্ছেন, সে বিচারের ভার থাকবে পাঠকের ওপর। আমরা শুধু খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।
দুই. পুরোনো কিছু কথা আবার মনে করিয়ে দিই। আফগানিস্তানে যখন সোভিয়েতের ভ্রাতৃপ্রতিম রাজনীতিকেরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন তাঁদেরই আহ্বানে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়েছিল ১৯৭৯ সালে। নিজ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত যেন আফগানিস্তানের চলমান অস্থিরতায় বিপর্যস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা ছিল সেটা। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র কী করেছিল? তারা আফগানিস্তানের সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা থেকে বিতাড়নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নদীর স্রোতের মতো তারা টাকা ঢেলেছিল রক্ষণশীল ও সন্ত্রাসবাদী দলগুলোকে সংগঠিত করার জন্য। পাকিস্তান সীমান্তেই সে টাকার লেনদেন হয়েছে, এই ঐতিহাসিক তথ্যটি এখন সবাই জানে।
এ সময়ই শাহকে বিতাড়নের মাধ্যমে ইরানেও যে সরকার এসেছে, তা পশ্চিমাদের বন্ধু নয়। এমনকি রাশিয়াও তখন নতুন ইরানি সরকারকে নিয়ে চিন্তিত হয়েছে। এরই মধ্যে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পোল্যান্ডে সমাজতন্ত্রবিরোধী লেখ ওয়ালেসার আন্দোলন শুরু হলো। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তও তাতে নড়বড়ে হয়ে উঠল। ১৯৮৯ সালে পরাজয় মেনে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে ফেরত আসার আগপর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনী তার সীমান্তের দুই ধারেই এ রকম অস্থিরতা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল।
এর কিছুকালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল, ওই ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের পতন হলো, সে ইতিহাস সবার জানা।
ধান ভানতে এই শিবের গীতটা গাইতে হলো এ জন্য যে, ২০০১ সালে জর্জ বুশ জুনিয়র যখন আল-কায়েদা নির্মূল করার জন্য আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠালেন, তার আগে থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্তানের একধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আফগানিস্তানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংলাপে মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে রাশিয়া। রাশিয়া আফগান গ্রুপগুলোর সন্ত্রাস সমর্থন করে না, কিন্তু বিভিন্ন সময় এদের সঙ্গে সম্পর্ক বদলেছে। বদলে চলেছে এখনো।
ভবিষ্যতের আফগানিস্তানের জন্য রাশিয়া যে একটি বড় খেলোয়াড়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
তিন. নজিবুল্লাহ ক্ষমতা ছেড়েছিলেন ১৯৯২ সালে। ১৯৯৬ সালে কাবুলে তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর জাতিসংঘের দপ্তরে আশ্রয়ে থাকা সাবেক প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। প্রকাশ্যে তাঁর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই দৃশ্য ছিল অবর্ণনীয়। শান্তিকামী মানুষ তখন তালেবানের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।
সে সময় রাশিয়ার টনক নড়ল। তারা বুঝতে পারল, তালেবান তাদের প্রভাবে রুশ সীমান্তের ভেতরের মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোকে অস্থির করে তুলতে পারে। সে সময় রাশিয়া, চীন ও কেন্দ্রীয় এশিয়ার পুরোনো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো চুক্তি স্বাক্ষর করে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়, যা ‘সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন’ নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করার ঐতিহাসিক জবাব হিসেবেই রাশিয়া আর চীন পরস্পর কাছে আসা। এখানে এসেই আমরা আরেক শক্তিশালী খেলোয়াড় পেয়ে গেলাম। চীন।
যে কারণ দেখিয়েই যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে থাকুক, মূলত আফগান ভূখণ্ডটিই ছিল বিবেচনার বিষয়। এই ভূখণ্ড কৌশলগতভাবে এমন এক জায়গা দখল করে আছে, যা স্থানীয় রাজনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভেবে দেখুন, আফগানিস্তানের কাছাকাছি অবস্থান চীন, রাশিয়ার ও ভারতের। সীমান্ত আছে ইরানের সঙ্গে। সুতরাং এ রকম একটি দেশকে নিজেদের কবজায় রাখার জন্য যে কেউ আগ্রহী হয়ে উঠবে। আর এ কারণেই স্তালিনের মৃত্যুর পর প্রথম রাশিয়া আর চীন একটা সংস্থায় একসঙ্গে নাম লেখাল।
তবে বলা দরকার, এরপর বহুবার নানাভাবে তালেবান আর রুশরা সম্পর্ককে অনেকটাই সহনশীল করে তুলেছে। নিজ অঞ্চলকে অস্থিরতার মধ্যে না ফেলে কীভাবে এই পরিস্থিতিতে নিজেকে লাভবান করা যায়, সে হিসাব কষছে রাশিয়া। চীনও তালেবানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছে।
চার. মার্কিনরা আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার সময় রাশিয়া, চীন হেসেছিল। অনেকেই ভেবেছিল, মার্কিনদের প্রভাব-প্রতিপত্তির শেষঘণ্টা বেজে উঠেছে। রাজনীতি বিশ্লেষক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তো বলেছিলেন, ‘এটা ইতিহাসের সমাপ্তি নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজোড়া ক্ষমতা প্রদর্শনের সমাপ্তি।’
কথাগুলোর মধ্যে আপাতসত্য আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনো আসেনি। নানামুখী মার্কিন সমালোচনার মধ্যেই আবার কেউ কেউ বলছেন, যদি এ অবস্থা সামলাতে হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রই সামলাতে পারবে।
চীন ভাবছে, আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদের কথা। অসাধারণ খনিজের ভান্ডার আফগানিস্তানের সঙ্গে চুক্তি হলে এই খনিজ ভান্ডারের বাণিজ্যিক পথটি খুলে দিতে পারে চীন। তাতে যে আর্থিক রমরমা আসবে, সেটা পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে চীনকে। চীন অবশ্য এ কথাটা এখন ভাবছে না যে চীনের ব্যবসায়ী ও প্রকৌশলীদের পাকিস্তানের মাটিতে অবলীলায় হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তান চীনের বন্ধু হলেও তা ঠেকানো যায়নি। সুতরাং আফগানিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সেটা তাদের জন্য কতটা নিরাপদ, সে এক রহস্যময় প্রশ্ন বটে।
পাঁচ. পাকিস্তান ভাবছে, তালেবান দাঁড়িয়ে যাবে চিরশত্রু ভারতের বিরুদ্ধে। আর তাতে লাভ হবে পাকিস্তানের। সেই কবে থেকে তালেবান তাদের বিভিন্ন কাজে সমর্থন পেয়ে এসেছে পাকিস্তানের।
পাকিস্তানের সীমানাতেই তো হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তালেবান। তাই ক্ষমতায় তালেবান এলে তাতে পাকিস্তান কৌশলগতভাবেই থাকবে নিরাপদ জায়গায়।
কিন্তু পাকিস্তানের সে গুড়ে বালি দিয়ে দিতে পারে স্বয়ং তালেবান। এ কথা তো গোপন নয় যে ব্রিটিশদের তৈরি করা ডুরান্ড লাইন কখনো মানেনি তালেবান। এর অর্থ হচ্ছে, পাকিস্তানে যে পশতুন জনগোষ্ঠী আছে, ম্যাপে তাদের পাকিস্তানের অংশ বলে স্বীকার করে না তালেবান। ডুরান্ড লাইন কেন মানছে না তালেবান? এর কারণ হচ্ছে, তাদের হয়তো ইচ্ছা, পাকিস্তানের যেখানে পশতুন অঞ্চল আছে, সেটাও চলে আসবে এক তালেবান মানচিত্রের আওতায়। সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তানের মাথা ঘোরা শুরু হতে পারে অচিরেই।
ছয়. এবার অন্য এক হিসাব-নিকাশের আলোচনা হোক। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি দেশ আফগানিস্তানের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই তালেবানের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক কী হতে পারে, তা নিয়ে ভাবছে। তবে এ কথা সত্যি, আফগানিস্তান থেকে আরেকটি অভিবাসনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ইউরোপ। এ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সামলানোর মুরোদ ইউরোপের নেই। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলকান থেকে চীন পর্যন্ত যে তুর্কি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে তালেবানই হয়ে উঠতে পারে মূল অনুঘটক। কিন্তু তার আগে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, তালেবান কি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে?
আন্তর্জাতিক ডকট্রিন তো বলছেই গৃহযুদ্ধ বা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। স্বীকৃতি পেতে হলে আসতে হবে স্বীকৃত কোনো পথে, সেটা ভোটের মাধ্যমে (এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ জরুরি), অথবা গণভোটের মাধ্যমে।
তালেবান অন্যান্য জোটের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে সত্যিই কোনো কার্যকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে কি না, তা নিয়ে এরই মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কৌশলগত অবস্থান, খনিজ সাম্রাজ্য, মাদক সাম্রাজ্য—এই সব মিলেমিশে আফগান সংকটটি যে শুধু কারও বিরুদ্ধে কারও জয়-পরাজয়ে নির্দিষ্ট হচ্ছে না, সে কথাই ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হচ্ছে। আফগান মাঠটি নতুন একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে। এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা
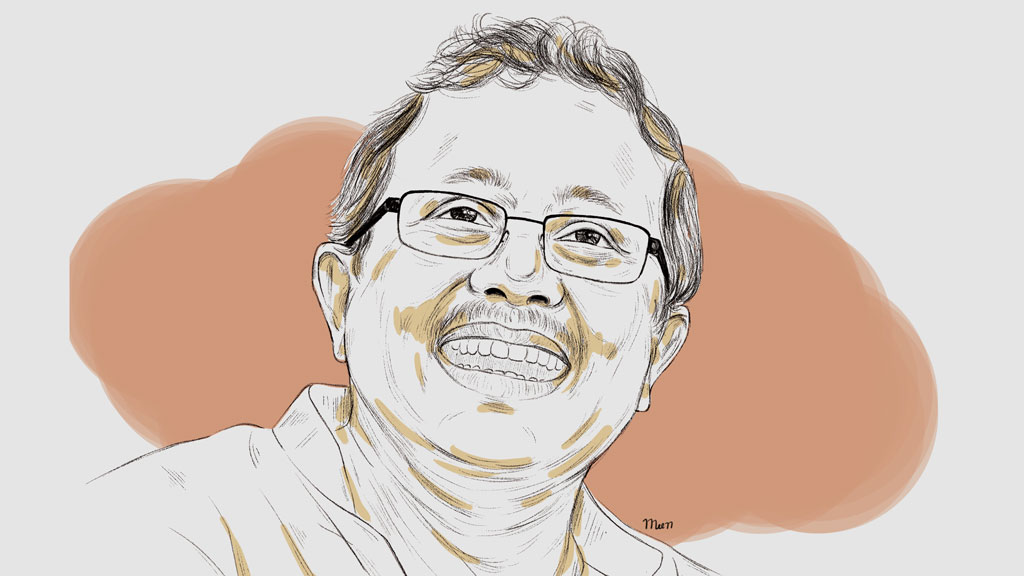
কাবুলের বিমানবন্দরে ভয়াবহ বোমা হামলার পর মনে হলো, লেখালেখির চোখ এখনো আফগানিস্তানে থাকা দরকার। আমাদের দেশে যাঁরা তালেবানের ক্ষমতায় আসা না-আসা নিয়ে খুব চিন্তিত, তাঁদের অনেকেই মনে করেন, মার্কিনদের হাত থেকে আফগানরা মুক্ত হলো, এটাই আসল বিজয়। কিন্তু এটা কার বিজয়, কেন বিজয়, আদতেই বিজয় কি না, আর বিজয় হয়ে থাকলে পরাজয়টা হলো কার, সে প্রশ্নগুলো নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। ভাবেন, সে প্রশ্নের উত্তর তাঁরা পেয়ে গেছেন।
আমাদের দেশে প্রধানত দুইভাবে এই বিজয়কে চিহ্নিত করা হয়। একটি হলো, আফগানিস্তানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতন হয়েছে। অন্যটি হলো, আফগানিস্তান নামক মুসলমানদের দেশে এখন ইসলামি হুকুমত কায়েম করবে তালেবান।
সত্যিকার অর্থে, এভাবে বিজয়ের স্বাদ নেওয়ার বাইরে যে বিশাল ক্ষেত্র রয়ে গেছে, তাতে ভাবনার চাষবাস কম। আফগানিস্তান কোন ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রয়েছে, সেটা এখনই বোঝা যাবে না। এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও। আর এই ভবিষ্যতের নাগাল পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলোয়াড়েরা কে কোথায় কোন প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, কে কতটা প্রস্তুত হয়ে আফগান স্টেডিয়ামে নামছেন, তার খোঁজও তো রাখতে হয়। এটা যে আফগানিস্তানে মার্কিন উপস্থিতির ২০ বছরের অবসান হয়েছে ভেবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার মতো ব্যাপার নয়, সে কথা বোঝা দরকার।
আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে মূলত সংকটটা কোথায়, সেটা বোঝার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আফগানিস্তানের প্রশস্ত মাঠে কে কোন জায়গার খেলোয়াড়, কে রক্ষণভাগ সামলাচ্ছেন, কে আক্রমণ শাণাচ্ছেন, সে বিচারের ভার থাকবে পাঠকের ওপর। আমরা শুধু খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।
দুই. পুরোনো কিছু কথা আবার মনে করিয়ে দিই। আফগানিস্তানে যখন সোভিয়েতের ভ্রাতৃপ্রতিম রাজনীতিকেরা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন তাঁদেরই আহ্বানে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়েছিল ১৯৭৯ সালে। নিজ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত যেন আফগানিস্তানের চলমান অস্থিরতায় বিপর্যস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা ছিল সেটা। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র কী করেছিল? তারা আফগানিস্তানের সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা থেকে বিতাড়নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নদীর স্রোতের মতো তারা টাকা ঢেলেছিল রক্ষণশীল ও সন্ত্রাসবাদী দলগুলোকে সংগঠিত করার জন্য। পাকিস্তান সীমান্তেই সে টাকার লেনদেন হয়েছে, এই ঐতিহাসিক তথ্যটি এখন সবাই জানে।
এ সময়ই শাহকে বিতাড়নের মাধ্যমে ইরানেও যে সরকার এসেছে, তা পশ্চিমাদের বন্ধু নয়। এমনকি রাশিয়াও তখন নতুন ইরানি সরকারকে নিয়ে চিন্তিত হয়েছে। এরই মধ্যে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পোল্যান্ডে সমাজতন্ত্রবিরোধী লেখ ওয়ালেসার আন্দোলন শুরু হলো। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তও তাতে নড়বড়ে হয়ে উঠল। ১৯৮৯ সালে পরাজয় মেনে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে ফেরত আসার আগপর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনী তার সীমান্তের দুই ধারেই এ রকম অস্থিরতা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল।
এর কিছুকালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল, ওই ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের পতন হলো, সে ইতিহাস সবার জানা।
ধান ভানতে এই শিবের গীতটা গাইতে হলো এ জন্য যে, ২০০১ সালে জর্জ বুশ জুনিয়র যখন আল-কায়েদা নির্মূল করার জন্য আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠালেন, তার আগে থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্তানের একধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আফগানিস্তানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংলাপে মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে রাশিয়া। রাশিয়া আফগান গ্রুপগুলোর সন্ত্রাস সমর্থন করে না, কিন্তু বিভিন্ন সময় এদের সঙ্গে সম্পর্ক বদলেছে। বদলে চলেছে এখনো।
ভবিষ্যতের আফগানিস্তানের জন্য রাশিয়া যে একটি বড় খেলোয়াড়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
তিন. নজিবুল্লাহ ক্ষমতা ছেড়েছিলেন ১৯৯২ সালে। ১৯৯৬ সালে কাবুলে তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর জাতিসংঘের দপ্তরে আশ্রয়ে থাকা সাবেক প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। প্রকাশ্যে তাঁর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই দৃশ্য ছিল অবর্ণনীয়। শান্তিকামী মানুষ তখন তালেবানের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।
সে সময় রাশিয়ার টনক নড়ল। তারা বুঝতে পারল, তালেবান তাদের প্রভাবে রুশ সীমান্তের ভেতরের মুসলিম প্রজাতন্ত্রগুলোকে অস্থির করে তুলতে পারে। সে সময় রাশিয়া, চীন ও কেন্দ্রীয় এশিয়ার পুরোনো সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো চুক্তি স্বাক্ষর করে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়, যা ‘সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন’ নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করার ঐতিহাসিক জবাব হিসেবেই রাশিয়া আর চীন পরস্পর কাছে আসা। এখানে এসেই আমরা আরেক শক্তিশালী খেলোয়াড় পেয়ে গেলাম। চীন।
যে কারণ দেখিয়েই যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে থাকুক, মূলত আফগান ভূখণ্ডটিই ছিল বিবেচনার বিষয়। এই ভূখণ্ড কৌশলগতভাবে এমন এক জায়গা দখল করে আছে, যা স্থানীয় রাজনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভেবে দেখুন, আফগানিস্তানের কাছাকাছি অবস্থান চীন, রাশিয়ার ও ভারতের। সীমান্ত আছে ইরানের সঙ্গে। সুতরাং এ রকম একটি দেশকে নিজেদের কবজায় রাখার জন্য যে কেউ আগ্রহী হয়ে উঠবে। আর এ কারণেই স্তালিনের মৃত্যুর পর প্রথম রাশিয়া আর চীন একটা সংস্থায় একসঙ্গে নাম লেখাল।
তবে বলা দরকার, এরপর বহুবার নানাভাবে তালেবান আর রুশরা সম্পর্ককে অনেকটাই সহনশীল করে তুলেছে। নিজ অঞ্চলকে অস্থিরতার মধ্যে না ফেলে কীভাবে এই পরিস্থিতিতে নিজেকে লাভবান করা যায়, সে হিসাব কষছে রাশিয়া। চীনও তালেবানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেছে।
চার. মার্কিনরা আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার সময় রাশিয়া, চীন হেসেছিল। অনেকেই ভেবেছিল, মার্কিনদের প্রভাব-প্রতিপত্তির শেষঘণ্টা বেজে উঠেছে। রাজনীতি বিশ্লেষক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তো বলেছিলেন, ‘এটা ইতিহাসের সমাপ্তি নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বজোড়া ক্ষমতা প্রদর্শনের সমাপ্তি।’
কথাগুলোর মধ্যে আপাতসত্য আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনো আসেনি। নানামুখী মার্কিন সমালোচনার মধ্যেই আবার কেউ কেউ বলছেন, যদি এ অবস্থা সামলাতে হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রই সামলাতে পারবে।
চীন ভাবছে, আফগানিস্তানের খনিজ সম্পদের কথা। অসাধারণ খনিজের ভান্ডার আফগানিস্তানের সঙ্গে চুক্তি হলে এই খনিজ ভান্ডারের বাণিজ্যিক পথটি খুলে দিতে পারে চীন। তাতে যে আর্থিক রমরমা আসবে, সেটা পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে চীনকে। চীন অবশ্য এ কথাটা এখন ভাবছে না যে চীনের ব্যবসায়ী ও প্রকৌশলীদের পাকিস্তানের মাটিতে অবলীলায় হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তান চীনের বন্ধু হলেও তা ঠেকানো যায়নি। সুতরাং আফগানিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সেটা তাদের জন্য কতটা নিরাপদ, সে এক রহস্যময় প্রশ্ন বটে।
পাঁচ. পাকিস্তান ভাবছে, তালেবান দাঁড়িয়ে যাবে চিরশত্রু ভারতের বিরুদ্ধে। আর তাতে লাভ হবে পাকিস্তানের। সেই কবে থেকে তালেবান তাদের বিভিন্ন কাজে সমর্থন পেয়ে এসেছে পাকিস্তানের।
পাকিস্তানের সীমানাতেই তো হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তালেবান। তাই ক্ষমতায় তালেবান এলে তাতে পাকিস্তান কৌশলগতভাবেই থাকবে নিরাপদ জায়গায়।
কিন্তু পাকিস্তানের সে গুড়ে বালি দিয়ে দিতে পারে স্বয়ং তালেবান। এ কথা তো গোপন নয় যে ব্রিটিশদের তৈরি করা ডুরান্ড লাইন কখনো মানেনি তালেবান। এর অর্থ হচ্ছে, পাকিস্তানে যে পশতুন জনগোষ্ঠী আছে, ম্যাপে তাদের পাকিস্তানের অংশ বলে স্বীকার করে না তালেবান। ডুরান্ড লাইন কেন মানছে না তালেবান? এর কারণ হচ্ছে, তাদের হয়তো ইচ্ছা, পাকিস্তানের যেখানে পশতুন অঞ্চল আছে, সেটাও চলে আসবে এক তালেবান মানচিত্রের আওতায়। সেটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তানের মাথা ঘোরা শুরু হতে পারে অচিরেই।
ছয়. এবার অন্য এক হিসাব-নিকাশের আলোচনা হোক। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি দেশ আফগানিস্তানের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই তালেবানের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক কী হতে পারে, তা নিয়ে ভাবছে। তবে এ কথা সত্যি, আফগানিস্তান থেকে আরেকটি অভিবাসনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ইউরোপ। এ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সামলানোর মুরোদ ইউরোপের নেই। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলকান থেকে চীন পর্যন্ত যে তুর্কি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন, সেখানে তালেবানই হয়ে উঠতে পারে মূল অনুঘটক। কিন্তু তার আগে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, তালেবান কি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে?
আন্তর্জাতিক ডকট্রিন তো বলছেই গৃহযুদ্ধ বা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। স্বীকৃতি পেতে হলে আসতে হবে স্বীকৃত কোনো পথে, সেটা ভোটের মাধ্যমে (এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ জরুরি), অথবা গণভোটের মাধ্যমে।
তালেবান অন্যান্য জোটের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে সত্যিই কোনো কার্যকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে কি না, তা নিয়ে এরই মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কৌশলগত অবস্থান, খনিজ সাম্রাজ্য, মাদক সাম্রাজ্য—এই সব মিলেমিশে আফগান সংকটটি যে শুধু কারও বিরুদ্ধে কারও জয়-পরাজয়ে নির্দিষ্ট হচ্ছে না, সে কথাই ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হচ্ছে। আফগান মাঠটি নতুন একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছে। এতে খুশি হওয়ার কিছু নেই।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। অনেকের কাছে এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ওপর আস্থা রেখেছেন। নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল এবং নির্বাচনের পর ভোট গণনার সময় সারা রাত বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার, শুধু আমার নয় বরং অনেকেরই। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, পাশ্চাত্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, তখন প্রথম দিন বড় বোনের কাছ থেকে শাড়ি এনে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলাম। সেই দিনের শিহরণ, অনুভূতি এখনো শরীর-মনে দোলা দেয়।
৫ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের পরে যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। প্রস্তাব এসেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে। সমালোচনার মুখে সেই পথ থেকে সরে এসেছে সরকার। বাতিল করা হয়েছে গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। বহু দুঃসংবাদের মধ্যে এটি একটি সুসংবাদ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ধরনের এই কেনাকাটার বিষয়টি
৫ ঘণ্টা আগে
জাতীয় প্রেসক্লাবে ৭ সেপ্টেম্বর গণশক্তি আয়োজন করে ‘জুলাই সনদ ও নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা। সেই সভায় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না যে প্রশ্নটি করেছেন, তা কোটি টাকার সঙ্গে তুলনা করাই যায়। তাঁর সহজ জিজ্ঞাসা—‘ভোটের দিন যাঁর যেখানে শক্তি আছে, তাঁর যদি মনে হয় জিততে পারবেন না...
১ দিন আগে