রাজীব কুমার সাহা
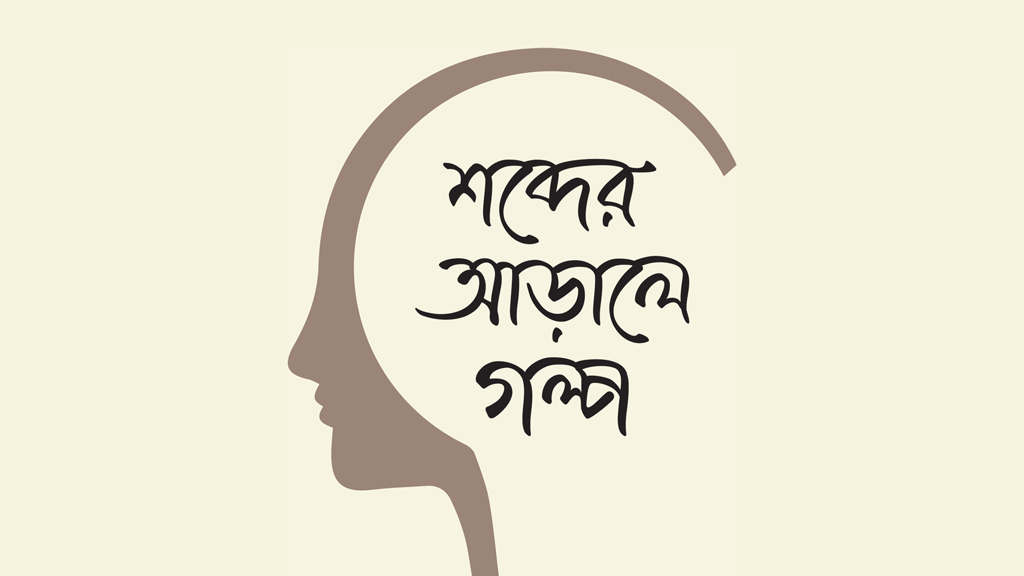
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু হয়ে উঠল? কীভাবে শিঙাড়া আমাদের জলখাবারের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠল? পাশাপাশি এ-ও জানা দরকার, আকৃতিগত দিক থেকে এটি তিনটি কোনাবিশিষ্ট কেন?
শিঙাড়া বাংলা শব্দ। এটি তৎসম শব্দ ‘শৃঙ্গাটক’ থেকে বাংলায় এসেছে। এটি বিশেষ্য পদ। অভিধানে শিঙাড়া শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। দুটি অর্থই ভোজ্য অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য। শিঙাড়া বলতে আমরা বুঝি মসলা মেশানো আলু, কপি প্রভৃতির পুর দিয়ে ময়দার তৈরি তেকোনা তেলে ভাজা খাদ্যবস্তুবিশেষ। আর অপর অর্থটি হলো পানিফল অর্থাৎ তিন দিকে তিনটি কাঁটাযুক্ত জলজ ফলবিশেষকে আমরা শিঙাড়া নামে চিনি। এর কাঁটাগুলো দেখতে শিংয়ের মতো। শিঙাড়ার সঙ্গে এই ফলের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শিঙাড়াকে ‘শৃঙ্গাটক’ বলে উল্লেখ করা হতো। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘পানীফলের মত ময়দার ঘৃত পক্ক খাদ্য বিশেষ।’ আর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙ্গলা ভাষার অভিধান’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘শৃঙ্গটিক ফল’। আবার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ‘ঘৃতে ভাজা পানিফলাকৃতি খাদ্য বিশেষ’।
দশম শতকের ইরানি ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বেহাগি তাঁর ‘তারিখ-ই-বেহাগি’ গ্রন্থে প্রথম ‘সাম্বুসাক’ খাবারটির কথা উল্লেখ করেন। ১৩ শতকে আমির খসরুর লেখায় পাওয়া যায়, দিল্লির অভিজাত মুসলিমদের খাদ্যতালিকায় খুব প্রিয় খাবার হিসেবে যে ‘সামোসা’র উল্লেখ করা হয়েছে তা তৈরি হতো মাংস ও পেঁয়াজ দিয়ে ঘিয়ে ভেজে। ইবনে বতুতার লেখা থেকে জানা যায়, তখন মাংসের কিমা অ্যামন্ড, আখরোট, পেস্তা বাটা, পেঁয়াজ ও মসলা সহযোগে কষে ময়দার মোড়কে পুরে দেওয়া হতো। তিনি অবশ্য খাবারটির নাম লিখেছিলেন ‘সামসুক’। তাঁর বর্ণনা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজসভায় ‘সামসুক’ পরিবেশনের বিষয়টি জানা যায়। ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে একইভাবে তৈরি করা খাদ্যটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘সানবুসা’। ষোল শতকের ভারতীয় রন্ধনপুস্তক ‘নিমতনামা-ই-নাসিরুদ্দিন-শাহি’-তেও ‘সানবুসা’ পরিবেশনের সুনিপুণ চিত্র রয়েছে। ‘সাম্বুসাক’ বা ‘সামোসা’ বা ‘সামসুক’ বা ‘সানবুসা’-ই হলো সোজা বাংলায় আমরা যাকে সমুচা নামে চিনি। উল্লিখিত নামগুলো থেকেই স্থান এবং সময় ভেদে সমুচা বা বাঙালির শিঙাড়ার চল যার অন্যতম কারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য। পাশাপাশি উল্লেখ্য যে, পর্তুগিজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আলু চাষ শুরু করে আনুমানিক ১৭ শতকে। ধারণা করা হয়, সে সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলের নিরামিষাশী মানুষ মাংসের পুরের বদলে আলু দিয়ে সমুচা বানানো শুরু করে। এতে সমুচার আসল আকার কিছুটা বদলে গিয়ে পানিফলের রূপ নেয়। সেই থেকে আলুর পুর ভরা সমুচা হয়ে যায় শিঙাড়া।
শিঙাড়ার জন্ম নিয়ে প্রচলিত আরেকটি কাহিনি হলো, ১৭৬৬ সালে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সে সময় রাজ-হালুইকর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন কলিঙ্গ তথা বর্তমান ওড়িষ্যা থেকে আগত গুণীনাথ হালুইকরের ষষ্ঠ পুত্র গিরিধারী হালুইকর। কথিত রয়েছে, তাঁর স্ত্রী ধরিত্রী দেবী শিঙাড়ার আদি রন্ধনশিল্পী। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে একটি গল্প। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ-হালুইকরের বানানো লুচি খেয়ে বেশ ক্ষিপ্ত হলেন। কারণ লুচি নেতানো, আহারে তিনি এর কোনো স্বাদ পেলেন না। নির্দেশ দিলেন হালুইকরকে রাজ্য ছাড়ার। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এই সময় একটা বুদ্ধি করলেন। রাজদরবারে গিয়ে বললেন, সুযোগ পেলে সে এমন লুচি-তরকারি রান্না করে খাওয়াতে পারবেন যা অনেক সময়ব্যাপী গরম থাকবে। এমনকি ভাজার সঙ্গে সঙ্গে খেলে জিভ পর্যন্ত পুড়ে যেতে পারে। এই ভেবেই তিনি তৈরি করলেন তিন পাটে ময়দার খোলস করে তার মধ্যে পুর ভরে ফুটন্ত তেলে ভাজা এই খাদ্যবস্তু। এই খাবার খেয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেষমেশ খুশি হয়ে হালুইকরের শাস্তি বাতিল করেন এবং ধরিত্রী দেবীকে মুক্তার মালা উপহার দেন। কথিত রয়েছে, এই থেকেই এমন ত্রিকোনাকৃতির শিঙাড়ার প্রচলন হয়।
সাম্প্রতিক সময়ে রুচিভেদে শিঙাড়ার বহুমুখী বিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাংসের শিঙাড়া, ফুলকপির শিঙাড়া, কলিজার শিঙাড়া, পনিরের শিঙাড়া, ক্ষীরের শিঙাড়া প্রভৃতি নানা স্বাদের শিঙাড়ার প্রচলন থাকলেও আলুর পুর দেওয়া শিঙাড়াই সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে শিঙাড়ার পুর কিংবা নাম যা-ই হোক না কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই শিঙ্গাড়ার আকার কিন্তু বর্তমানে এক রকমই—ত্রিকোনাকৃতি। আর তার পেটের মধ্যে ভরা থাকে সুস্বাদু পুর। ধারণা করা হয়, শিঙাড়ায় পুর ভরার সুবিধার জন্য এটিকে গোল বা লম্বা আকৃতির না করে তিন কোনাবিশিষ্ট করা হয়েছিল।
লেখক:–আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক
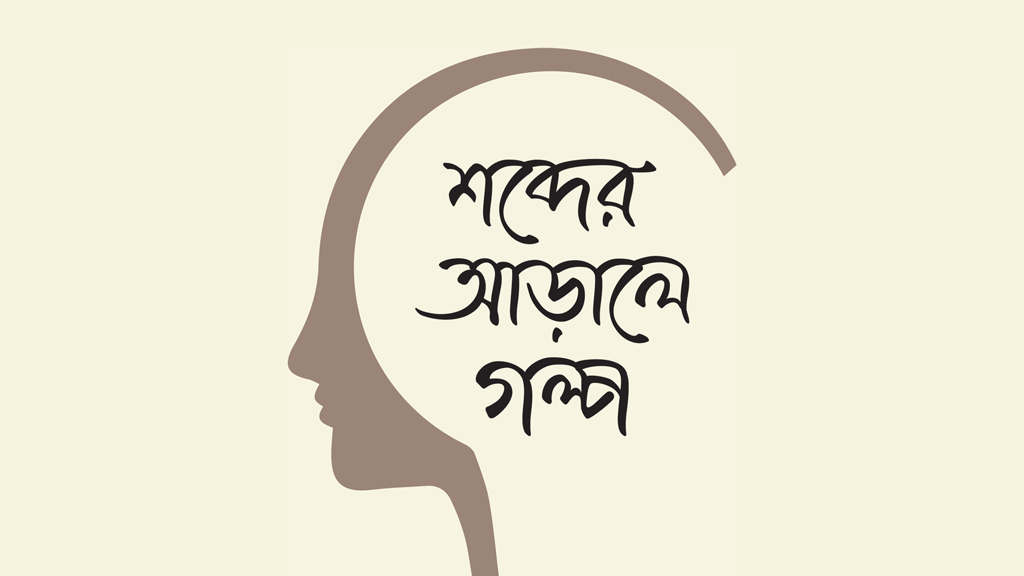
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু হয়ে উঠল? কীভাবে শিঙাড়া আমাদের জলখাবারের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠল? পাশাপাশি এ-ও জানা দরকার, আকৃতিগত দিক থেকে এটি তিনটি কোনাবিশিষ্ট কেন?
শিঙাড়া বাংলা শব্দ। এটি তৎসম শব্দ ‘শৃঙ্গাটক’ থেকে বাংলায় এসেছে। এটি বিশেষ্য পদ। অভিধানে শিঙাড়া শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। দুটি অর্থই ভোজ্য অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য। শিঙাড়া বলতে আমরা বুঝি মসলা মেশানো আলু, কপি প্রভৃতির পুর দিয়ে ময়দার তৈরি তেকোনা তেলে ভাজা খাদ্যবস্তুবিশেষ। আর অপর অর্থটি হলো পানিফল অর্থাৎ তিন দিকে তিনটি কাঁটাযুক্ত জলজ ফলবিশেষকে আমরা শিঙাড়া নামে চিনি। এর কাঁটাগুলো দেখতে শিংয়ের মতো। শিঙাড়ার সঙ্গে এই ফলের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শিঙাড়াকে ‘শৃঙ্গাটক’ বলে উল্লেখ করা হতো। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘পানীফলের মত ময়দার ঘৃত পক্ক খাদ্য বিশেষ।’ আর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙ্গলা ভাষার অভিধান’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘শৃঙ্গটিক ফল’। আবার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ‘ঘৃতে ভাজা পানিফলাকৃতি খাদ্য বিশেষ’।
দশম শতকের ইরানি ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বেহাগি তাঁর ‘তারিখ-ই-বেহাগি’ গ্রন্থে প্রথম ‘সাম্বুসাক’ খাবারটির কথা উল্লেখ করেন। ১৩ শতকে আমির খসরুর লেখায় পাওয়া যায়, দিল্লির অভিজাত মুসলিমদের খাদ্যতালিকায় খুব প্রিয় খাবার হিসেবে যে ‘সামোসা’র উল্লেখ করা হয়েছে তা তৈরি হতো মাংস ও পেঁয়াজ দিয়ে ঘিয়ে ভেজে। ইবনে বতুতার লেখা থেকে জানা যায়, তখন মাংসের কিমা অ্যামন্ড, আখরোট, পেস্তা বাটা, পেঁয়াজ ও মসলা সহযোগে কষে ময়দার মোড়কে পুরে দেওয়া হতো। তিনি অবশ্য খাবারটির নাম লিখেছিলেন ‘সামসুক’। তাঁর বর্ণনা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজসভায় ‘সামসুক’ পরিবেশনের বিষয়টি জানা যায়। ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে একইভাবে তৈরি করা খাদ্যটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘সানবুসা’। ষোল শতকের ভারতীয় রন্ধনপুস্তক ‘নিমতনামা-ই-নাসিরুদ্দিন-শাহি’-তেও ‘সানবুসা’ পরিবেশনের সুনিপুণ চিত্র রয়েছে। ‘সাম্বুসাক’ বা ‘সামোসা’ বা ‘সামসুক’ বা ‘সানবুসা’-ই হলো সোজা বাংলায় আমরা যাকে সমুচা নামে চিনি। উল্লিখিত নামগুলো থেকেই স্থান এবং সময় ভেদে সমুচা বা বাঙালির শিঙাড়ার চল যার অন্যতম কারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য। পাশাপাশি উল্লেখ্য যে, পর্তুগিজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আলু চাষ শুরু করে আনুমানিক ১৭ শতকে। ধারণা করা হয়, সে সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলের নিরামিষাশী মানুষ মাংসের পুরের বদলে আলু দিয়ে সমুচা বানানো শুরু করে। এতে সমুচার আসল আকার কিছুটা বদলে গিয়ে পানিফলের রূপ নেয়। সেই থেকে আলুর পুর ভরা সমুচা হয়ে যায় শিঙাড়া।
শিঙাড়ার জন্ম নিয়ে প্রচলিত আরেকটি কাহিনি হলো, ১৭৬৬ সালে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সে সময় রাজ-হালুইকর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন কলিঙ্গ তথা বর্তমান ওড়িষ্যা থেকে আগত গুণীনাথ হালুইকরের ষষ্ঠ পুত্র গিরিধারী হালুইকর। কথিত রয়েছে, তাঁর স্ত্রী ধরিত্রী দেবী শিঙাড়ার আদি রন্ধনশিল্পী। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে একটি গল্প। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ-হালুইকরের বানানো লুচি খেয়ে বেশ ক্ষিপ্ত হলেন। কারণ লুচি নেতানো, আহারে তিনি এর কোনো স্বাদ পেলেন না। নির্দেশ দিলেন হালুইকরকে রাজ্য ছাড়ার। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এই সময় একটা বুদ্ধি করলেন। রাজদরবারে গিয়ে বললেন, সুযোগ পেলে সে এমন লুচি-তরকারি রান্না করে খাওয়াতে পারবেন যা অনেক সময়ব্যাপী গরম থাকবে। এমনকি ভাজার সঙ্গে সঙ্গে খেলে জিভ পর্যন্ত পুড়ে যেতে পারে। এই ভেবেই তিনি তৈরি করলেন তিন পাটে ময়দার খোলস করে তার মধ্যে পুর ভরে ফুটন্ত তেলে ভাজা এই খাদ্যবস্তু। এই খাবার খেয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেষমেশ খুশি হয়ে হালুইকরের শাস্তি বাতিল করেন এবং ধরিত্রী দেবীকে মুক্তার মালা উপহার দেন। কথিত রয়েছে, এই থেকেই এমন ত্রিকোনাকৃতির শিঙাড়ার প্রচলন হয়।
সাম্প্রতিক সময়ে রুচিভেদে শিঙাড়ার বহুমুখী বিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাংসের শিঙাড়া, ফুলকপির শিঙাড়া, কলিজার শিঙাড়া, পনিরের শিঙাড়া, ক্ষীরের শিঙাড়া প্রভৃতি নানা স্বাদের শিঙাড়ার প্রচলন থাকলেও আলুর পুর দেওয়া শিঙাড়াই সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে শিঙাড়ার পুর কিংবা নাম যা-ই হোক না কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই শিঙ্গাড়ার আকার কিন্তু বর্তমানে এক রকমই—ত্রিকোনাকৃতি। আর তার পেটের মধ্যে ভরা থাকে সুস্বাদু পুর। ধারণা করা হয়, শিঙাড়ায় পুর ভরার সুবিধার জন্য এটিকে গোল বা লম্বা আকৃতির না করে তিন কোনাবিশিষ্ট করা হয়েছিল।
লেখক:–আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক
রাজীব কুমার সাহা
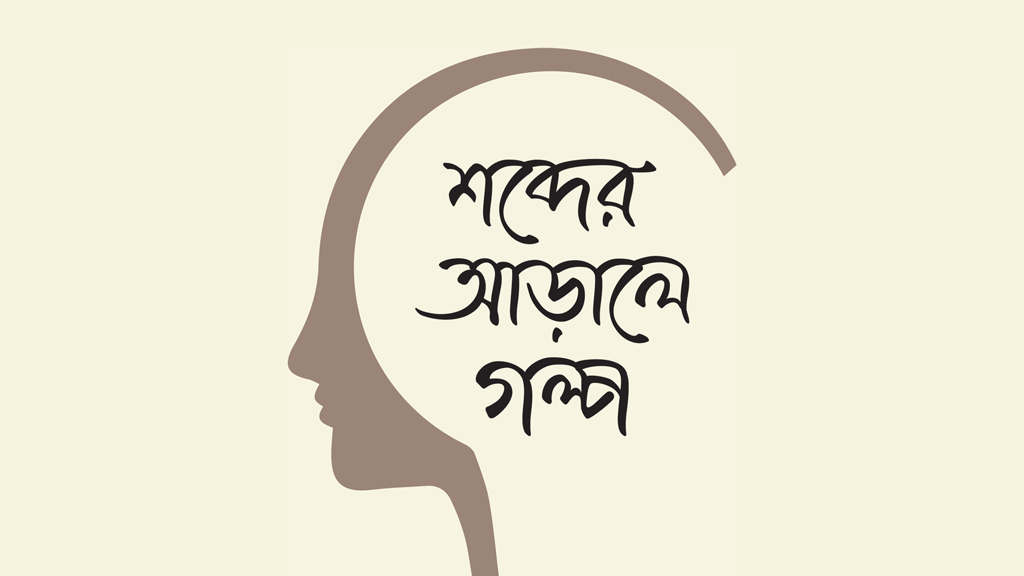
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু হয়ে উঠল? কীভাবে শিঙাড়া আমাদের জলখাবারের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠল? পাশাপাশি এ-ও জানা দরকার, আকৃতিগত দিক থেকে এটি তিনটি কোনাবিশিষ্ট কেন?
শিঙাড়া বাংলা শব্দ। এটি তৎসম শব্দ ‘শৃঙ্গাটক’ থেকে বাংলায় এসেছে। এটি বিশেষ্য পদ। অভিধানে শিঙাড়া শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। দুটি অর্থই ভোজ্য অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য। শিঙাড়া বলতে আমরা বুঝি মসলা মেশানো আলু, কপি প্রভৃতির পুর দিয়ে ময়দার তৈরি তেকোনা তেলে ভাজা খাদ্যবস্তুবিশেষ। আর অপর অর্থটি হলো পানিফল অর্থাৎ তিন দিকে তিনটি কাঁটাযুক্ত জলজ ফলবিশেষকে আমরা শিঙাড়া নামে চিনি। এর কাঁটাগুলো দেখতে শিংয়ের মতো। শিঙাড়ার সঙ্গে এই ফলের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শিঙাড়াকে ‘শৃঙ্গাটক’ বলে উল্লেখ করা হতো। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘পানীফলের মত ময়দার ঘৃত পক্ক খাদ্য বিশেষ।’ আর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙ্গলা ভাষার অভিধান’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘শৃঙ্গটিক ফল’। আবার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ‘ঘৃতে ভাজা পানিফলাকৃতি খাদ্য বিশেষ’।
দশম শতকের ইরানি ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বেহাগি তাঁর ‘তারিখ-ই-বেহাগি’ গ্রন্থে প্রথম ‘সাম্বুসাক’ খাবারটির কথা উল্লেখ করেন। ১৩ শতকে আমির খসরুর লেখায় পাওয়া যায়, দিল্লির অভিজাত মুসলিমদের খাদ্যতালিকায় খুব প্রিয় খাবার হিসেবে যে ‘সামোসা’র উল্লেখ করা হয়েছে তা তৈরি হতো মাংস ও পেঁয়াজ দিয়ে ঘিয়ে ভেজে। ইবনে বতুতার লেখা থেকে জানা যায়, তখন মাংসের কিমা অ্যামন্ড, আখরোট, পেস্তা বাটা, পেঁয়াজ ও মসলা সহযোগে কষে ময়দার মোড়কে পুরে দেওয়া হতো। তিনি অবশ্য খাবারটির নাম লিখেছিলেন ‘সামসুক’। তাঁর বর্ণনা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজসভায় ‘সামসুক’ পরিবেশনের বিষয়টি জানা যায়। ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে একইভাবে তৈরি করা খাদ্যটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘সানবুসা’। ষোল শতকের ভারতীয় রন্ধনপুস্তক ‘নিমতনামা-ই-নাসিরুদ্দিন-শাহি’-তেও ‘সানবুসা’ পরিবেশনের সুনিপুণ চিত্র রয়েছে। ‘সাম্বুসাক’ বা ‘সামোসা’ বা ‘সামসুক’ বা ‘সানবুসা’-ই হলো সোজা বাংলায় আমরা যাকে সমুচা নামে চিনি। উল্লিখিত নামগুলো থেকেই স্থান এবং সময় ভেদে সমুচা বা বাঙালির শিঙাড়ার চল যার অন্যতম কারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য। পাশাপাশি উল্লেখ্য যে, পর্তুগিজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আলু চাষ শুরু করে আনুমানিক ১৭ শতকে। ধারণা করা হয়, সে সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলের নিরামিষাশী মানুষ মাংসের পুরের বদলে আলু দিয়ে সমুচা বানানো শুরু করে। এতে সমুচার আসল আকার কিছুটা বদলে গিয়ে পানিফলের রূপ নেয়। সেই থেকে আলুর পুর ভরা সমুচা হয়ে যায় শিঙাড়া।
শিঙাড়ার জন্ম নিয়ে প্রচলিত আরেকটি কাহিনি হলো, ১৭৬৬ সালে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সে সময় রাজ-হালুইকর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন কলিঙ্গ তথা বর্তমান ওড়িষ্যা থেকে আগত গুণীনাথ হালুইকরের ষষ্ঠ পুত্র গিরিধারী হালুইকর। কথিত রয়েছে, তাঁর স্ত্রী ধরিত্রী দেবী শিঙাড়ার আদি রন্ধনশিল্পী। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে একটি গল্প। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ-হালুইকরের বানানো লুচি খেয়ে বেশ ক্ষিপ্ত হলেন। কারণ লুচি নেতানো, আহারে তিনি এর কোনো স্বাদ পেলেন না। নির্দেশ দিলেন হালুইকরকে রাজ্য ছাড়ার। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এই সময় একটা বুদ্ধি করলেন। রাজদরবারে গিয়ে বললেন, সুযোগ পেলে সে এমন লুচি-তরকারি রান্না করে খাওয়াতে পারবেন যা অনেক সময়ব্যাপী গরম থাকবে। এমনকি ভাজার সঙ্গে সঙ্গে খেলে জিভ পর্যন্ত পুড়ে যেতে পারে। এই ভেবেই তিনি তৈরি করলেন তিন পাটে ময়দার খোলস করে তার মধ্যে পুর ভরে ফুটন্ত তেলে ভাজা এই খাদ্যবস্তু। এই খাবার খেয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেষমেশ খুশি হয়ে হালুইকরের শাস্তি বাতিল করেন এবং ধরিত্রী দেবীকে মুক্তার মালা উপহার দেন। কথিত রয়েছে, এই থেকেই এমন ত্রিকোনাকৃতির শিঙাড়ার প্রচলন হয়।
সাম্প্রতিক সময়ে রুচিভেদে শিঙাড়ার বহুমুখী বিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাংসের শিঙাড়া, ফুলকপির শিঙাড়া, কলিজার শিঙাড়া, পনিরের শিঙাড়া, ক্ষীরের শিঙাড়া প্রভৃতি নানা স্বাদের শিঙাড়ার প্রচলন থাকলেও আলুর পুর দেওয়া শিঙাড়াই সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে শিঙাড়ার পুর কিংবা নাম যা-ই হোক না কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই শিঙ্গাড়ার আকার কিন্তু বর্তমানে এক রকমই—ত্রিকোনাকৃতি। আর তার পেটের মধ্যে ভরা থাকে সুস্বাদু পুর। ধারণা করা হয়, শিঙাড়ায় পুর ভরার সুবিধার জন্য এটিকে গোল বা লম্বা আকৃতির না করে তিন কোনাবিশিষ্ট করা হয়েছিল।
লেখক:–আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক
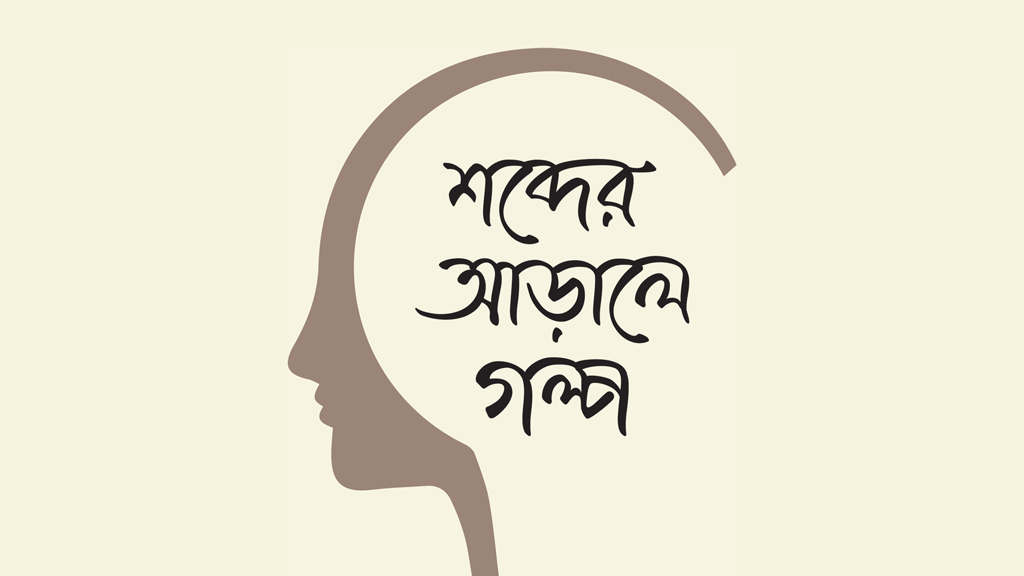
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু হয়ে উঠল? কীভাবে শিঙাড়া আমাদের জলখাবারের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠল? পাশাপাশি এ-ও জানা দরকার, আকৃতিগত দিক থেকে এটি তিনটি কোনাবিশিষ্ট কেন?
শিঙাড়া বাংলা শব্দ। এটি তৎসম শব্দ ‘শৃঙ্গাটক’ থেকে বাংলায় এসেছে। এটি বিশেষ্য পদ। অভিধানে শিঙাড়া শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। দুটি অর্থই ভোজ্য অর্থাৎ খাওয়ার যোগ্য। শিঙাড়া বলতে আমরা বুঝি মসলা মেশানো আলু, কপি প্রভৃতির পুর দিয়ে ময়দার তৈরি তেকোনা তেলে ভাজা খাদ্যবস্তুবিশেষ। আর অপর অর্থটি হলো পানিফল অর্থাৎ তিন দিকে তিনটি কাঁটাযুক্ত জলজ ফলবিশেষকে আমরা শিঙাড়া নামে চিনি। এর কাঁটাগুলো দেখতে শিংয়ের মতো। শিঙাড়ার সঙ্গে এই ফলের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শিঙাড়াকে ‘শৃঙ্গাটক’ বলে উল্লেখ করা হতো। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘পানীফলের মত ময়দার ঘৃত পক্ক খাদ্য বিশেষ।’ আর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ‘বাঙ্গলা ভাষার অভিধান’-এ শিঙাড়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে ‘শৃঙ্গটিক ফল’। আবার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ‘ঘৃতে ভাজা পানিফলাকৃতি খাদ্য বিশেষ’।
দশম শতকের ইরানি ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বেহাগি তাঁর ‘তারিখ-ই-বেহাগি’ গ্রন্থে প্রথম ‘সাম্বুসাক’ খাবারটির কথা উল্লেখ করেন। ১৩ শতকে আমির খসরুর লেখায় পাওয়া যায়, দিল্লির অভিজাত মুসলিমদের খাদ্যতালিকায় খুব প্রিয় খাবার হিসেবে যে ‘সামোসা’র উল্লেখ করা হয়েছে তা তৈরি হতো মাংস ও পেঁয়াজ দিয়ে ঘিয়ে ভেজে। ইবনে বতুতার লেখা থেকে জানা যায়, তখন মাংসের কিমা অ্যামন্ড, আখরোট, পেস্তা বাটা, পেঁয়াজ ও মসলা সহযোগে কষে ময়দার মোড়কে পুরে দেওয়া হতো। তিনি অবশ্য খাবারটির নাম লিখেছিলেন ‘সামসুক’। তাঁর বর্ণনা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজসভায় ‘সামসুক’ পরিবেশনের বিষয়টি জানা যায়। ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে একইভাবে তৈরি করা খাদ্যটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘সানবুসা’। ষোল শতকের ভারতীয় রন্ধনপুস্তক ‘নিমতনামা-ই-নাসিরুদ্দিন-শাহি’-তেও ‘সানবুসা’ পরিবেশনের সুনিপুণ চিত্র রয়েছে। ‘সাম্বুসাক’ বা ‘সামোসা’ বা ‘সামসুক’ বা ‘সানবুসা’-ই হলো সোজা বাংলায় আমরা যাকে সমুচা নামে চিনি। উল্লিখিত নামগুলো থেকেই স্থান এবং সময় ভেদে সমুচা বা বাঙালির শিঙাড়ার চল যার অন্যতম কারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য। পাশাপাশি উল্লেখ্য যে, পর্তুগিজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আলু চাষ শুরু করে আনুমানিক ১৭ শতকে। ধারণা করা হয়, সে সময় ভারতের পশ্চিম উপকূলের নিরামিষাশী মানুষ মাংসের পুরের বদলে আলু দিয়ে সমুচা বানানো শুরু করে। এতে সমুচার আসল আকার কিছুটা বদলে গিয়ে পানিফলের রূপ নেয়। সেই থেকে আলুর পুর ভরা সমুচা হয়ে যায় শিঙাড়া।
শিঙাড়ার জন্ম নিয়ে প্রচলিত আরেকটি কাহিনি হলো, ১৭৬৬ সালে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সে সময় রাজ-হালুইকর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন কলিঙ্গ তথা বর্তমান ওড়িষ্যা থেকে আগত গুণীনাথ হালুইকরের ষষ্ঠ পুত্র গিরিধারী হালুইকর। কথিত রয়েছে, তাঁর স্ত্রী ধরিত্রী দেবী শিঙাড়ার আদি রন্ধনশিল্পী। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে একটি গল্প। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ-হালুইকরের বানানো লুচি খেয়ে বেশ ক্ষিপ্ত হলেন। কারণ লুচি নেতানো, আহারে তিনি এর কোনো স্বাদ পেলেন না। নির্দেশ দিলেন হালুইকরকে রাজ্য ছাড়ার। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এই সময় একটা বুদ্ধি করলেন। রাজদরবারে গিয়ে বললেন, সুযোগ পেলে সে এমন লুচি-তরকারি রান্না করে খাওয়াতে পারবেন যা অনেক সময়ব্যাপী গরম থাকবে। এমনকি ভাজার সঙ্গে সঙ্গে খেলে জিভ পর্যন্ত পুড়ে যেতে পারে। এই ভেবেই তিনি তৈরি করলেন তিন পাটে ময়দার খোলস করে তার মধ্যে পুর ভরে ফুটন্ত তেলে ভাজা এই খাদ্যবস্তু। এই খাবার খেয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেষমেশ খুশি হয়ে হালুইকরের শাস্তি বাতিল করেন এবং ধরিত্রী দেবীকে মুক্তার মালা উপহার দেন। কথিত রয়েছে, এই থেকেই এমন ত্রিকোনাকৃতির শিঙাড়ার প্রচলন হয়।
সাম্প্রতিক সময়ে রুচিভেদে শিঙাড়ার বহুমুখী বিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাংসের শিঙাড়া, ফুলকপির শিঙাড়া, কলিজার শিঙাড়া, পনিরের শিঙাড়া, ক্ষীরের শিঙাড়া প্রভৃতি নানা স্বাদের শিঙাড়ার প্রচলন থাকলেও আলুর পুর দেওয়া শিঙাড়াই সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে শিঙাড়ার পুর কিংবা নাম যা-ই হোক না কেন, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই শিঙ্গাড়ার আকার কিন্তু বর্তমানে এক রকমই—ত্রিকোনাকৃতি। আর তার পেটের মধ্যে ভরা থাকে সুস্বাদু পুর। ধারণা করা হয়, শিঙাড়ায় পুর ভরার সুবিধার জন্য এটিকে গোল বা লম্বা আকৃতির না করে তিন কোনাবিশিষ্ট করা হয়েছিল।
লেখক:–আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক

৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো
২ ঘণ্টা আগে
এ বছরের জুন মাসে যখন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মনোনয়নের জন্য ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি হলো, তখন অন্য প্রার্থী নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দিয়েছিলেন মামদানি। প্রাইমারির সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম।
২ ঘণ্টা আগে
সরকারের একজন দায়িত্বরত ব্যক্তি নাকি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ইতিহাসের সর্বোত্তম নির্বাচন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটা পোস্ট বেশ ঘোরাঘুরি করছে। চোখে লাগল কথাটা বেশ। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? হলে তো ভালোই। জনগণ তো যুগ যুগ ধরে সেটাই চেয়ে এসেছে।
২ ঘণ্টা আগে
সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।
১ দিন আগেসম্পাদকীয়

পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেলও ঋত্বিককে নিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করেছে সংবাদ, ফিচার, প্রতিবেদন। কিন্তু ৫ নভেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে চোখ গেলে দেখা যায়, রাজশাহীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঋত্বিকের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িটিতেই হয়েছে ঋত্বিক স্মরণ। সেই যে গত বছরের ৬ ও ৭ আগস্ট গোপনে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো, তার পর থেকে তা ধ্বংসস্তূপ হিসেবেই টিকে আছে!
অবাক কাণ্ড, ঋত্বিকের বাড়ি লন্ডভন্ড করে দেওয়ার এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু ঋত্বিকের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো মহলের মাথাব্যথা আছে কি না, সেটাও বোঝার কোনো উপায় নেই। কোন উল্লাসের সঙ্গী হয়ে ঋত্বিকের বাড়ি ভেঙেছিল দুর্বৃত্তের দল, সে উত্তর কেউ দেয়নি। ঋত্বিক যে আমাদের সংস্কৃতি-সাধনার একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ, সে কথা ভুলে গেলে কোন পরিচয়ে পরিচিত হবে আমাদের সংস্কৃতি?
রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক রাজনৈতিক সরকারগুলোও কি এই প্রশ্নগুলোর ঠিক মূল্যায়ন করে? ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যতটা সজাগ থাকতে হয়, সেই সচেতনতা আমাদের আছে কি? রাজশাহীতে ঋত্বিকের বাড়ি বছর পেরিয়েও ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে কেন? আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে, এ বছরের জুন মাসেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শাহজাদপুরের কাছারিবাড়িতে হামলা করেছিল একদল আত্মবিস্মৃত দুর্বৃত্তের দল। এসব কিসের ইঙ্গিত, তা বোঝার দরকার আছে।
ঋত্বিককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁর স্মৃতি পুনরুদ্ধার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রগুলোর ডিজিটাল সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রকাশ খুবই জরুরি। রাজশাহীতে ধ্বংসস্তূপ থেকেই ফিনিক্স পাখির মতো জন্ম নিক ঋত্বিক স্মৃতি জাদুঘর। সেই জাদুঘরে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত জিনিস ও চিঠিপত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। পাশাপাশি যাদের বর্বরোচিত হামলায় ধ্বংস হয়েছে ঋত্বিকের বাড়ি, তাদের দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করার জন্য কঠোর হোক সরকার। এ জন্য শুধু সরকার নয়, সচেতন সংস্কৃতিসেবীদেরও সোচ্চার হওয়া দরকার। সমাজের সব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নইলে সত্যিই একদিন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি বলে কিছুই থাকবে না। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করা না হলে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাব।
ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে রাজশাহীর মিয়াপাড়ার ঋত্বিকের পৈতৃক বাড়িতে ঐতিহ্য অনুযায়ী এ বছরও চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ২০০৯ সাল থেকেই ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি নিয়মিতভাবে এই চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালন করে আসছে। আশা করব, ঋত্বিক যেন কারও মতলবি দুরভিসন্ধির কারণে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যান। শুধু ঋত্বিক নন, আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অর্জন সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। নইলে এই লজ্জা আমাদের ঘুচবে না কখনো।

পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেলও ঋত্বিককে নিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করেছে সংবাদ, ফিচার, প্রতিবেদন। কিন্তু ৫ নভেম্বর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে চোখ গেলে দেখা যায়, রাজশাহীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঋত্বিকের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িটিতেই হয়েছে ঋত্বিক স্মরণ। সেই যে গত বছরের ৬ ও ৭ আগস্ট গোপনে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো, তার পর থেকে তা ধ্বংসস্তূপ হিসেবেই টিকে আছে!
অবাক কাণ্ড, ঋত্বিকের বাড়ি লন্ডভন্ড করে দেওয়ার এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু ঋত্বিকের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো মহলের মাথাব্যথা আছে কি না, সেটাও বোঝার কোনো উপায় নেই। কোন উল্লাসের সঙ্গী হয়ে ঋত্বিকের বাড়ি ভেঙেছিল দুর্বৃত্তের দল, সে উত্তর কেউ দেয়নি। ঋত্বিক যে আমাদের সংস্কৃতি-সাধনার একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ, সে কথা ভুলে গেলে কোন পরিচয়ে পরিচিত হবে আমাদের সংস্কৃতি?
রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক রাজনৈতিক সরকারগুলোও কি এই প্রশ্নগুলোর ঠিক মূল্যায়ন করে? ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যতটা সজাগ থাকতে হয়, সেই সচেতনতা আমাদের আছে কি? রাজশাহীতে ঋত্বিকের বাড়ি বছর পেরিয়েও ধ্বংসস্তূপ হয়ে থাকবে কেন? আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে, এ বছরের জুন মাসেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শাহজাদপুরের কাছারিবাড়িতে হামলা করেছিল একদল আত্মবিস্মৃত দুর্বৃত্তের দল। এসব কিসের ইঙ্গিত, তা বোঝার দরকার আছে।
ঋত্বিককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁর স্মৃতি পুনরুদ্ধার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর তৈরি চলচ্চিত্রগুলোর ডিজিটাল সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রকাশ খুবই জরুরি। রাজশাহীতে ধ্বংসস্তূপ থেকেই ফিনিক্স পাখির মতো জন্ম নিক ঋত্বিক স্মৃতি জাদুঘর। সেই জাদুঘরে ঋত্বিকের চলচ্চিত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত জিনিস ও চিঠিপত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। পাশাপাশি যাদের বর্বরোচিত হামলায় ধ্বংস হয়েছে ঋত্বিকের বাড়ি, তাদের দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করার জন্য কঠোর হোক সরকার। এ জন্য শুধু সরকার নয়, সচেতন সংস্কৃতিসেবীদেরও সোচ্চার হওয়া দরকার। সমাজের সব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নইলে সত্যিই একদিন হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি বলে কিছুই থাকবে না। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করা না হলে বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় আমরা পিছিয়ে যাব।
ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে রাজশাহীর মিয়াপাড়ার ঋত্বিকের পৈতৃক বাড়িতে ঐতিহ্য অনুযায়ী এ বছরও চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ২০০৯ সাল থেকেই ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি নিয়মিতভাবে এই চলচ্চিত্রকারের জন্মবার্ষিকী পালন করে আসছে। আশা করব, ঋত্বিক যেন কারও মতলবি দুরভিসন্ধির কারণে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যান। শুধু ঋত্বিক নন, আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক অর্জন সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। নইলে এই লজ্জা আমাদের ঘুচবে না কখনো।
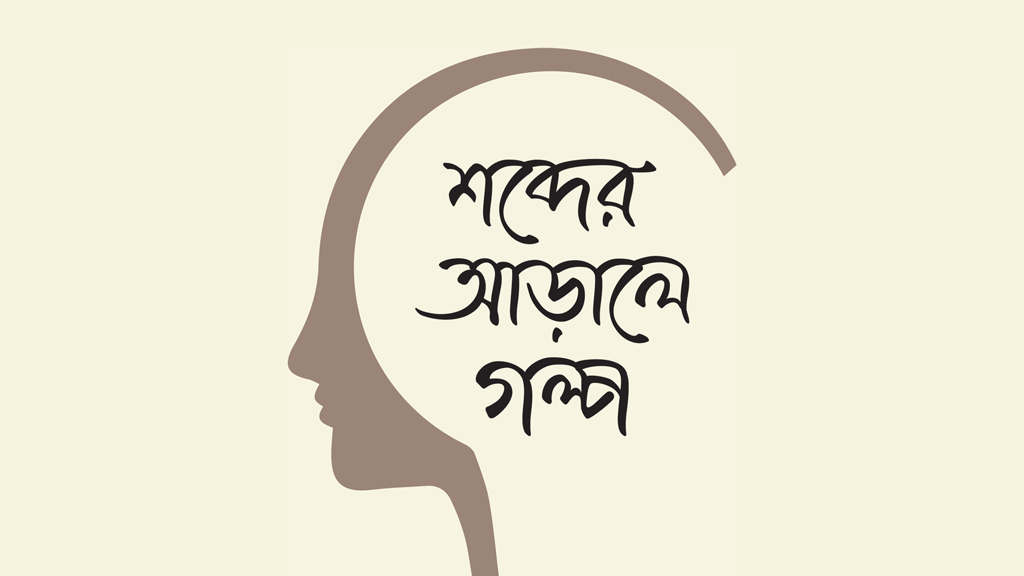
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু
১০ জুলাই ২০২৫
এ বছরের জুন মাসে যখন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মনোনয়নের জন্য ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি হলো, তখন অন্য প্রার্থী নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দিয়েছিলেন মামদানি। প্রাইমারির সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম।
২ ঘণ্টা আগে
সরকারের একজন দায়িত্বরত ব্যক্তি নাকি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ইতিহাসের সর্বোত্তম নির্বাচন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটা পোস্ট বেশ ঘোরাঘুরি করছে। চোখে লাগল কথাটা বেশ। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? হলে তো ভালোই। জনগণ তো যুগ যুগ ধরে সেটাই চেয়ে এসেছে।
২ ঘণ্টা আগে
সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।
১ দিন আগেজাহীদ রেজা নূর, উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি যে বিজয়ী হবেন, সে বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে রাজনীতিতে প্রায় নতুন একজন প্রার্থী
কীভাবে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, তা নিয়ে একটা বিশ্লেষণ হতেই পারে।
১. এ বছরের জুন মাসে যখন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মনোনয়নের জন্য ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি হলো, তখন অন্য প্রার্থী নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দিয়েছিলেন মামদানি। প্রাইমারির সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। আমাদের দেশে নির্বাচনী ডামাডোলে রাস্তাঘাট যেভাবে রোমাঞ্চিত হতে থাকে, সে রকম কিছুই সেখানে দেখিনি। বড়লোক কুমোর পারিবারিক ঐতিহ্য, তাঁর অগাধ অর্থ, ডেমোক্র্যাট নেতা হিসেবে তাঁর আভিজাত্য—কিছুই তাঁকে মামদানির সামনে দাঁড়াতে দেয়নি। নির্বাচনের আগে ও পরে মামদানিকে নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, ইতিমধ্যেই অনেকে তা জানেন। ফলে এখন সে বিষয়ে কিছু বললে তা পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে।
নিউইয়র্ক সিটির ১১১তম মেয়র নির্বাচনে কুমো দাঁড়িয়েছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। রিপাবলিকানদের প্রার্থী ছিলেন কার্টিস স্লিওয়া। কিন্তু মামদানির জনসমর্থনের কারণে তাঁরা দুজনই ভেসে গেছেন খড়কুটোর মতো। তাই এই সময় জোহরান মামদানির বিজয়ের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা জরুরি।
২ . মামদানির বিরাট বিজয়ের পাশাপাশি একই সময়ে ভার্জিনিয়ায় গভর্নর পদে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী এবিগেইল স্প্যানবার্গার জয়ী হয়েছেন। নিউ জার্সির গভর্নর পদে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মাইকি শেরিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বড় তিনটি নির্বাচনেই ডেমোক্র্যাটদের জয় হলো। এটাকে ট্রাম্প-নীতির পরাজয় হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই মামদানির বিজয়কে এই আলোকেই দেখতে হবে।
দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন তেলেসমাতি কারবার শুরু করেছেন যে খুব দ্রুত তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। জো বাইডেনের শাসনামলে অনেক মার্কিনই বাইডেনকে যোগ্য প্রেসিডেন্ট ভাবতে পারেননি। অভিবাসী মানুষদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ছিল বলে শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নাগরিকেরা ডেমোক্র্যাটদের ওপর বিরক্ত ছিল। বাইডেনের আমলে সমাজে নিম্নবিত্ত মানুষের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কারণেও অনেকে ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকেছিল। যুক্তরাষ্ট্র দেশটিই যে অভিবাসীদের দিয়ে গড়া এবং সে দেশ গড়তে গিয়ে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল—এই ইতিহাস বেমালুম ভুলে গিয়েছিল এই কট্টর শ্বেতাঙ্গরা। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পেছনে এটা একটি বড় কারণ। তবে আফ্রিকান ও এশিয়ান বংশোদ্ভূত মার্কিনদের একটা বড় অংশও ট্রাম্পের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। আরও অনেক কারণ আছে নিশ্চয়। যেমন এখন পর্যন্ত মার্কিনরা কোনো নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেনি, সেটাই কমলা হ্যারিসের জন্য কাল হয়েছিল কি না কে জানে? আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কথা উঠেছে। মার্কিনরা তাই নতুন কিছু চাইছিল।
নতুন কিছু করে দেখানোর জন্য কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জরুরি হয়ে পড়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁকে ভোট দেওয়া মানুষেরাও এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে। ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির কারণে পুরো দেশটাই যখন শঙ্কিত, তখন নিউইয়র্কের মতো ডেমোক্র্যাটদের স্বর্গরাজ্যে নতুন কিছু ঘটবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। গরিব ও মধ্যবিত্ত নিউইয়র্কবাসীর স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকার করে মামদানি তাঁর বলিষ্ঠ অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। এটাই মামদানির সবচেয়ে বড় জাদু ছিল বলে অনেকেই মনে করে থাকেন।
৩. তরুণেরা পরিবর্তন চায়। সব সময়ই চায়। সব দেশেই চায়। কোনো কোনো দেশে তরুণদের সাহস ও সততা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোনো কোনো দেশে তরুণেরা সহজেই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তরুণদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখে দেশের মানুষ, সে স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়ে।
জোহরান মামদানি তরুণ। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি মেয়র হলেন। নিউইয়র্ক কখনো এত কম বয়সী মেয়র পায়নি। তাই যে প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ মামদানির দিকে তাকিয়ে আছে, সে প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশা গ্রাস করবে নগরবাসীকে। সেটা মামদানি জানেন। তিনি কীভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মোকাবিলা করেছেন, সেটাও তাঁর সাহসের দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে। এবার দেখা যাক, কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মামদানি। এই প্রতিশ্রুতিগুলো কেন নিউইয়র্কবাসীকে তাঁর দিকে টেনে আনল?
৪. মামদানি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় দৃষ্টি দিয়েছেন তাঁর শহরের দিকেই। মার্কিন রাজনীতি বা বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে তিনি কখনোই কিছু বলেননি, এমন নয়। কিন্তু মূলত নিউইয়র্কের সংকটগুলোকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করেছেন। পাঁচটি অংশে বিভক্ত নিউইয়র্কের সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের দিকেই তিনি আন্তরিক ছিলেন। এ সময় যে সমস্যাগুলোয় পড়েছে নিউইয়র্কবাসী, সেগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে বেরিয়ে আসার অঙ্গীকার করেছেন।
নিউইয়র্কে বাড়িভাড়া সমস্যা প্রকট। কেউ বাড়িভাড়া নিতে চাইলে আয় ও ব্যয়ের হিসাব মেলাতে হিমশিম খেয়ে যায়। মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে এ এক মহাসংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বছর পাঁচেক ধরে এই সংকট বেড়েই চলেছে। এত মানুষের শহরে কীভাবে আবাসন সামাল দেওয়া হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। কোনো বাড়ির বেজমেন্টে বসবাস কিংবা চুলা রাখা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন জনসংখ্যার চাপে সেই আইনকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। লাখ লাখ নিউইয়র্কবাসী বেজমেন্টে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।
এই নাগরিকদের ওপর বাড়িওয়ালারা যেন বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন, তা নিয়ে কাজ করবেন মামদানি। এটা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছে।
দ্বিতীয় বড় যে সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন মামদানি, তা হলো ট্রান্সপোর্ট। বাস, মেট্রো ধরনের পরিবহনের ভাড়া হ্রাস করা নিয়ে তিনি নানা চিন্তাভাবনা করছেন। এখন সাধারণ পরিবহনের একটি ভ্রমণে প্রায় ৩ ডলার খরচ হয়। এই সংকট কাটানোর জন্য পরিবহন শুল্কমুক্ত করার কথা তিনি ভাবছেন। শিশুদের দিকে নজর দিয়েছেন তিনি। শিশু পরিচর্যায় বাজেট বাড়ানোর কথা ভাবছেন তিনি।
চতুর্থ যে বিষয়টি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় তুলে ধরেছেন মামদানি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল। তিনি বড়লোকদের ওপর বেশি বেশি কর চাপিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন মসৃণ করার কথা ভাবছেন। এই প্রতিশ্রুতি পালন করা তাঁর জন্য কতটা সহজ হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। নিউইয়র্কে ব্যবসার মালিকেরা কর বাড়ানোর কারণে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে অন্য কোথাও তাঁদের ব্যবসা নিয়ে যাবেন কি না, সেটাও ভাবতে হবে। নির্বাচনের আগে থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো মামদানি নির্বাচিত হলে ফেডারেল বাজেট সংকুচিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। মামদানিকে ইহুদিবিদ্বেষী বলেছেন। মামদানির সমাজতান্ত্রিক পরিচয় নিয়ে সমালোচনা করেছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে মামদানির সঙ্গে অসহযোগিতা করা হলে, নিউইয়র্কের বড়লোকেরা মামদানির কর আরোপের ভাবনাকে মেনে না নিলে কীভাবে বাজেট সমস্যার সমাধান হবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে মামদানিকে।
৫. মামদানিকে নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র বলা হচ্ছে। উগান্ডায় জন্ম নেওয়া মুসলিম বাবা ও হিন্দু মায়ের সন্তান এই জোহরান মামদানি। বাবা মাহমুদ মামদানি ও মা মীরা নায়ার দুজনেই স্বনামধন্য। স্ত্রী সিরীয় বংশোদ্ভূত রমা দুওয়াজি।
‘ইসলামোফোবিয়া’ দিয়ে আর কাজ হবে না—এ রকম একটি সাহসী বার্তা দিয়েছেন মামদানি। ইসলামি জুজুর ভয় দেখিয়ে মার্কিন নাগরিকদের যেভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ প্রণিধানযোগ্য। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, তিনি ইহুদিবিদ্বেষী নন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা গেছে, মেয়র নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ ইহুদি মামদানিকেই ভোট দিয়েছেন।
নিউইয়র্ক সিটি ও আশপাশের এলাকায় প্রায় ১০ লাখ ইহুদি বাস করে—ইসরায়েলের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইহুদি জনসংখ্যা এখানেই। মামদানি তাঁর নির্বাচনী
প্রচারণায় ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রকাশ্যে ইহুদিবিরোধী মনোভাবের (অ্যান্টিসেমিটিজম) বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ভাগ্যের কী পরিহাস, একই সঙ্গে মামদানি ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলের রাজনীতিকদের ইসলামোফোবিয়ার শিকার হয়েছেন।
ডেমোক্র্যাটদের প্রগতিশীল ধারায় মামদানির অবস্থান। মূলত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি আছে। যাঁরা শ্রমিকদের অধিকার, সম্পদের নির্দিষ্ট বণ্টন, বড়লোকদের প্রতি বেশি করে কর আরোপ, সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলেন। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে উন্নত করার একটি ভাবনা তাঁদের আছে। এই দলে বার্নি স্যান্ডার্স, আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্টেজকেও দেখতে পাওয়া যায়।
তবে স্বীকার করে নেওয়া ভালো, ডেমোক্রেটিক সমাজতন্ত্রীরা বিশুদ্ধ মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের কথা বলেন না, মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং কর্মীদের ও নিম্ন-মধ্য আয়ের মানুষের অধিকারের কথাই বলে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটরা যে ব্যবস্থা চাইছেন, তা হচ্ছে মিশ্র অর্থনীতির মিশেল। ব্যক্তিমালিকানা থাকবে, বাজারও থাকবে, কিন্তু তা হবে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা যদি পূরণ করতে পারেন, তাহলে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নাভিশ্বাস উঠে যাওয়া নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নিউইয়র্কবাসীর জীবনে শান্তি নেমে আসতে পারে। কিন্তু সেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি পথ। পদে পদে বাধা রয়েছে। মামদানি সে বাধা অতিক্রম করে যেতে পারেন কি না, সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। তবে একটা কথা ঠিক, মামদানির বিজয় মার্কিন উগ্র ডানপন্থী পপুলিজমের গালে এক তীব্র কশাঘাত। দেশে দেশে যেভাবে উগ্র ডানপন্থা জেগে উঠছে, তার বিরুদ্ধে মামদানির বিজয়কে একটি নতুন আশাব্যঞ্জক বার্তা হিসেবে দেখলে ভুল হবে না।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি যে বিজয়ী হবেন, সে বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ ছিল না। তবে রাজনীতিতে প্রায় নতুন একজন প্রার্থী
কীভাবে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, তা নিয়ে একটা বিশ্লেষণ হতেই পারে।
১. এ বছরের জুন মাসে যখন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মনোনয়নের জন্য ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি হলো, তখন অন্য প্রার্থী নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দিয়েছিলেন মামদানি। প্রাইমারির সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। আমাদের দেশে নির্বাচনী ডামাডোলে রাস্তাঘাট যেভাবে রোমাঞ্চিত হতে থাকে, সে রকম কিছুই সেখানে দেখিনি। বড়লোক কুমোর পারিবারিক ঐতিহ্য, তাঁর অগাধ অর্থ, ডেমোক্র্যাট নেতা হিসেবে তাঁর আভিজাত্য—কিছুই তাঁকে মামদানির সামনে দাঁড়াতে দেয়নি। নির্বাচনের আগে ও পরে মামদানিকে নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, ইতিমধ্যেই অনেকে তা জানেন। ফলে এখন সে বিষয়ে কিছু বললে তা পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে।
নিউইয়র্ক সিটির ১১১তম মেয়র নির্বাচনে কুমো দাঁড়িয়েছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। রিপাবলিকানদের প্রার্থী ছিলেন কার্টিস স্লিওয়া। কিন্তু মামদানির জনসমর্থনের কারণে তাঁরা দুজনই ভেসে গেছেন খড়কুটোর মতো। তাই এই সময় জোহরান মামদানির বিজয়ের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা জরুরি।
২ . মামদানির বিরাট বিজয়ের পাশাপাশি একই সময়ে ভার্জিনিয়ায় গভর্নর পদে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী এবিগেইল স্প্যানবার্গার জয়ী হয়েছেন। নিউ জার্সির গভর্নর পদে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মাইকি শেরিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বড় তিনটি নির্বাচনেই ডেমোক্র্যাটদের জয় হলো। এটাকে ট্রাম্প-নীতির পরাজয় হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই মামদানির বিজয়কে এই আলোকেই দেখতে হবে।
দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন তেলেসমাতি কারবার শুরু করেছেন যে খুব দ্রুত তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। জো বাইডেনের শাসনামলে অনেক মার্কিনই বাইডেনকে যোগ্য প্রেসিডেন্ট ভাবতে পারেননি। অভিবাসী মানুষদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ছিল বলে শ্বেতাঙ্গ মার্কিন নাগরিকেরা ডেমোক্র্যাটদের ওপর বিরক্ত ছিল। বাইডেনের আমলে সমাজে নিম্নবিত্ত মানুষের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কারণেও অনেকে ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকেছিল। যুক্তরাষ্ট্র দেশটিই যে অভিবাসীদের দিয়ে গড়া এবং সে দেশ গড়তে গিয়ে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল—এই ইতিহাস বেমালুম ভুলে গিয়েছিল এই কট্টর শ্বেতাঙ্গরা। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পেছনে এটা একটি বড় কারণ। তবে আফ্রিকান ও এশিয়ান বংশোদ্ভূত মার্কিনদের একটা বড় অংশও ট্রাম্পের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। আরও অনেক কারণ আছে নিশ্চয়। যেমন এখন পর্যন্ত মার্কিনরা কোনো নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেনি, সেটাই কমলা হ্যারিসের জন্য কাল হয়েছিল কি না কে জানে? আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কথা উঠেছে। মার্কিনরা তাই নতুন কিছু চাইছিল।
নতুন কিছু করে দেখানোর জন্য কেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জরুরি হয়ে পড়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁকে ভোট দেওয়া মানুষেরাও এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে। ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির কারণে পুরো দেশটাই যখন শঙ্কিত, তখন নিউইয়র্কের মতো ডেমোক্র্যাটদের স্বর্গরাজ্যে নতুন কিছু ঘটবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। গরিব ও মধ্যবিত্ত নিউইয়র্কবাসীর স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকার করে মামদানি তাঁর বলিষ্ঠ অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। এটাই মামদানির সবচেয়ে বড় জাদু ছিল বলে অনেকেই মনে করে থাকেন।
৩. তরুণেরা পরিবর্তন চায়। সব সময়ই চায়। সব দেশেই চায়। কোনো কোনো দেশে তরুণদের সাহস ও সততা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোনো কোনো দেশে তরুণেরা সহজেই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তরুণদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখে দেশের মানুষ, সে স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়ে।
জোহরান মামদানি তরুণ। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তিনি মেয়র হলেন। নিউইয়র্ক কখনো এত কম বয়সী মেয়র পায়নি। তাই যে প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ মামদানির দিকে তাকিয়ে আছে, সে প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশা গ্রাস করবে নগরবাসীকে। সেটা মামদানি জানেন। তিনি কীভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মোকাবিলা করেছেন, সেটাও তাঁর সাহসের দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে। এবার দেখা যাক, কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মামদানি। এই প্রতিশ্রুতিগুলো কেন নিউইয়র্কবাসীকে তাঁর দিকে টেনে আনল?
৪. মামদানি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় দৃষ্টি দিয়েছেন তাঁর শহরের দিকেই। মার্কিন রাজনীতি বা বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে তিনি কখনোই কিছু বলেননি, এমন নয়। কিন্তু মূলত নিউইয়র্কের সংকটগুলোকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করেছেন। পাঁচটি অংশে বিভক্ত নিউইয়র্কের সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের দিকেই তিনি আন্তরিক ছিলেন। এ সময় যে সমস্যাগুলোয় পড়েছে নিউইয়র্কবাসী, সেগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে বেরিয়ে আসার অঙ্গীকার করেছেন।
নিউইয়র্কে বাড়িভাড়া সমস্যা প্রকট। কেউ বাড়িভাড়া নিতে চাইলে আয় ও ব্যয়ের হিসাব মেলাতে হিমশিম খেয়ে যায়। মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে এ এক মহাসংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বছর পাঁচেক ধরে এই সংকট বেড়েই চলেছে। এত মানুষের শহরে কীভাবে আবাসন সামাল দেওয়া হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। কোনো বাড়ির বেজমেন্টে বসবাস কিংবা চুলা রাখা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন জনসংখ্যার চাপে সেই আইনকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। লাখ লাখ নিউইয়র্কবাসী বেজমেন্টে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।
এই নাগরিকদের ওপর বাড়িওয়ালারা যেন বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে না পারেন, তা নিয়ে কাজ করবেন মামদানি। এটা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছে।
দ্বিতীয় বড় যে সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন মামদানি, তা হলো ট্রান্সপোর্ট। বাস, মেট্রো ধরনের পরিবহনের ভাড়া হ্রাস করা নিয়ে তিনি নানা চিন্তাভাবনা করছেন। এখন সাধারণ পরিবহনের একটি ভ্রমণে প্রায় ৩ ডলার খরচ হয়। এই সংকট কাটানোর জন্য পরিবহন শুল্কমুক্ত করার কথা তিনি ভাবছেন। শিশুদের দিকে নজর দিয়েছেন তিনি। শিশু পরিচর্যায় বাজেট বাড়ানোর কথা ভাবছেন তিনি।
চতুর্থ যে বিষয়টি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় তুলে ধরেছেন মামদানি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল। তিনি বড়লোকদের ওপর বেশি বেশি কর চাপিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন মসৃণ করার কথা ভাবছেন। এই প্রতিশ্রুতি পালন করা তাঁর জন্য কতটা সহজ হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে। নিউইয়র্কে ব্যবসার মালিকেরা কর বাড়ানোর কারণে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে অন্য কোথাও তাঁদের ব্যবসা নিয়ে যাবেন কি না, সেটাও ভাবতে হবে। নির্বাচনের আগে থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তো মামদানি নির্বাচিত হলে ফেডারেল বাজেট সংকুচিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। মামদানিকে ইহুদিবিদ্বেষী বলেছেন। মামদানির সমাজতান্ত্রিক পরিচয় নিয়ে সমালোচনা করেছেন। কেন্দ্রীয়ভাবে মামদানির সঙ্গে অসহযোগিতা করা হলে, নিউইয়র্কের বড়লোকেরা মামদানির কর আরোপের ভাবনাকে মেনে না নিলে কীভাবে বাজেট সমস্যার সমাধান হবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে মামদানিকে।
৫. মামদানিকে নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র বলা হচ্ছে। উগান্ডায় জন্ম নেওয়া মুসলিম বাবা ও হিন্দু মায়ের সন্তান এই জোহরান মামদানি। বাবা মাহমুদ মামদানি ও মা মীরা নায়ার দুজনেই স্বনামধন্য। স্ত্রী সিরীয় বংশোদ্ভূত রমা দুওয়াজি।
‘ইসলামোফোবিয়া’ দিয়ে আর কাজ হবে না—এ রকম একটি সাহসী বার্তা দিয়েছেন মামদানি। ইসলামি জুজুর ভয় দেখিয়ে মার্কিন নাগরিকদের যেভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ প্রণিধানযোগ্য। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, তিনি ইহুদিবিদ্বেষী নন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা গেছে, মেয়র নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ ইহুদি মামদানিকেই ভোট দিয়েছেন।
নিউইয়র্ক সিটি ও আশপাশের এলাকায় প্রায় ১০ লাখ ইহুদি বাস করে—ইসরায়েলের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইহুদি জনসংখ্যা এখানেই। মামদানি তাঁর নির্বাচনী
প্রচারণায় ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রকাশ্যে ইহুদিবিরোধী মনোভাবের (অ্যান্টিসেমিটিজম) বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। ভাগ্যের কী পরিহাস, একই সঙ্গে মামদানি ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয় দলের রাজনীতিকদের ইসলামোফোবিয়ার শিকার হয়েছেন।
ডেমোক্র্যাটদের প্রগতিশীল ধারায় মামদানির অবস্থান। মূলত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি আছে। যাঁরা শ্রমিকদের অধিকার, সম্পদের নির্দিষ্ট বণ্টন, বড়লোকদের প্রতি বেশি করে কর আরোপ, সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলেন। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে উন্নত করার একটি ভাবনা তাঁদের আছে। এই দলে বার্নি স্যান্ডার্স, আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্টেজকেও দেখতে পাওয়া যায়।
তবে স্বীকার করে নেওয়া ভালো, ডেমোক্রেটিক সমাজতন্ত্রীরা বিশুদ্ধ মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের কথা বলেন না, মূলত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং কর্মীদের ও নিম্ন-মধ্য আয়ের মানুষের অধিকারের কথাই বলে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটরা যে ব্যবস্থা চাইছেন, তা হচ্ছে মিশ্র অর্থনীতির মিশেল। ব্যক্তিমালিকানা থাকবে, বাজারও থাকবে, কিন্তু তা হবে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা যদি পূরণ করতে পারেন, তাহলে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নাভিশ্বাস উঠে যাওয়া নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত নিউইয়র্কবাসীর জীবনে শান্তি নেমে আসতে পারে। কিন্তু সেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি পথ। পদে পদে বাধা রয়েছে। মামদানি সে বাধা অতিক্রম করে যেতে পারেন কি না, সেটা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। তবে একটা কথা ঠিক, মামদানির বিজয় মার্কিন উগ্র ডানপন্থী পপুলিজমের গালে এক তীব্র কশাঘাত। দেশে দেশে যেভাবে উগ্র ডানপন্থা জেগে উঠছে, তার বিরুদ্ধে মামদানির বিজয়কে একটি নতুন আশাব্যঞ্জক বার্তা হিসেবে দেখলে ভুল হবে না।
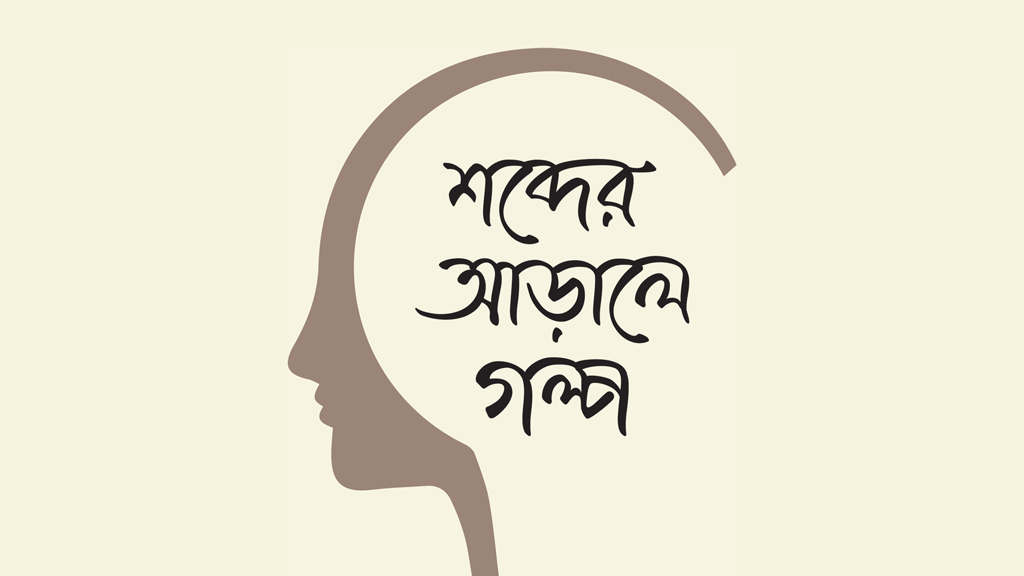
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু
১০ জুলাই ২০২৫
৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো
২ ঘণ্টা আগে
সরকারের একজন দায়িত্বরত ব্যক্তি নাকি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ইতিহাসের সর্বোত্তম নির্বাচন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটা পোস্ট বেশ ঘোরাঘুরি করছে। চোখে লাগল কথাটা বেশ। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? হলে তো ভালোই। জনগণ তো যুগ যুগ ধরে সেটাই চেয়ে এসেছে।
২ ঘণ্টা আগে
সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।
১ দিন আগেস্বপ্না রেজা

সরকারের একজন দায়িত্বরত ব্যক্তি নাকি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ইতিহাসের সর্বোত্তম নির্বাচন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটা পোস্ট বেশ ঘোরাঘুরি করছে। চোখে লাগল কথাটা বেশ। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? হলে তো ভালোই। জনগণ তো যুগ যুগ ধরে সেটাই চেয়ে এসেছে।
একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হলে তো রাষ্ট্রের জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা থাকে জনগণের কাছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী নয়, জনগণই যে সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী—এমন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ইদানীং অনেক কথাই শুনি, যার আগামাথা বুঝতে পারি না। মনে হয়, বুঝবার মতো জ্ঞান হয়নি। কিংবা ওসব হারিয়ে গেছে।
সত্যি বলছি, তেমনই লাগে। এমনকি নিজেকে এসব কথাবার্তায় বড্ড বেমানান লাগে। অচল লাগে। যা জেনে এসেছি, শিখে এসেছি সবকিছুই অর্থহীন মনে হয়। ফলে কথা বলা, আলোচনায় অংশগ্রহণ করা কমে গেছে। শোনা যায়, আজকাল নাকি বেশি কথা বলা যায় না। ভয় নামক একটা শব্দ তার প্রচলন বাড়িয়েছে। কিন্তু এমন তো কথা ছিল না। কথা রাখেনি কেউ!
যাহোক, ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে অবশেষে রাজনৈতিক দলগুলো বেশ সরব হয়েছে। যদিও দলগুলোর ভেতর অন্তর্কলহ দূর হয়নি মোটেও। চিরাচরিত নিয়মে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতার মোহ কমবেশি প্রায় সবারই। কর্মী থেকে শুরু করে নেতা, যোগ্য, অযোগ্য ব্যক্তি সবাই রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন চান। ফলে কলহ বাড়ে। দল ভাঙে। সম্প্রতি দেখা গেল বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করেছেন। এমন দৃশ্য দেখার জন্য কিন্তু সাধারণ জনগণ অপেক্ষায় ছিল না। সাধারণ জনগণের চিন্তাচেতনা বদলেছে। অতীতের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হোক, তা সাধারণ জনগণ আর প্রত্যাশা করে না কোনোভাবেই। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হওয়ার যে রোগটা, সেই রোগটা কিন্তু ঘুরেফিরে থেকেই যাচ্ছে, নিরাময় অযোগ্য থেকে যাচ্ছে।
একটা শ্রেণির মানুষ ভেবে বসেই আছে, নির্বাচন হবে না। আরেকটা শ্রেণির জনগণ নির্বাচন নিয়ে সংশয়ে আছে। বলছে, এটা আইওয়াশ, পাতানো খেলা। আবার আরেকটা শ্রেণি মনে করে, নির্বাচন হতেই হবে। নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সরকার ছাড়া এই দেশ ঠিকমতো পরিচালিত হবে না, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দূর হবে না। সাধারণ জনগণের অধিকার, নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। বৈষম্য থেকে যাবে। যদিও প্রশ্ন ওঠে, অতীতে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার কি দেশকে স্থিতিশীল করতে সমর্থ হয়েছিল? উত্তর, শতভাগ না। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তার যে হাল, সেটা ছিল না। মব সন্ত্রাস, ইচ্ছে হলেই আইন হাতে তুলে নেওয়া, চাঁদাবাজি, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, কাউকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা, অবমূল্যায়ন করা ইত্যাদি এখন বেশ দৃশ্যমান।
অতীতে এসব থাকলেও মাত্রা ছিল কম। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। তারা অতীতের মতো সক্রিয় নয় বলে এই শ্রেণির ধারণা। একজন বলছিলেন, পুলিশের ভেতর মনে হয় চাপা অভিমান কাজ করছে, তারা জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তেমন সক্রিয় হচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন তো সব সরকারের এবং রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজনৈতিক সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। সরকারের আদেশ বা সিদ্ধান্ত অমান্য করা, এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের থাকে না। বিশেষ করে মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ের সদস্যদের। অতীতে পুলিশ প্রশাসনকে প্রতিটি রাজনৈতিক সরকার কীভাবে ব্যবহার করেছে সেটা সবাই জানে।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে জনগণের হত্যার বিচারের বিষয়ে কথা উঠলেও পুলিশ হত্যার বিষয়ে কিন্তু কথা উঠতে দেখা যায়নি। যাঁরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কোনো তথ্যও প্রকাশ পায়নি। যেকোনো হত্যাকাণ্ডই কাঙ্ক্ষিত নয়। অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান থাকে। ছাত্র-জনতার নির্মম হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া যেমন শুরু হয়েছে, তেমন করে পুলিশ হত্যার বিচারও হওয়া দরকার ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। সেই সময় গণহারে পুলিশ হত্যা পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণ বলে তাঁরা মনে করেন।
সম্প্রতি মফস্বল ও গ্রামে যেতে হয়েছে কাজে। চোখে পড়ল নির্বাচনী হাওয়া। এইসব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ নির্বাচনে আগ্রহী। তাদের নিজেদের পছন্দের দল ও নেতা আছে। যদিও এবার আওয়ামী লীগকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নির্বাচনপ্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের লোকজনের ভেতরে আওয়ামী লীগের বিকল্প প্রার্থী পছন্দের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ দ্বিধান্বিত পছন্দ নিয়ে। এখানে একটা কথা বলাবাহুল্য যে মুক্তিযুদ্ধ ও নারীর অধিকার বিষয়ে এই দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ বেশ সচেতন। একটা সুস্থ, সুন্দর ও নির্মল চিন্তাচেতনায় জীবনযাপনে পক্ষপাতী তারা। এই সত্য প্রমাণের উত্তম পন্থা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া।
এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে একপর্যায়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার কারণ ছিল নিরীহ ছাত্র-জনতা হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে শিশুদের নির্মম ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর বিষয়টি। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ কখনোই অন্যায়, অত্যাচার বিশেষ করে ছাত্র, শিশুহত্যা মেনে নিতে পারেনি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অবতারণা তারই দৃষ্টান্ত। ২০২৪-এ তারই পুনরাবৃত্তি। একটা স্বাধীন দেশে এমন ঘটনা কখনোই আশা করা যায় না, কল্পনাতীত বটেই।
জনগণ সমর্থিত সরকার গঠনে নতুন রাজনৈতিক দলসহ সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল পাওয়া যেত বলে অনেকের ধারণা। তবে এটা ঠিক যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে কমবেশি সবারই একধরনের অনীহা দেখা গেছে সব সময়। নির্বাচন নিয়ে জনমনে যে আশঙ্কা, তা কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলে না। বরং আদতে কী হয় বা হবে, তা নিয়ে হাজারো গল্প-কেচ্ছা। তবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আশা করি জনগণ তাদের সঠিক রায় দিতে সমর্থ হবে। আর
আমরা সেটাই চাই।

সরকারের একজন দায়িত্বরত ব্যক্তি নাকি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ইতিহাসের সর্বোত্তম নির্বাচন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটা পোস্ট বেশ ঘোরাঘুরি করছে। চোখে লাগল কথাটা বেশ। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? হলে তো ভালোই। জনগণ তো যুগ যুগ ধরে সেটাই চেয়ে এসেছে।
একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হলে তো রাষ্ট্রের জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা থাকে জনগণের কাছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী নয়, জনগণই যে সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী—এমন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও ইদানীং অনেক কথাই শুনি, যার আগামাথা বুঝতে পারি না। মনে হয়, বুঝবার মতো জ্ঞান হয়নি। কিংবা ওসব হারিয়ে গেছে।
সত্যি বলছি, তেমনই লাগে। এমনকি নিজেকে এসব কথাবার্তায় বড্ড বেমানান লাগে। অচল লাগে। যা জেনে এসেছি, শিখে এসেছি সবকিছুই অর্থহীন মনে হয়। ফলে কথা বলা, আলোচনায় অংশগ্রহণ করা কমে গেছে। শোনা যায়, আজকাল নাকি বেশি কথা বলা যায় না। ভয় নামক একটা শব্দ তার প্রচলন বাড়িয়েছে। কিন্তু এমন তো কথা ছিল না। কথা রাখেনি কেউ!
যাহোক, ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে অবশেষে রাজনৈতিক দলগুলো বেশ সরব হয়েছে। যদিও দলগুলোর ভেতর অন্তর্কলহ দূর হয়নি মোটেও। চিরাচরিত নিয়মে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতার মোহ কমবেশি প্রায় সবারই। কর্মী থেকে শুরু করে নেতা, যোগ্য, অযোগ্য ব্যক্তি সবাই রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন চান। ফলে কলহ বাড়ে। দল ভাঙে। সম্প্রতি দেখা গেল বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা মনোনয়ন না পাওয়ায় তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করেছেন। এমন দৃশ্য দেখার জন্য কিন্তু সাধারণ জনগণ অপেক্ষায় ছিল না। সাধারণ জনগণের চিন্তাচেতনা বদলেছে। অতীতের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হোক, তা সাধারণ জনগণ আর প্রত্যাশা করে না কোনোভাবেই। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হওয়ার যে রোগটা, সেই রোগটা কিন্তু ঘুরেফিরে থেকেই যাচ্ছে, নিরাময় অযোগ্য থেকে যাচ্ছে।
একটা শ্রেণির মানুষ ভেবে বসেই আছে, নির্বাচন হবে না। আরেকটা শ্রেণির জনগণ নির্বাচন নিয়ে সংশয়ে আছে। বলছে, এটা আইওয়াশ, পাতানো খেলা। আবার আরেকটা শ্রেণি মনে করে, নির্বাচন হতেই হবে। নির্বাচন হবে। নির্বাচিত সরকার ছাড়া এই দেশ ঠিকমতো পরিচালিত হবে না, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দূর হবে না। সাধারণ জনগণের অধিকার, নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। বৈষম্য থেকে যাবে। যদিও প্রশ্ন ওঠে, অতীতে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার কি দেশকে স্থিতিশীল করতে সমর্থ হয়েছিল? উত্তর, শতভাগ না। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তার যে হাল, সেটা ছিল না। মব সন্ত্রাস, ইচ্ছে হলেই আইন হাতে তুলে নেওয়া, চাঁদাবাজি, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, কাউকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা, অবমূল্যায়ন করা ইত্যাদি এখন বেশ দৃশ্যমান।
অতীতে এসব থাকলেও মাত্রা ছিল কম। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। তারা অতীতের মতো সক্রিয় নয় বলে এই শ্রেণির ধারণা। একজন বলছিলেন, পুলিশের ভেতর মনে হয় চাপা অভিমান কাজ করছে, তারা জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তেমন সক্রিয় হচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন তো সব সরকারের এবং রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজনৈতিক সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। সরকারের আদেশ বা সিদ্ধান্ত অমান্য করা, এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের থাকে না। বিশেষ করে মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ের সদস্যদের। অতীতে পুলিশ প্রশাসনকে প্রতিটি রাজনৈতিক সরকার কীভাবে ব্যবহার করেছে সেটা সবাই জানে।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে জনগণের হত্যার বিচারের বিষয়ে কথা উঠলেও পুলিশ হত্যার বিষয়ে কিন্তু কথা উঠতে দেখা যায়নি। যাঁরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কোনো তথ্যও প্রকাশ পায়নি। যেকোনো হত্যাকাণ্ডই কাঙ্ক্ষিত নয়। অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান থাকে। ছাত্র-জনতার নির্মম হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া যেমন শুরু হয়েছে, তেমন করে পুলিশ হত্যার বিচারও হওয়া দরকার ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। সেই সময় গণহারে পুলিশ হত্যা পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণ বলে তাঁরা মনে করেন।
সম্প্রতি মফস্বল ও গ্রামে যেতে হয়েছে কাজে। চোখে পড়ল নির্বাচনী হাওয়া। এইসব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ নির্বাচনে আগ্রহী। তাদের নিজেদের পছন্দের দল ও নেতা আছে। যদিও এবার আওয়ামী লীগকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নির্বাচনপ্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের লোকজনের ভেতরে আওয়ামী লীগের বিকল্প প্রার্থী পছন্দের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ দ্বিধান্বিত পছন্দ নিয়ে। এখানে একটা কথা বলাবাহুল্য যে মুক্তিযুদ্ধ ও নারীর অধিকার বিষয়ে এই দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ বেশ সচেতন। একটা সুস্থ, সুন্দর ও নির্মল চিন্তাচেতনায় জীবনযাপনে পক্ষপাতী তারা। এই সত্য প্রমাণের উত্তম পন্থা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া।
এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে চব্বিশের বৈষম্যবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে একপর্যায়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার কারণ ছিল নিরীহ ছাত্র-জনতা হত্যাকাণ্ড, বিশেষ করে শিশুদের নির্মম ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর বিষয়টি। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ কখনোই অন্যায়, অত্যাচার বিশেষ করে ছাত্র, শিশুহত্যা মেনে নিতে পারেনি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অবতারণা তারই দৃষ্টান্ত। ২০২৪-এ তারই পুনরাবৃত্তি। একটা স্বাধীন দেশে এমন ঘটনা কখনোই আশা করা যায় না, কল্পনাতীত বটেই।
জনগণ সমর্থিত সরকার গঠনে নতুন রাজনৈতিক দলসহ সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল পাওয়া যেত বলে অনেকের ধারণা। তবে এটা ঠিক যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে কমবেশি সবারই একধরনের অনীহা দেখা গেছে সব সময়। নির্বাচন নিয়ে জনমনে যে আশঙ্কা, তা কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলে না। বরং আদতে কী হয় বা হবে, তা নিয়ে হাজারো গল্প-কেচ্ছা। তবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আশা করি জনগণ তাদের সঠিক রায় দিতে সমর্থ হবে। আর
আমরা সেটাই চাই।
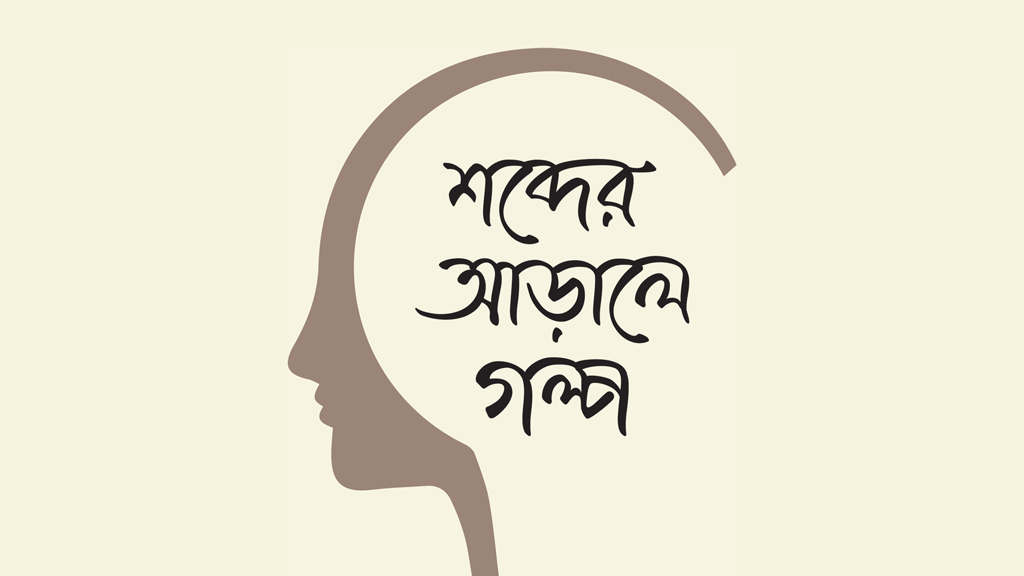
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু
১০ জুলাই ২০২৫
৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো
২ ঘণ্টা আগে
এ বছরের জুন মাসে যখন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মনোনয়নের জন্য ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি হলো, তখন অন্য প্রার্থী নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দিয়েছিলেন মামদানি। প্রাইমারির সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম।
২ ঘণ্টা আগে
সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)।
১ দিন আগেআব্দুর রহমান

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ মানবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে সুদানে।
দারফুরের সোনার জন্য লড়াই-ই এই গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ। তবে এই সংকট বোঝার জন্য একটু অতীতে ফিরে যাওয়া জরুরি। আরএসএফের যাত্রা শুরু ২০০৩ সালে, দারফুর যুদ্ধের সময়। তখন তাদের নাম ছিল ‘জানজাওয়িদ’। তারা ছিল এক যাযাবর সশস্ত্র দল। সে সময় তারা প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পক্ষে লড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল। এতে ১ লাখ থেকে ৩ লাখ মানুষ নিহত হয় এবং ২৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।
২০১৩ সালে আল-বশির জানজাওয়িদ বাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস’ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ সালে আইন করে এই বাহিনীকে স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে আরএসএফ গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেয় এবং ওমর আল- বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সহায়তা করে। পরে ২০২১ সালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে তারা বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লাহ হামদককে উৎখাত করে। এতে দেশটির বেসামরিক-সামরিক যৌথ শাসনব্যবস্থা শেষ হয়ে যায়।
এরপর ক্রমেই আরএসএফ নেতা হেমেদতি ও সেনাপ্রধান আল-বুরহানের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তে থাকে দেশটির শাসনব্যবস্থায় অংশীদারত্বকে কেন্দ্র করে। মূল প্রশ্ন ছিল, আরএসএফ কবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত হবে এবং কে দেশের নেতৃত্ব দেবে। ২০২৩ সালের ১৫ এপ্রিল এই বিরোধ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়। সেনাবাহিনী চায়, আরএসএফ পুরোপুরি তাদের অধীনে আসুক। কিন্তু আরএসএফ স্বাধীন থাকতে চায়। দুই পক্ষের এই টানাপোড়েনই শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।
এই গৃহযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুদানের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশটির অর্থনীতির মূল ভরকেন্দ্র কৃষি প্রায় ধ্বংসের মুখে। ২০২৩ সালে শস্য উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্যসংকট বেড়েছে, আমদানিনির্ভরতা বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামগ্রিকভাবে দেশটির অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ৩০-৪০ শতাংশ। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। রাজস্ব কমে যাওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রমও ভেঙে পড়েছে। একসময় তেলের আয় ও কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অর্থনীতি এখন মূলত সোনা রপ্তানির মতো একক খাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। এই সোনার বেশির ভাগই আবার উত্তোলন করা দারফুর অঞ্চলে, যা আবার আরএসএফের নিয়ন্ত্রণে।
সুদান দীর্ঘদিন ধরে সামরিক প্রভাবাধীন হয়ে আছে। ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পতনের পর দেশটিতে বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা দেখা গেলেও তা দ্রুতই ভেস্তে যায়। ক্ষমতার ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের দ্বন্দ্বই আজকের এই বিপর্যয়ের কারণ। দুই পক্ষই দেশের সম্পদ, অস্ত্র এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখতে চায়।
এই সংঘাতের কারণে দেশটির শাসনকাঠামো কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, বিচারব্যবস্থা পঙ্গু এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শিশু সৈনিক নিয়োগের মতো ঘটনাগুলো এখন নিয়মিত ঘটনা। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আরএসএফ দারফুরের এল-ফাশেরে যে ‘গণহত্যা’ চালিয়েছে, তার প্রমাণ লোপাটে তারা গণকবর খুঁড়ছে।
দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধে সুদানের ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার অর্ধেকের বেশি নারী। বিভিন্ন প্রতিবেদন মতে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে সুদানে ২ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছে।
সুদানের এই সংকট কেবল অভ্যন্তরীণ নয়, দেশটি এখন আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাতের এক রক্তাক্ত রণক্ষেত্র। লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যের অন্যতম মূল কেন্দ্র। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো উপসাগরীয় দেশগুলো এখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় আছে। প্রমাণ আছে, আরব আমিরাত বিদ্রোহী আরএসএফকে গোপনে সমর্থন দিচ্ছে। অপর দিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান ও রাশিয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখছে। ফলে সুদান এখন একধরনের প্রক্সি যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে দেশীয় সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে বিদেশি স্বার্থ।
এই বহিরাগত প্রভাব শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতেও এর প্রতিক্রিয়া পড়ছে। লাখ লাখ সুদানি শরণার্থী পার্শ্ববর্তী দেশ চাদ, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া ও মিসরে আশ্রয় নিয়েছে। এতে সীমান্ত উত্তেজনা বাড়ছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আরও নড়বড়ে হচ্ছে।
সুদানের সংকট তাই কেবল একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি গোটা আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাজারেও এর প্রভাব পড়ছে। কারণ, সুদান সোনা ও কৃষিপণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যুদ্ধের কারণে উৎপাদন ও রপ্তানি বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারেও অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।
সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকান ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় বহুবার আলোচনার চেষ্টা হয়েছে এই সংঘাত নিরসনে। কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত মিলে ‘কোয়াড’ জোট গঠন করেছে। তারা ১২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।
পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, তিন মাসের মানবিক বিরতি দেওয়া হবে, যাতে ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ করতে পারে। এরপর স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ৯ মাসের মধ্যে বেসামরিক সরকারে ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রথমে সেনাপ্রধান আল-বুরহান এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চান, আরএসএফ ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু ১৫ অক্টোবর মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি কিছুটা নমনীয় হন।
কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে দুই পক্ষের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা হয়। অক্টোবরের শেষে আরও বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই আরএসএফ এল-ফাশের দখল করে নেয়। এখন আলোচনা কোন পথে যাবে, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে এই অবস্থায় আশঙ্কা বাড়ছে, যেহেতু দারফুর অঞ্চল প্রায় পুরোটাই আরএসএফের হাতে চলে গেছে, তাহলে কি সুদান আরও একবার ভাঙতে চলেছে?
সবশেষে বলা যায়, সুদান এখন এক গভীর বিভাজনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত, রাজনীতি অস্ত্রনির্ভর, আর ভূরাজনৈতিক কারণে দেশটি পরিণত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর খেলাঘরে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশটির সাধারণ মানুষ—যারা না সেনাবাহিনীর পক্ষে আর না আরএসএফের পক্ষে, বরং তারা কেবলই বেঁচে থাকার লড়াই করছে।
এই সংকট যদি দ্রুত সমাধানের পথে না যায়, তবে শুধু সুদান নয়; সমগ্র পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিতসাগর উপকূলীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতাই ভেঙে পড়বে। তাই এখন প্রয়োজন কূটনৈতিক চাপ, মানবিক সহায়তা এবং একটি বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অন্যথায় সুদান আরও একবার ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুর অধ্যায়ে ঢুকে পড়বে, যেখান থেকে সাধারণত আর ফেরার পথ থাকবে না।
লেখক: সাংবাদিক

সুদান আফ্রিকার আলোচিত একটি দেশ। ২০১১ সালে একদফা ভাঙনের পর আবারও দেশটি সেই শঙ্কায় পড়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লড়াইরত আছে সুদানিজ আর্মড ফোর্সেস (এসএফ) বা সেনাবাহিনী এবং আধা সামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ মানবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে সুদানে।
দারফুরের সোনার জন্য লড়াই-ই এই গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ। তবে এই সংকট বোঝার জন্য একটু অতীতে ফিরে যাওয়া জরুরি। আরএসএফের যাত্রা শুরু ২০০৩ সালে, দারফুর যুদ্ধের সময়। তখন তাদের নাম ছিল ‘জানজাওয়িদ’। তারা ছিল এক যাযাবর সশস্ত্র দল। সে সময় তারা প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পক্ষে লড়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল। এতে ১ লাখ থেকে ৩ লাখ মানুষ নিহত হয় এবং ২৫ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।
২০১৩ সালে আল-বশির জানজাওয়িদ বাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস’ নামে প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৭ সালে আইন করে এই বাহিনীকে স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে আরএসএফ গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেয় এবং ওমর আল- বশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সহায়তা করে। পরে ২০২১ সালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে তারা বেসামরিক প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লাহ হামদককে উৎখাত করে। এতে দেশটির বেসামরিক-সামরিক যৌথ শাসনব্যবস্থা শেষ হয়ে যায়।
এরপর ক্রমেই আরএসএফ নেতা হেমেদতি ও সেনাপ্রধান আল-বুরহানের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তে থাকে দেশটির শাসনব্যবস্থায় অংশীদারত্বকে কেন্দ্র করে। মূল প্রশ্ন ছিল, আরএসএফ কবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত হবে এবং কে দেশের নেতৃত্ব দেবে। ২০২৩ সালের ১৫ এপ্রিল এই বিরোধ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়। সেনাবাহিনী চায়, আরএসএফ পুরোপুরি তাদের অধীনে আসুক। কিন্তু আরএসএফ স্বাধীন থাকতে চায়। দুই পক্ষের এই টানাপোড়েনই শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়।
এই গৃহযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুদানের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশটির অর্থনীতির মূল ভরকেন্দ্র কৃষি প্রায় ধ্বংসের মুখে। ২০২৩ সালে শস্য উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কমে যাওয়ায় খাদ্যসংকট বেড়েছে, আমদানিনির্ভরতা বাড়ছে এবং মুদ্রাস্ফীতি আকাশছোঁয়া পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামগ্রিকভাবে দেশটির অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ৩০-৪০ শতাংশ। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। রাজস্ব কমে যাওয়ায় প্রশাসনিক কার্যক্রমও ভেঙে পড়েছে। একসময় তেলের আয় ও কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অর্থনীতি এখন মূলত সোনা রপ্তানির মতো একক খাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যা দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা আরও অনিশ্চিত করে তুলছে। এই সোনার বেশির ভাগই আবার উত্তোলন করা দারফুর অঞ্চলে, যা আবার আরএসএফের নিয়ন্ত্রণে।
সুদান দীর্ঘদিন ধরে সামরিক প্রভাবাধীন হয়ে আছে। ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের পতনের পর দেশটিতে বেসামরিক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা দেখা গেলেও তা দ্রুতই ভেস্তে যায়। ক্ষমতার ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের দ্বন্দ্বই আজকের এই বিপর্যয়ের কারণ। দুই পক্ষই দেশের সম্পদ, অস্ত্র এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখতে চায়।
এই সংঘাতের কারণে দেশটির শাসনকাঠামো কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, বিচারব্যবস্থা পঙ্গু এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শিশু সৈনিক নিয়োগের মতো ঘটনাগুলো এখন নিয়মিত ঘটনা। স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, আরএসএফ দারফুরের এল-ফাশেরে যে ‘গণহত্যা’ চালিয়েছে, তার প্রমাণ লোপাটে তারা গণকবর খুঁড়ছে।
দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধে সুদানের ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার অর্ধেকের বেশি নারী। বিভিন্ন প্রতিবেদন মতে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে সুদানে ২ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছে।
সুদানের এই সংকট কেবল অভ্যন্তরীণ নয়, দেশটি এখন আন্তর্জাতিক স্বার্থের সংঘাতের এক রক্তাক্ত রণক্ষেত্র। লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যের অন্যতম মূল কেন্দ্র। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো উপসাগরীয় দেশগুলো এখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় আছে। প্রমাণ আছে, আরব আমিরাত বিদ্রোহী আরএসএফকে গোপনে সমর্থন দিচ্ছে। অপর দিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান ও রাশিয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখছে। ফলে সুদান এখন একধরনের প্রক্সি যুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে দেশীয় সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে বিদেশি স্বার্থ।
এই বহিরাগত প্রভাব শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতেও এর প্রতিক্রিয়া পড়ছে। লাখ লাখ সুদানি শরণার্থী পার্শ্ববর্তী দেশ চাদ, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া ও মিসরে আশ্রয় নিয়েছে। এতে সীমান্ত উত্তেজনা বাড়ছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আরও নড়বড়ে হচ্ছে।
সুদানের সংকট তাই কেবল একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি গোটা আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাজারেও এর প্রভাব পড়ছে। কারণ, সুদান সোনা ও কৃষিপণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যুদ্ধের কারণে উৎপাদন ও রপ্তানি বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারেও অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে।
সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকান ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় বহুবার আলোচনার চেষ্টা হয়েছে এই সংঘাত নিরসনে। কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত মিলে ‘কোয়াড’ জোট গঠন করেছে। তারা ১২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।
পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, তিন মাসের মানবিক বিরতি দেওয়া হবে, যাতে ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ করতে পারে। এরপর স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ৯ মাসের মধ্যে বেসামরিক সরকারে ফেরার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রথমে সেনাপ্রধান আল-বুরহান এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি চান, আরএসএফ ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু ১৫ অক্টোবর মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি কিছুটা নমনীয় হন।
কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে দুই পক্ষের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা হয়। অক্টোবরের শেষে আরও বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই আরএসএফ এল-ফাশের দখল করে নেয়। এখন আলোচনা কোন পথে যাবে, তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে এই অবস্থায় আশঙ্কা বাড়ছে, যেহেতু দারফুর অঞ্চল প্রায় পুরোটাই আরএসএফের হাতে চলে গেছে, তাহলে কি সুদান আরও একবার ভাঙতে চলেছে?
সবশেষে বলা যায়, সুদান এখন এক গভীর বিভাজনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত, রাজনীতি অস্ত্রনির্ভর, আর ভূরাজনৈতিক কারণে দেশটি পরিণত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর খেলাঘরে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশটির সাধারণ মানুষ—যারা না সেনাবাহিনীর পক্ষে আর না আরএসএফের পক্ষে, বরং তারা কেবলই বেঁচে থাকার লড়াই করছে।
এই সংকট যদি দ্রুত সমাধানের পথে না যায়, তবে শুধু সুদান নয়; সমগ্র পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিতসাগর উপকূলীয় অঞ্চলের স্থিতিশীলতাই ভেঙে পড়বে। তাই এখন প্রয়োজন কূটনৈতিক চাপ, মানবিক সহায়তা এবং একটি বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অন্যথায় সুদান আরও একবার ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুর অধ্যায়ে ঢুকে পড়বে, যেখান থেকে সাধারণত আর ফেরার পথ থাকবে না।
লেখক: সাংবাদিক
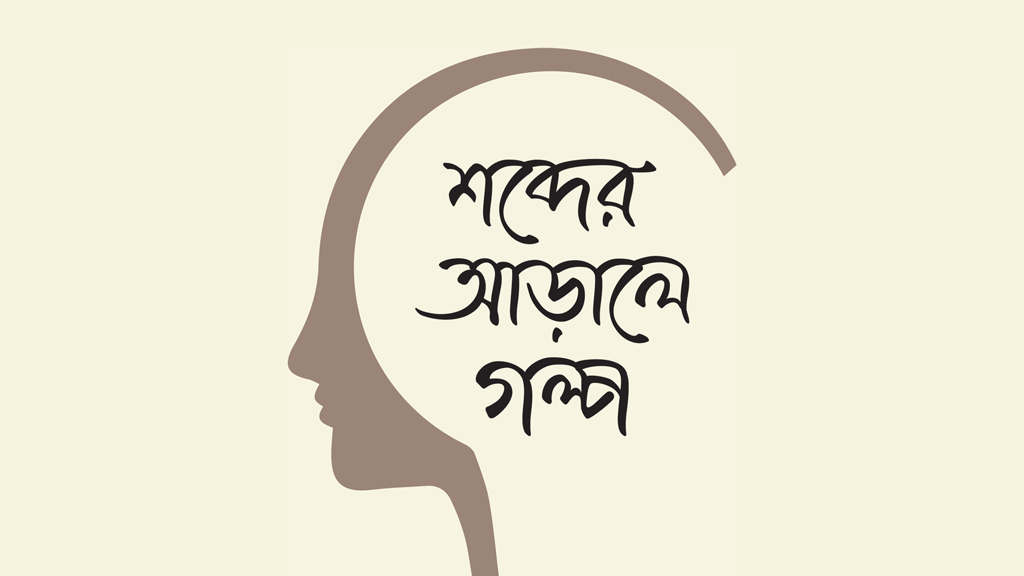
আমাদের যাপিত জীবনে অন্যতম মুখরোচক একটি খাবার হলো শিঙাড়া। বন্ধুবান্ধবদের বিকেল-সন্ধ্যার আড্ডা থেকে শুরু করে অতিথি আপ্যায়নে শিঙাড়ার জুড়ি মেলা ভার। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিচিত্র রকমের সুস্বাদু শিঙাড়া আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে চলেছে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, শিঙাড়া কীভাবে আমাদের এমন পছন্দের মুখরোচক খাদ্যবস্তু
১০ জুলাই ২০২৫
৪ নভেম্বর স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। রাজধানীতে বেশ জাঁকালোভাবেই পালিত হয়েছে বরেণ্য এই চলচ্চিত্রকারের জন্মের একশ বছর। কোনো কোনো
২ ঘণ্টা আগে
এ বছরের জুন মাসে যখন নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মনোনয়নের জন্য ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি হলো, তখন অন্য প্রার্থী নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দিয়েছিলেন মামদানি। প্রাইমারির সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম।
২ ঘণ্টা আগে
সরকারের একজন দায়িত্বরত ব্যক্তি নাকি বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে ইতিহাসের সর্বোত্তম নির্বাচন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন একটা পোস্ট বেশ ঘোরাঘুরি করছে। চোখে লাগল কথাটা বেশ। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? হলে তো ভালোই। জনগণ তো যুগ যুগ ধরে সেটাই চেয়ে এসেছে।
২ ঘণ্টা আগে