ড. আবদুল আলীম তালুকদার
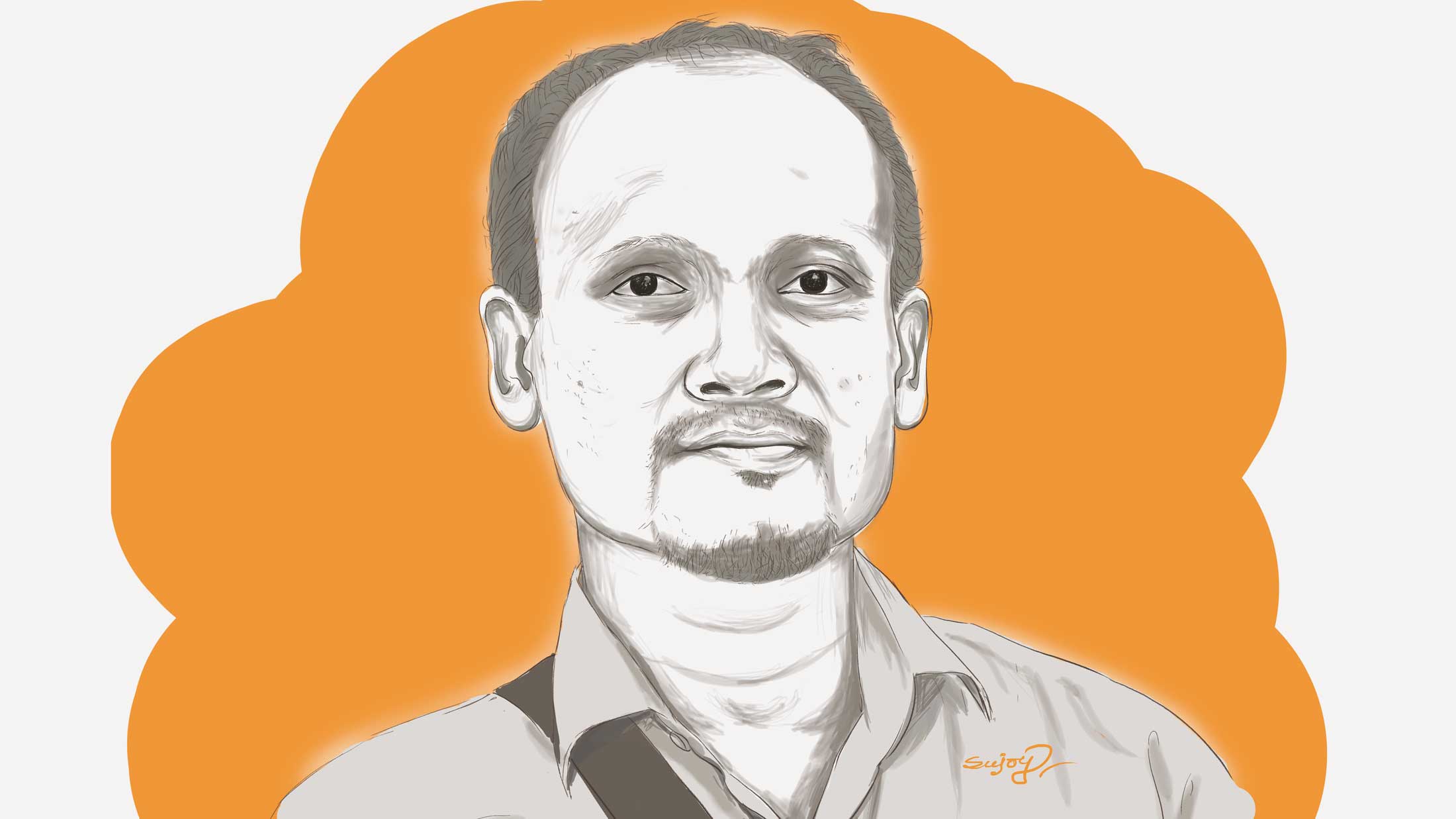
বিশ্ববাসীর সঙ্গে বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৯ আগস্ট পালন করা হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বিভিন্ন দেশের সংখ্যায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরার গুরুত্ব নিয়েই পালন করা হয় এই আন্তর্জাতিক দিবসটি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবহেলিত, সুযোগবঞ্চিত আদিবাসী জাতির সমস্যাগুলোর ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাদের অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রত্যয় নিয়ে জাতিসংঘ ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালন করে আসছে এ দিবসটি।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে আদিবাসী শব্দটি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে তাদের আখ্যায়িত করেছে। এ ছাড়া ২০১০ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের আদিবাসীদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করেছে; যদিও বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিজেদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। জাতিসংঘও তাদের দাপ্তরিক কাজে ইন্ডিজিনাস, অর্থাৎ আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।
১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্ব আদিবাসী দিবসটি পালনে ৪৯/২১৪ বিধিমালায় স্বীকৃতি পায় এবং বিশ্বের ৯০টি দেশে ৩৭০ বিলিয়ন আদিবাসী প্রতিবছর ৯ আগস্ট এ দিবসটি উদযাপন করে থাকে। দিবসটি পালনের মূল লক্ষ্য হলো আদিবাসীদের জীবনধারা, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার, আদিবাসী জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করে তোলা। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভূমির অধিকার, অঞ্চল বা টেরিটরির অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার স্বীকৃতির দাবিতে দিবসটি পালন করে থাকে। প্রতিবছর ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হলেও বাংলাদেশে ২০০৪ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে।
বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকদের সাধারণ বাঙালিদের থেকে যেমন তাদের জীবনশৈলী আলাদা, তেমনি নানা নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, খাদ্য, উৎসব, জীবন-জীবিকার মাধ্যম, জন্ম-মৃত্যুর হার, সামাজিক-পারিবারিক ও বিবাহপ্রথা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা একে অপরের থেকে ভিন্নতর। এ ছাড়া তাদের যেমন রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা, তেমনি রয়েছে স্বকীয় সমাজব্যবস্থা। এসব জাতিগোষ্ঠী মূলত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-মধ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চল তথা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, বগুড়া ইত্যাদি জেলায় সাঁওতাল, রাজবংশী, গঞ্জু, ওঁরাও, কোচ, ভুইমালি, কোল, খুমি, লুসাই, টিপরা, মুন্ডারি, রাজোয়ার, কড়া, মাল পাহাড়িয়া, মাহালী, কর্মকার, বেদিয়া মাহাতো, খিয়াং, বম (বনজোগী), তেলি, তুরি ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে। অন্যদিকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া, টিপরা, হাজং, মণিপুরি, জৈন্তিয়া আর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর জেলায় গারো, হাজং, বংশী, বর্মণ, হরিজন, কোচ, ডালু, মান্দি জাতিগোষ্ঠী; কক্সবাজার, পটুয়াখালী জেলায় রাখাইন, মারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, টিপরা, খিয়াং, খুমি, খাজো, খজন, কুকি, মুণ্ডা, ওঁরাও, মালো, মাহাতো, মগ, মুরং, চাক, বনজোগী, বম, পাংখোয়া ও তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে।
ভিন্ন জীবনধারা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আর অনন্য শিল্পশৈলীর অফুরান মিশ্রণে ঘেরা এই সব জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হলো চাকমা। বিশ্বের সমুদয় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রায় ৫৫টির বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসী তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভূমির অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার স্বীকৃতির দাবিতে দিবসটি উদযাপন করে থাকে।
পৃথিবীজুড়ে ৯০টির অধিক দেশে বসবাসরত ৫ সহস্রাধিক আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষের সংখ্যা ৩৫-৩৬ কোটি, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ এবং পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫ শতাংশ। এসব আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী প্রায় ৭ হাজার ভাষায় কথা বলে এবং তাদের রয়েছে ৫ হাজার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। বাংলাদেশে প্রায় ৫৫টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, জীবনধারা, উৎসব-অনুষ্ঠানাদি রয়েছে এবং এরা প্রায় ২৬টির মতো ভিন্ন নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় ৩০ লাখ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ এ দেশের প্রগতিশীল, সংবেদনশীল ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষ বেশ জাঁকজমকভাবেই প্রতিবছর এ দিবসটি পালন করে থাকে। এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব জাতিগোষ্ঠী বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য প্রতিপালন ও রক্ষা করছে। তাদের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে, যেমন উপজাতি, প্রথম জাতি, আদিবাসী, ক্ষুদ্র-জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচয় প্রদান করা হয়। নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ায় যুগে যুগে এদের অনেকে প্রান্তিকায়িত, শোষিত, বাধ্যতামূলকভাবে একীভূত হয়েছে এবং যখন এসব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারের সপক্ষে তারা কথা বলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা দমন-নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। পরে জাতিসংঘের আলোচনায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ ও চর্চাকে অব্যাহত রাখতে জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে প্রথম আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেয়। তারপর বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও তাদের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ‘জাতিসংঘ ও আদিবাসী জাতি এক নতুন অংশীদারত্ব’ শিরোনামে ১৯৯৩ সালকে ‘আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী বর্ষ’ ঘোষণা করে।
আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালে ১৯৯৫-০৪ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক এবং ২০০৪ সালে ২০০৫-১৪ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশেও সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।
বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষার অনগ্রসরতা, বেহাল যোগাযোগব্যবস্থা, অসচেতনতা, পেশাগত বৈচিত্র্যের অভাব, ভূমি হ্রাস, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আদিবাসীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ না থাকা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের বাস্তবায়নের শ্লথগতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আদিবাসীদের উন্নয়ন আশাব্যঞ্জক নয়। তাই তাদের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত আদিবাসীবান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এহেন অবস্থায় তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আদিবাসী যুবসমাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান, স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি আশু প্রয়োজন বলে বিভিন্ন সময় জোর দাবি জানিয়ে আসছেন বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নেতারা।
করোনা মহামারির এই মহা আপৎকালীন সময়েও বিশ্বে বসবাসরত সব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনগণের জন্য নিরন্তর শুভকামনা রইল।
লেখক: সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর
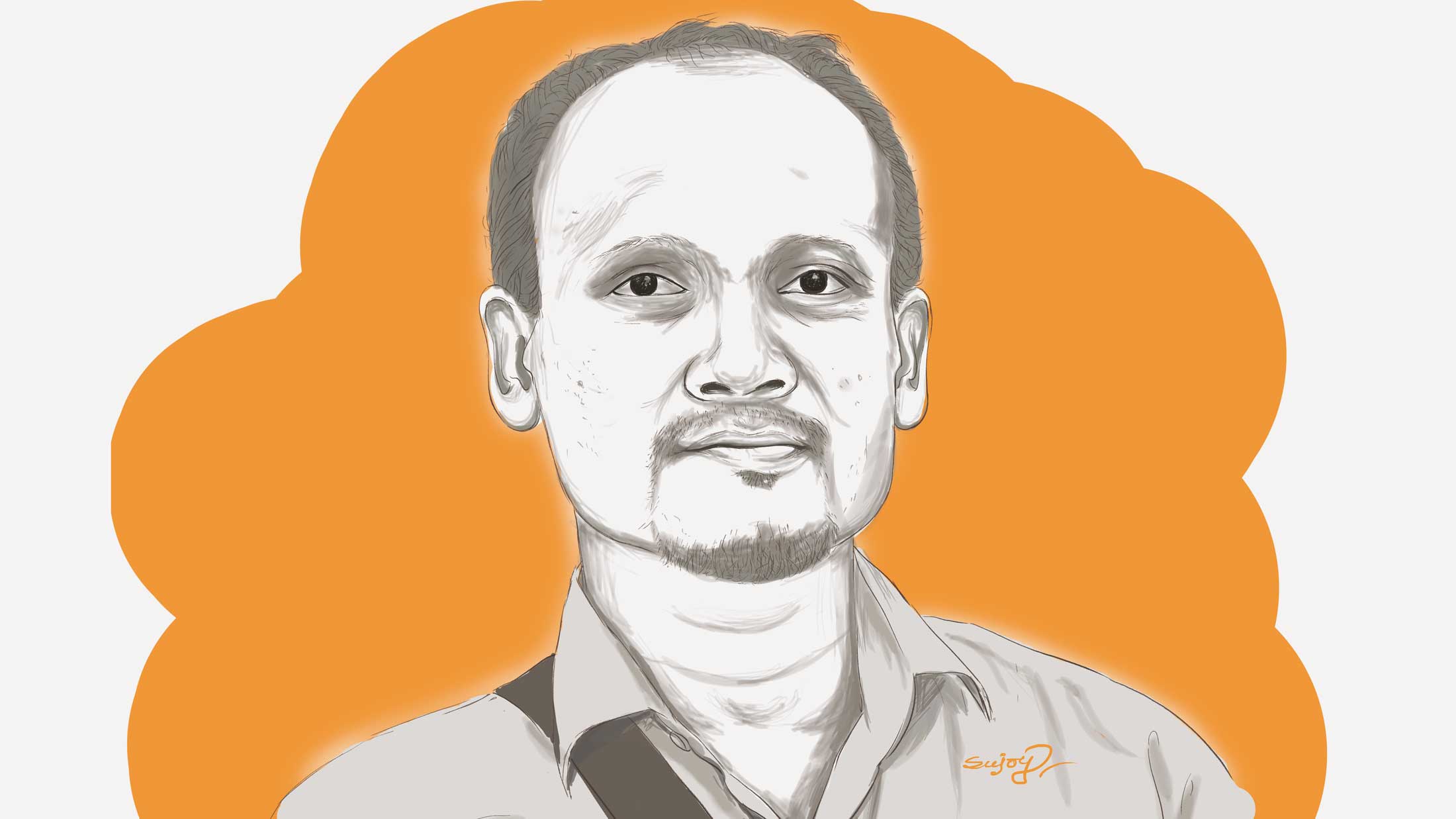
বিশ্ববাসীর সঙ্গে বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৯ আগস্ট পালন করা হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বিভিন্ন দেশের সংখ্যায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসীদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরার গুরুত্ব নিয়েই পালন করা হয় এই আন্তর্জাতিক দিবসটি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবহেলিত, সুযোগবঞ্চিত আদিবাসী জাতির সমস্যাগুলোর ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাদের অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রত্যয় নিয়ে জাতিসংঘ ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পালন করে আসছে এ দিবসটি।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে আদিবাসী শব্দটি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে উপজাতি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে তাদের আখ্যায়িত করেছে। এ ছাড়া ২০১০ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের আদিবাসীদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করেছে; যদিও বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিজেদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। জাতিসংঘও তাদের দাপ্তরিক কাজে ইন্ডিজিনাস, অর্থাৎ আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।
১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্ব আদিবাসী দিবসটি পালনে ৪৯/২১৪ বিধিমালায় স্বীকৃতি পায় এবং বিশ্বের ৯০টি দেশে ৩৭০ বিলিয়ন আদিবাসী প্রতিবছর ৯ আগস্ট এ দিবসটি উদযাপন করে থাকে। দিবসটি পালনের মূল লক্ষ্য হলো আদিবাসীদের জীবনধারা, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার, আদিবাসী জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করে তোলা। এ ছাড়া বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভূমির অধিকার, অঞ্চল বা টেরিটরির অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার স্বীকৃতির দাবিতে দিবসটি পালন করে থাকে। প্রতিবছর ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হলেও বাংলাদেশে ২০০৪ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে।
বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকদের সাধারণ বাঙালিদের থেকে যেমন তাদের জীবনশৈলী আলাদা, তেমনি নানা নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, খাদ্য, উৎসব, জীবন-জীবিকার মাধ্যম, জন্ম-মৃত্যুর হার, সামাজিক-পারিবারিক ও বিবাহপ্রথা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা একে অপরের থেকে ভিন্নতর। এ ছাড়া তাদের যেমন রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা, তেমনি রয়েছে স্বকীয় সমাজব্যবস্থা। এসব জাতিগোষ্ঠী মূলত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-মধ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চল তথা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, বগুড়া ইত্যাদি জেলায় সাঁওতাল, রাজবংশী, গঞ্জু, ওঁরাও, কোচ, ভুইমালি, কোল, খুমি, লুসাই, টিপরা, মুন্ডারি, রাজোয়ার, কড়া, মাল পাহাড়িয়া, মাহালী, কর্মকার, বেদিয়া মাহাতো, খিয়াং, বম (বনজোগী), তেলি, তুরি ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে। অন্যদিকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া, টিপরা, হাজং, মণিপুরি, জৈন্তিয়া আর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর জেলায় গারো, হাজং, বংশী, বর্মণ, হরিজন, কোচ, ডালু, মান্দি জাতিগোষ্ঠী; কক্সবাজার, পটুয়াখালী জেলায় রাখাইন, মারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, টিপরা, খিয়াং, খুমি, খাজো, খজন, কুকি, মুণ্ডা, ওঁরাও, মালো, মাহাতো, মগ, মুরং, চাক, বনজোগী, বম, পাংখোয়া ও তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছে।
ভিন্ন জীবনধারা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আর অনন্য শিল্পশৈলীর অফুরান মিশ্রণে ঘেরা এই সব জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হলো চাকমা। বিশ্বের সমুদয় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রায় ৫৫টির বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসী তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভূমির অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার স্বীকৃতির দাবিতে দিবসটি উদযাপন করে থাকে।
পৃথিবীজুড়ে ৯০টির অধিক দেশে বসবাসরত ৫ সহস্রাধিক আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষের সংখ্যা ৩৫-৩৬ কোটি, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ এবং পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৫ শতাংশ। এসব আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী প্রায় ৭ হাজার ভাষায় কথা বলে এবং তাদের রয়েছে ৫ হাজার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। বাংলাদেশে প্রায় ৫৫টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, জীবনধারা, উৎসব-অনুষ্ঠানাদি রয়েছে এবং এরা প্রায় ২৬টির মতো ভিন্ন নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় ৩০ লাখ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ এ দেশের প্রগতিশীল, সংবেদনশীল ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষ বেশ জাঁকজমকভাবেই প্রতিবছর এ দিবসটি পালন করে থাকে। এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব জাতিগোষ্ঠী বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য প্রতিপালন ও রক্ষা করছে। তাদের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে, যেমন উপজাতি, প্রথম জাতি, আদিবাসী, ক্ষুদ্র-জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচয় প্রদান করা হয়। নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ায় যুগে যুগে এদের অনেকে প্রান্তিকায়িত, শোষিত, বাধ্যতামূলকভাবে একীভূত হয়েছে এবং যখন এসব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারের সপক্ষে তারা কথা বলেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা দমন-নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। পরে জাতিসংঘের আলোচনায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ ও চর্চাকে অব্যাহত রাখতে জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে প্রথম আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেয়। তারপর বিশ্বের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও তাদের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ‘জাতিসংঘ ও আদিবাসী জাতি এক নতুন অংশীদারত্ব’ শিরোনামে ১৯৯৩ সালকে ‘আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী বর্ষ’ ঘোষণা করে।
আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালে ১৯৯৫-০৪ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক এবং ২০০৪ সালে ২০০৫-১৪ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশেও সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।
বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষার অনগ্রসরতা, বেহাল যোগাযোগব্যবস্থা, অসচেতনতা, পেশাগত বৈচিত্র্যের অভাব, ভূমি হ্রাস, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আদিবাসীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ না থাকা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের বাস্তবায়নের শ্লথগতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আদিবাসীদের উন্নয়ন আশাব্যঞ্জক নয়। তাই তাদের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ও সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত আদিবাসীবান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এহেন অবস্থায় তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ আদিবাসী যুবসমাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান, স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি আশু প্রয়োজন বলে বিভিন্ন সময় জোর দাবি জানিয়ে আসছেন বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নেতারা।
করোনা মহামারির এই মহা আপৎকালীন সময়েও বিশ্বে বসবাসরত সব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনগণের জন্য নিরন্তর শুভকামনা রইল।
লেখক: সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। অনেকের কাছে এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ওপর আস্থা রেখেছেন। নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল এবং নির্বাচনের পর ভোট গণনার সময় সারা রাত বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৬ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার, শুধু আমার নয় বরং অনেকেরই। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, পাশ্চাত্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, তখন প্রথম দিন বড় বোনের কাছ থেকে শাড়ি এনে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলাম। সেই দিনের শিহরণ, অনুভূতি এখনো শরীর-মনে দোলা দেয়।
১৬ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের পরে যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। প্রস্তাব এসেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে। সমালোচনার মুখে সেই পথ থেকে সরে এসেছে সরকার। বাতিল করা হয়েছে গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। বহু দুঃসংবাদের মধ্যে এটি একটি সুসংবাদ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ধরনের এই কেনাকাটার বিষয়টি
১৬ ঘণ্টা আগে
জাতীয় প্রেসক্লাবে ৭ সেপ্টেম্বর গণশক্তি আয়োজন করে ‘জুলাই সনদ ও নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা। সেই সভায় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না যে প্রশ্নটি করেছেন, তা কোটি টাকার সঙ্গে তুলনা করাই যায়। তাঁর সহজ জিজ্ঞাসা—‘ভোটের দিন যাঁর যেখানে শক্তি আছে, তাঁর যদি মনে হয় জিততে পারবেন না...
২ দিন আগে