জাহীদ রেজা নূর
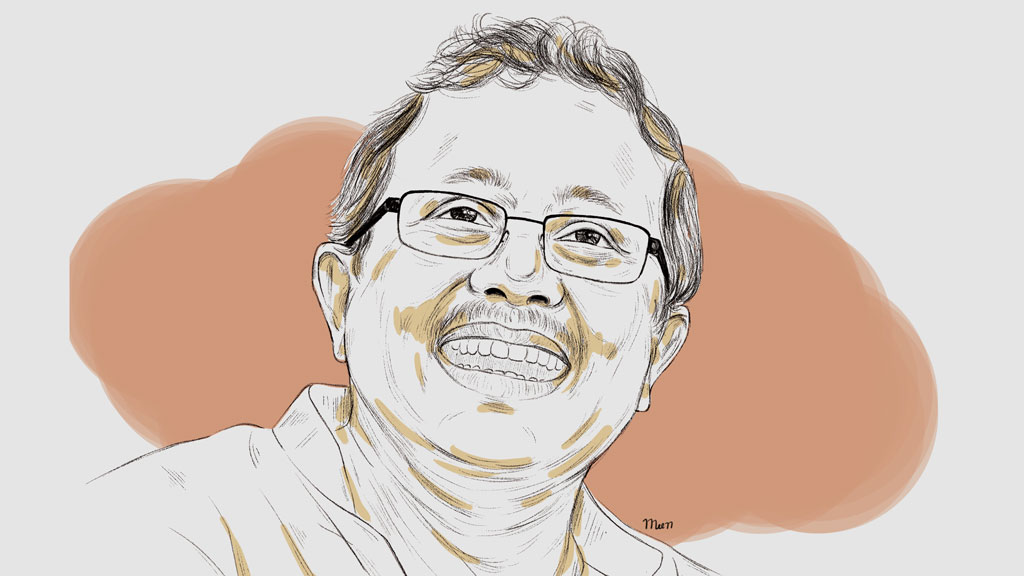
আমার এক প্রিয় তরুণ পোর্ট এলাকায় গিয়ে এমন কিছু খেয়েছিল, যাতে তার ফুড পয়জনিং হয়েছিল এবং তাকে দীর্ঘ সময় হাসপাতালের আইসিইউতে থাকতে হয়েছিল। সে যা সেবন করেছিল, তা ছিল ভয়ংকর কিছু। এ কারণে কিছুটা সুস্থ হলে ওকে নিয়ে মনোবিদের সঙ্গে বসার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে দুদিন যাওয়ার পর থেকেই তরুণটি সেখানে যেতে অনীহা প্রকাশ করতে থাকল। বলল, ‘মনোচিকিৎসক আপডেটেড নয়।’ বিশ্বে মনোরোগ নিয়ে গবেষণা কত দূর এগিয়েছে, তা নাকি এই চিকিৎসক জানেন না। তাই পুরোনো কালের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চাইছেন, যা তরুণের কোনো কাজে লাগবে না।
অসুস্থ সেই তরুণের হাতে একটা মনকাড়া বই তুলে দিলে ও কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে সেটা সরিয়ে রাখল। দুদিন পর ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, বইটা সেভাবেই পড়ে আছে।
২.
বইটা পড়েই থাকল। কেন পড়ে থাকল? বইয়ের প্রতি কি আকর্ষণ নেই এ সময়ের তরুণদের? ওরা আসলে কী নিয়ে ব্যস্ত?
সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু তরুণদের মনোজগৎটা যে বর্ষীয়ানদের কাছে অধরা হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আজ এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা হবে, যা পারিবারিক জীবনযাপনে প্রতিটি মানুষই দেখছেন, কিন্তু নতুন এই বাস্তবতা কীভাবে মোকাবিলা করবেন, তা নিয়ে সন্দিহান।
টিনএজ যেকোনো দেশে, যেকোনো পরিবারের জন্যই একটা ক্রান্তিকাল।
কে না জানে, অভিভাবকেরা চান, সন্তানেরা তাঁদের কথামতো চলুক আর তরুণেরা চায় অভিভাবকহীন ওড়ার আকাশ। তরুণদের ঘরগুলো থাকে অপরিচ্ছন্ন, কারণে-অকারণে ওরা মিথ্যে বলে, কখনো কখনো চুরি করে—এ রকম কত অভিযোগ রয়েছে তরুণদের বিরুদ্ধে! মা-বাবা হয়তো মনোবিদের কাছে গিয়ে বলতে থাকেন, ‘আমাদের সন্তানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনুন!’ আমরা সবাই জানি, তরুণ-বর্ষীয়ান দ্বন্দ্বের প্রতিটি ঘটনাই আলাদা, তারপরও কিছু ব্যাপার থাকে, যেগুলোর মধ্য থেকে সাধারণ একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।
৩.
তরুণের এই অস্থিরতা একসময় কেটে যাবে—এটাই স্বতঃসিদ্ধ। অনেক অভিভাবকই মনে রাখেন না, তিনিও একসময় এ রকমই জীবন কাটিয়েছেন। মা-বাবা হওয়ার আগে তাঁরা ছিলেন কারও না কারও সন্তান।
অনেক অভিভাবকই টিনএজারদের মুখের কথায় দুঃখ পান। আসলে শব্দের গুরুত্ব বা ভার অনুভব না করেই তরুণেরা অনেক কথা বলে থাকে। বেশির ভাগ অভিভাবকই প্রচণ্ড কষ্ট পান সন্তানদের এ ধরনের কথোপকথনে। একটি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য যে সময় ও জায়গার দরকার আছে, তরুণমনে তার চাষবাস কেবল শুরু হয়। এ কারণেই আগে-পিছে না ভেবে সে যেকোনো কথা অনায়াসে বলে দিতে পারে। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, এ রকম সময় তার মনে মানুষের প্রতি ভালোবাসাও তীব্র। দুই প্রজন্মের এই দূরত্বের কারণ আসলে খুঁজতে হয় প্রতিটি ঘটনাকে আলাদা করেই। তবে, তরুণেরা সব মা-বাবার কথা শুনে লক্ষ্মী হয়ে উঠবে, এ রকম আশা না করে সে সমাজের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে, সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার।
৪.
শহুরে পরিবারগুলোয় একটা ব্যাপার এখন খুব দেখা যায়। সন্তানকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। তাকে আগলে রাখতে পছন্দ করেন অভিভাবকেরা। এর ফল হয় মারাত্মক। জীবনের নানা সংকট মোকাবিলা করার মতো করে এরা বেড়ে ওঠে না। শুধু জিপিএ-ফাইভ ঠিক থাকলেই হলো, বাকি সব গোল্লায় যাক—এই মনোভাবের কারণে সন্তান হয়তো তুখোড় বইপোকা হয়ে উঠবে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ কি গড়ে উঠবে? কেন বাড়ির বাজার সে করবে না? কেন বিলগুলো সে দেবে না? কেন ব্যাংক থেকে সে টাকা তুলে আনবে না? আমি এমনও বাবাকে দেখেছি, যিনি তাঁর ৩০ বছর বয়সী সন্তানের জন্য খাবারদাবার নিজে কিনে আনেন। মা ছেলের কাছে জানতে চান, অফিস থেকে ফিরে সে কী খাবে। এ রকম সংসারে সন্তান কেন দায়িত্ব নিয়ে বেড়ে উঠবে? সময়-সময় রান্নাবান্নাই বা সে করবে না কেন?
বাড়ির আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও পরিচিত হোক তরুণ। কত টাকা আসে সংসারে, কোথায় কত টাকা খরচ হয়, কীভাবে খরচ করলে একটু সঞ্চয় হয়, সঞ্চয় থেকে কতটা টাকা নিয়ে ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ও জানা থাকা দরকার সন্তানের। তাতে দুই প্রজন্মের সম্পর্ক নিবিড় হয়।
এসব কাজে তাকে উৎসাহ দিতে হবে। তাতে সন্তানের দিক থেকেও দায়িত্ববোধ বেড়ে উঠবে। সে পারিবারিক মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।
৫.
সন্তানকে ভুল করার সুযোগ দিতে হবে। এই এক জায়গায় এসে অভিভাবকেরা মস্ত ভুল করে থাকেন। তাঁরা মনেই করেন, তাঁর সন্তান কোনো ভুল করতে পারে না। অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানের ভুলকে অপরাধ গণ্য করে তাকে বকাবকি করেন। এর পরিমাণ হয় খুব খারাপ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবক আর সন্তানদের মধ্যে এই কারণে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ভুল করার পর তা নিয়ে বারবার কথা বলারও অভ্যাস আছে অনেক অভিভাবকের।
আর একটা ব্যাপারেও অভিভাবকদের একচেটিয়া রাজত্ব। তুলনা। অন্যের সন্তানের সঙ্গে নিজের সন্তানের তুলনা করে সন্তানের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেওয়া এবং তাকে হতাশা বা ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এ কথা অধিকাংশ অভিভাবকই বুঝতে পারেন না। বর্তমানে তরুণ বয়সে ডিপ্রেশনের রোগী কেন বেড়ে গেছে, তা খোঁজ করলেই বোঝা যাবে, এর পেছনে মা-বাবার অবহেলাও কম দায়ী নয়।
উঠতি বয়সী সন্তান যদি মিথ্যে কথা বলে, তবে তার একটা বড় কারণ কিন্তু অভিভাবকের নিষ্ঠুর শাসন। অভিভাবকেরা এমন নিয়ন্ত্রণ আনতে চান সন্তানের ওপর, যা সন্তানের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তখন মা-বাবার দেখানো পথের বাইরে কিছু করলেই তাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। এ থেকে বের হওয়ার পথ কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে অভিভাবককেই। কড়া নিয়ন্ত্রণ বিগড়ে দিতে পারে উঠতি প্রজন্মকে।
৬.
‘তালগাছটা আমার’—সন্তানের সঙ্গে বিতর্কের ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা কিন্তু এই মনোভাব নিয়েই অগ্রসর হন। সন্তান যে বড় হয়েছে, গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব মতামত, সেদিকটাকে অগ্রাহ্য করা হয় বেশির ভাগ সময় এবং নিজের অভিমতটা সন্তানের ওপর চাপিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত যেন শান্তি নেই কারও। অভিভাবকেরা যদি মনে রাখেন, সন্তানের যুক্তিগুলো অধিকতর গ্রহণযোগ্য, তাহলে তা মেনে নিন। এতে যৌক্তিকভাবে নিজেকে বিকশিত করার পথ খুঁজে পাবে সন্তান।
অথচ এসব জায়গায় অভিভাবকেরা কী বলেন? বলেন, ‘আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না! আমার ভাবনাটাই ঠিক!’
এরপরও যদি কেউ মনে করেন, সন্তানই সব অশান্তির জন্য দায়ী, তাহলে গোড়ায় যে গলদ, তা কোনোকালেই
কাটবে না।
৭.
তরুণের জন্য তাদের এই বয়সে অভিভাবকেরাই সবচেয়ে দামি নন। শিশুকালে অভিভাবকদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার দিন আর নেই। এখন যারা তরুণের মন দখল করেছে, তাদের বড় অংশ সমবয়সীরা। নিজেদের ভাবনায়, ভাষায় পরিবর্তন এসেছে। আর এ জন্য গড়ে উঠেছে একটা ভিন্ন মনোজগৎ। যে জগতের ঠিকানা অধিকাংশ অভিভাবকেরই থাকে অজানা। ফলে, অভিভাবকদের সঙ্গে নিত্য ঠোকাঠুকির একটা বড় কারণ হলো, দুটো জগতে বসে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ দুই চোখে দেখছে দুই প্রজন্ম। নিজেদের কাছিয়ে আনার দায়িত্ব দুই পক্ষের ওপরই বর্তায়।
৮.
আরও বহু কিছু বলার আছে। কিন্তু থামা দরকার আরেকটা কথা বলেই। তরুণেরা বুঝে না-বুঝে অভিভাবকদের একটা পরীক্ষার সামনে দাঁড় করায়। বুঝতে চায়, সম্পর্ক কতটা নিবিড়। কিন্তু সন্তানের বাজে কাজে চোখ বন্ধ করে রাখা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়াও সন্তান লালনপালনের বড় শর্ত। অভিভাবক যখন কঠোর হচ্ছেন তাঁর সন্তানের প্রতি, তখনো সন্তান যেন অভিভাবকের ভালোবাসা আর স্নেহ বুঝতে পারে। সেই সঙ্গে তার দুঃখটাও।
আরেকটা ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কয়েকটি দেশের গবেষণায় দেখছি, তরুণেরা এখন স্মার্টফোন-লগ্ন হওয়ার সময়টিতে বইয়ের প্রতি যেমন কম আকৃষ্ট হচ্ছে, তেমনি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রতিও তাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। নতুন নতুন যেসব প্ল্যাটফর্মে সে আসছে-যাচ্ছে, তার মধ্যেও ভালো-মন্দ আছে। অভিভাবকেরা কি জানেন, তাদের এই গন্তব্যে কোথায় ভালো আর কোথায় মন্দ আছে?
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা
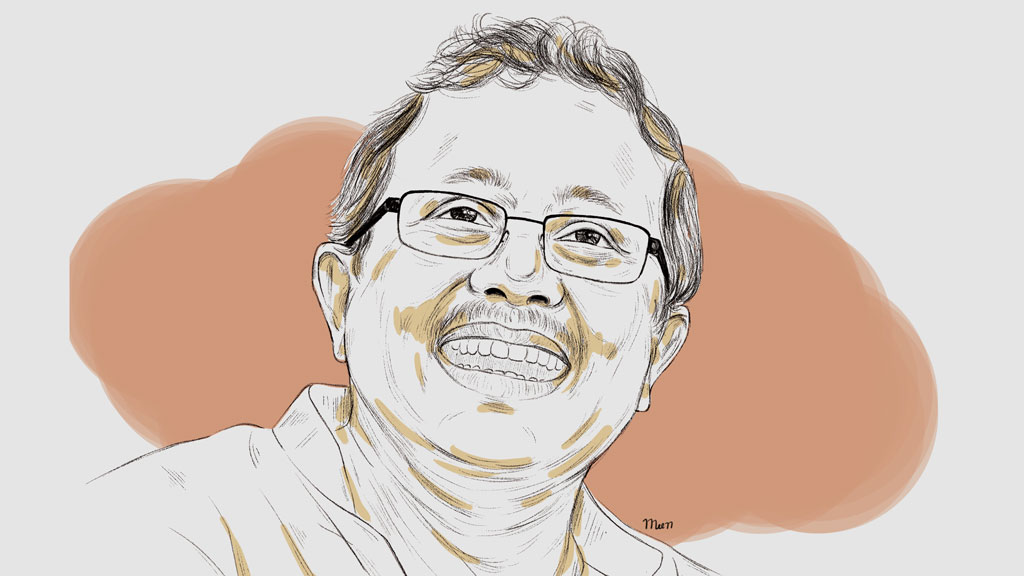
আমার এক প্রিয় তরুণ পোর্ট এলাকায় গিয়ে এমন কিছু খেয়েছিল, যাতে তার ফুড পয়জনিং হয়েছিল এবং তাকে দীর্ঘ সময় হাসপাতালের আইসিইউতে থাকতে হয়েছিল। সে যা সেবন করেছিল, তা ছিল ভয়ংকর কিছু। এ কারণে কিছুটা সুস্থ হলে ওকে নিয়ে মনোবিদের সঙ্গে বসার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে দুদিন যাওয়ার পর থেকেই তরুণটি সেখানে যেতে অনীহা প্রকাশ করতে থাকল। বলল, ‘মনোচিকিৎসক আপডেটেড নয়।’ বিশ্বে মনোরোগ নিয়ে গবেষণা কত দূর এগিয়েছে, তা নাকি এই চিকিৎসক জানেন না। তাই পুরোনো কালের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চাইছেন, যা তরুণের কোনো কাজে লাগবে না।
অসুস্থ সেই তরুণের হাতে একটা মনকাড়া বই তুলে দিলে ও কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে সেটা সরিয়ে রাখল। দুদিন পর ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, বইটা সেভাবেই পড়ে আছে।
২.
বইটা পড়েই থাকল। কেন পড়ে থাকল? বইয়ের প্রতি কি আকর্ষণ নেই এ সময়ের তরুণদের? ওরা আসলে কী নিয়ে ব্যস্ত?
সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু তরুণদের মনোজগৎটা যে বর্ষীয়ানদের কাছে অধরা হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আজ এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা হবে, যা পারিবারিক জীবনযাপনে প্রতিটি মানুষই দেখছেন, কিন্তু নতুন এই বাস্তবতা কীভাবে মোকাবিলা করবেন, তা নিয়ে সন্দিহান।
টিনএজ যেকোনো দেশে, যেকোনো পরিবারের জন্যই একটা ক্রান্তিকাল।
কে না জানে, অভিভাবকেরা চান, সন্তানেরা তাঁদের কথামতো চলুক আর তরুণেরা চায় অভিভাবকহীন ওড়ার আকাশ। তরুণদের ঘরগুলো থাকে অপরিচ্ছন্ন, কারণে-অকারণে ওরা মিথ্যে বলে, কখনো কখনো চুরি করে—এ রকম কত অভিযোগ রয়েছে তরুণদের বিরুদ্ধে! মা-বাবা হয়তো মনোবিদের কাছে গিয়ে বলতে থাকেন, ‘আমাদের সন্তানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনুন!’ আমরা সবাই জানি, তরুণ-বর্ষীয়ান দ্বন্দ্বের প্রতিটি ঘটনাই আলাদা, তারপরও কিছু ব্যাপার থাকে, যেগুলোর মধ্য থেকে সাধারণ একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।
৩.
তরুণের এই অস্থিরতা একসময় কেটে যাবে—এটাই স্বতঃসিদ্ধ। অনেক অভিভাবকই মনে রাখেন না, তিনিও একসময় এ রকমই জীবন কাটিয়েছেন। মা-বাবা হওয়ার আগে তাঁরা ছিলেন কারও না কারও সন্তান।
অনেক অভিভাবকই টিনএজারদের মুখের কথায় দুঃখ পান। আসলে শব্দের গুরুত্ব বা ভার অনুভব না করেই তরুণেরা অনেক কথা বলে থাকে। বেশির ভাগ অভিভাবকই প্রচণ্ড কষ্ট পান সন্তানদের এ ধরনের কথোপকথনে। একটি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য যে সময় ও জায়গার দরকার আছে, তরুণমনে তার চাষবাস কেবল শুরু হয়। এ কারণেই আগে-পিছে না ভেবে সে যেকোনো কথা অনায়াসে বলে দিতে পারে। খেয়াল করলেই দেখা যাবে, এ রকম সময় তার মনে মানুষের প্রতি ভালোবাসাও তীব্র। দুই প্রজন্মের এই দূরত্বের কারণ আসলে খুঁজতে হয় প্রতিটি ঘটনাকে আলাদা করেই। তবে, তরুণেরা সব মা-বাবার কথা শুনে লক্ষ্মী হয়ে উঠবে, এ রকম আশা না করে সে সমাজের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে, সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার।
৪.
শহুরে পরিবারগুলোয় একটা ব্যাপার এখন খুব দেখা যায়। সন্তানকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। তাকে আগলে রাখতে পছন্দ করেন অভিভাবকেরা। এর ফল হয় মারাত্মক। জীবনের নানা সংকট মোকাবিলা করার মতো করে এরা বেড়ে ওঠে না। শুধু জিপিএ-ফাইভ ঠিক থাকলেই হলো, বাকি সব গোল্লায় যাক—এই মনোভাবের কারণে সন্তান হয়তো তুখোড় বইপোকা হয়ে উঠবে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ কি গড়ে উঠবে? কেন বাড়ির বাজার সে করবে না? কেন বিলগুলো সে দেবে না? কেন ব্যাংক থেকে সে টাকা তুলে আনবে না? আমি এমনও বাবাকে দেখেছি, যিনি তাঁর ৩০ বছর বয়সী সন্তানের জন্য খাবারদাবার নিজে কিনে আনেন। মা ছেলের কাছে জানতে চান, অফিস থেকে ফিরে সে কী খাবে। এ রকম সংসারে সন্তান কেন দায়িত্ব নিয়ে বেড়ে উঠবে? সময়-সময় রান্নাবান্নাই বা সে করবে না কেন?
বাড়ির আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গেও পরিচিত হোক তরুণ। কত টাকা আসে সংসারে, কোথায় কত টাকা খরচ হয়, কীভাবে খরচ করলে একটু সঞ্চয় হয়, সঞ্চয় থেকে কতটা টাকা নিয়ে ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ও জানা থাকা দরকার সন্তানের। তাতে দুই প্রজন্মের সম্পর্ক নিবিড় হয়।
এসব কাজে তাকে উৎসাহ দিতে হবে। তাতে সন্তানের দিক থেকেও দায়িত্ববোধ বেড়ে উঠবে। সে পারিবারিক মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।
৫.
সন্তানকে ভুল করার সুযোগ দিতে হবে। এই এক জায়গায় এসে অভিভাবকেরা মস্ত ভুল করে থাকেন। তাঁরা মনেই করেন, তাঁর সন্তান কোনো ভুল করতে পারে না। অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানের ভুলকে অপরাধ গণ্য করে তাকে বকাবকি করেন। এর পরিমাণ হয় খুব খারাপ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবক আর সন্তানদের মধ্যে এই কারণে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ভুল করার পর তা নিয়ে বারবার কথা বলারও অভ্যাস আছে অনেক অভিভাবকের।
আর একটা ব্যাপারেও অভিভাবকদের একচেটিয়া রাজত্ব। তুলনা। অন্যের সন্তানের সঙ্গে নিজের সন্তানের তুলনা করে সন্তানের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেওয়া এবং তাকে হতাশা বা ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এ কথা অধিকাংশ অভিভাবকই বুঝতে পারেন না। বর্তমানে তরুণ বয়সে ডিপ্রেশনের রোগী কেন বেড়ে গেছে, তা খোঁজ করলেই বোঝা যাবে, এর পেছনে মা-বাবার অবহেলাও কম দায়ী নয়।
উঠতি বয়সী সন্তান যদি মিথ্যে কথা বলে, তবে তার একটা বড় কারণ কিন্তু অভিভাবকের নিষ্ঠুর শাসন। অভিভাবকেরা এমন নিয়ন্ত্রণ আনতে চান সন্তানের ওপর, যা সন্তানের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তখন মা-বাবার দেখানো পথের বাইরে কিছু করলেই তাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। এ থেকে বের হওয়ার পথ কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে অভিভাবককেই। কড়া নিয়ন্ত্রণ বিগড়ে দিতে পারে উঠতি প্রজন্মকে।
৬.
‘তালগাছটা আমার’—সন্তানের সঙ্গে বিতর্কের ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা কিন্তু এই মনোভাব নিয়েই অগ্রসর হন। সন্তান যে বড় হয়েছে, গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব মতামত, সেদিকটাকে অগ্রাহ্য করা হয় বেশির ভাগ সময় এবং নিজের অভিমতটা সন্তানের ওপর চাপিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত যেন শান্তি নেই কারও। অভিভাবকেরা যদি মনে রাখেন, সন্তানের যুক্তিগুলো অধিকতর গ্রহণযোগ্য, তাহলে তা মেনে নিন। এতে যৌক্তিকভাবে নিজেকে বিকশিত করার পথ খুঁজে পাবে সন্তান।
অথচ এসব জায়গায় অভিভাবকেরা কী বলেন? বলেন, ‘আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না! আমার ভাবনাটাই ঠিক!’
এরপরও যদি কেউ মনে করেন, সন্তানই সব অশান্তির জন্য দায়ী, তাহলে গোড়ায় যে গলদ, তা কোনোকালেই
কাটবে না।
৭.
তরুণের জন্য তাদের এই বয়সে অভিভাবকেরাই সবচেয়ে দামি নন। শিশুকালে অভিভাবকদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার দিন আর নেই। এখন যারা তরুণের মন দখল করেছে, তাদের বড় অংশ সমবয়সীরা। নিজেদের ভাবনায়, ভাষায় পরিবর্তন এসেছে। আর এ জন্য গড়ে উঠেছে একটা ভিন্ন মনোজগৎ। যে জগতের ঠিকানা অধিকাংশ অভিভাবকেরই থাকে অজানা। ফলে, অভিভাবকদের সঙ্গে নিত্য ঠোকাঠুকির একটা বড় কারণ হলো, দুটো জগতে বসে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ দুই চোখে দেখছে দুই প্রজন্ম। নিজেদের কাছিয়ে আনার দায়িত্ব দুই পক্ষের ওপরই বর্তায়।
৮.
আরও বহু কিছু বলার আছে। কিন্তু থামা দরকার আরেকটা কথা বলেই। তরুণেরা বুঝে না-বুঝে অভিভাবকদের একটা পরীক্ষার সামনে দাঁড় করায়। বুঝতে চায়, সম্পর্ক কতটা নিবিড়। কিন্তু সন্তানের বাজে কাজে চোখ বন্ধ করে রাখা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়াও সন্তান লালনপালনের বড় শর্ত। অভিভাবক যখন কঠোর হচ্ছেন তাঁর সন্তানের প্রতি, তখনো সন্তান যেন অভিভাবকের ভালোবাসা আর স্নেহ বুঝতে পারে। সেই সঙ্গে তার দুঃখটাও।
আরেকটা ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কয়েকটি দেশের গবেষণায় দেখছি, তরুণেরা এখন স্মার্টফোন-লগ্ন হওয়ার সময়টিতে বইয়ের প্রতি যেমন কম আকৃষ্ট হচ্ছে, তেমনি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রতিও তাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। নতুন নতুন যেসব প্ল্যাটফর্মে সে আসছে-যাচ্ছে, তার মধ্যেও ভালো-মন্দ আছে। অভিভাবকেরা কি জানেন, তাদের এই গন্তব্যে কোথায় ভালো আর কোথায় মন্দ আছে?
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। অনেকের কাছে এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীরা এই নির্বাচনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ওপর আস্থা রেখেছেন। নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল এবং নির্বাচনের পর ভোট গণনার সময় সারা রাত বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমার, শুধু আমার নয় বরং অনেকেরই। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, পাশ্চাত্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, তখন প্রথম দিন বড় বোনের কাছ থেকে শাড়ি এনে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলাম। সেই দিনের শিহরণ, অনুভূতি এখনো শরীর-মনে দোলা দেয়।
১৯ ঘণ্টা আগে
নির্বাচনের পরে যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। প্রস্তাব এসেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে। সমালোচনার মুখে সেই পথ থেকে সরে এসেছে সরকার। বাতিল করা হয়েছে গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। বহু দুঃসংবাদের মধ্যে এটি একটি সুসংবাদ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ধরনের এই কেনাকাটার বিষয়টি
২০ ঘণ্টা আগে
জাতীয় প্রেসক্লাবে ৭ সেপ্টেম্বর গণশক্তি আয়োজন করে ‘জুলাই সনদ ও নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা। সেই সভায় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না যে প্রশ্নটি করেছেন, তা কোটি টাকার সঙ্গে তুলনা করাই যায়। তাঁর সহজ জিজ্ঞাসা—‘ভোটের দিন যাঁর যেখানে শক্তি আছে, তাঁর যদি মনে হয় জিততে পারবেন না...
২ দিন আগে