জাহীদ রেজা নূর, ঢাকা

মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁকে সুবা বাংলার দেওয়ান করেছিলেন। নতুন দেওয়ান দেখলেন, বাংলার জমিদারেরা ঠিকভাবে খাজনা পরিশোধ করেন না। কী করে কর আদায় করা যায়, তা ভাবতে লাগলেন তিনি। প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন বাংলার সুবাদার বাদশাহের দৌহিত্র আজিমুশ্শান। তবে রাজস্ব আদায়ে সর্বেসর্বা ছিলেন দেওয়ান। তাই আর্থিক দিকগুলোর উন্নতি কী করে করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে থাকেন মুর্শিদকুলি খাঁ।
মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে বিরোধ ছিল বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত আজিমুশ্শানের। মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে তাঁর অফিস নিয়ে গেলেন মোজাফফরাবাদে। সে শহরের নাম দিলেন মুর্শিদাবাদ। ১৭১৭ সালে তিনি হলেন বাংলার সুবাদার। নবাব হিসেবেই পরিচিত হলেন তিনি। বাংলার রাজধানী হিসেবে পরিচিত হলো মুর্শিদাবাদ।
সে সময় নবাবের প্রশাসনে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমরা পৌঁছে যাব মূল আলোচনায়। সর্বক্ষেত্রে কেন মুসলমানেরা পিছিয়ে ছিলেন, তার একটা আভাস পাওয়া যাবে তাতে।
নবাবি শাসনামলে সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী শ্রেণি ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু বানিয়া, মুৎসুদ্দি, বড় জমিদার ও প্রশাসনিক আমলা গোষ্ঠী। মুসলিম নবাবেরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিয়ে একটি সুসংগঠিত আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন। প্রশাসনযন্ত্রে হিন্দু আমলাদের অন্তর্ভুক্তি এত দ্রুত ঘটেছিল যে, নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনামলে প্রশাসনে হিন্দু আমলারাই পেয়ে গিয়েছিলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এতে নবাবদের সঙ্গে হিন্দু প্রশাসন একত্র হতে পেরেছিল এবং রাষ্ট্র গঠনে তা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।
কেন প্রশাসনে মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল অপেক্ষাকৃত কম? খুব খেয়াল করলে দেখা যাবে, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় আভিজাত্য থেকে স্থানীয় মুসলিমদের দূরে রাখা হয়েছিল। নবাবি রাষ্ট্রের সামরিক ও বিচার বিভাগে ছিল মুসলিম আধিক্য। কিন্তু এই মুসলমানেরা স্থানীয় মুসলমান নন।
তাঁরা সবাই ছিলেন বাইরে থেকে আসা মুসলমান। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের রাখা হতো রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে দূরে। এ কাজটি করেছেন বাইরে থেকে আগত মুসলমানেরাই। তাঁরা স্থানীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছেন; কিন্তু বাদ দিয়েছিলেন স্থানীয় মুসলিমদেরকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া অন্য হিন্দুরাও বঞ্চিত হয়েছিলেন এ সময়।
নবাবি আমলে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বাইরে থেকে আসা মুসলমান ও অভিজাত হিন্দুদের মধ্যে। স্থানীয় মুসলিমরা ক্ষমতার ভাগ পাননি। তাই ব্রিটিশ উপনিবেশ শুরু হলো যখন, তখন তা স্থানীয় মুসলিমদের জন্য খুব বেশি উত্তেজনার কারণ ঘটায়নি। তাঁদের জন্য এটা ছিল এক মালিকের হাত থেকে আরেক মালিকের হাতে পড়ার মতো ব্যাপার। এতে তাঁরা হারাননি কিছু। যে তিমিরে ছিলেন তাঁরা, সেই তিমিরই তাঁদের ঘিরে রেখেছিল পরিবর্তনের পরও। বরং আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন যখন শ্বেতাঙ্গদের দিয়ে তৈরি হয়, তখন এর ভুক্তভোগী ছিল মূলত মুঘল ও হিন্দু অভিজাত শ্রেণি। হিন্দু অভিজাত আমলা শ্রেণি ক্ষমতা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এসে এই সর্বসময়ের নির্যাতিত স্থানীয় মুসলিমরা ভাবতে শুরু করলেন তাঁরা ক্ষমতা হারিয়েছেন। সে-ও এক ব্যাখ্যাহীন বিষয়। তবে রাজনীতির কৌশলী পথই যে এ রকম একটি মিথ্যাকে ভিত্তি দিয়েছিল, সে কথাই বলা হবে এবার।

মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁকে সুবা বাংলার দেওয়ান করেছিলেন। নতুন দেওয়ান দেখলেন, বাংলার জমিদারেরা ঠিকভাবে খাজনা পরিশোধ করেন না। কী করে কর আদায় করা যায়, তা ভাবতে লাগলেন তিনি। প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন বাংলার সুবাদার বাদশাহের দৌহিত্র আজিমুশ্শান। তবে রাজস্ব আদায়ে সর্বেসর্বা ছিলেন দেওয়ান। তাই আর্থিক দিকগুলোর উন্নতি কী করে করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে থাকেন মুর্শিদকুলি খাঁ।
মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে বিরোধ ছিল বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত আজিমুশ্শানের। মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে তাঁর অফিস নিয়ে গেলেন মোজাফফরাবাদে। সে শহরের নাম দিলেন মুর্শিদাবাদ। ১৭১৭ সালে তিনি হলেন বাংলার সুবাদার। নবাব হিসেবেই পরিচিত হলেন তিনি। বাংলার রাজধানী হিসেবে পরিচিত হলো মুর্শিদাবাদ।
সে সময় নবাবের প্রশাসনে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমরা পৌঁছে যাব মূল আলোচনায়। সর্বক্ষেত্রে কেন মুসলমানেরা পিছিয়ে ছিলেন, তার একটা আভাস পাওয়া যাবে তাতে।
নবাবি শাসনামলে সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী শ্রেণি ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু বানিয়া, মুৎসুদ্দি, বড় জমিদার ও প্রশাসনিক আমলা গোষ্ঠী। মুসলিম নবাবেরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিয়ে একটি সুসংগঠিত আমলাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন। প্রশাসনযন্ত্রে হিন্দু আমলাদের অন্তর্ভুক্তি এত দ্রুত ঘটেছিল যে, নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনামলে প্রশাসনে হিন্দু আমলারাই পেয়ে গিয়েছিলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এতে নবাবদের সঙ্গে হিন্দু প্রশাসন একত্র হতে পেরেছিল এবং রাষ্ট্র গঠনে তা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।
কেন প্রশাসনে মুসলিমদের উপস্থিতি ছিল অপেক্ষাকৃত কম? খুব খেয়াল করলে দেখা যাবে, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় আভিজাত্য থেকে স্থানীয় মুসলিমদের দূরে রাখা হয়েছিল। নবাবি রাষ্ট্রের সামরিক ও বিচার বিভাগে ছিল মুসলিম আধিক্য। কিন্তু এই মুসলমানেরা স্থানীয় মুসলমান নন।
তাঁরা সবাই ছিলেন বাইরে থেকে আসা মুসলমান। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের রাখা হতো রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে দূরে। এ কাজটি করেছেন বাইরে থেকে আগত মুসলমানেরাই। তাঁরা স্থানীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছেন; কিন্তু বাদ দিয়েছিলেন স্থানীয় মুসলিমদেরকে। উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া অন্য হিন্দুরাও বঞ্চিত হয়েছিলেন এ সময়।
নবাবি আমলে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয় বাইরে থেকে আসা মুসলমান ও অভিজাত হিন্দুদের মধ্যে। স্থানীয় মুসলিমরা ক্ষমতার ভাগ পাননি। তাই ব্রিটিশ উপনিবেশ শুরু হলো যখন, তখন তা স্থানীয় মুসলিমদের জন্য খুব বেশি উত্তেজনার কারণ ঘটায়নি। তাঁদের জন্য এটা ছিল এক মালিকের হাত থেকে আরেক মালিকের হাতে পড়ার মতো ব্যাপার। এতে তাঁরা হারাননি কিছু। যে তিমিরে ছিলেন তাঁরা, সেই তিমিরই তাঁদের ঘিরে রেখেছিল পরিবর্তনের পরও। বরং আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন যখন শ্বেতাঙ্গদের দিয়ে তৈরি হয়, তখন এর ভুক্তভোগী ছিল মূলত মুঘল ও হিন্দু অভিজাত শ্রেণি। হিন্দু অভিজাত আমলা শ্রেণি ক্ষমতা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এরপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এসে এই সর্বসময়ের নির্যাতিত স্থানীয় মুসলিমরা ভাবতে শুরু করলেন তাঁরা ক্ষমতা হারিয়েছেন। সে-ও এক ব্যাখ্যাহীন বিষয়। তবে রাজনীতির কৌশলী পথই যে এ রকম একটি মিথ্যাকে ভিত্তি দিয়েছিল, সে কথাই বলা হবে এবার।

সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) পুরোনো দুর্নীতির একটি ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। আজকের পত্রিকায় ১৯ আগস্ট প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০১৬ সালে সোনামসজিদ স্থলবন্দরে প্রায় ৪৫০ টন জুয়েলারি (গয়না) আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু অসাধু আমদানিকারকেরা ‘কৃত্রিম মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ আমদানির ভুয়া ঘোষণা...
৯ ঘণ্টা আগে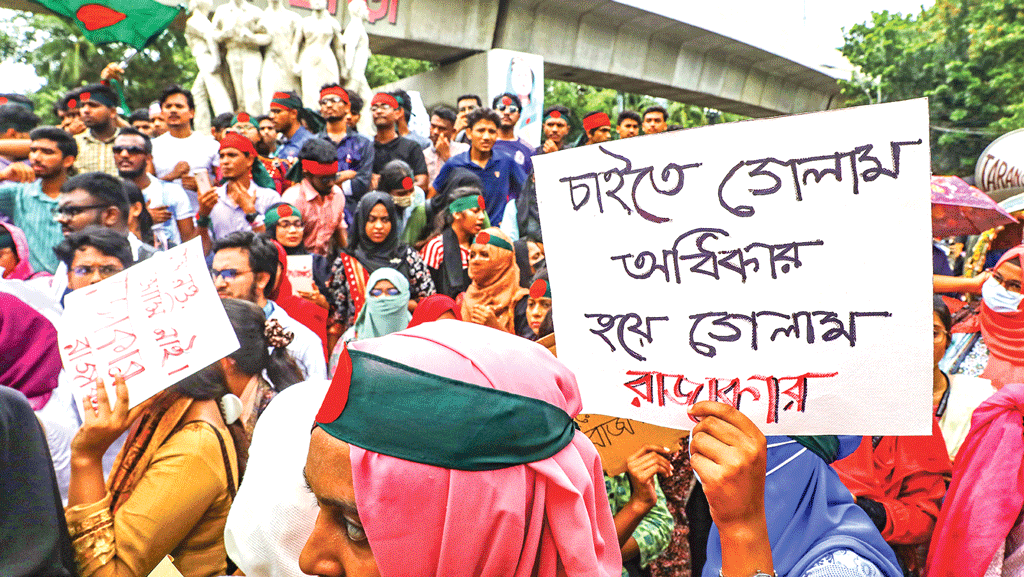
এই উপমহাদেশে সমবেত জনতার কণ্ঠে প্রতিবাদের যে ভাষা আমরা দেখি, অন্ত্যমিলসহ বা ছাড়া, তা আদতে, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘কাপলেট’, বাংলায় ‘দ্বিপদী’ সেটাই। স্বরবৃত্ত ছন্দে অন্ত্যমিলে স্লোগান রচনা করলে, সমবেত কণ্ঠে তার আবেদন বেশ জোরালো হয়। আর সে ক্ষেত্রে শব্দচয়ন যদি মিছরির ছুরির মতো হয়, তবে তো কথাই নেই।
৯ ঘণ্টা আগে
মানবতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৫ সালে গঠিত হয় জাতিসংঘ। বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসন ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকারের পক্ষে থাকাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। অথচ সবচেয়ে দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর দখলদারত্বের শিকার ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ।
৯ ঘণ্টা আগে
প্রাচীন মানুষ নিঃসঙ্গ অবস্থা থেকে যখন দলবদ্ধ হতে চেয়েছিল তাদের মাথায় কোন প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল? নিরাপত্তা, নিয়ম, স্বস্তি নাকি একসঙ্গে সবকিছু? হয়তো এভাবেই ধীরে ধীরে একসময় পরিবার তৈরি করে ফেলেছিল মানুষ! এর সঙ্গে তৈরি হয়েছিল সমাজও।
৯ ঘণ্টা আগে