বিধান রিবেরু
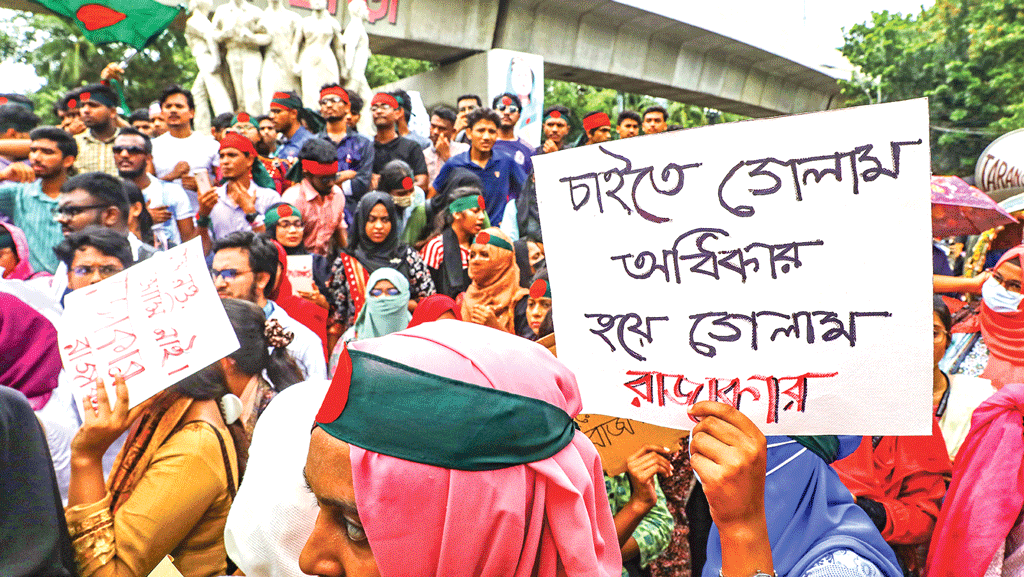
এই উপমহাদেশে সমবেত জনতার কণ্ঠে প্রতিবাদের যে ভাষা আমরা দেখি, অন্ত্যমিলসহ বা ছাড়া, তা আদতে, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘কাপলেট’, বাংলায় ‘দ্বিপদী’ সেটাই। স্বরবৃত্ত ছন্দে অন্ত্যমিলে স্লোগান রচনা করলে, সমবেত কণ্ঠে তার আবেদন বেশ জোরালো হয়। আর সে ক্ষেত্রে শব্দচয়ন যদি মিছরির ছুরির মতো হয়, তবে তো কথাই নেই। সাধারণত রাজনৈতিক মিছিলে আসা মানুষের মুখই মুখরিত হয় স্লোগানে। আন্দোলন ও সংগ্রামে স্লোগান, এক জায়গার জড়ো হওয়া জনতাকে ঐক্যের অনুভূতি দেয় এবং নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ে চিত্তকে আরও দৃঢ় করে। কালে কালে স্লোগান পাল্টেছে, কারণ যুগে যুগে মানুষের সংকট পরিবর্তন হয়েছে, সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তিত হয়েছে। তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনাকে প্রতিপক্ষের সামনে সম্মিলিত সুরে ছন্দের মাত্রায় বেঁধে জানান দিয়ে আসছে বহুকাল ধরেই। আমরা যদি ১৮৫৭ সালে যাই, দেখব উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধে সিপাহিরা সম্মিলিত কণ্ঠে বলেছিল: ইনকিলাব জিন্দাবাদ, শব্দবন্ধটি হিন্দুস্তানি। তবে অনেকের ধারণা আরবি ‘ইকলাব’ শব্দ থেকে ‘ইনকিলাব’ শব্দটির উদ্ভব। ইকলাবের আসল অর্থ ‘পরিবর্তন’। অপরদিকে ‘জিন্দাবাদ’ শব্দটি উর্দু ও ফারসি ভাষার মিশ্রণ। ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানের বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’।
সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানটি শোনা যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা-কর্মীদের মুখে। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে তাঁরাই সম্ভব করে তুলেছিলেন। তাঁরা ও তাঁদের সমভাবাপন্ন রাজনীতিমনস্ক শিক্ষার্থীদের কণ্ঠেই আমরা গত বছর শুনেছিলাম: আমি কে তুমি কে/রাজাকার রাজাকার/কে বলেছে, কে বলেছে/স্বৈরাচার স্বৈরাচার। এই প্রজন্মই, যাদের আমরা জেন-জি বলে জানি, ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে যুক্ত ছিল। সে সময়ও তারা স্লোগান রচনা করেছে এবং রাজপথে ব্যবহার করেছে। সম্ভবত তখন থেকেই তারা স্লোগানে ইংরেজিতে ‘স্ল্যাং’, ব্যবহার করতে শুরু করে। যার পরিণত রূপ আমরা দেখলাম এই কদিন আগে: এক, দুই, তিন, চার/অমুকের ... মার; অথবা টিনের চালে কাউয়া/অমুক একটা ...।
আরও অনেকের মতো আমিও মনে করি, ভাষা মানুষের মনোজগতে প্রবেশের প্রশস্ত দরজা। এই দরজা দিয়ে ঢুকে বোঝা যায় মানুষের মননের গঠন কেমন। জেন-জিদের একটি স্লোগানে আমরা দেখেছি ইনকিলাব ও জিন্দাবাদ শব্দের ব্যবহার। তারা নিজেরা ভারতবিদ্বেষী হলেও, ব্যবহার করছে ‘হিন্দুস্তানি স্লোগান’ এবং স্লোগানটির প্রথম ব্যবহারকারী কিন্তু ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্ম নেওয়া একজন বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও কবি মাওলানা হাসরাত মোহানি। তিনি এটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯২১ সালে। এরপর এই স্লোগান ব্যবহার করেন উপনিবেশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের নেতা ভগত সিং। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এখনো ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানটি ব্যবহার করে। সে জন্য এটা ভাবার কোনো কারণ নেই জাতীয় নাগরিক পার্টি কোনো সাম্যবাদী দল।
অনুপ্রেরণা যেকোনো জায়গা থেকে আসতে পারে এবং অনুপ্রাণিত হওয়া দোষের কিছু নয়। কিন্তু অন্ধ বিদ্বেষ অবশ্যই দোষের মধ্যে পড়ে এবং সেটি বিপজ্জনকও বটে। আরও বিপদের দেখা মেলে যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি অশ্রাব্য গালি স্থান করে নেয় স্লোগানে। অক্ষমের শেষ অস্ত্র হলো গালি। যখন কেউ খুব সহজেই নিজের ভাষায় গালাগালিকে স্থান দেয়, তখন বুঝতে হবে সে অথবা তারা ভাষাগত দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে, সৃজনশীলতা দূর হয়ে গেছে এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা, যা গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র, সেটিও তাদের ভেতর থেকে উবে গেছে।
যখন কেউ কারও সম্পর্কে মানহানিকর, বিশেষ করে অশ্রাব্য গালাগাল ব্যবহার করে, তখন তার সাংস্কৃতিক মান যেমন পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তেমনি তার রুচিও নগ্ন হয়ে পড়ে। গালাগালের ভেতর সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রকাশ পেলেও ভুলে গেলে চলবে না, স্লোগানে গালাগাল কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হয় না। খুব ভেবেচিন্তে সেসব স্লোগান রচনা করা হয় এবং সম্মিলিত কণ্ঠে সেসব উচ্চারিত হয়। একটি মিছিলে বা সমাবেশে ছোট ও বড় নানা বয়সী মানুষ থাকে। ছেলে ও মেয়ে থাকে। ভাবুন, তারা সবাই মিলে অশালীন গালাগালি করছে এবং অদ্ভুত বিষয়, এতে তারা প্রত্যেকেই যেন একত্রে একধরনের ‘যৌনসুখ’ অনুভব করছে।
স্লোগান কি কেবলই স্লোগান? এটি তো রাজনৈতিক সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নানা সময়ে নানা ধরনের স্লোগানে ধরা থাকে সময় ও কালের সংগ্রামী চেতনা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দে মাতরম’। পাকিস্তান আন্দোলনে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু স্লোগান নয়, রণধ্বনিতে পরিণত হয় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান। অসহযোগ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রচিত একটি স্লোগান: ‘তোমার আমার ঠিকানা/পদ্মা মেঘনা যমুনা’, কী চমৎকার শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে এখানে! কাব্যিক ঢঙের বাইরে গিয়েও হুমকি, ধমক ও শ্লেষের ঠাঁই মিলেছে তখনকার স্লোগানে। তবে সে সময়কার মধ্যপন্থী ও বামপন্থীদের দলগুলোর স্লোগানের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের স্লোগানে বিস্তর ফারাক লক্ষ করা যায়। একদল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য হুমকি দিচ্ছে, অন্যায্য চুক্তি বাতিল করার আলটিমেটাম দিচ্ছে, গণতান্ত্রিক দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে: ‘ডোন্ট থ্রো দ্য বেবি আউট উইদ দ্য বাথওয়াটার’, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের পরম ধন, সন্তানের মতো। মুক্তিযুদ্ধ যাদের নেতৃত্বে এসেছে, তারা যদি পরবর্তী সময়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও লুটেরা হয়ে ওঠে, তার মানে এই নয় যে তাদের বিতাড়িত করার পাশাপাশি আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধকেও বিতাড়িত করব। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আপামর জনসাধারণই করেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সেই অপচেষ্টাই আমরা জোরেশোরে হতে দেখছি। আজকাল ইউটিউবার, টিকটকাররাও ইতিহাসবেত্তা হয়ে উঠেছেন। নানা সময় তাঁরা নানা ধরনের ব্যবস্থাপত্র হাজির করছেন, আর সেটা দেখে হইহই করে সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে থাকা ব্যবহারকারীরা। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, যাঁরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্ববিরোধী ফতোয়া হাজির করছেন, তাঁদের সেই কর্মের পেছনে লাইক, কমেন্ট, ক্লিক ও রিচের ব্যবসা রয়েছে। যাঁর যত ‘অ্যাঙ্গেজমেন্ট’ তাঁর তত পয়সা উপার্জন। কাজেই অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁদের সার্বক্ষণিক উত্তেজনা উৎপাদন করতে হয়। এই উত্তেজনা উৎপাদন করতে গিয়ে তাঁরা অকপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করে চলেছেন। এই অস্থির ডিজিটাল সময়ে সবাই সেসব কনটেন্ট ক্রিয়েটরের হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা ঠাওরে পেছন পেছন চলে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপারে থাকা রহস্যঘেরা অজানা জগতে।
কারও যেন কোনো দায় নেই। ইতিহাসের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। একটা গোটা প্রজন্ম শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেল। মাতৃভাষায় দক্ষতা থাকার বিচারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আমরা যেন নিজেদের পতন নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি প্রতিদিন। পতনের একটি উৎকৃষ্ট নির্দেশক এই স্লোগান। যাঁরা এইসব স্লোগান ব্যবহার করছেন, তাঁরা বুঝতেই পারলেন না, ইতিহাসের পাতায় তাঁরা কলঙ্কিত অধ্যায়ের অংশ হয়ে গেলেন। এই অধ্যায়ের বেদনায় গোটা জাতি একদিন আক্রান্ত হবে। তত দিনে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।
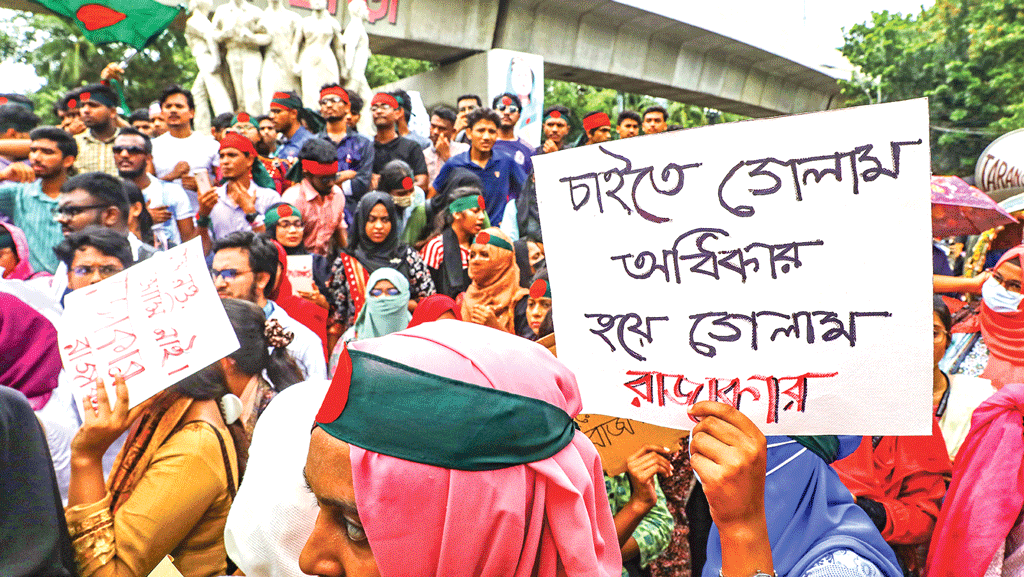
এই উপমহাদেশে সমবেত জনতার কণ্ঠে প্রতিবাদের যে ভাষা আমরা দেখি, অন্ত্যমিলসহ বা ছাড়া, তা আদতে, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘কাপলেট’, বাংলায় ‘দ্বিপদী’ সেটাই। স্বরবৃত্ত ছন্দে অন্ত্যমিলে স্লোগান রচনা করলে, সমবেত কণ্ঠে তার আবেদন বেশ জোরালো হয়। আর সে ক্ষেত্রে শব্দচয়ন যদি মিছরির ছুরির মতো হয়, তবে তো কথাই নেই। সাধারণত রাজনৈতিক মিছিলে আসা মানুষের মুখই মুখরিত হয় স্লোগানে। আন্দোলন ও সংগ্রামে স্লোগান, এক জায়গার জড়ো হওয়া জনতাকে ঐক্যের অনুভূতি দেয় এবং নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ে চিত্তকে আরও দৃঢ় করে। কালে কালে স্লোগান পাল্টেছে, কারণ যুগে যুগে মানুষের সংকট পরিবর্তন হয়েছে, সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তিত হয়েছে। তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনাকে প্রতিপক্ষের সামনে সম্মিলিত সুরে ছন্দের মাত্রায় বেঁধে জানান দিয়ে আসছে বহুকাল ধরেই। আমরা যদি ১৮৫৭ সালে যাই, দেখব উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধে সিপাহিরা সম্মিলিত কণ্ঠে বলেছিল: ইনকিলাব জিন্দাবাদ, শব্দবন্ধটি হিন্দুস্তানি। তবে অনেকের ধারণা আরবি ‘ইকলাব’ শব্দ থেকে ‘ইনকিলাব’ শব্দটির উদ্ভব। ইকলাবের আসল অর্থ ‘পরিবর্তন’। অপরদিকে ‘জিন্দাবাদ’ শব্দটি উর্দু ও ফারসি ভাষার মিশ্রণ। ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানের বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’।
সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানটি শোনা যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা-কর্মীদের মুখে। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে তাঁরাই সম্ভব করে তুলেছিলেন। তাঁরা ও তাঁদের সমভাবাপন্ন রাজনীতিমনস্ক শিক্ষার্থীদের কণ্ঠেই আমরা গত বছর শুনেছিলাম: আমি কে তুমি কে/রাজাকার রাজাকার/কে বলেছে, কে বলেছে/স্বৈরাচার স্বৈরাচার। এই প্রজন্মই, যাদের আমরা জেন-জি বলে জানি, ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে যুক্ত ছিল। সে সময়ও তারা স্লোগান রচনা করেছে এবং রাজপথে ব্যবহার করেছে। সম্ভবত তখন থেকেই তারা স্লোগানে ইংরেজিতে ‘স্ল্যাং’, ব্যবহার করতে শুরু করে। যার পরিণত রূপ আমরা দেখলাম এই কদিন আগে: এক, দুই, তিন, চার/অমুকের ... মার; অথবা টিনের চালে কাউয়া/অমুক একটা ...।
আরও অনেকের মতো আমিও মনে করি, ভাষা মানুষের মনোজগতে প্রবেশের প্রশস্ত দরজা। এই দরজা দিয়ে ঢুকে বোঝা যায় মানুষের মননের গঠন কেমন। জেন-জিদের একটি স্লোগানে আমরা দেখেছি ইনকিলাব ও জিন্দাবাদ শব্দের ব্যবহার। তারা নিজেরা ভারতবিদ্বেষী হলেও, ব্যবহার করছে ‘হিন্দুস্তানি স্লোগান’ এবং স্লোগানটির প্রথম ব্যবহারকারী কিন্তু ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্ম নেওয়া একজন বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও কবি মাওলানা হাসরাত মোহানি। তিনি এটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯২১ সালে। এরপর এই স্লোগান ব্যবহার করেন উপনিবেশবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের নেতা ভগত সিং। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এখনো ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগানটি ব্যবহার করে। সে জন্য এটা ভাবার কোনো কারণ নেই জাতীয় নাগরিক পার্টি কোনো সাম্যবাদী দল।
অনুপ্রেরণা যেকোনো জায়গা থেকে আসতে পারে এবং অনুপ্রাণিত হওয়া দোষের কিছু নয়। কিন্তু অন্ধ বিদ্বেষ অবশ্যই দোষের মধ্যে পড়ে এবং সেটি বিপজ্জনকও বটে। আরও বিপদের দেখা মেলে যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি অশ্রাব্য গালি স্থান করে নেয় স্লোগানে। অক্ষমের শেষ অস্ত্র হলো গালি। যখন কেউ খুব সহজেই নিজের ভাষায় গালাগালিকে স্থান দেয়, তখন বুঝতে হবে সে অথবা তারা ভাষাগত দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে, সৃজনশীলতা দূর হয়ে গেছে এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা, যা গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র, সেটিও তাদের ভেতর থেকে উবে গেছে।
যখন কেউ কারও সম্পর্কে মানহানিকর, বিশেষ করে অশ্রাব্য গালাগাল ব্যবহার করে, তখন তার সাংস্কৃতিক মান যেমন পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তেমনি তার রুচিও নগ্ন হয়ে পড়ে। গালাগালের ভেতর সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রকাশ পেলেও ভুলে গেলে চলবে না, স্লোগানে গালাগাল কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হয় না। খুব ভেবেচিন্তে সেসব স্লোগান রচনা করা হয় এবং সম্মিলিত কণ্ঠে সেসব উচ্চারিত হয়। একটি মিছিলে বা সমাবেশে ছোট ও বড় নানা বয়সী মানুষ থাকে। ছেলে ও মেয়ে থাকে। ভাবুন, তারা সবাই মিলে অশালীন গালাগালি করছে এবং অদ্ভুত বিষয়, এতে তারা প্রত্যেকেই যেন একত্রে একধরনের ‘যৌনসুখ’ অনুভব করছে।
স্লোগান কি কেবলই স্লোগান? এটি তো রাজনৈতিক সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নানা সময়ে নানা ধরনের স্লোগানে ধরা থাকে সময় ও কালের সংগ্রামী চেতনা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় ‘জয় হিন্দ’, ‘বন্দে মাতরম’। পাকিস্তান আন্দোলনে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু স্লোগান নয়, রণধ্বনিতে পরিণত হয় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান। অসহযোগ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রচিত একটি স্লোগান: ‘তোমার আমার ঠিকানা/পদ্মা মেঘনা যমুনা’, কী চমৎকার শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে এখানে! কাব্যিক ঢঙের বাইরে গিয়েও হুমকি, ধমক ও শ্লেষের ঠাঁই মিলেছে তখনকার স্লোগানে। তবে সে সময়কার মধ্যপন্থী ও বামপন্থীদের দলগুলোর স্লোগানের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের স্লোগানে বিস্তর ফারাক লক্ষ করা যায়। একদল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য হুমকি দিচ্ছে, অন্যায্য চুক্তি বাতিল করার আলটিমেটাম দিচ্ছে, গণতান্ত্রিক দাবি মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে: ‘ডোন্ট থ্রো দ্য বেবি আউট উইদ দ্য বাথওয়াটার’, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের পরম ধন, সন্তানের মতো। মুক্তিযুদ্ধ যাদের নেতৃত্বে এসেছে, তারা যদি পরবর্তী সময়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও লুটেরা হয়ে ওঠে, তার মানে এই নয় যে তাদের বিতাড়িত করার পাশাপাশি আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধকেও বিতাড়িত করব। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আপামর জনসাধারণই করেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সেই অপচেষ্টাই আমরা জোরেশোরে হতে দেখছি। আজকাল ইউটিউবার, টিকটকাররাও ইতিহাসবেত্তা হয়ে উঠেছেন। নানা সময় তাঁরা নানা ধরনের ব্যবস্থাপত্র হাজির করছেন, আর সেটা দেখে হইহই করে সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে থাকা ব্যবহারকারীরা। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, যাঁরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্ববিরোধী ফতোয়া হাজির করছেন, তাঁদের সেই কর্মের পেছনে লাইক, কমেন্ট, ক্লিক ও রিচের ব্যবসা রয়েছে। যাঁর যত ‘অ্যাঙ্গেজমেন্ট’ তাঁর তত পয়সা উপার্জন। কাজেই অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁদের সার্বক্ষণিক উত্তেজনা উৎপাদন করতে হয়। এই উত্তেজনা উৎপাদন করতে গিয়ে তাঁরা অকপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করে চলেছেন। এই অস্থির ডিজিটাল সময়ে সবাই সেসব কনটেন্ট ক্রিয়েটরের হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালা ঠাওরে পেছন পেছন চলে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপারে থাকা রহস্যঘেরা অজানা জগতে।
কারও যেন কোনো দায় নেই। ইতিহাসের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। একটা গোটা প্রজন্ম শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেল। মাতৃভাষায় দক্ষতা থাকার বিচারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আমরা যেন নিজেদের পতন নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি প্রতিদিন। পতনের একটি উৎকৃষ্ট নির্দেশক এই স্লোগান। যাঁরা এইসব স্লোগান ব্যবহার করছেন, তাঁরা বুঝতেই পারলেন না, ইতিহাসের পাতায় তাঁরা কলঙ্কিত অধ্যায়ের অংশ হয়ে গেলেন। এই অধ্যায়ের বেদনায় গোটা জাতি একদিন আক্রান্ত হবে। তত দিনে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) পুরোনো দুর্নীতির একটি ঘটনা বেরিয়ে এসেছে। আজকের পত্রিকায় ১৯ আগস্ট প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০১৬ সালে সোনামসজিদ স্থলবন্দরে প্রায় ৪৫০ টন জুয়েলারি (গয়না) আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু অসাধু আমদানিকারকেরা ‘কৃত্রিম মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ’ আমদানির ভুয়া ঘোষণা...
৩ ঘণ্টা আগে
মানবতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৫ সালে গঠিত হয় জাতিসংঘ। বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসন ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকারের পক্ষে থাকাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। অথচ সবচেয়ে দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর দখলদারত্বের শিকার ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ।
৪ ঘণ্টা আগে
প্রাচীন মানুষ নিঃসঙ্গ অবস্থা থেকে যখন দলবদ্ধ হতে চেয়েছিল তাদের মাথায় কোন প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল? নিরাপত্তা, নিয়ম, স্বস্তি নাকি একসঙ্গে সবকিছু? হয়তো এভাবেই ধীরে ধীরে একসময় পরিবার তৈরি করে ফেলেছিল মানুষ! এর সঙ্গে তৈরি হয়েছিল সমাজও।
৪ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধই ছিল পৃথিবীতে প্রথম বড় ধরনের সামরিক সংঘাত। ১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বরের জাতিসংঘ প্রস্তাবের নাম করে বস্তুত ব্রিটিশ ও মার্কিন মদদে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতেই ওই যুদ্ধের শুরু এবং একধরনের...
১ দিন আগে