ইসলাম ডেস্ক

রোজার বিধান মহানবী (সা.)-এর আনীত ধর্ম ইসলামেই রয়েছে, এমনটি নয়। প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অনেক নবী-রাসুলের আমলেই রোজার বিধানের কথা জানা যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের জন্য রোজা ফরজ করেন, তখন সেদিকে ইঙ্গিত করে মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, ‘হে ইমানদারগণ, তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরজ করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’ (সুরা বাকারা: ১৮৩)
আদম (আ.)-এর সময়ে রোজা
প্রথম নবী হজরত আদম (আ.)-এর ধর্মে রোজার বিধান দেওয়া হয়েছিল বলে তাফসির গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সেই রোজার ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল—তা জানা যায় না। এ বিষয়ে বাইবেল, কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, আগের যুগের প্রত্যেক নবীর ধর্মেই চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার বিধান ছিল। এই রোজা আইয়ামে বিজের রোজা নামে পরিচিত।
নুহ (আ.)-এর সময়ে রোজা
তাফসিরে ইবনে কাসিরে এসেছে, প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদ মুয়াজ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আতা (রহ.), কাতাদা (রহ.) ও দহহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, হজরত নুহ (আ.) থেকে শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার বিধান ছিল। পরে তা রমজানের রোজার বিধানের মাধ্যমে রহিত হয়। (ইবনে কাসির: ১ / ৪৯৭) ; কুরতুবি : ২ / ২৭৫) ; তাবারি: ৩ / ৪১১), তাফসিরুল মানার : ২ / ১১৬)
অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত নুহ (আ.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন বাদে সারা বছর রোজা রাখতেন। (ইবনে মাজাহ : ১৭১৪)
তবে আলবানি বলেছেন, হাদিসটির সনদ দুর্বল।
ইবরাহিম (আ.)-এর সময়ে রোজা
মুসলিম জাতির পিতা সহিফাপ্রাপ্ত নবী হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর যুগে ৩০টি রোজা ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইবরাহিম (আ.)-এর প্রতি রমজানের ১ তারিখ সহিফা অবতীর্ণ হয়। এ জন্য তিনি রমজানের ১ তারিখ রোজা রাখতেন। তাঁর অনুসারীদের জন্য ১, ২ ও ৩ রমজান রোজা রাখা ফরজ ছিল। নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তির স্মরণে ১০ মহররম তিনি ও তাঁর অনুসারীদের জন্য রোজা রাখা ফরজ ছিল। কোরবানির স্মরণে ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজসহ মোট সাত দিন ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাক (আ.)-এর উম্মতের জন্য রোজা ফরজ ছিল।
দাউদ (আ.)-এর সময়ে রোজা
আসমানি কিতাব যবুরপ্রাপ্ত নবী হজরত দাউদ (আ.)-এর সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি এক দিন রোজা রাখতেন এবং এক দিন বিনা রোজায় থাকতেন।’ (মুসলিম: ১১৫৯) অর্থাৎ, নবী দাউদ (আ.) সারা বছর একদিন পরপর রোজা রাখতেন।
মুসা (আ.)-এর সময়ে রোজা
ইহুদিদের জন্য প্রতি শনিবার, বছরের মধ্যে মহররমের ১০ তারিখে আশুরার দিন এবং অন্যান্য সময় রোজা ফরজ ছিল। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করে ইহুদিদের আশুরার দিনে রোজা রাখতে দেখলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ তোমরা কিসের রোজা রাখছ?’ তারা বলল, ‘এটা সেই মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে বনি ইসরাইল ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বরূপ মুসা (আ.) ওই দিনে রোজা রেখেছিলেন, তাই আমরা আজ রোজা রাখছি।’ এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘আমি তোমাদের চেয়ে মুসা (আ.)-এর অধিক নিকটজন।’ এরপর তিনি এই দিন রোজা রাখলেন এবং সবাইকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। (বুখারি: ২০০৪ ; মুসলিম: ১১৩০)
এ ছাড়া মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে আল্লাহর কাছ থেকে তাওরাতপ্রাপ্তির আগে ৪০ দিন পানাহার ত্যাগ করেছিলেন বলে জানা যায়। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে বিষয়টি বর্ণিত আছে। ইহুদিরা সাধারণভাবে এই ৪০টি রোজা রাখা ভালো মনে করত। ৪০তম দিনটিতে রোজা রাখা তাদের জন্য ফরজ ছিল। ওই দিনটিকেই আশুরা বা দশম দিন বলা হয়। এ ছাড়া ইহুদি সহিফাতে অন্যান্য রোজারও সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।
ইসা (আ.)-এর সময়ে রোজা
আসমানি কিতাব ইঞ্জিলপ্রাপ্ত নবী হজরত ইসা (আ.)-এর যুগেও রোজার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসা (আ.)-এর অনুসারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায় রোজা রাখতেন। বর্তমানে তাদের মধ্যে দুই ধরনের রোজা প্রচলিত আছে।
প্রথমটি হলো, তাদের পিতার উপদেশে নির্দিষ্ট কয়েক দিন খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা, আর ইফতার হবে নিরামিষ দিয়ে, মাছ, মাংস ও দুগ্ধজাত জিনিস খাওয়া যাবে না। যেমন— বড় দিনের রোজা, তওবার রোজা, যা ৫৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয়; এমনিভাবে সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবারের রোজা। দ্বিতীয়টি হলো— খাদ্য থেকে বিরত থাকা, তবে মাছ ভক্ষণ করা যাবে। এই রোজার মধ্যে ছোট রোজা বা জন্মদিনের রোজা, যা ৪৩ দিন দীর্ঘায়িত হয়, দূতগণের রোজা, মারিয়ামের রোজা ইত্যাদি। তবে খ্রিষ্টান ধর্মে কোনো রোজাই ফরজ নয়। (তাফসিরে তাবারি : ৩ / ৪১১)
ইসা (আ.) ধর্ম প্রচারের শুরুতে ইঞ্জিল পাওয়ার আগে জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম সাধনা করেছিলেন। একদিন ইসা (আ.)-কে তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করেন যে, ‘আমরা অপবিত্র আত্মাকে কী করে বের করব?’ জবাবে তিনি বলেন, ‘তা দোয়া ও রোজা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না।’ (মথি: ৭-৬৬ ; সিরাতুন নবী, ৫ / ২৮৭-২৮৮)
সূত্র : আবদুল্লাহ আল-মামুন আল-আযহারী রচিত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে সাওম

রোজার বিধান মহানবী (সা.)-এর আনীত ধর্ম ইসলামেই রয়েছে, এমনটি নয়। প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অনেক নবী-রাসুলের আমলেই রোজার বিধানের কথা জানা যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের জন্য রোজা ফরজ করেন, তখন সেদিকে ইঙ্গিত করে মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, ‘হে ইমানদারগণ, তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ফরজ করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’ (সুরা বাকারা: ১৮৩)
আদম (আ.)-এর সময়ে রোজা
প্রথম নবী হজরত আদম (আ.)-এর ধর্মে রোজার বিধান দেওয়া হয়েছিল বলে তাফসির গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য সেই রোজার ধরন ও প্রকৃতি কেমন ছিল—তা জানা যায় না। এ বিষয়ে বাইবেল, কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের কিতাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, আগের যুগের প্রত্যেক নবীর ধর্মেই চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখার বিধান ছিল। এই রোজা আইয়ামে বিজের রোজা নামে পরিচিত।
নুহ (আ.)-এর সময়ে রোজা
তাফসিরে ইবনে কাসিরে এসেছে, প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদ মুয়াজ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আতা (রহ.), কাতাদা (রহ.) ও দহহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, হজরত নুহ (আ.) থেকে শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার বিধান ছিল। পরে তা রমজানের রোজার বিধানের মাধ্যমে রহিত হয়। (ইবনে কাসির: ১ / ৪৯৭) ; কুরতুবি : ২ / ২৭৫) ; তাবারি: ৩ / ৪১১), তাফসিরুল মানার : ২ / ১১৬)
অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত নুহ (আ.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন বাদে সারা বছর রোজা রাখতেন। (ইবনে মাজাহ : ১৭১৪)
তবে আলবানি বলেছেন, হাদিসটির সনদ দুর্বল।
ইবরাহিম (আ.)-এর সময়ে রোজা
মুসলিম জাতির পিতা সহিফাপ্রাপ্ত নবী হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর যুগে ৩০টি রোজা ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইবরাহিম (আ.)-এর প্রতি রমজানের ১ তারিখ সহিফা অবতীর্ণ হয়। এ জন্য তিনি রমজানের ১ তারিখ রোজা রাখতেন। তাঁর অনুসারীদের জন্য ১, ২ ও ৩ রমজান রোজা রাখা ফরজ ছিল। নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তির স্মরণে ১০ মহররম তিনি ও তাঁর অনুসারীদের জন্য রোজা রাখা ফরজ ছিল। কোরবানির স্মরণে ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজসহ মোট সাত দিন ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাক (আ.)-এর উম্মতের জন্য রোজা ফরজ ছিল।
দাউদ (আ.)-এর সময়ে রোজা
আসমানি কিতাব যবুরপ্রাপ্ত নবী হজরত দাউদ (আ.)-এর সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি এক দিন রোজা রাখতেন এবং এক দিন বিনা রোজায় থাকতেন।’ (মুসলিম: ১১৫৯) অর্থাৎ, নবী দাউদ (আ.) সারা বছর একদিন পরপর রোজা রাখতেন।
মুসা (আ.)-এর সময়ে রোজা
ইহুদিদের জন্য প্রতি শনিবার, বছরের মধ্যে মহররমের ১০ তারিখে আশুরার দিন এবং অন্যান্য সময় রোজা ফরজ ছিল। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করে ইহুদিদের আশুরার দিনে রোজা রাখতে দেখলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ তোমরা কিসের রোজা রাখছ?’ তারা বলল, ‘এটা সেই মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা মুসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে বনি ইসরাইল ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বরূপ মুসা (আ.) ওই দিনে রোজা রেখেছিলেন, তাই আমরা আজ রোজা রাখছি।’ এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘আমি তোমাদের চেয়ে মুসা (আ.)-এর অধিক নিকটজন।’ এরপর তিনি এই দিন রোজা রাখলেন এবং সবাইকে রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। (বুখারি: ২০০৪ ; মুসলিম: ১১৩০)
এ ছাড়া মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে আল্লাহর কাছ থেকে তাওরাতপ্রাপ্তির আগে ৪০ দিন পানাহার ত্যাগ করেছিলেন বলে জানা যায়। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে বিষয়টি বর্ণিত আছে। ইহুদিরা সাধারণভাবে এই ৪০টি রোজা রাখা ভালো মনে করত। ৪০তম দিনটিতে রোজা রাখা তাদের জন্য ফরজ ছিল। ওই দিনটিকেই আশুরা বা দশম দিন বলা হয়। এ ছাড়া ইহুদি সহিফাতে অন্যান্য রোজারও সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।
ইসা (আ.)-এর সময়ে রোজা
আসমানি কিতাব ইঞ্জিলপ্রাপ্ত নবী হজরত ইসা (আ.)-এর যুগেও রোজার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসা (আ.)-এর অনুসারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায় রোজা রাখতেন। বর্তমানে তাদের মধ্যে দুই ধরনের রোজা প্রচলিত আছে।
প্রথমটি হলো, তাদের পিতার উপদেশে নির্দিষ্ট কয়েক দিন খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা, আর ইফতার হবে নিরামিষ দিয়ে, মাছ, মাংস ও দুগ্ধজাত জিনিস খাওয়া যাবে না। যেমন— বড় দিনের রোজা, তওবার রোজা, যা ৫৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয়; এমনিভাবে সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবারের রোজা। দ্বিতীয়টি হলো— খাদ্য থেকে বিরত থাকা, তবে মাছ ভক্ষণ করা যাবে। এই রোজার মধ্যে ছোট রোজা বা জন্মদিনের রোজা, যা ৪৩ দিন দীর্ঘায়িত হয়, দূতগণের রোজা, মারিয়ামের রোজা ইত্যাদি। তবে খ্রিষ্টান ধর্মে কোনো রোজাই ফরজ নয়। (তাফসিরে তাবারি : ৩ / ৪১১)
ইসা (আ.) ধর্ম প্রচারের শুরুতে ইঞ্জিল পাওয়ার আগে জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম সাধনা করেছিলেন। একদিন ইসা (আ.)-কে তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করেন যে, ‘আমরা অপবিত্র আত্মাকে কী করে বের করব?’ জবাবে তিনি বলেন, ‘তা দোয়া ও রোজা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না।’ (মথি: ৭-৬৬ ; সিরাতুন নবী, ৫ / ২৮৭-২৮৮)
সূত্র : আবদুল্লাহ আল-মামুন আল-আযহারী রচিত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে সাওম

নামাজ বা সালাত অন্যতম প্রধান ফরজ ইবাদত। পবিত্র কোরআনের ৮২টি স্থানে নামাজের কথা উল্লেখ করে এর অপরিসীম গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যখন তোমরা সালাত (নামাজ) পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে, তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে।
১৫ ঘণ্টা আগে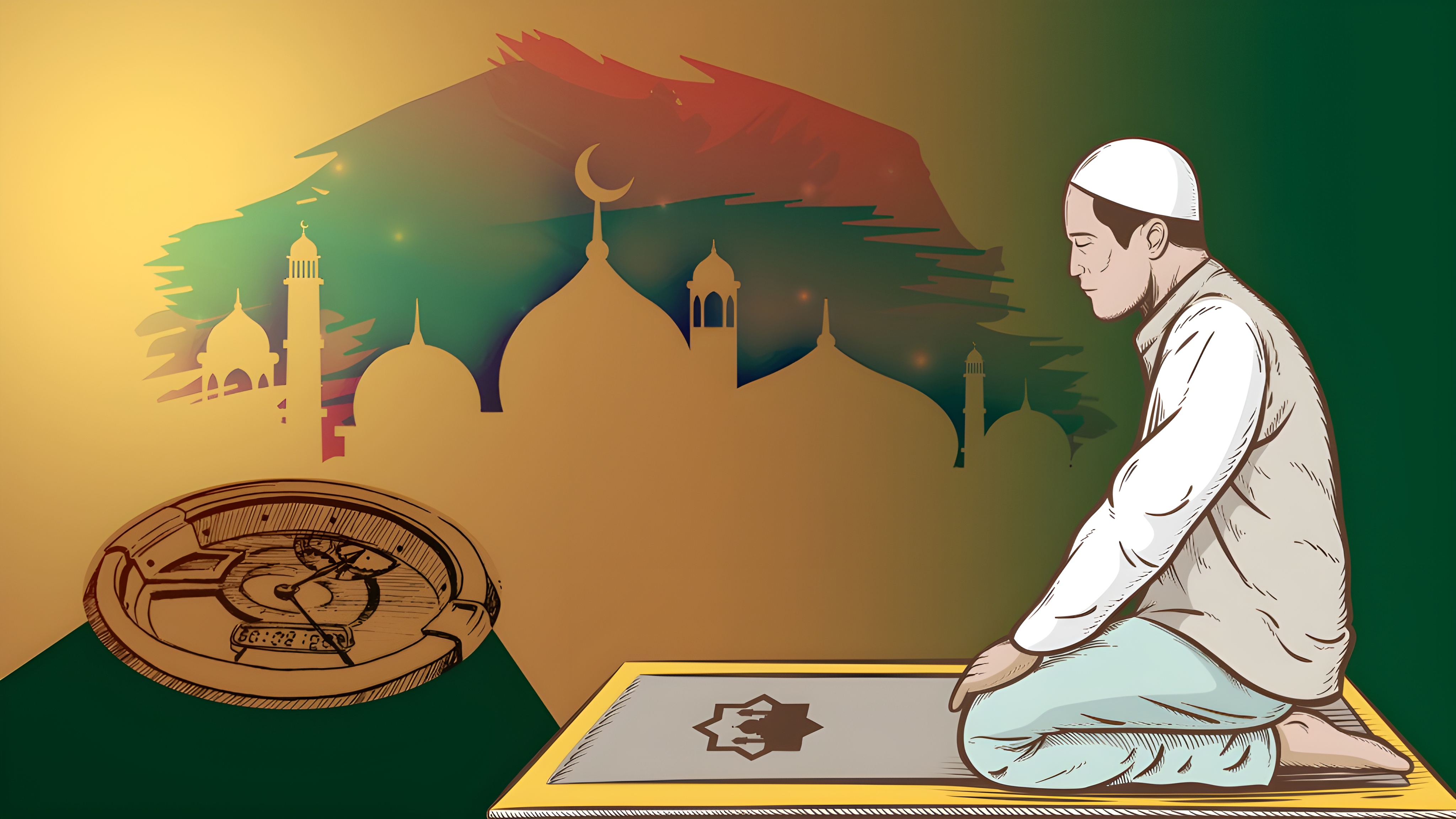
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
১ দিন আগে
ইসলামি শরিয়তে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং যারা নামাজে অবনত হয়...
২ দিন আগে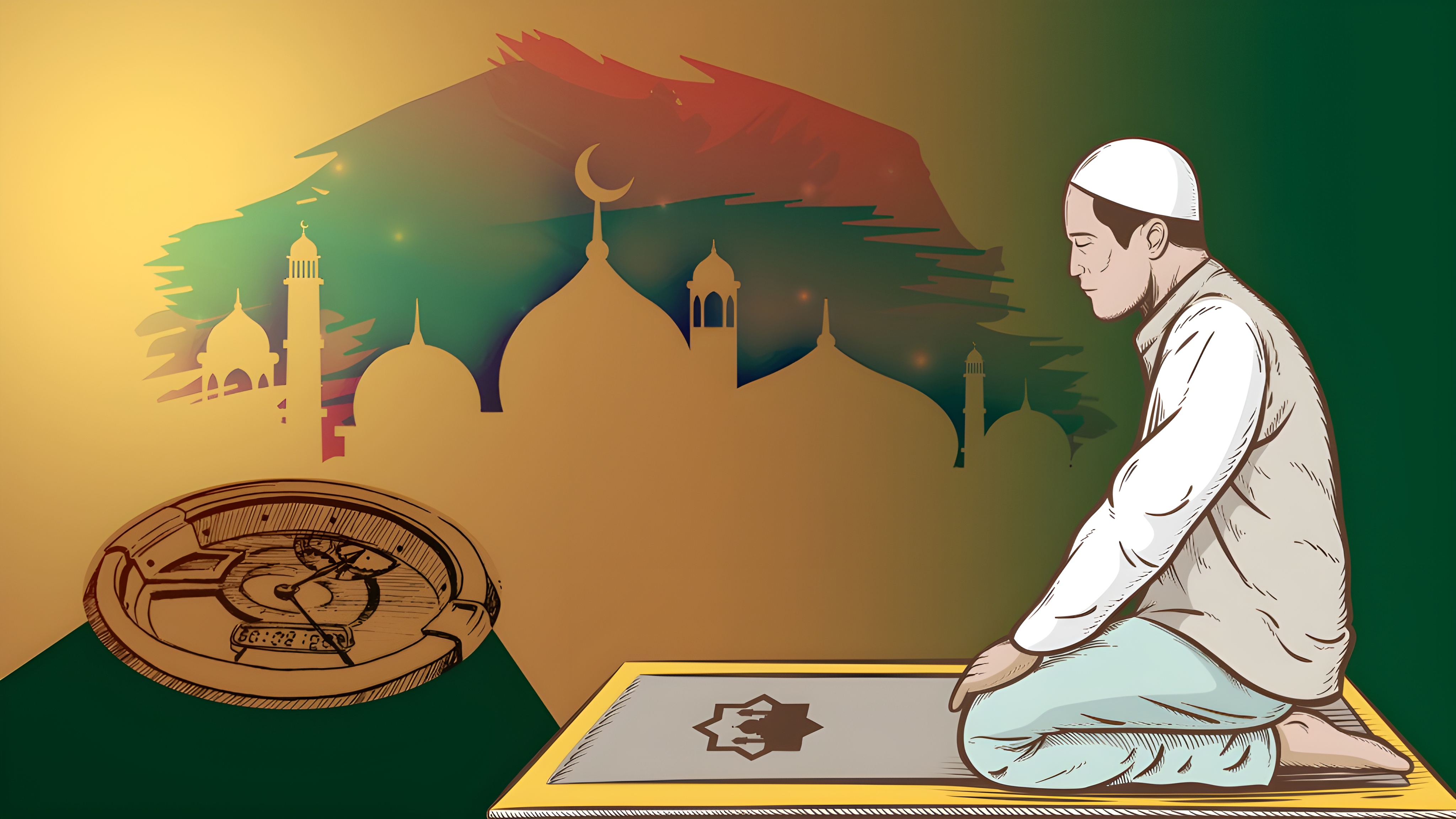
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
২ দিন আগেইসলাম ডেস্ক

নামাজ বা সালাত অন্যতম প্রধান ফরজ ইবাদত। পবিত্র কোরআনের ৮২টি স্থানে নামাজের কথা উল্লেখ করে এর অপরিসীম গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যখন তোমরা সালাত (নামাজ) পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে, তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।’ (সুরা নিসা: ১০৩)
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসেও বারবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়াক্তমতো নামাজ আদায়ের ওপর। এমনকি আল্লাহর কাছেও এটি অত্যন্ত প্রিয় একটি আমল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ‘যথাসময়ে সালাত আদায় করা।’ আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার।’ আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘এরপর কোনটি?’ রাসুল (সা.) বললেন, ‘আল্লাহর পথে লড়াই করা’। (সহিহ্ বুখারি: ৫০২)
নামাজ পড়া সত্ত্বেও তিন শ্রেণির নামাজির জন্য পরকালে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারি। এই তিন শ্রেণি হলো: ১. যারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করে। ২. যারা নামাজে চরম অমনোযোগী। ৩. যারা নামাজে চুরি করে, অর্থাৎ রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে না।
পবিত্র কোরআনে প্রথম দুই শ্রেণির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, ‘অতএব সেই নামাজ আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের নামাজে অমনোযোগী এবং যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।’ (সুরা মাউন: ৪-৬)
অন্যদিকে, তৃতীয় শ্রেণির নামাজি তথা নামাজ চোরদের সম্পর্কে আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘চোরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর হলো ওই ব্যক্তি, যে নামাজে চুরি করে।’ সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, নামাজে চুরি কীভাবে হয়?’ জবাবে নবীজি (সা.) বললেন, ‘নামাজে চুরি হলো রুকু-সিজদা পূর্ণ না করা (ঠিকমতো আদায় না করা)।’ (মিশকাতুল মাসাবিহ্: ৮৮৫)

নামাজ বা সালাত অন্যতম প্রধান ফরজ ইবাদত। পবিত্র কোরআনের ৮২টি স্থানে নামাজের কথা উল্লেখ করে এর অপরিসীম গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যখন তোমরা সালাত (নামাজ) পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে, তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।’ (সুরা নিসা: ১০৩)
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসেও বারবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওয়াক্তমতো নামাজ আদায়ের ওপর। এমনকি আল্লাহর কাছেও এটি অত্যন্ত প্রিয় একটি আমল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ‘যথাসময়ে সালাত আদায় করা।’ আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, ‘পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার।’ আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ‘এরপর কোনটি?’ রাসুল (সা.) বললেন, ‘আল্লাহর পথে লড়াই করা’। (সহিহ্ বুখারি: ৫০২)
নামাজ পড়া সত্ত্বেও তিন শ্রেণির নামাজির জন্য পরকালে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারি। এই তিন শ্রেণি হলো: ১. যারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করে। ২. যারা নামাজে চরম অমনোযোগী। ৩. যারা নামাজে চুরি করে, অর্থাৎ রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে না।
পবিত্র কোরআনে প্রথম দুই শ্রেণির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, ‘অতএব সেই নামাজ আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের নামাজে অমনোযোগী এবং যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।’ (সুরা মাউন: ৪-৬)
অন্যদিকে, তৃতীয় শ্রেণির নামাজি তথা নামাজ চোরদের সম্পর্কে আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘চোরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর হলো ওই ব্যক্তি, যে নামাজে চুরি করে।’ সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, নামাজে চুরি কীভাবে হয়?’ জবাবে নবীজি (সা.) বললেন, ‘নামাজে চুরি হলো রুকু-সিজদা পূর্ণ না করা (ঠিকমতো আদায় না করা)।’ (মিশকাতুল মাসাবিহ্: ৮৮৫)

প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অনেক নবী-রাসুলের আমলেই রোজার বিধানের কথা জানা যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের জন্য রোজা ফরজ করেন, তখন সেদিকে ইঙ্গিত করে মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন।
০৯ মার্চ ২০২৫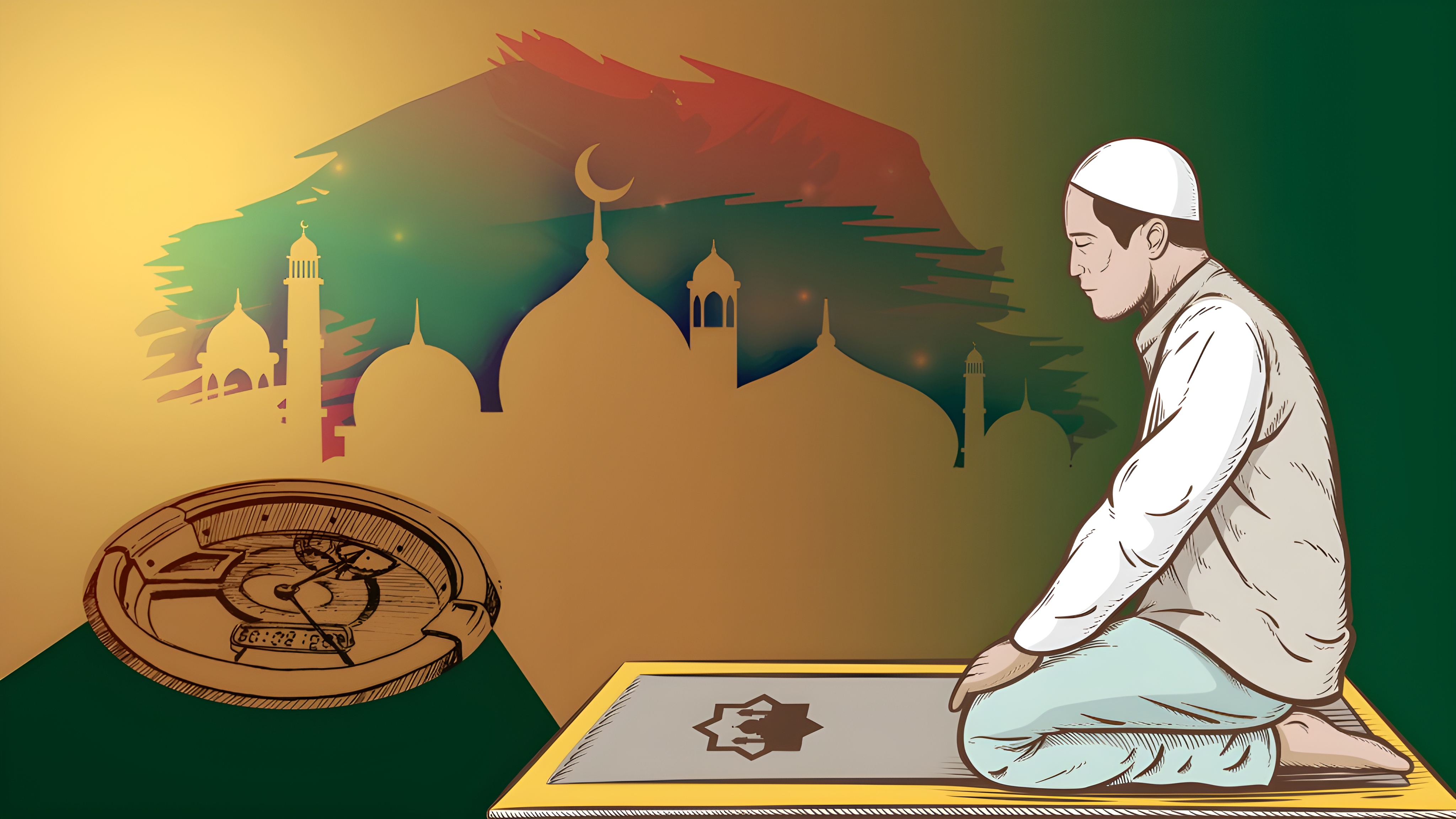
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
১ দিন আগে
ইসলামি শরিয়তে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং যারা নামাজে অবনত হয়...
২ দিন আগে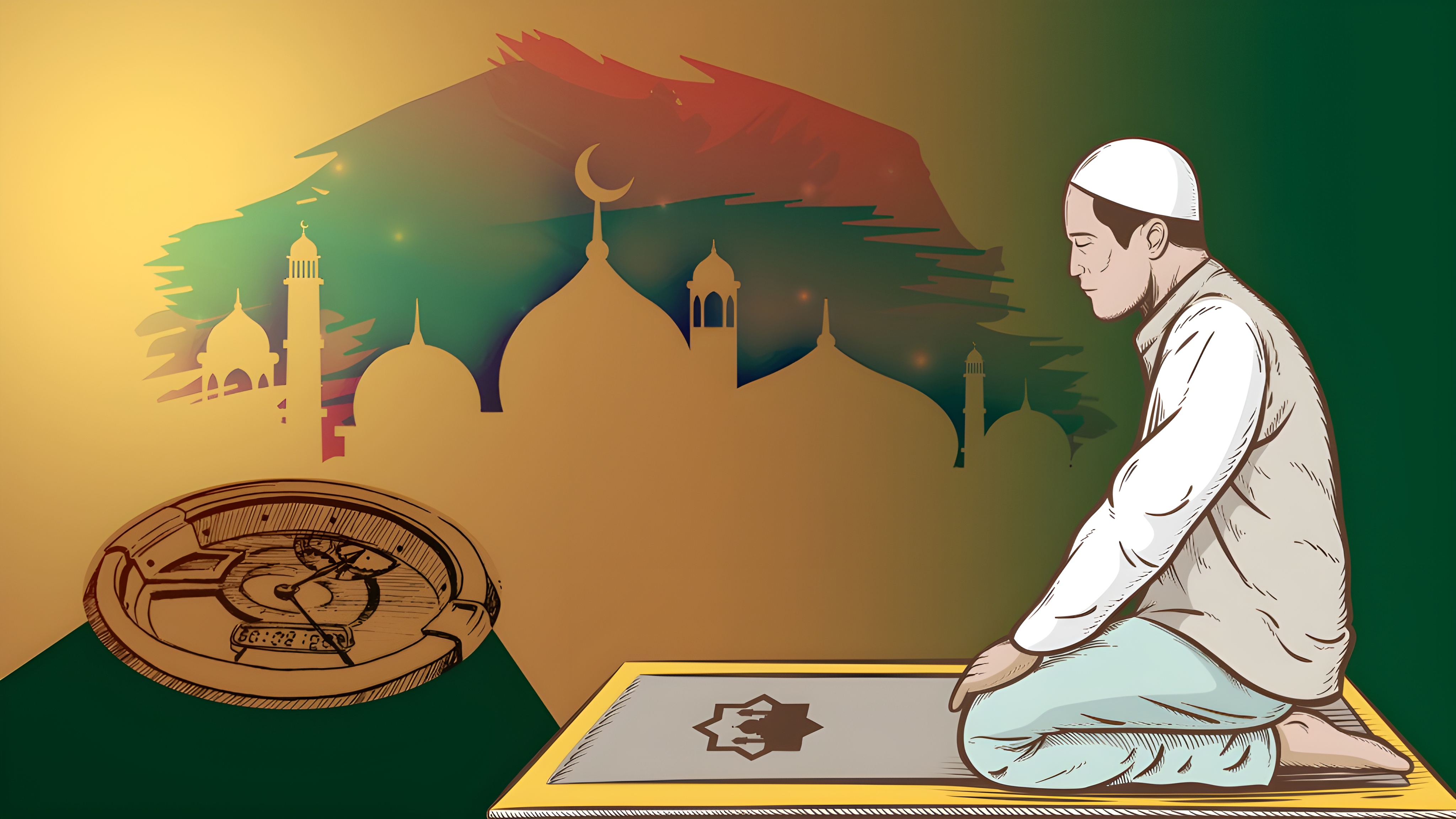
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
২ দিন আগেইসলাম ডেস্ক
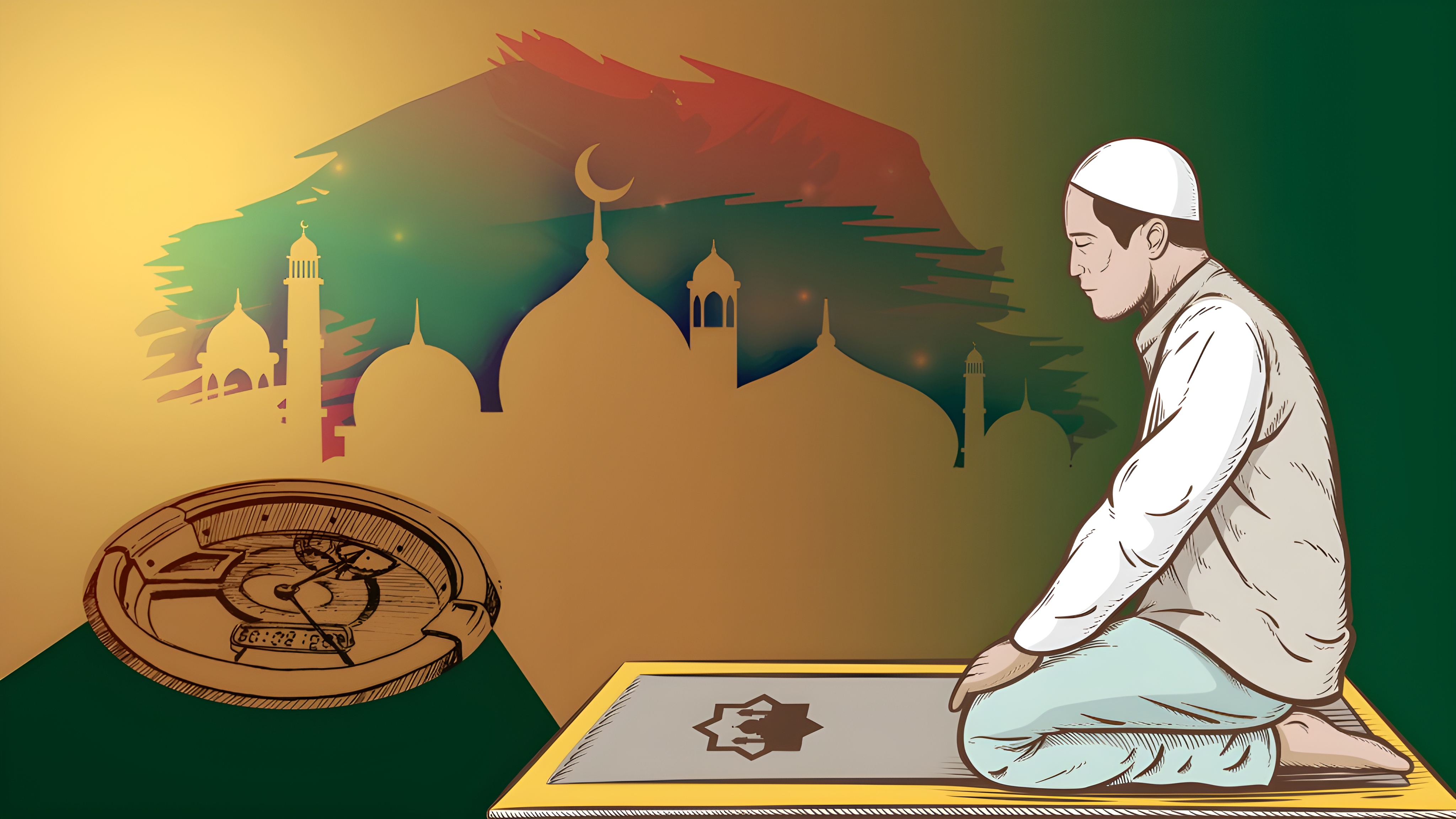
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৯ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ০৩ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
| নামাজ | ওয়াক্ত শুরু | ওয়াক্ত শেষ |
|---|---|---|
| তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় | ০০: ০০ | ০৫: ১৬ মিনিট |
| ফজর | ০৫: ১৭ মিনিট | ০৬: ৩৭ মিনিট |
| জোহর | ১১: ৫৯ মিনিট | ০৩: ৪১ মিনিট |
| আসর | ০৩: ৪২ মিনিট | ০৫: ১৭ মিনিট |
| মাগরিব | ০৫: ১৯ মিনিট | ০৬: ৩৮ মিনিট |
| এশা | ০৬: ৩৯ মিনিট | ০৫: ১৬ মিনিট |
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
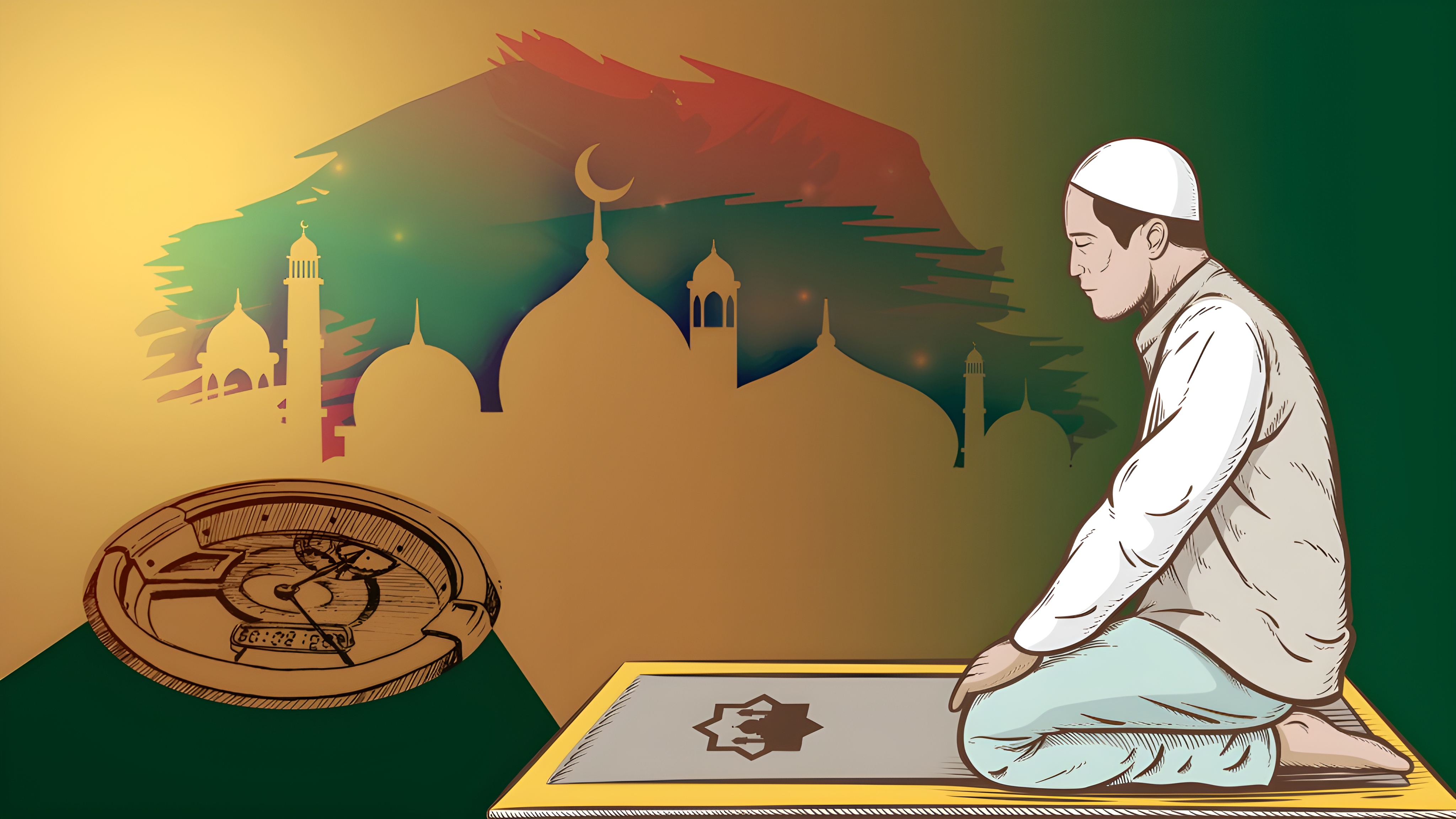
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৯ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ০৩ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
| নামাজ | ওয়াক্ত শুরু | ওয়াক্ত শেষ |
|---|---|---|
| তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় | ০০: ০০ | ০৫: ১৬ মিনিট |
| ফজর | ০৫: ১৭ মিনিট | ০৬: ৩৭ মিনিট |
| জোহর | ১১: ৫৯ মিনিট | ০৩: ৪১ মিনিট |
| আসর | ০৩: ৪২ মিনিট | ০৫: ১৭ মিনিট |
| মাগরিব | ০৫: ১৯ মিনিট | ০৬: ৩৮ মিনিট |
| এশা | ০৬: ৩৯ মিনিট | ০৫: ১৬ মিনিট |
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অনেক নবী-রাসুলের আমলেই রোজার বিধানের কথা জানা যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের জন্য রোজা ফরজ করেন, তখন সেদিকে ইঙ্গিত করে মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন।
০৯ মার্চ ২০২৫
নামাজ বা সালাত অন্যতম প্রধান ফরজ ইবাদত। পবিত্র কোরআনের ৮২টি স্থানে নামাজের কথা উল্লেখ করে এর অপরিসীম গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যখন তোমরা সালাত (নামাজ) পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে, তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে।
১৫ ঘণ্টা আগে
ইসলামি শরিয়তে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং যারা নামাজে অবনত হয়...
২ দিন আগে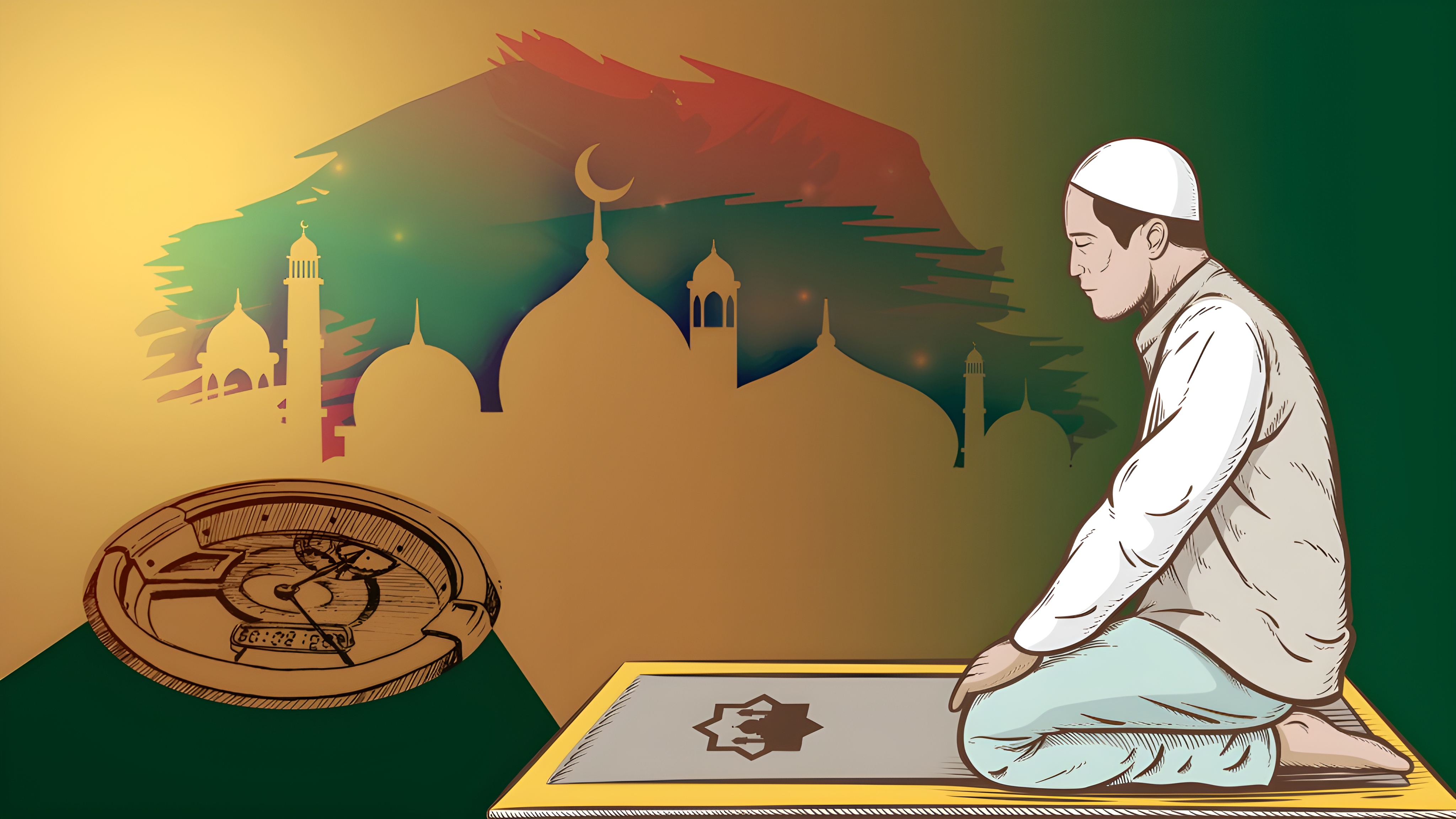
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
২ দিন আগেইসলাম ডেস্ক

ইসলামি শরিয়তে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং যারা নামাজে অবনত হয়, তাদের সঙ্গে তোমরাও অবনত হও।’ (সুরা বাকারা: ৪৩)
নামাজের প্রতি মুমিনের যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘সব নামাজের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের (আসর) ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়াও।’ (সুরা বাকারা: ২৩৮)
প্রতিদিন পাঁচবার আজানের মাধ্যমে মুসল্লিদের আল্লাহর ঘরের দিকে ডাকা হয়। আজানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা প্রতিটি মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব। নামাজ কবুল হওয়ার জন্য তা নির্দিষ্ট সময়ে বা ওয়াক্তমতো আদায় করা অপরিহার্য। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।’ (সুরা নিসা: ১০৩)
এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি, নামাজের জন্য ওয়াক্ত হওয়া শর্ত, আজান হওয়া নয়। আজানের মূল উদ্দেশ্য হলো জামাতের সঙ্গে ফরজ নামাজ আদায়ের আহ্বান জানানো। যদি কোনো কারণে আজান হতে দেরি হয়, কিন্তু নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তবে আজানের আগেই নামাজ আদায় করে নেওয়া বৈধ এবং নামাজ হয়ে যাবে। মূলত, একাকী নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে আজান হওয়া জরুরি নয়, বরং ওয়াক্ত শুরু হওয়াটাই আসল শর্ত। তবে ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামাজ আদায় করলে তা কবুল হবে না।

ইসলামি শরিয়তে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং যারা নামাজে অবনত হয়, তাদের সঙ্গে তোমরাও অবনত হও।’ (সুরা বাকারা: ৪৩)
নামাজের প্রতি মুমিনের যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘সব নামাজের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের (আসর) ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সঙ্গে দাঁড়াও।’ (সুরা বাকারা: ২৩৮)
প্রতিদিন পাঁচবার আজানের মাধ্যমে মুসল্লিদের আল্লাহর ঘরের দিকে ডাকা হয়। আজানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা প্রতিটি মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব। নামাজ কবুল হওয়ার জন্য তা নির্দিষ্ট সময়ে বা ওয়াক্তমতো আদায় করা অপরিহার্য। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।’ (সুরা নিসা: ১০৩)
এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি, নামাজের জন্য ওয়াক্ত হওয়া শর্ত, আজান হওয়া নয়। আজানের মূল উদ্দেশ্য হলো জামাতের সঙ্গে ফরজ নামাজ আদায়ের আহ্বান জানানো। যদি কোনো কারণে আজান হতে দেরি হয়, কিন্তু নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়, তবে আজানের আগেই নামাজ আদায় করে নেওয়া বৈধ এবং নামাজ হয়ে যাবে। মূলত, একাকী নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে আজান হওয়া জরুরি নয়, বরং ওয়াক্ত শুরু হওয়াটাই আসল শর্ত। তবে ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামাজ আদায় করলে তা কবুল হবে না।

প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অনেক নবী-রাসুলের আমলেই রোজার বিধানের কথা জানা যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের জন্য রোজা ফরজ করেন, তখন সেদিকে ইঙ্গিত করে মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন।
০৯ মার্চ ২০২৫
নামাজ বা সালাত অন্যতম প্রধান ফরজ ইবাদত। পবিত্র কোরআনের ৮২টি স্থানে নামাজের কথা উল্লেখ করে এর অপরিসীম গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যখন তোমরা সালাত (নামাজ) পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে, তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে।
১৫ ঘণ্টা আগে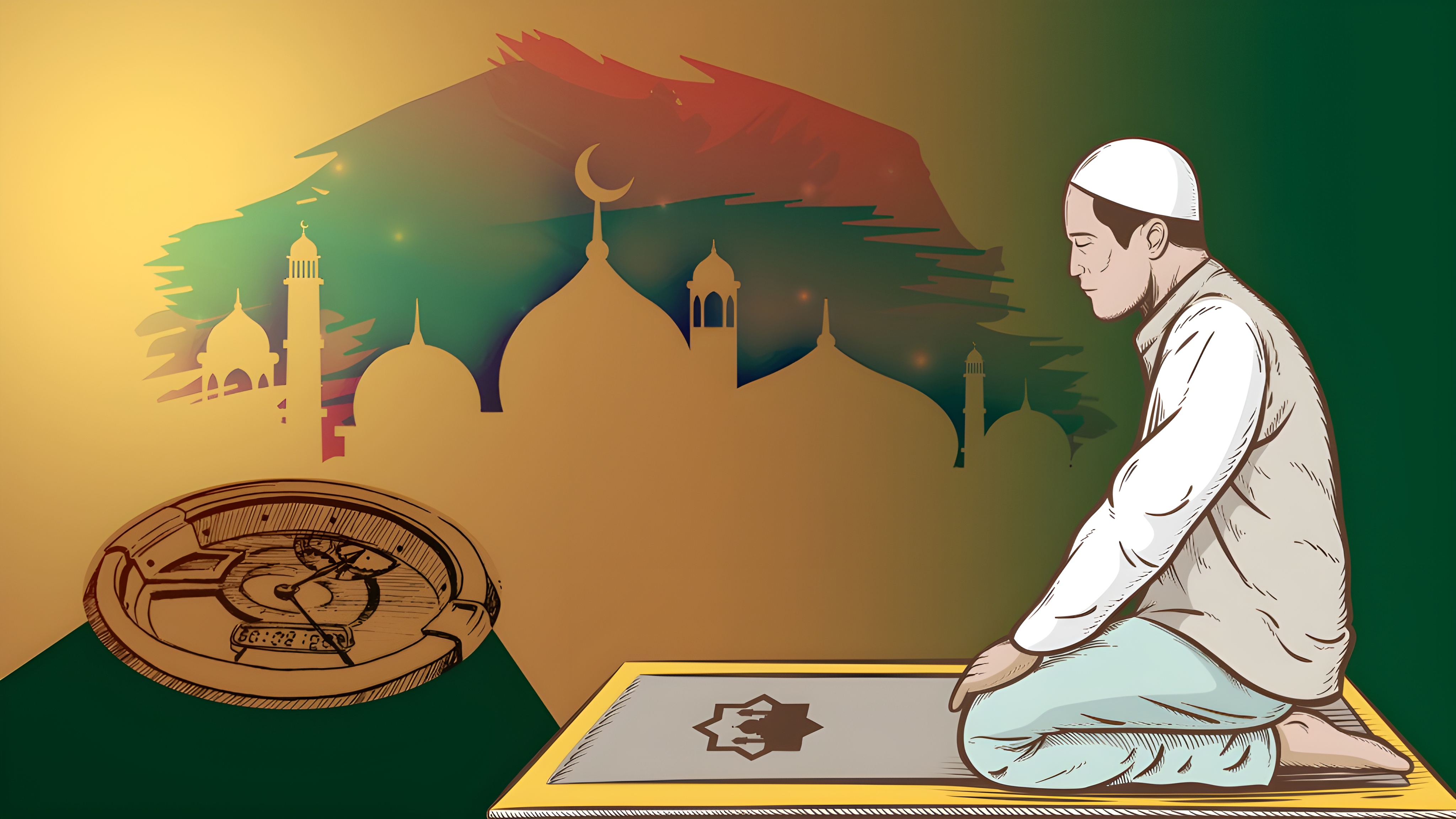
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
১ দিন আগে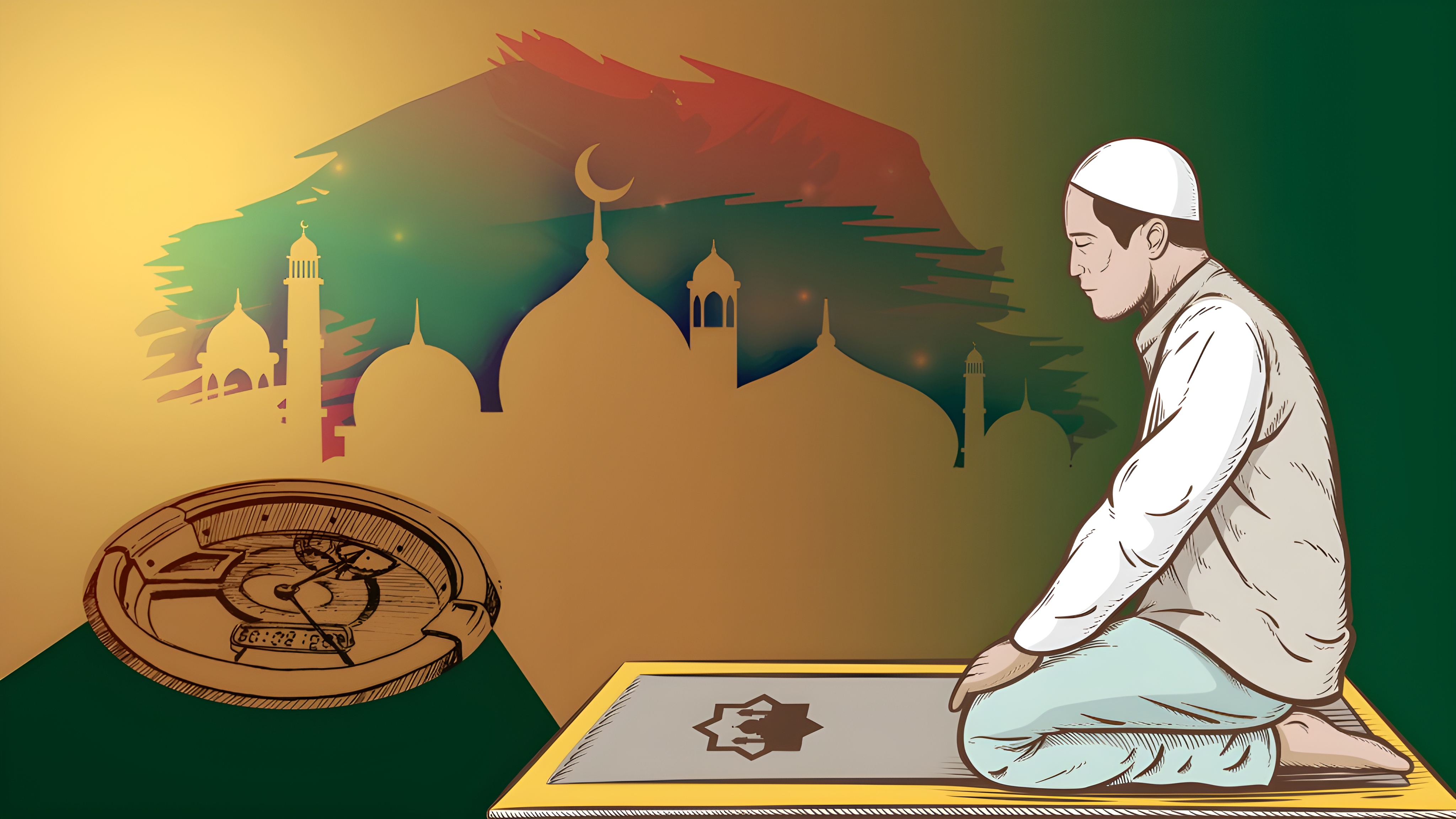
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
২ দিন আগেইসলাম ডেস্ক
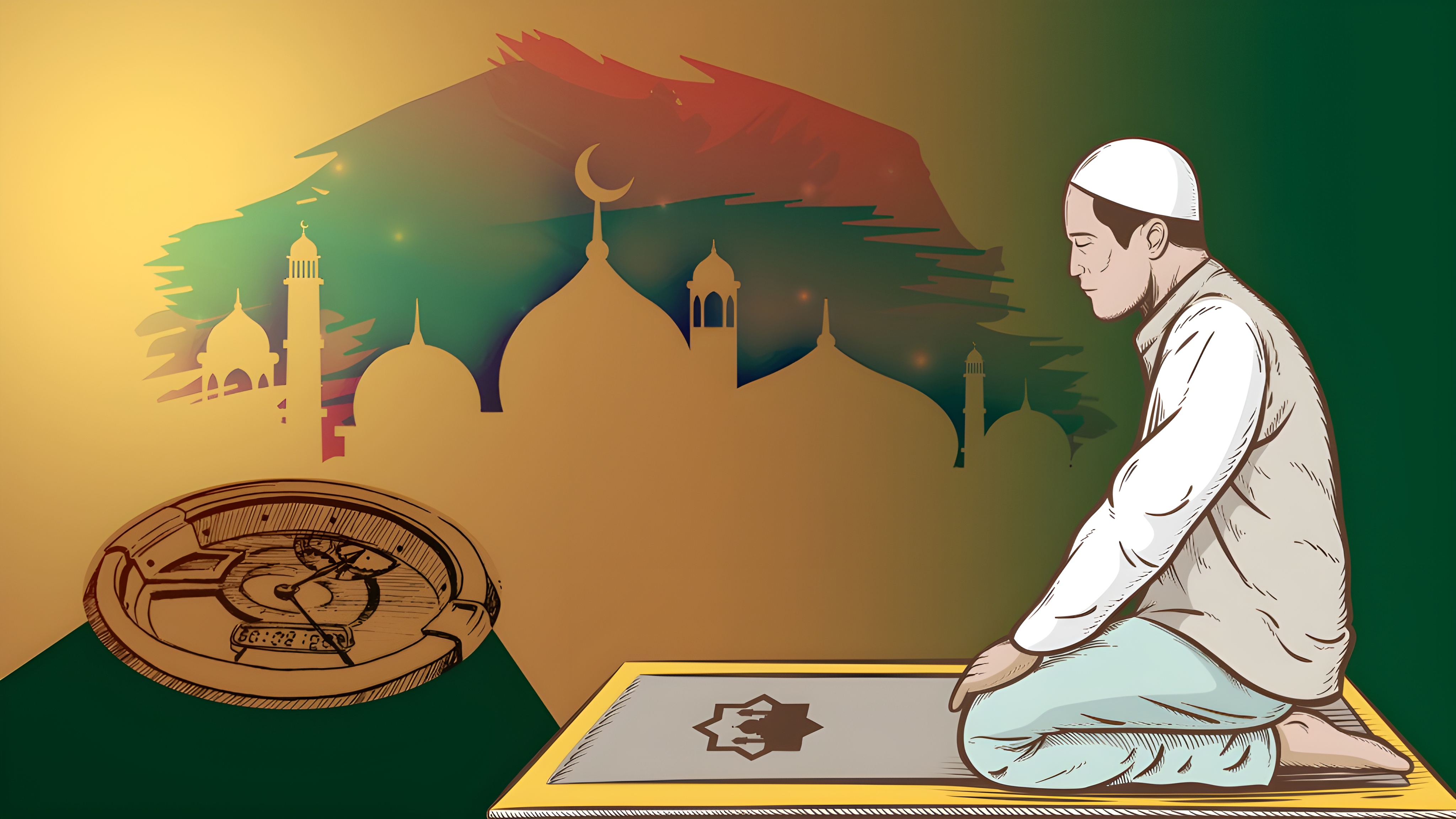
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৮ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ০২ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
| নামাজ | ওয়াক্ত শুরু | ওয়াক্ত শেষ |
|---|---|---|
| তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় | ০০: ০০ | ০৫: ১৫ মিনিট |
| ফজর | ০৫: ১৬ মিনিট | ০৬: ৩৬ মিনিট |
| জোহর | ১১: ৫৮ মিনিট | ০৩: ৪১ মিনিট |
| আসর | ০৩: ৪২ মিনিট | ০৫: ১৭ মিনিট |
| মাগরিব | ০৫: ১৯ মিনিট | ০৬: ৩৭ মিনিট |
| এশা | ০৬: ৩৮ মিনিট | ০৫: ১৫ মিনিট |
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
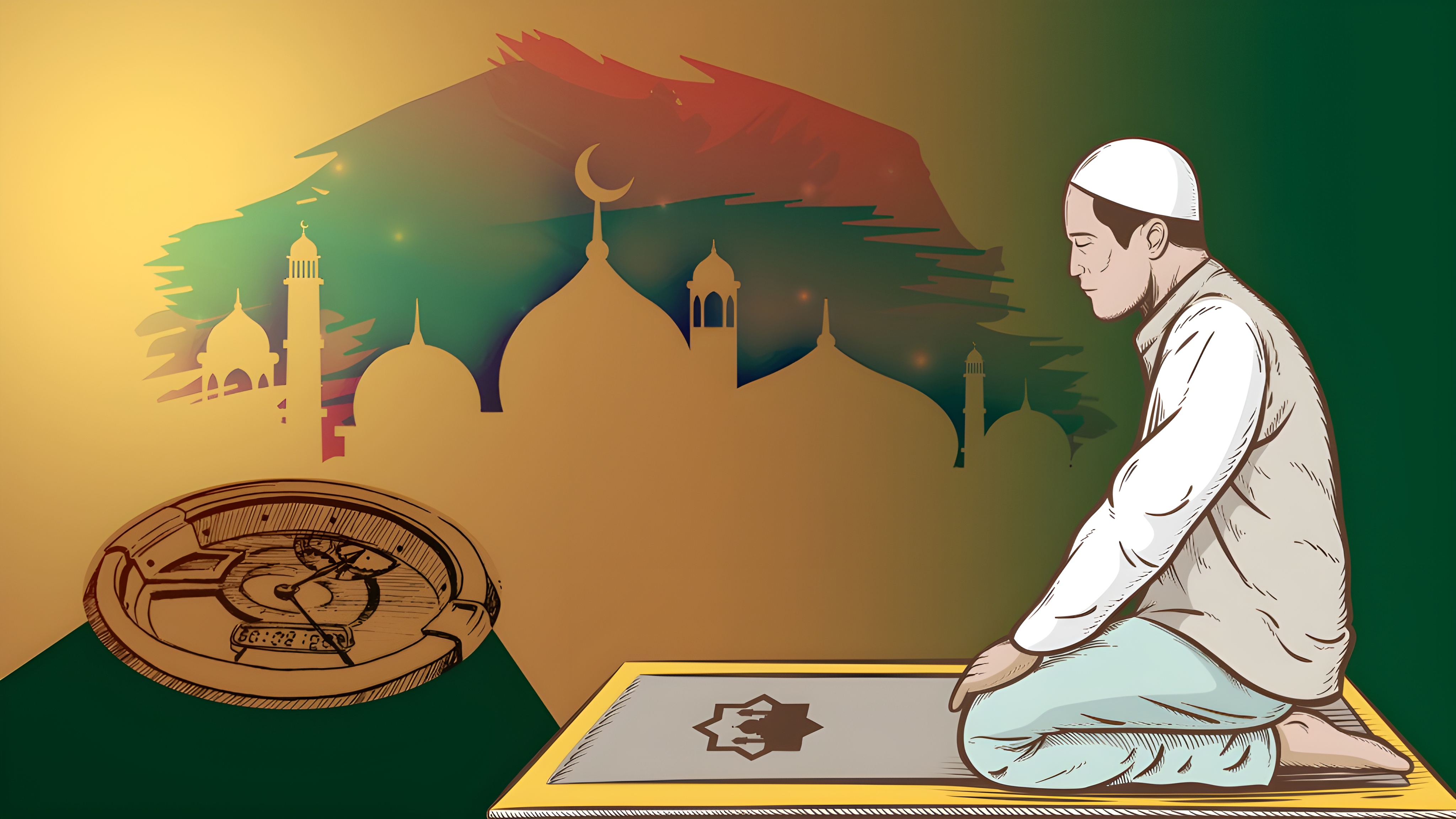
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ০৮ পৌষ ১৪৩২ বাংলা, ০২ রজব ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
| নামাজ | ওয়াক্ত শুরু | ওয়াক্ত শেষ |
|---|---|---|
| তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময় | ০০: ০০ | ০৫: ১৫ মিনিট |
| ফজর | ০৫: ১৬ মিনিট | ০৬: ৩৬ মিনিট |
| জোহর | ১১: ৫৮ মিনিট | ০৩: ৪১ মিনিট |
| আসর | ০৩: ৪২ মিনিট | ০৫: ১৭ মিনিট |
| মাগরিব | ০৫: ১৯ মিনিট | ০৬: ৩৭ মিনিট |
| এশা | ০৬: ৩৮ মিনিট | ০৫: ১৫ মিনিট |
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে অনেক নবী-রাসুলের আমলেই রোজার বিধানের কথা জানা যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের জন্য রোজা ফরজ করেন, তখন সেদিকে ইঙ্গিত করে মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন।
০৯ মার্চ ২০২৫
নামাজ বা সালাত অন্যতম প্রধান ফরজ ইবাদত। পবিত্র কোরআনের ৮২টি স্থানে নামাজের কথা উল্লেখ করে এর অপরিসীম গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যখন তোমরা সালাত (নামাজ) পূর্ণ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে, তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে।
১৫ ঘণ্টা আগে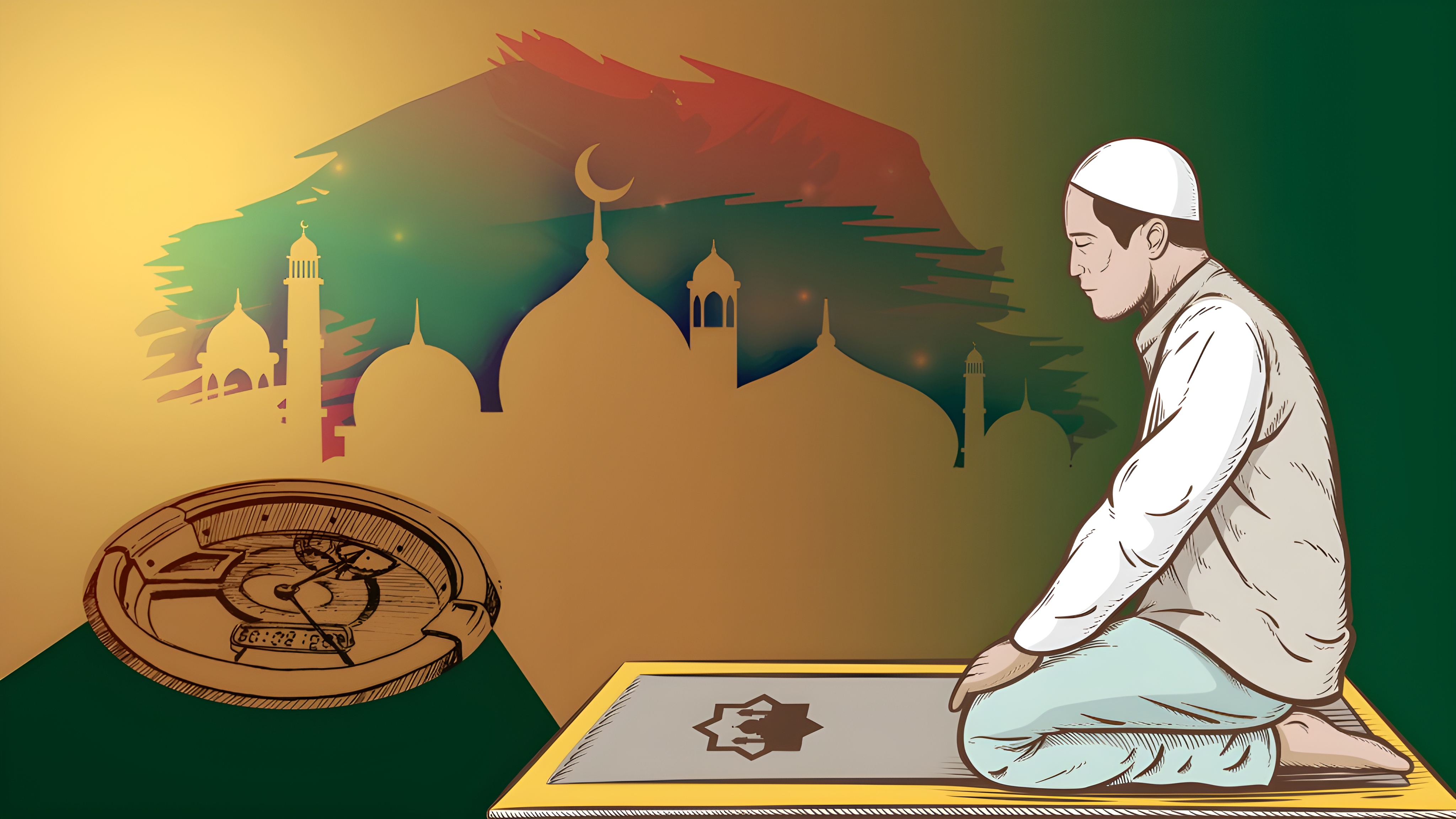
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
১ দিন আগে
ইসলামি শরিয়তে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মুসলমানের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। এটি ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং যারা নামাজে অবনত হয়...
২ দিন আগে