ওমর ফারুক, চট্টগ্রাম
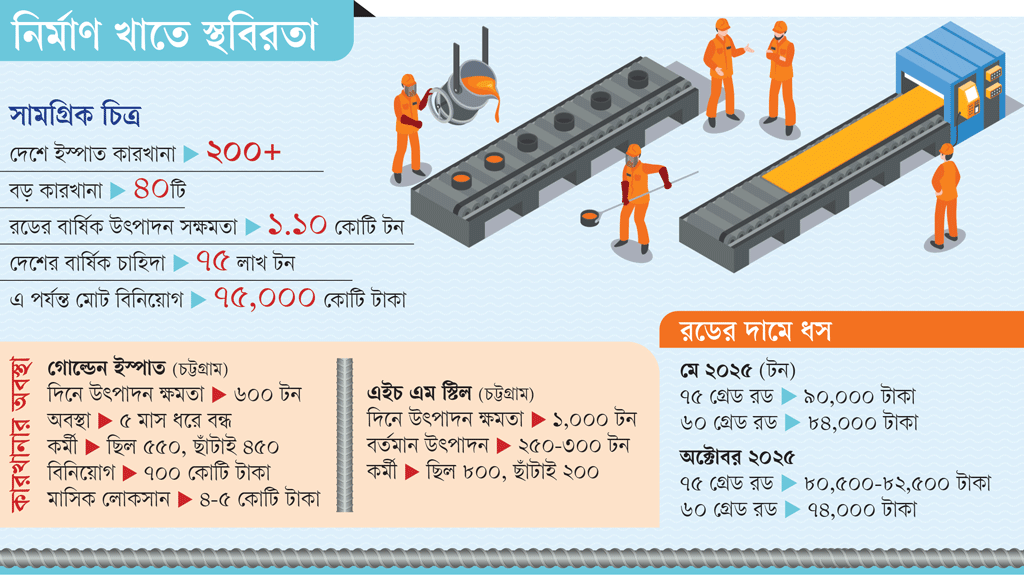
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরা শিল্প এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা গোল্ডেন ইস্পাত কারখানাটি এখন নিস্তব্ধ। একসময় ফার্নেসে জ্বলত আগুন, টন টন ইস্পাত গলে নামত এমএস রডের ধারা। সেই উৎপাদন হঠাৎ থেমে গেছে। মাত্র কয়েক মাস আগেও এখানে ৫৫০ শ্রমিক কাজ করতেন, অথচ এখন ছাঁটাই হয়ে গেছেন ৪৫০ জন। হাতে গোনা স্থায়ী ১০০ কর্মীকে রাখা হয়েছে শুধু সুদিন ফেরার আশায়। কারখানার চারদিকে নীরবতা আর শ্রমিকদের বিমর্ষ মুখ যেন বলে দিচ্ছে, দেশের ইস্পাতশিল্প বড় সংকটে।
গোল্ডেন ইস্পাতের মালিকানা থাকা একই গ্রুপের এইচএম স্টিলও টিকে আছে অর্ধেক শক্তিতে। দৈনিক এক হাজার টন উৎপাদনক্ষমতা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে ২৫০-৩০০ টনে। তিন শিফটের পরিবর্তে চলছে দুই শিফট। এখানেও ৮০০ কর্মীর মধ্যে ২০০ জন চাকরি হারিয়েছেন। কারখানা দুটির পরিচালক সরওয়ার আলমের ভাষায়, লোকসান ঠেকাতে বাধ্য হয়েই একটি কারখানার উৎপাদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে, আরেকটির উৎপাদন বড় পরিসরে কমাতে হয়েছে। তবু মাসে ৪-৫ কোটি টাকা ক্ষতি গুনতে হচ্ছে।
এ চিত্র শুধু দুটি কারখানার নয়; উৎপাদন খরচ ও পণ্যের দামের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় লোকসান কমাতে চট্টগ্রামের কেআর স্টিল, বায়েজিদ স্টিল, সীমা স্টিল, শীতলপুর স্টিল, ঢাকার পিএইচপি স্টিলসহ অনেক প্রতিষ্ঠানই উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে দৈনিক হাজার টনের উৎপাদন সক্ষমতা থাকা বহু কারখানা এখন খালি শেডের ভেতর থেমে আছে। আর যারা কোনোভাবে উৎপাদনে টিকে আছে, তাদেরও উৎপাদন ক্ষমতার বড় অংশ অনুৎপাদনশীল থেকে যাচ্ছে।
কারণ একটাই—দেশের নির্মাণ খাত থমকে গেছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বড় প্রকল্পগুলো গত এক বছর ধরে কার্যত স্থবির। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে আর কোনো নতুন বড় উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি। পুরোনো প্রকল্পগুলোর অর্থ ছাড়ও হয়েছে ধীরগতিতে; যার প্রভাব পড়েছে সরাসরি ইস্পাতশিল্পে।
পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে আন্তর্জাতিক বাজারে স্ক্র্যাপ ধাতুর দাম টনে ১২০০ টাকা কমলেও দেশের বাজারে রডের দাম গত কয়েক মাসে কমেছে ৭-৯ হাজার টাকা। ৭৫ গ্রেডের এমএস রড এখন বিক্রি হচ্ছে মিলগেটে ৮০,৫০০ থেকে ৮২,৫০০ টাকায়, যা মে মাসে ছিল কমপক্ষে ৯০ হাজার টাকা। ৬০ গ্রেডের দাম ৮৪ হাজার থেকে নেমে এসেছে ৭৪ হাজারে। অথচ উদ্যোক্তারা বলছেন, উৎপাদন খরচ ও বিক্রির দামের এই অমিলের কারণে তাঁরা প্রতি টনে ৬-৮ হাজার টাকা লোকসান দিচ্ছেন।
ব্যাংকের চাপও বাড়িয়েছে সংকট। আগে কাঁচামাল আমদানিতে যেখানে ১০ শতাংশ মার্জিন জমা রাখতে হতো, এখন নিতে হচ্ছে ৫০-৬০ শতাংশ। সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় ঋণের বোঝা আরও ভারী হয়েছে। এর মধ্যেই কারখানাগুলোকে গ্যাস-বিদ্যুৎ ও বেতন বাবদ ন্যূনতম মাসিক বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে ৫০-৬০ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে উদ্যোক্তাদের জন্য এটি দাঁড়িয়েছে টিকে থাকার লড়াই।
বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসএমএ) তথ্য বলছে, দেশে উৎপাদিত রডের ৬২-৬৫ শতাংশ ব্যবহৃত হয় সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে। ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক আবাসন খাতে ব্যবহার হয় বাকি ৩৫ শতাংশ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুমন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে জানান, নতুন প্রকল্প কার্যত নেওয়া হচ্ছে না। আগের প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে গড়িমসির কারণে কাজের গতি একেবারেই শ্লথ। এ জন্যই বাজারে রডের চাহিদা ভেঙে পড়েছে।
দেশের অন্যতম শীর্ষ রড উৎপাদনকারী বিএসআরএমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন সেনগুপ্ত বলেন, নির্মাণ খাতের গতির ওপর নির্ভর করে ইস্পাতসহ আরও অনেক খাত। এক বছর ধরে গতি না থাকায় চাহিদা কমেছে, বিক্রি কমেছে, দামও কমেছে। এতে বিনিয়োগকারীরা মারাত্মক চাপে পড়েছেন।
কেআর গ্রুপের চেয়ারম্যান সেকান্দার হোসেন আরও স্পষ্ট করে দিলেন সংকটের চিত্র। তিনি জানান, ‘২৫০-২৭০ টন উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন খরচের সঙ্গে বাজারদরের সামঞ্জস্য নেই। তাই গত বছরের আগস্ট থেকেই কারখানার উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছি।’
অন্যদিকে দেশের অন্যতম বৃহৎ উৎপাদক কেএসআরএম দিনে ২,৫০০-৩,০০০ টন রড উৎপাদন ও বিক্রি করলেও এখন সেটি নেমে এসেছে হাজার টনের নিচে। প্রতিষ্ঠানের মিডিয়া অ্যাডভাইজার মিজানুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরকারি প্রকল্পের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। চাহিদা ৬০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। লোকসান দিয়েই বিক্রি করতে হচ্ছে; কারণ, রড বেশি দিন মজুত রাখা যায় না; দাগ পড়ে গেলে দাম পড়ে যায়।
এই ধস শুধু কারখানার ভেতরে নয়, আঘাত করেছে বাজারেও। চট্টগ্রামের আসাদগঞ্জের মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এস এম কামরুজ্জামান জানালেন, আগে যেখানে দিনে ৩০০-৩৫০ টন রড বিক্রি করতেন, সেখানে এখন বিক্রি নেমে এসেছে ৫০ টনের নিচে।
সব মিলিয়ে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ দাঁড়িয়ে আছে ঝুঁকির মুখে। দেশে ২০০টির বেশি ইস্পাত কারখানা থাকলেও এর মধ্যে ৪০টি বড় প্রতিষ্ঠান মূল উৎপাদন সামলাচ্ছে। এদের বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১ কোটি ১০ লাখ টন হলেও দেশের বার্ষিক চাহিদা মাত্র ৭৫ লাখ টন। সেই চাহিদাও এখন আর তৈরি হচ্ছে না।
তবু উদ্যোক্তারা আশায় আছেন। তাঁদের বিশ্বাস, সরকার যদি দ্রুত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়, পুরোনো প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করে এবং কম সুদে গৃহঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে, তবে আবার ইস্পাতশিল্প ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তবে যত দিন যাচ্ছে, ততই দিগন্তে জমছে অনিশ্চয়তার ঘন মেঘ।
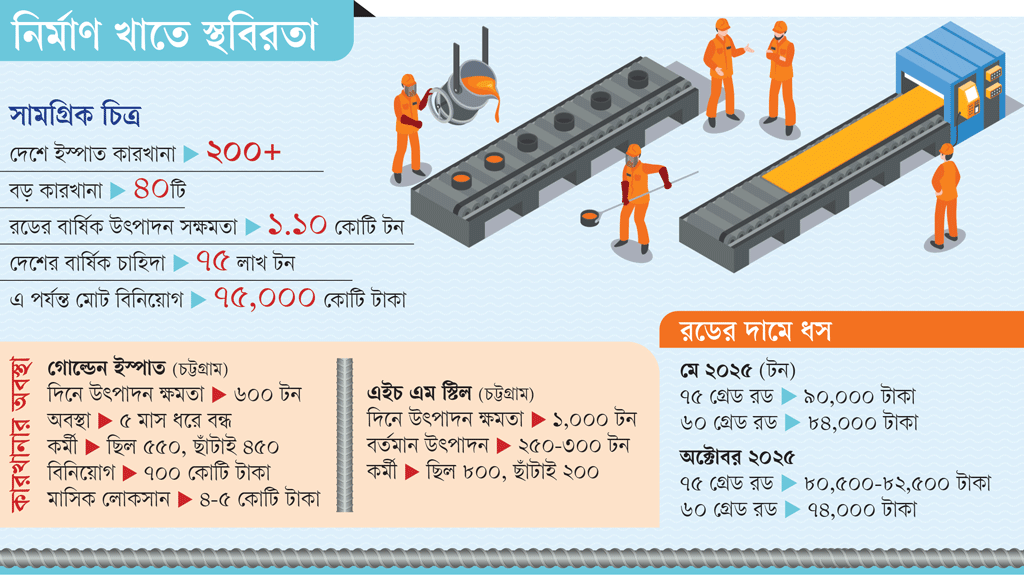
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরা শিল্প এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা গোল্ডেন ইস্পাত কারখানাটি এখন নিস্তব্ধ। একসময় ফার্নেসে জ্বলত আগুন, টন টন ইস্পাত গলে নামত এমএস রডের ধারা। সেই উৎপাদন হঠাৎ থেমে গেছে। মাত্র কয়েক মাস আগেও এখানে ৫৫০ শ্রমিক কাজ করতেন, অথচ এখন ছাঁটাই হয়ে গেছেন ৪৫০ জন। হাতে গোনা স্থায়ী ১০০ কর্মীকে রাখা হয়েছে শুধু সুদিন ফেরার আশায়। কারখানার চারদিকে নীরবতা আর শ্রমিকদের বিমর্ষ মুখ যেন বলে দিচ্ছে, দেশের ইস্পাতশিল্প বড় সংকটে।
গোল্ডেন ইস্পাতের মালিকানা থাকা একই গ্রুপের এইচএম স্টিলও টিকে আছে অর্ধেক শক্তিতে। দৈনিক এক হাজার টন উৎপাদনক্ষমতা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে ২৫০-৩০০ টনে। তিন শিফটের পরিবর্তে চলছে দুই শিফট। এখানেও ৮০০ কর্মীর মধ্যে ২০০ জন চাকরি হারিয়েছেন। কারখানা দুটির পরিচালক সরওয়ার আলমের ভাষায়, লোকসান ঠেকাতে বাধ্য হয়েই একটি কারখানার উৎপাদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে, আরেকটির উৎপাদন বড় পরিসরে কমাতে হয়েছে। তবু মাসে ৪-৫ কোটি টাকা ক্ষতি গুনতে হচ্ছে।
এ চিত্র শুধু দুটি কারখানার নয়; উৎপাদন খরচ ও পণ্যের দামের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় লোকসান কমাতে চট্টগ্রামের কেআর স্টিল, বায়েজিদ স্টিল, সীমা স্টিল, শীতলপুর স্টিল, ঢাকার পিএইচপি স্টিলসহ অনেক প্রতিষ্ঠানই উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে দৈনিক হাজার টনের উৎপাদন সক্ষমতা থাকা বহু কারখানা এখন খালি শেডের ভেতর থেমে আছে। আর যারা কোনোভাবে উৎপাদনে টিকে আছে, তাদেরও উৎপাদন ক্ষমতার বড় অংশ অনুৎপাদনশীল থেকে যাচ্ছে।
কারণ একটাই—দেশের নির্মাণ খাত থমকে গেছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বড় প্রকল্পগুলো গত এক বছর ধরে কার্যত স্থবির। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের আগস্টে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে আর কোনো নতুন বড় উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়নি। পুরোনো প্রকল্পগুলোর অর্থ ছাড়ও হয়েছে ধীরগতিতে; যার প্রভাব পড়েছে সরাসরি ইস্পাতশিল্পে।
পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে আন্তর্জাতিক বাজারে স্ক্র্যাপ ধাতুর দাম টনে ১২০০ টাকা কমলেও দেশের বাজারে রডের দাম গত কয়েক মাসে কমেছে ৭-৯ হাজার টাকা। ৭৫ গ্রেডের এমএস রড এখন বিক্রি হচ্ছে মিলগেটে ৮০,৫০০ থেকে ৮২,৫০০ টাকায়, যা মে মাসে ছিল কমপক্ষে ৯০ হাজার টাকা। ৬০ গ্রেডের দাম ৮৪ হাজার থেকে নেমে এসেছে ৭৪ হাজারে। অথচ উদ্যোক্তারা বলছেন, উৎপাদন খরচ ও বিক্রির দামের এই অমিলের কারণে তাঁরা প্রতি টনে ৬-৮ হাজার টাকা লোকসান দিচ্ছেন।
ব্যাংকের চাপও বাড়িয়েছে সংকট। আগে কাঁচামাল আমদানিতে যেখানে ১০ শতাংশ মার্জিন জমা রাখতে হতো, এখন নিতে হচ্ছে ৫০-৬০ শতাংশ। সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় ঋণের বোঝা আরও ভারী হয়েছে। এর মধ্যেই কারখানাগুলোকে গ্যাস-বিদ্যুৎ ও বেতন বাবদ ন্যূনতম মাসিক বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে ৫০-৬০ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে উদ্যোক্তাদের জন্য এটি দাঁড়িয়েছে টিকে থাকার লড়াই।
বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসএমএ) তথ্য বলছে, দেশে উৎপাদিত রডের ৬২-৬৫ শতাংশ ব্যবহৃত হয় সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে। ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক আবাসন খাতে ব্যবহার হয় বাকি ৩৫ শতাংশ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুমন চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে জানান, নতুন প্রকল্প কার্যত নেওয়া হচ্ছে না। আগের প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে গড়িমসির কারণে কাজের গতি একেবারেই শ্লথ। এ জন্যই বাজারে রডের চাহিদা ভেঙে পড়েছে।
দেশের অন্যতম শীর্ষ রড উৎপাদনকারী বিএসআরএমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন সেনগুপ্ত বলেন, নির্মাণ খাতের গতির ওপর নির্ভর করে ইস্পাতসহ আরও অনেক খাত। এক বছর ধরে গতি না থাকায় চাহিদা কমেছে, বিক্রি কমেছে, দামও কমেছে। এতে বিনিয়োগকারীরা মারাত্মক চাপে পড়েছেন।
কেআর গ্রুপের চেয়ারম্যান সেকান্দার হোসেন আরও স্পষ্ট করে দিলেন সংকটের চিত্র। তিনি জানান, ‘২৫০-২৭০ টন উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন খরচের সঙ্গে বাজারদরের সামঞ্জস্য নেই। তাই গত বছরের আগস্ট থেকেই কারখানার উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছি।’
অন্যদিকে দেশের অন্যতম বৃহৎ উৎপাদক কেএসআরএম দিনে ২,৫০০-৩,০০০ টন রড উৎপাদন ও বিক্রি করলেও এখন সেটি নেমে এসেছে হাজার টনের নিচে। প্রতিষ্ঠানের মিডিয়া অ্যাডভাইজার মিজানুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সরকারি প্রকল্পের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। চাহিদা ৬০ শতাংশের বেশি কমে গেছে। লোকসান দিয়েই বিক্রি করতে হচ্ছে; কারণ, রড বেশি দিন মজুত রাখা যায় না; দাগ পড়ে গেলে দাম পড়ে যায়।
এই ধস শুধু কারখানার ভেতরে নয়, আঘাত করেছে বাজারেও। চট্টগ্রামের আসাদগঞ্জের মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এস এম কামরুজ্জামান জানালেন, আগে যেখানে দিনে ৩০০-৩৫০ টন রড বিক্রি করতেন, সেখানে এখন বিক্রি নেমে এসেছে ৫০ টনের নিচে।
সব মিলিয়ে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ দাঁড়িয়ে আছে ঝুঁকির মুখে। দেশে ২০০টির বেশি ইস্পাত কারখানা থাকলেও এর মধ্যে ৪০টি বড় প্রতিষ্ঠান মূল উৎপাদন সামলাচ্ছে। এদের বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১ কোটি ১০ লাখ টন হলেও দেশের বার্ষিক চাহিদা মাত্র ৭৫ লাখ টন। সেই চাহিদাও এখন আর তৈরি হচ্ছে না।
তবু উদ্যোক্তারা আশায় আছেন। তাঁদের বিশ্বাস, সরকার যদি দ্রুত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়, পুরোনো প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করে এবং কম সুদে গৃহঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে, তবে আবার ইস্পাতশিল্প ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তবে যত দিন যাচ্ছে, ততই দিগন্তে জমছে অনিশ্চয়তার ঘন মেঘ।

দেশের পুঁজিবাজারের জন্য মন্দার বছর ছিল ২০২৪ সাল। বছরটিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মতোই ব্যাংকগুলোও মুনাফা করতে পারেনি। উল্টো বড় অঙ্কের লোকসান গুনেছে অনেক ব্যাংক। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এবং তালিকাভুক্ত নয়, এমন ৩৪ ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে ২০২৪ সালে...
৪ ঘণ্টা আগে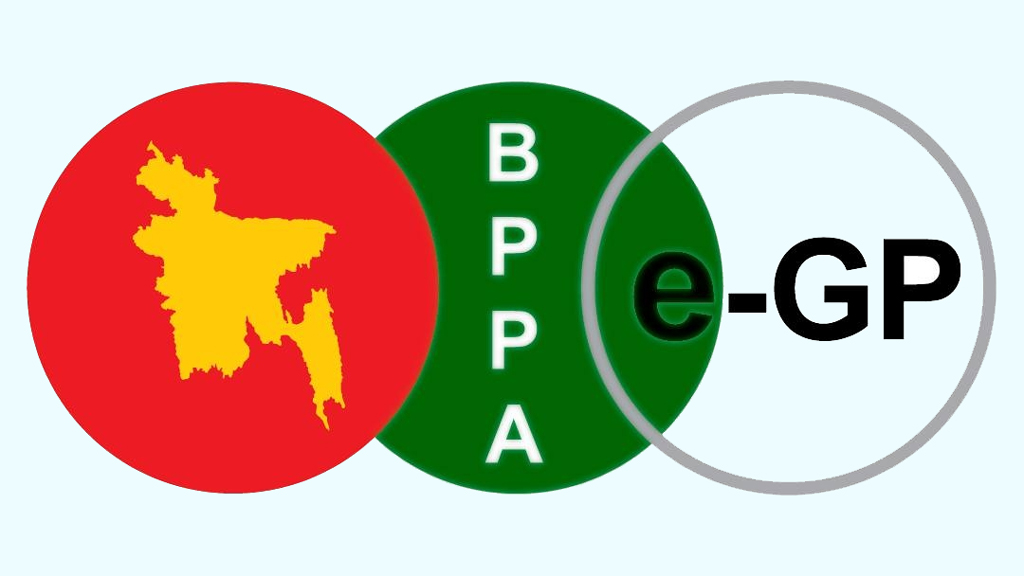
সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে সরকারি ক্রয়নীতিতে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী সব ধরনের সরকারি কেনাকাটায় অনলাইনে দরপত্র (ই-জিপি) দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত রোববার নতুন এই বিধিমালা গেজেট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়েছে।
৬ ঘণ্টা আগে
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির কর্মকর্তাদের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষায় ৮৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছেন। বাকি ১২ শতাংশ কর্মকর্তার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে। গত মঙ্গলবার রাতে এই বিশেষ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিত
৬ ঘণ্টা আগে
এসবিকে টেক ভেঞ্চারস লিমিটেড বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি না রাখায় দেশের পাঁচটি স্টার্টআপ মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এসবিকে টেকের কর্ণধার সোনিয়া বশির কবিরের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এসব স্টার্টআপের কার্যক্রম থমকে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
৬ ঘণ্টা আগে