মাসুদ রানা
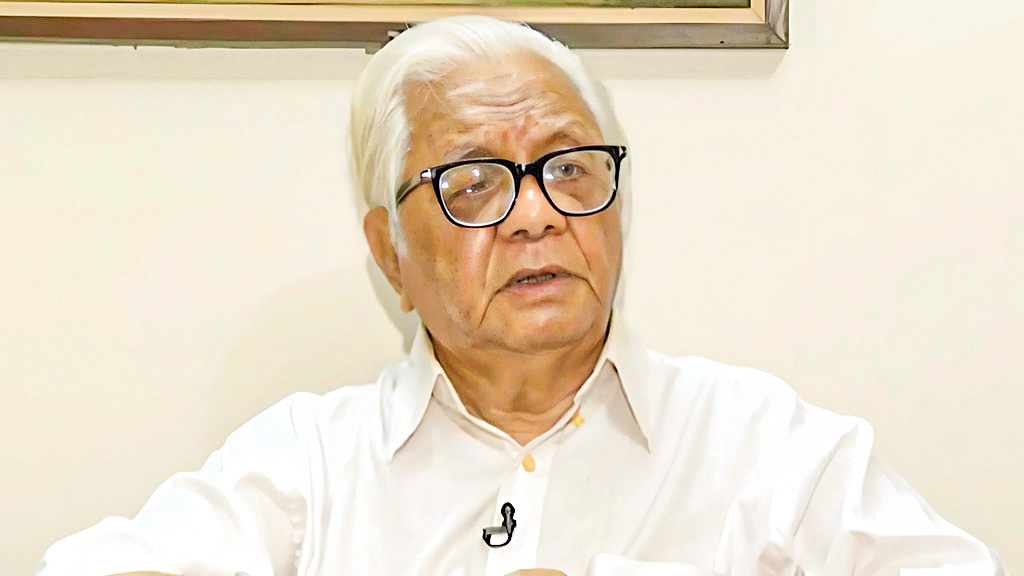
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
বদরুদ্দীন উমর একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ, লেখক-গবেষক, ইতিহাসবিদ ও মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক। ক্ষমতার কাছে মাথা নত করেননি শেষ পর্যন্ত। তাঁকে অনেকে শুধু ভাষা আন্দোলনের গবেষক হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু এর বাইরেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।
পাকিস্তান জমানায় অনেক বুদ্ধিজীবী, লেখক-গবেষকে দেশের যুগান্তকারী আন্দোলনগুলোকে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনকে একপার্শ্বিকভাবে দেখেছিলেন, তখন তিনি সেই আন্দোলনে জনমানুষের ভূমিকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের বিদ্রোহ, জনগণের কোন অংশ তাতে শক্তি জোগাল, দুর্বলতাটা কোথায় ছিল বলে আজও মুক্তি আসেনি, তা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর লিখিত তিন খণ্ডে—‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’তে।
বার্ধক্য অনেকের শরীর ও মনের শিরদাঁড়া বাঁকা করে দেয়, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে সততা ও মনীষা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সময়ের কাছে একজন রাজনীতিবিদের কাজ শুধু বিজয়ের জয়গান গাওয়া নয়, পরাজয় এবং তার কারণটা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা অনুসন্ধান এবং পথ বাতলে দেওয়াটাও অন্যতম কাজ। তিনি এই জরুরি কাজেরই অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।
পাকিস্তান আমলে তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার ট্রিলজি যেমন ‘সাম্প্রদায়িকতা’, ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’ ও ‘সংস্কৃতির সংকট’ বইগুলো পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোমর ফাঁস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিত্বের সঙ্গে মুসলমানিত্বের বিরোধ যে কৃত্রিম ব্যাপার, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়, তা যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, জাতীয়তাবাদী ধারণা শেষ পর্যন্ত কীভাবে স্বৈরতন্ত্রে রূপ নেয়, রাজনীতি যে শ্রেণির বাইরে ক্রিয়া করে না—সেসব তিনি তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। এই বই তিনটি প্রকাশ হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁর প্রতি নাখোশ হয়। পরবর্তী সময়ে জীবন কীভাবে চলবে, সে চিন্তা না করে এক মহা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাঁর লেখক-গবেষকসত্তার পাশাপাশি তিনি শুধু অক্সফোর্ড ফেরত বিদ্বানের গরিমাই ছাড়েননি, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। সেটা ১৯৬৮ সালের কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি ও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
বদরুদ্দীন উমরের আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ থেকে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও সক্রিয়তার কথা। যার শুরু ১৯৬৪ সালে। সে বছর ভিয়েতনামে মার্কিন বিমানবাহিনীর টংকিং উপসাগরে হামলার ঘটনায় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জনের বেশি শিক্ষককে সমবেত এবং বিবৃতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী হামলার প্রতিবাদ করেন। তিনি বিবৃতি সংগঠিত করেই নিষ্ক্রিয় থাকেননি; ভিয়েতনামে হামলার প্রতিবাদে তিনি মার্কিন কনস্যুলেটে চিঠি দিয়ে তিন মাসের জন্য আমেরিকায় লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যাওয়ার আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে পাকিস্তানের মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করার কারণে সরকারের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা প্রবল হতে থাকায় তিনি পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ব্রিটেনের সোয়াসয়ে পিএইচডি করতে যাওয়ার বিষয়টি আর গ্রহণ করেননি।
এরপর তিনি লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসের গিঁটগুলো খুলতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে তিনি পাল্টা যুক্তি হাজির করেন, যা এত দিন ধরে সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে মহা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সেই জায়গা ধরে তিনি হাজির করেন বঙ্গীয় রেনসাঁর পাল্টা বয়ান, যা তিনি ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক’ ও ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ’ বই দুটিতে তুলে এনেছেন। এই ধারণা আমাদের নতুন এক ইতিহাসের কাছে নিয়ে যায়। আবার বঙ্গভঙ্গ ও ভারত ভাগের দায় যে কংগ্রেস নেতাদের, সেটা প্রমাণ করে তিনি তুলে এনেছেন ‘বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি’ ও ‘ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন’ গ্রন্থে। এই বই দুটি লেখার আগপর্যন্ত জয়া চ্যাটার্জির ‘ভারত ভাগ’ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাংলা বিভাজনের রাজনীতি-অর্থনীতি’ প্রকাশিত হয়নি।
এ ধরনের লেখালেখির পাশাপাশি তাঁকে আমরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে দেখি। আমাদের দেশে রাজনীতির বাইরে গিয়ে বুদ্ধিজীবিতার চর্চার একটা রেওয়াজ প্রচলিত আছে। মানে বুদ্ধিজীবিতার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির একটা ফারাক দেখা যায়। কিন্তু তিনি রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবিতাকে সমান্তরাল রেখায় ধরে হেঁটেছেন। সে কারণে তাঁর লেখালেখি শুধু বুদ্ধিজীবিতার বুদবুদে আবিষ্ট থাকেনি, সেই লেখালেখির তাড়না তাঁকে রাজনৈতিক সক্রিয়তার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এ কারণে প্রথমে তিনি বিভিন্ন তৎকালীন পিকিংপন্থী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে পার্টির কিংবদন্তি নেতাদের সঙ্গে বাস্তব কাজের বিরোধ থেকে তিনি পার্টি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যেমন স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে বিরোধ ঘটে পিকিং ধারার অন্যতম নেতা কমরেড আবদুল হক ও তোয়াহার সঙ্গে। তাঁরা দুজন পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নিলে বদরুদ্দীন উমর সেই তত্ত্বের বিরোধিতা করে সেই সময় বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।
’৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে তিনি নতুন ভাবনায় পার্টি গঠনের দিকে অগ্রসর হন, যেটা কোনোভাবেই উপমহাদেশের প্রচলিত বাম ধারার রাজনীতির মতো রুশ, পিকিং ও মাও ধারার মতো ছিল না। তিনি পার্টি গঠনের প্রথম থেকেই নির্বাচনী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। আবার তিনি গ্রাম দিয়ে শহর দখলের রাজনীতির পথকেও ভুল বলেছেন। সে জন্য তাঁর পার্টির ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ছিল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের পথ। এই চিন্তার ধারায় তিনি আজীবন স্থির ছিলেন। যদিও তাঁর নেতৃত্বাধীন পার্টি তেমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি।
আমার কাছে মনে হয়, তাঁর মতো জেদি, সৎ ও সাহসী মানুষের রাজনৈতিক নেতা হওয়ার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? তিনি তো একাই একটি প্রতিষ্ঠান। সে কারণেই আদমজী, ফিলিপস, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা পদক প্রত্যাখ্যান করতে তিনি এতটুকু দ্বিধান্বিত ছিলেন না।
সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ‘যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ’ এবং ‘যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ’ বই দুটি সেই সময়ের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির ভিন্ন এক দৃষ্টিতে লেখা। সেসব লেখা থেকে পাঠক জানতে পারবে সেই সময়ের ঘটনার ধারা বিবরণী।
বদরুদ্দীন উমর জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছেন, পুঁজিবাদই শেষ কথা নয়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, তবে একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন পুঁজিবাদেরও শেষ পরিণতি আছে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সমাজতন্ত্রের আদৌ কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না, এ প্রশ্ন যদি কেউ তোলে, তাহলে এর বিপরীতে প্রশ্ন করতে হবে, পুঁজিবাদেরও কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না।’ সেই আশাবাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে স্থির ছিলেন। তিনি প্রস্থান করেছেন। তবে তাঁর আপসহীন মনীষা দীর্ঘ সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।
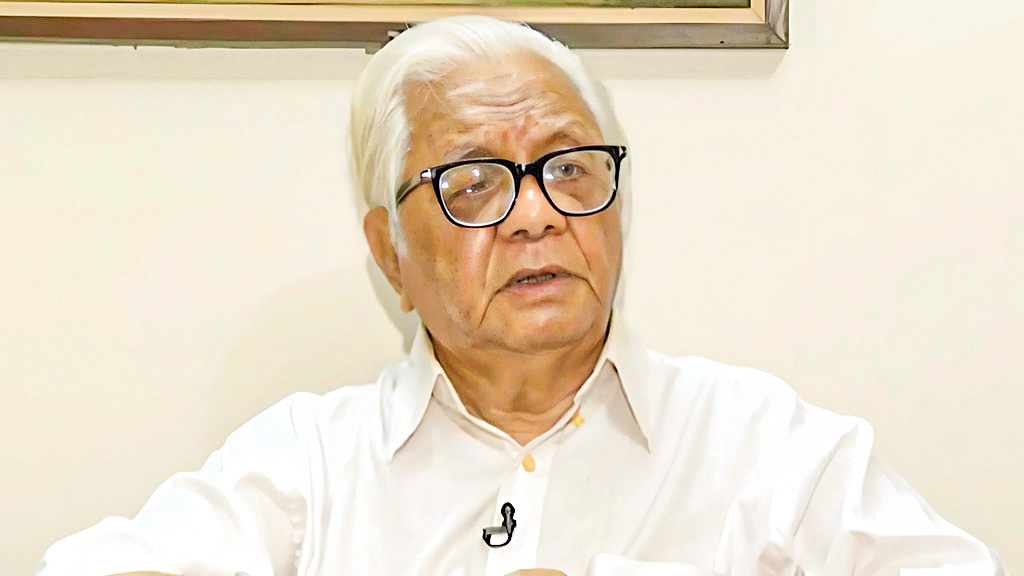
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
বদরুদ্দীন উমর একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ, লেখক-গবেষক, ইতিহাসবিদ ও মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক। ক্ষমতার কাছে মাথা নত করেননি শেষ পর্যন্ত। তাঁকে অনেকে শুধু ভাষা আন্দোলনের গবেষক হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু এর বাইরেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।
পাকিস্তান জমানায় অনেক বুদ্ধিজীবী, লেখক-গবেষকে দেশের যুগান্তকারী আন্দোলনগুলোকে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনকে একপার্শ্বিকভাবে দেখেছিলেন, তখন তিনি সেই আন্দোলনে জনমানুষের ভূমিকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের বিদ্রোহ, জনগণের কোন অংশ তাতে শক্তি জোগাল, দুর্বলতাটা কোথায় ছিল বলে আজও মুক্তি আসেনি, তা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর লিখিত তিন খণ্ডে—‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’তে।
বার্ধক্য অনেকের শরীর ও মনের শিরদাঁড়া বাঁকা করে দেয়, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে সততা ও মনীষা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সময়ের কাছে একজন রাজনীতিবিদের কাজ শুধু বিজয়ের জয়গান গাওয়া নয়, পরাজয় এবং তার কারণটা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা অনুসন্ধান এবং পথ বাতলে দেওয়াটাও অন্যতম কাজ। তিনি এই জরুরি কাজেরই অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।
পাকিস্তান আমলে তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার ট্রিলজি যেমন ‘সাম্প্রদায়িকতা’, ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’ ও ‘সংস্কৃতির সংকট’ বইগুলো পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোমর ফাঁস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিত্বের সঙ্গে মুসলমানিত্বের বিরোধ যে কৃত্রিম ব্যাপার, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়, তা যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, জাতীয়তাবাদী ধারণা শেষ পর্যন্ত কীভাবে স্বৈরতন্ত্রে রূপ নেয়, রাজনীতি যে শ্রেণির বাইরে ক্রিয়া করে না—সেসব তিনি তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। এই বই তিনটি প্রকাশ হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁর প্রতি নাখোশ হয়। পরবর্তী সময়ে জীবন কীভাবে চলবে, সে চিন্তা না করে এক মহা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাঁর লেখক-গবেষকসত্তার পাশাপাশি তিনি শুধু অক্সফোর্ড ফেরত বিদ্বানের গরিমাই ছাড়েননি, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। সেটা ১৯৬৮ সালের কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি ও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
বদরুদ্দীন উমরের আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ থেকে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও সক্রিয়তার কথা। যার শুরু ১৯৬৪ সালে। সে বছর ভিয়েতনামে মার্কিন বিমানবাহিনীর টংকিং উপসাগরে হামলার ঘটনায় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জনের বেশি শিক্ষককে সমবেত এবং বিবৃতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী হামলার প্রতিবাদ করেন। তিনি বিবৃতি সংগঠিত করেই নিষ্ক্রিয় থাকেননি; ভিয়েতনামে হামলার প্রতিবাদে তিনি মার্কিন কনস্যুলেটে চিঠি দিয়ে তিন মাসের জন্য আমেরিকায় লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যাওয়ার আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে পাকিস্তানের মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করার কারণে সরকারের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা প্রবল হতে থাকায় তিনি পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ব্রিটেনের সোয়াসয়ে পিএইচডি করতে যাওয়ার বিষয়টি আর গ্রহণ করেননি।
এরপর তিনি লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসের গিঁটগুলো খুলতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে তিনি পাল্টা যুক্তি হাজির করেন, যা এত দিন ধরে সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে মহা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সেই জায়গা ধরে তিনি হাজির করেন বঙ্গীয় রেনসাঁর পাল্টা বয়ান, যা তিনি ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক’ ও ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ’ বই দুটিতে তুলে এনেছেন। এই ধারণা আমাদের নতুন এক ইতিহাসের কাছে নিয়ে যায়। আবার বঙ্গভঙ্গ ও ভারত ভাগের দায় যে কংগ্রেস নেতাদের, সেটা প্রমাণ করে তিনি তুলে এনেছেন ‘বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি’ ও ‘ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন’ গ্রন্থে। এই বই দুটি লেখার আগপর্যন্ত জয়া চ্যাটার্জির ‘ভারত ভাগ’ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাংলা বিভাজনের রাজনীতি-অর্থনীতি’ প্রকাশিত হয়নি।
এ ধরনের লেখালেখির পাশাপাশি তাঁকে আমরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে দেখি। আমাদের দেশে রাজনীতির বাইরে গিয়ে বুদ্ধিজীবিতার চর্চার একটা রেওয়াজ প্রচলিত আছে। মানে বুদ্ধিজীবিতার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির একটা ফারাক দেখা যায়। কিন্তু তিনি রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবিতাকে সমান্তরাল রেখায় ধরে হেঁটেছেন। সে কারণে তাঁর লেখালেখি শুধু বুদ্ধিজীবিতার বুদবুদে আবিষ্ট থাকেনি, সেই লেখালেখির তাড়না তাঁকে রাজনৈতিক সক্রিয়তার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এ কারণে প্রথমে তিনি বিভিন্ন তৎকালীন পিকিংপন্থী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে পার্টির কিংবদন্তি নেতাদের সঙ্গে বাস্তব কাজের বিরোধ থেকে তিনি পার্টি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যেমন স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে বিরোধ ঘটে পিকিং ধারার অন্যতম নেতা কমরেড আবদুল হক ও তোয়াহার সঙ্গে। তাঁরা দুজন পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নিলে বদরুদ্দীন উমর সেই তত্ত্বের বিরোধিতা করে সেই সময় বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।
’৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে তিনি নতুন ভাবনায় পার্টি গঠনের দিকে অগ্রসর হন, যেটা কোনোভাবেই উপমহাদেশের প্রচলিত বাম ধারার রাজনীতির মতো রুশ, পিকিং ও মাও ধারার মতো ছিল না। তিনি পার্টি গঠনের প্রথম থেকেই নির্বাচনী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। আবার তিনি গ্রাম দিয়ে শহর দখলের রাজনীতির পথকেও ভুল বলেছেন। সে জন্য তাঁর পার্টির ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ছিল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের পথ। এই চিন্তার ধারায় তিনি আজীবন স্থির ছিলেন। যদিও তাঁর নেতৃত্বাধীন পার্টি তেমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি।
আমার কাছে মনে হয়, তাঁর মতো জেদি, সৎ ও সাহসী মানুষের রাজনৈতিক নেতা হওয়ার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? তিনি তো একাই একটি প্রতিষ্ঠান। সে কারণেই আদমজী, ফিলিপস, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা পদক প্রত্যাখ্যান করতে তিনি এতটুকু দ্বিধান্বিত ছিলেন না।
সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ‘যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ’ এবং ‘যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ’ বই দুটি সেই সময়ের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির ভিন্ন এক দৃষ্টিতে লেখা। সেসব লেখা থেকে পাঠক জানতে পারবে সেই সময়ের ঘটনার ধারা বিবরণী।
বদরুদ্দীন উমর জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছেন, পুঁজিবাদই শেষ কথা নয়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, তবে একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন পুঁজিবাদেরও শেষ পরিণতি আছে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সমাজতন্ত্রের আদৌ কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না, এ প্রশ্ন যদি কেউ তোলে, তাহলে এর বিপরীতে প্রশ্ন করতে হবে, পুঁজিবাদেরও কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না।’ সেই আশাবাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে স্থির ছিলেন। তিনি প্রস্থান করেছেন। তবে তাঁর আপসহীন মনীষা দীর্ঘ সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।
মাসুদ রানা
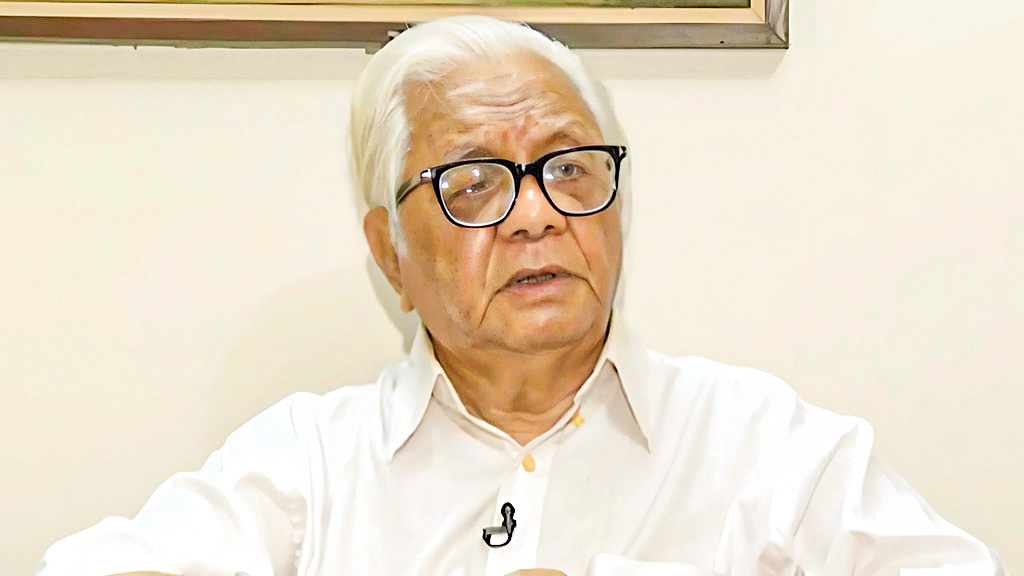
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
বদরুদ্দীন উমর একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ, লেখক-গবেষক, ইতিহাসবিদ ও মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক। ক্ষমতার কাছে মাথা নত করেননি শেষ পর্যন্ত। তাঁকে অনেকে শুধু ভাষা আন্দোলনের গবেষক হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু এর বাইরেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।
পাকিস্তান জমানায় অনেক বুদ্ধিজীবী, লেখক-গবেষকে দেশের যুগান্তকারী আন্দোলনগুলোকে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনকে একপার্শ্বিকভাবে দেখেছিলেন, তখন তিনি সেই আন্দোলনে জনমানুষের ভূমিকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের বিদ্রোহ, জনগণের কোন অংশ তাতে শক্তি জোগাল, দুর্বলতাটা কোথায় ছিল বলে আজও মুক্তি আসেনি, তা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর লিখিত তিন খণ্ডে—‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’তে।
বার্ধক্য অনেকের শরীর ও মনের শিরদাঁড়া বাঁকা করে দেয়, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে সততা ও মনীষা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সময়ের কাছে একজন রাজনীতিবিদের কাজ শুধু বিজয়ের জয়গান গাওয়া নয়, পরাজয় এবং তার কারণটা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা অনুসন্ধান এবং পথ বাতলে দেওয়াটাও অন্যতম কাজ। তিনি এই জরুরি কাজেরই অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।
পাকিস্তান আমলে তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার ট্রিলজি যেমন ‘সাম্প্রদায়িকতা’, ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’ ও ‘সংস্কৃতির সংকট’ বইগুলো পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোমর ফাঁস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিত্বের সঙ্গে মুসলমানিত্বের বিরোধ যে কৃত্রিম ব্যাপার, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়, তা যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, জাতীয়তাবাদী ধারণা শেষ পর্যন্ত কীভাবে স্বৈরতন্ত্রে রূপ নেয়, রাজনীতি যে শ্রেণির বাইরে ক্রিয়া করে না—সেসব তিনি তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। এই বই তিনটি প্রকাশ হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁর প্রতি নাখোশ হয়। পরবর্তী সময়ে জীবন কীভাবে চলবে, সে চিন্তা না করে এক মহা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাঁর লেখক-গবেষকসত্তার পাশাপাশি তিনি শুধু অক্সফোর্ড ফেরত বিদ্বানের গরিমাই ছাড়েননি, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। সেটা ১৯৬৮ সালের কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি ও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
বদরুদ্দীন উমরের আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ থেকে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও সক্রিয়তার কথা। যার শুরু ১৯৬৪ সালে। সে বছর ভিয়েতনামে মার্কিন বিমানবাহিনীর টংকিং উপসাগরে হামলার ঘটনায় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জনের বেশি শিক্ষককে সমবেত এবং বিবৃতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী হামলার প্রতিবাদ করেন। তিনি বিবৃতি সংগঠিত করেই নিষ্ক্রিয় থাকেননি; ভিয়েতনামে হামলার প্রতিবাদে তিনি মার্কিন কনস্যুলেটে চিঠি দিয়ে তিন মাসের জন্য আমেরিকায় লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যাওয়ার আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে পাকিস্তানের মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করার কারণে সরকারের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা প্রবল হতে থাকায় তিনি পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ব্রিটেনের সোয়াসয়ে পিএইচডি করতে যাওয়ার বিষয়টি আর গ্রহণ করেননি।
এরপর তিনি লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসের গিঁটগুলো খুলতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে তিনি পাল্টা যুক্তি হাজির করেন, যা এত দিন ধরে সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে মহা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সেই জায়গা ধরে তিনি হাজির করেন বঙ্গীয় রেনসাঁর পাল্টা বয়ান, যা তিনি ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক’ ও ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ’ বই দুটিতে তুলে এনেছেন। এই ধারণা আমাদের নতুন এক ইতিহাসের কাছে নিয়ে যায়। আবার বঙ্গভঙ্গ ও ভারত ভাগের দায় যে কংগ্রেস নেতাদের, সেটা প্রমাণ করে তিনি তুলে এনেছেন ‘বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি’ ও ‘ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন’ গ্রন্থে। এই বই দুটি লেখার আগপর্যন্ত জয়া চ্যাটার্জির ‘ভারত ভাগ’ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাংলা বিভাজনের রাজনীতি-অর্থনীতি’ প্রকাশিত হয়নি।
এ ধরনের লেখালেখির পাশাপাশি তাঁকে আমরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে দেখি। আমাদের দেশে রাজনীতির বাইরে গিয়ে বুদ্ধিজীবিতার চর্চার একটা রেওয়াজ প্রচলিত আছে। মানে বুদ্ধিজীবিতার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির একটা ফারাক দেখা যায়। কিন্তু তিনি রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবিতাকে সমান্তরাল রেখায় ধরে হেঁটেছেন। সে কারণে তাঁর লেখালেখি শুধু বুদ্ধিজীবিতার বুদবুদে আবিষ্ট থাকেনি, সেই লেখালেখির তাড়না তাঁকে রাজনৈতিক সক্রিয়তার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এ কারণে প্রথমে তিনি বিভিন্ন তৎকালীন পিকিংপন্থী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে পার্টির কিংবদন্তি নেতাদের সঙ্গে বাস্তব কাজের বিরোধ থেকে তিনি পার্টি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যেমন স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে বিরোধ ঘটে পিকিং ধারার অন্যতম নেতা কমরেড আবদুল হক ও তোয়াহার সঙ্গে। তাঁরা দুজন পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নিলে বদরুদ্দীন উমর সেই তত্ত্বের বিরোধিতা করে সেই সময় বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।
’৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে তিনি নতুন ভাবনায় পার্টি গঠনের দিকে অগ্রসর হন, যেটা কোনোভাবেই উপমহাদেশের প্রচলিত বাম ধারার রাজনীতির মতো রুশ, পিকিং ও মাও ধারার মতো ছিল না। তিনি পার্টি গঠনের প্রথম থেকেই নির্বাচনী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। আবার তিনি গ্রাম দিয়ে শহর দখলের রাজনীতির পথকেও ভুল বলেছেন। সে জন্য তাঁর পার্টির ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ছিল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের পথ। এই চিন্তার ধারায় তিনি আজীবন স্থির ছিলেন। যদিও তাঁর নেতৃত্বাধীন পার্টি তেমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি।
আমার কাছে মনে হয়, তাঁর মতো জেদি, সৎ ও সাহসী মানুষের রাজনৈতিক নেতা হওয়ার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? তিনি তো একাই একটি প্রতিষ্ঠান। সে কারণেই আদমজী, ফিলিপস, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা পদক প্রত্যাখ্যান করতে তিনি এতটুকু দ্বিধান্বিত ছিলেন না।
সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ‘যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ’ এবং ‘যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ’ বই দুটি সেই সময়ের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির ভিন্ন এক দৃষ্টিতে লেখা। সেসব লেখা থেকে পাঠক জানতে পারবে সেই সময়ের ঘটনার ধারা বিবরণী।
বদরুদ্দীন উমর জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছেন, পুঁজিবাদই শেষ কথা নয়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, তবে একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন পুঁজিবাদেরও শেষ পরিণতি আছে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সমাজতন্ত্রের আদৌ কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না, এ প্রশ্ন যদি কেউ তোলে, তাহলে এর বিপরীতে প্রশ্ন করতে হবে, পুঁজিবাদেরও কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না।’ সেই আশাবাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে স্থির ছিলেন। তিনি প্রস্থান করেছেন। তবে তাঁর আপসহীন মনীষা দীর্ঘ সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।
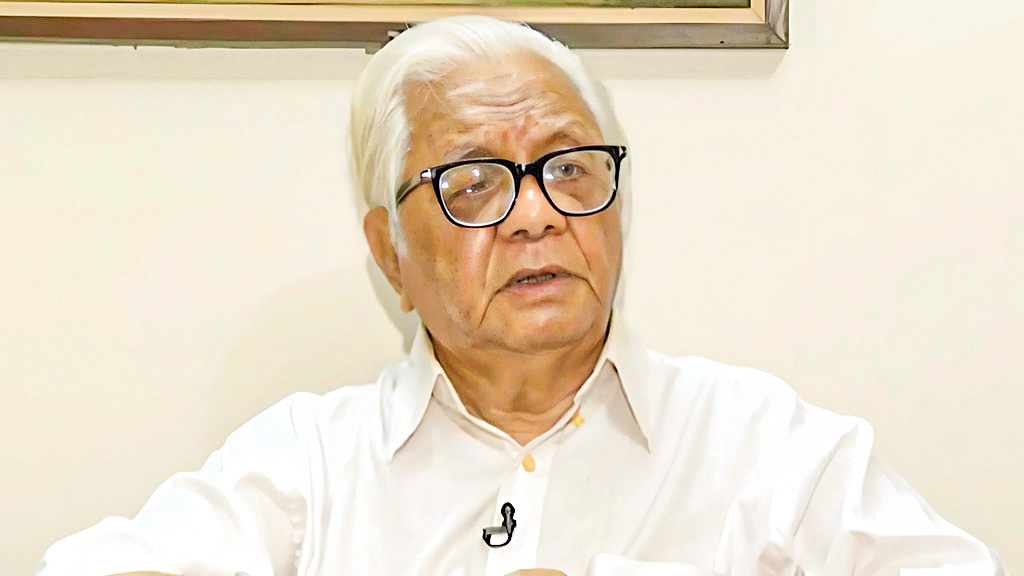
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
বদরুদ্দীন উমর একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ, লেখক-গবেষক, ইতিহাসবিদ ও মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক। ক্ষমতার কাছে মাথা নত করেননি শেষ পর্যন্ত। তাঁকে অনেকে শুধু ভাষা আন্দোলনের গবেষক হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু এর বাইরেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।
পাকিস্তান জমানায় অনেক বুদ্ধিজীবী, লেখক-গবেষকে দেশের যুগান্তকারী আন্দোলনগুলোকে বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনকে একপার্শ্বিকভাবে দেখেছিলেন, তখন তিনি সেই আন্দোলনে জনমানুষের ভূমিকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের বিদ্রোহ, জনগণের কোন অংশ তাতে শক্তি জোগাল, দুর্বলতাটা কোথায় ছিল বলে আজও মুক্তি আসেনি, তা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর লিখিত তিন খণ্ডে—‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’তে।
বার্ধক্য অনেকের শরীর ও মনের শিরদাঁড়া বাঁকা করে দেয়, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে সততা ও মনীষা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সময়ের কাছে একজন রাজনীতিবিদের কাজ শুধু বিজয়ের জয়গান গাওয়া নয়, পরাজয় এবং তার কারণটা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা অনুসন্ধান এবং পথ বাতলে দেওয়াটাও অন্যতম কাজ। তিনি এই জরুরি কাজেরই অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।
পাকিস্তান আমলে তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার ট্রিলজি যেমন ‘সাম্প্রদায়িকতা’, ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’ ও ‘সংস্কৃতির সংকট’ বইগুলো পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোমর ফাঁস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিত্বের সঙ্গে মুসলমানিত্বের বিরোধ যে কৃত্রিম ব্যাপার, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়, তা যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, জাতীয়তাবাদী ধারণা শেষ পর্যন্ত কীভাবে স্বৈরতন্ত্রে রূপ নেয়, রাজনীতি যে শ্রেণির বাইরে ক্রিয়া করে না—সেসব তিনি তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন। এই বই তিনটি প্রকাশ হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁর প্রতি নাখোশ হয়। পরবর্তী সময়ে জীবন কীভাবে চলবে, সে চিন্তা না করে এক মহা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাঁর লেখক-গবেষকসত্তার পাশাপাশি তিনি শুধু অক্সফোর্ড ফেরত বিদ্বানের গরিমাই ছাড়েননি, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। সেটা ১৯৬৮ সালের কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি ও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।
বদরুদ্দীন উমরের আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ থেকে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও সক্রিয়তার কথা। যার শুরু ১৯৬৪ সালে। সে বছর ভিয়েতনামে মার্কিন বিমানবাহিনীর টংকিং উপসাগরে হামলার ঘটনায় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জনের বেশি শিক্ষককে সমবেত এবং বিবৃতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী হামলার প্রতিবাদ করেন। তিনি বিবৃতি সংগঠিত করেই নিষ্ক্রিয় থাকেননি; ভিয়েতনামে হামলার প্রতিবাদে তিনি মার্কিন কনস্যুলেটে চিঠি দিয়ে তিন মাসের জন্য আমেরিকায় লিডারশিপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে যাওয়ার আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। একইভাবে পাকিস্তানের মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করার কারণে সরকারের সঙ্গে তাঁর বৈরিতা প্রবল হতে থাকায় তিনি পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ব্রিটেনের সোয়াসয়ে পিএইচডি করতে যাওয়ার বিষয়টি আর গ্রহণ করেননি।
এরপর তিনি লেখালেখির মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসের গিঁটগুলো খুলতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে তিনি পাল্টা যুক্তি হাজির করেন, যা এত দিন ধরে সেখানকার বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গীয় রেনেসাঁ নিয়ে মহা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সেই জায়গা ধরে তিনি হাজির করেন বঙ্গীয় রেনসাঁর পাল্টা বয়ান, যা তিনি ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক’ ও ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ’ বই দুটিতে তুলে এনেছেন। এই ধারণা আমাদের নতুন এক ইতিহাসের কাছে নিয়ে যায়। আবার বঙ্গভঙ্গ ও ভারত ভাগের দায় যে কংগ্রেস নেতাদের, সেটা প্রমাণ করে তিনি তুলে এনেছেন ‘বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি’ ও ‘ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন’ গ্রন্থে। এই বই দুটি লেখার আগপর্যন্ত জয়া চ্যাটার্জির ‘ভারত ভাগ’ এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাংলা বিভাজনের রাজনীতি-অর্থনীতি’ প্রকাশিত হয়নি।
এ ধরনের লেখালেখির পাশাপাশি তাঁকে আমরা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে দেখি। আমাদের দেশে রাজনীতির বাইরে গিয়ে বুদ্ধিজীবিতার চর্চার একটা রেওয়াজ প্রচলিত আছে। মানে বুদ্ধিজীবিতার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির একটা ফারাক দেখা যায়। কিন্তু তিনি রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবিতাকে সমান্তরাল রেখায় ধরে হেঁটেছেন। সে কারণে তাঁর লেখালেখি শুধু বুদ্ধিজীবিতার বুদবুদে আবিষ্ট থাকেনি, সেই লেখালেখির তাড়না তাঁকে রাজনৈতিক সক্রিয়তার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এ কারণে প্রথমে তিনি বিভিন্ন তৎকালীন পিকিংপন্থী পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে পার্টির কিংবদন্তি নেতাদের সঙ্গে বাস্তব কাজের বিরোধ থেকে তিনি পার্টি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যেমন স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে বিরোধ ঘটে পিকিং ধারার অন্যতম নেতা কমরেড আবদুল হক ও তোয়াহার সঙ্গে। তাঁরা দুজন পাকিস্তানিদের পক্ষে অবস্থান নিলে বদরুদ্দীন উমর সেই তত্ত্বের বিরোধিতা করে সেই সময় বাঙালির মুক্তির সংগ্রামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।
’৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে তিনি নতুন ভাবনায় পার্টি গঠনের দিকে অগ্রসর হন, যেটা কোনোভাবেই উপমহাদেশের প্রচলিত বাম ধারার রাজনীতির মতো রুশ, পিকিং ও মাও ধারার মতো ছিল না। তিনি পার্টি গঠনের প্রথম থেকেই নির্বাচনী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। আবার তিনি গ্রাম দিয়ে শহর দখলের রাজনীতির পথকেও ভুল বলেছেন। সে জন্য তাঁর পার্টির ক্ষমতা দখলের রাজনীতি ছিল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের পথ। এই চিন্তার ধারায় তিনি আজীবন স্থির ছিলেন। যদিও তাঁর নেতৃত্বাধীন পার্টি তেমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি।
আমার কাছে মনে হয়, তাঁর মতো জেদি, সৎ ও সাহসী মানুষের রাজনৈতিক নেতা হওয়ার কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? তিনি তো একাই একটি প্রতিষ্ঠান। সে কারণেই আদমজী, ফিলিপস, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা পদক প্রত্যাখ্যান করতে তিনি এতটুকু দ্বিধান্বিত ছিলেন না।
সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ‘যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ’ এবং ‘যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ’ বই দুটি সেই সময়ের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির ভিন্ন এক দৃষ্টিতে লেখা। সেসব লেখা থেকে পাঠক জানতে পারবে সেই সময়ের ঘটনার ধারা বিবরণী।
বদরুদ্দীন উমর জীবনের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রেখেছেন, পুঁজিবাদই শেষ কথা নয়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, তবে একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন পুঁজিবাদেরও শেষ পরিণতি আছে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সমাজতন্ত্রের আদৌ কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না, এ প্রশ্ন যদি কেউ তোলে, তাহলে এর বিপরীতে প্রশ্ন করতে হবে, পুঁজিবাদেরও কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না।’ সেই আশাবাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে স্থির ছিলেন। তিনি প্রস্থান করেছেন। তবে তাঁর আপসহীন মনীষা দীর্ঘ সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

দেখতে দেখতেই যেন বছরটা শেষ হয়ে আসছে। ২০২৫ সালের হতাশা-প্রত্যাশার হিসাব কষতে কষতে বড়দিন কড়া নেড়ে দিল দরজায়। সব হতাশা ভুলে প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগমন হয়, ভালোবাসা ও একতার বাণী ছড়িয়ে।
১৩ ঘণ্টা আগে
গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে চোখ রাখলে সমাজ তার অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করতে পারে, ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পায়। এ কারণেই যুগে যুগে সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা গণমাধ্যমকে ‘শত্রু’ মনে করে এসেছে। অর্থশক্তি, পেশিশক্তি দিয়ে তারা সমাজের এই দর্পণের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে।
১৩ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় যুদ্ধের ধারণা আমূল বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সীমান্ত, সেনাবাহিনী কিংবা প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র আর একমাত্র ক্ষমতার মানদণ্ড নয়; বরং অদৃশ্য, নীরব ও প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাইবার স্পেস।
১৩ ঘণ্টা আগে
আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে তুরস্কের ভূমিকা বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল হলো, এটিকে নস্টালজিক ‘নব্য ওসমানি খেলাফত’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। বাস্তবে তুরস্ক আজ যে রাজনীতি করছে, তা আবেগের নয়, সুচিন্তিত হিসাবের। তুরস্কের এই রাজনীতি সাম্রাজ্য ফেরানোর চেষ্টা নয়, বরং শক্তির শূন্যতা কাজে লাগিয়ে...
১৩ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

দেখতে দেখতেই যেন বছরটা শেষ হয়ে আসছে। ২০২৫ সালের হতাশা-প্রত্যাশার হিসাব কষতে কষতে বড়দিন কড়া নেড়ে দিল দরজায়। সব হতাশা ভুলে প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগমন হয়, ভালোবাসা ও একতার বাণী ছড়িয়ে। এ দিনে পৃথিবীতে যিশুখ্রিষ্টের আগমন, শান্তি আর সৎপথের বার্তা নিয়ে। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাই দিনটি বিশেষ।
আজ বড়দিন। যিশুর অনুসারী তথা খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় উৎসব। পবিত্র এ দিনটি আজ বিশ্বজুড়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে। বহুবিধ সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশেও ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই মিলে উদ্যাপন করছে যিশুর জন্মদিন। গির্জা কিংবা ঘরোয়া পার্বণ—সবখানে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হচ্ছে সেই যিশুকে, যিনি বেথলেহেমের এক গোয়ালঘরে জন্মেছিলেন। স্মরণ করা হচ্ছে তাঁর জন্মের পবিত্র লগ্নকে।
আজ যিশুর বন্দনা গাওয়ার দিন। কারণ, এই দিনে ধরণিতে তাঁর আবির্ভাব হয় বিশেষ উদ্দেশ্যে—ত্রাতা হিসেবে। তিনি অন্যকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন পাপ-পঙ্কিলতা বর্জন করে করুণা, পবিত্রতা ও সুন্দর পথে কীভাবে জীবন পরিচালনা করা যায়। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা এনে মুক্তির পথ খুঁজতে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।
বড়দিনে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের কাহিনি পাঠ ও ধ্যান করা হয়। সেই কাহিনি অবলম্বনে গির্জায় এবং বাড়িতে বাড়িতে গোশালা নির্মাণ করে ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়। এ দিনে চলে গানবাজনা, নামসংকীর্তন, ভোজন, আনন্দ-উল্লাস। এসব উৎসব-আয়োজনের চেয়েও বড় ব্যাপার হয়ে ওঠে নিজেদের হৃদয়-মন ও অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস। তাই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা বড়দিনের পূর্ববর্তী চার সপ্তাহব্যাপী ধ্যান-অনুধ্যান, মন পরীক্ষা, ব্যক্তিগত পাপ স্বীকার, সমবেত পুনর্মিলন বা ক্ষমা-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষে-মানুষে সুসম্পর্ক গড়তে সচেষ্ট হন।
ঈশ্বরের মহান বার্তাবাহক যিশুকে অনুসরণ করলে কতই না সুন্দর একটি সমাজ গঠন করা যায়! অথচ পাপাচারের পৃথিবীতে সেই সমাজ থেকে আমরা যোজন যোজন দূরে বাস করি। মানবজাতির জন্য এ এক দুর্ভাগ্য! এ রকম সংকটের মুহূর্তেই যিশুর বাণী, বড়দিনের বার্তা যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—মানুষে-মানুষে ভালোবাসা ও একতার বীজ বুনতে হবে; ধর্ম-বর্ণ-জাতিনির্বিশেষে সবার প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কোনো জাতি, ধর্ম বা তার অনুসারীর প্রতিই বিরুদ্ধাচরণ কাম্য নয়।
বড়দিন উপলক্ষে প্রতিবছর বাংলাদেশে সরকারি ছুটি থাকে। শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপনের পাশাপাশি দিনটিতে প্রিয় স্বদেশের মঙ্গল কামনার জন্য খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা প্রার্থনা করতে ভোলেন না। এই প্রার্থনা আর শান্তিরাজ যিশুর দেখানো পথে চলার প্রয়াসই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারে। বড়দিন সবাইকে বারবার সুযোগ দেয় দুর্নীতি, অনাচার, পাপাচার বর্জন করে সৎপথে চলার। সেই সুযোগ হেলায় হারানো যাবে না। বরং কাজে লাগিয়ে গড়তে হবে একতার বাংলাদেশ; যে বাংলাদেশে ধর্মকে পুঁজি করে মিথ্যা অপবাদে কাউকে হত্যা করা হবে না—সে যে কেউ হোক।
সবার জীবনে বড়দিন শান্তি বয়ে আনুক। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা।

দেখতে দেখতেই যেন বছরটা শেষ হয়ে আসছে। ২০২৫ সালের হতাশা-প্রত্যাশার হিসাব কষতে কষতে বড়দিন কড়া নেড়ে দিল দরজায়। সব হতাশা ভুলে প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগমন হয়, ভালোবাসা ও একতার বাণী ছড়িয়ে। এ দিনে পৃথিবীতে যিশুখ্রিষ্টের আগমন, শান্তি আর সৎপথের বার্তা নিয়ে। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাই দিনটি বিশেষ।
আজ বড়দিন। যিশুর অনুসারী তথা খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় উৎসব। পবিত্র এ দিনটি আজ বিশ্বজুড়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে। বহুবিধ সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশেও ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই মিলে উদ্যাপন করছে যিশুর জন্মদিন। গির্জা কিংবা ঘরোয়া পার্বণ—সবখানে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হচ্ছে সেই যিশুকে, যিনি বেথলেহেমের এক গোয়ালঘরে জন্মেছিলেন। স্মরণ করা হচ্ছে তাঁর জন্মের পবিত্র লগ্নকে।
আজ যিশুর বন্দনা গাওয়ার দিন। কারণ, এই দিনে ধরণিতে তাঁর আবির্ভাব হয় বিশেষ উদ্দেশ্যে—ত্রাতা হিসেবে। তিনি অন্যকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। শিখিয়েছেন পাপ-পঙ্কিলতা বর্জন করে করুণা, পবিত্রতা ও সুন্দর পথে কীভাবে জীবন পরিচালনা করা যায়। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা এনে মুক্তির পথ খুঁজতে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তিনি।
বড়দিনে যিশুখ্রিষ্টের জন্মের কাহিনি পাঠ ও ধ্যান করা হয়। সেই কাহিনি অবলম্বনে গির্জায় এবং বাড়িতে বাড়িতে গোশালা নির্মাণ করে ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়। এ দিনে চলে গানবাজনা, নামসংকীর্তন, ভোজন, আনন্দ-উল্লাস। এসব উৎসব-আয়োজনের চেয়েও বড় ব্যাপার হয়ে ওঠে নিজেদের হৃদয়-মন ও অন্তরাত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস। তাই খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা বড়দিনের পূর্ববর্তী চার সপ্তাহব্যাপী ধ্যান-অনুধ্যান, মন পরীক্ষা, ব্যক্তিগত পাপ স্বীকার, সমবেত পুনর্মিলন বা ক্ষমা-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষে-মানুষে সুসম্পর্ক গড়তে সচেষ্ট হন।
ঈশ্বরের মহান বার্তাবাহক যিশুকে অনুসরণ করলে কতই না সুন্দর একটি সমাজ গঠন করা যায়! অথচ পাপাচারের পৃথিবীতে সেই সমাজ থেকে আমরা যোজন যোজন দূরে বাস করি। মানবজাতির জন্য এ এক দুর্ভাগ্য! এ রকম সংকটের মুহূর্তেই যিশুর বাণী, বড়দিনের বার্তা যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—মানুষে-মানুষে ভালোবাসা ও একতার বীজ বুনতে হবে; ধর্ম-বর্ণ-জাতিনির্বিশেষে সবার প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কোনো জাতি, ধর্ম বা তার অনুসারীর প্রতিই বিরুদ্ধাচরণ কাম্য নয়।
বড়দিন উপলক্ষে প্রতিবছর বাংলাদেশে সরকারি ছুটি থাকে। শান্তিপূর্ণভাবে উদ্যাপনের পাশাপাশি দিনটিতে প্রিয় স্বদেশের মঙ্গল কামনার জন্য খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা প্রার্থনা করতে ভোলেন না। এই প্রার্থনা আর শান্তিরাজ যিশুর দেখানো পথে চলার প্রয়াসই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারে। বড়দিন সবাইকে বারবার সুযোগ দেয় দুর্নীতি, অনাচার, পাপাচার বর্জন করে সৎপথে চলার। সেই সুযোগ হেলায় হারানো যাবে না। বরং কাজে লাগিয়ে গড়তে হবে একতার বাংলাদেশ; যে বাংলাদেশে ধর্মকে পুঁজি করে মিথ্যা অপবাদে কাউকে হত্যা করা হবে না—সে যে কেউ হোক।
সবার জীবনে বড়দিন শান্তি বয়ে আনুক। সবাইকে বড়দিনের শুভেচ্ছা।
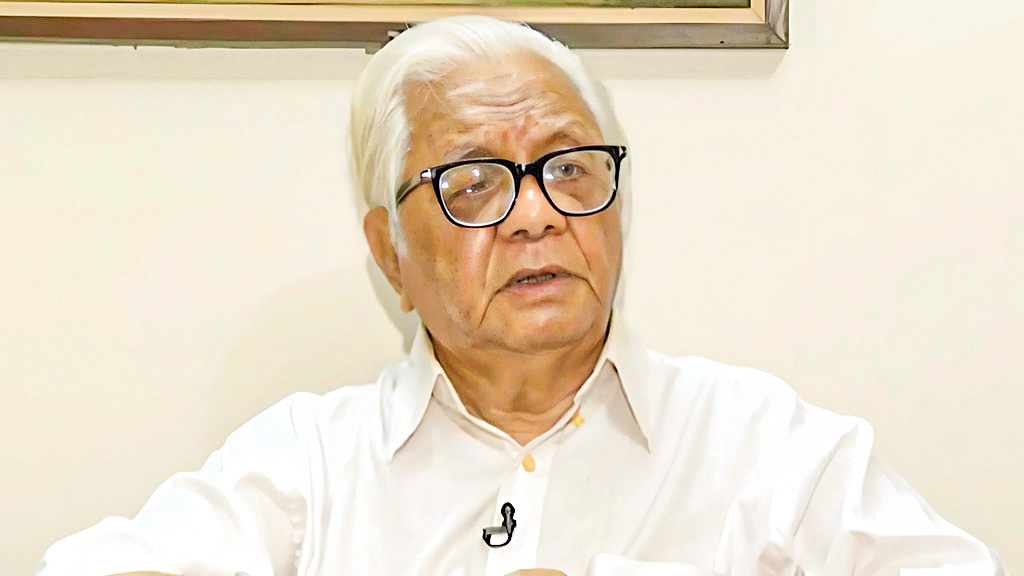
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে চোখ রাখলে সমাজ তার অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করতে পারে, ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পায়। এ কারণেই যুগে যুগে সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা গণমাধ্যমকে ‘শত্রু’ মনে করে এসেছে। অর্থশক্তি, পেশিশক্তি দিয়ে তারা সমাজের এই দর্পণের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে।
১৩ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় যুদ্ধের ধারণা আমূল বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সীমান্ত, সেনাবাহিনী কিংবা প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র আর একমাত্র ক্ষমতার মানদণ্ড নয়; বরং অদৃশ্য, নীরব ও প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাইবার স্পেস।
১৩ ঘণ্টা আগে
আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে তুরস্কের ভূমিকা বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল হলো, এটিকে নস্টালজিক ‘নব্য ওসমানি খেলাফত’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। বাস্তবে তুরস্ক আজ যে রাজনীতি করছে, তা আবেগের নয়, সুচিন্তিত হিসাবের। তুরস্কের এই রাজনীতি সাম্রাজ্য ফেরানোর চেষ্টা নয়, বরং শক্তির শূন্যতা কাজে লাগিয়ে...
১৩ ঘণ্টা আগেরাজিউল হাসান

গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে চোখ রাখলে সমাজ তার অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করতে পারে, ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পায়। এ কারণেই যুগে যুগে সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা গণমাধ্যমকে ‘শত্রু’ মনে করে এসেছে। অর্থশক্তি, পেশিশক্তি দিয়ে তারা সমাজের এই দর্পণের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে। সেই ধারাবাহিকতা ২০২৫ সালেও ছিল। এ বছরেও গণমাধ্যম আক্রান্ত হয়েছে, সাংবাদিকদের প্রাণ গেছে।
সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা ফ্রান্সের প্যারিসভিত্তিক আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডাসের তথ্য বলছে, বিদ্বেষ ও দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে ২০২৫ সালেও সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। এ বছর পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিক শুধু প্রাণই দেননি, তাঁরা হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তুও হয়েছেন।
সংগঠনটির তথ্য বলছে, বিগত ১২ মাসে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকসহ ৬৭ জন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৩ জনই প্রাণ দিয়েছেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অপরাধী চক্রের লক্ষ্যবস্তু হয়ে। এই ৬৭ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই প্রাণ গেছে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে। এ ছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধেও সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে সাংবাদিকদের। আফ্রিকার দেশ সুদান সাংবাদিকদের জন্য হয়ে উঠেছে প্রাণঘাতী যুদ্ধক্ষেত্র। মেক্সিকোয় অপরাধী চক্রের হাতে প্রাণ গেছে ৯ সাংবাদিকের। উত্তর আমেরিকার এই দেশটিকে বলা হয় সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের দ্বিতীয় বিপজ্জনক রাষ্ট্র।
সাংবাদিকেরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শুধু প্রাণই দিচ্ছেন না, তাঁরা আটক-গ্রেপ্তারেরও শিকার হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অন্তত ৫০৩ জন সাংবাদিক কারান্তরীণ হয়ে আছেন।
কেবল অপরাধ চক্রের উৎপাতে অতিষ্ঠ দেশ কিংবা যুদ্ধকবলিত দেশই নয়, গণতন্ত্রের চর্চার দাবি করা দেশেও সাংবাদিকেরা দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকের ওপর সহিংসতা বেড়ে গেছে। ফ্রিডম অব দ্য প্রেস ফাউন্ডেশন নামের অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যত সাংবাদিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তা গত তিন বছরের মোট সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনার সংখ্যার বেশি।
ফ্রিডম অব দ্য প্রেস ফাউন্ডেশন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে নিপীড়নের শিকার সাংবাদিকদের বেশির ভাগই আক্রান্ত হয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা।
প্রশ্ন উঠতে পারে, সাংবাদিক কেন আক্রান্ত হন? বিশ্বজুড়েই দেখা যায়, যখন কোথাও অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়, সাংবাদিক সেখানে যান পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করতে। তিনি কারও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করেন না। শুধু জনসাধারণকে সঠিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টায় কোনো না কোনো পক্ষ ক্ষুব্ধ হয় সেই পক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশ হওয়ার ভয়ে।
আবার অপরাধী চক্র সাংবাদিককে আক্রমণ করে তাদের গোমর ফাঁসের ভয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বেশি থাকে। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে মানবাধিকারের বালাই থাকে না। মাঠের পরিস্থিতি যেন বিশ্বমানবতা জানতে না পারে, সে চেষ্টার অংশ হিসেবে আক্রমণ করা হয় সাংবাদিককে।
কখনো কখনো শুধু রোষের বশেও সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করা হয়। শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী না, কখনো কখনো রাষ্ট্রও গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরে। সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, এর উদাহরণ বিশ্বজুড়েই রয়েছে। নতুন করে আর কোনো দেশের নামোল্লেখ করতে চাই না।
কিন্তু গণমাধ্যম সরকার ও সমাজের বন্ধু হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল সমাজের নানা ত্রুটি তুলে ধরে গণমাধ্যম রাষ্ট্র গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। গণমাধ্যম সে প্রচেষ্টা করেও যাচ্ছে। গণমাধ্যমের শাসক কিংবা কোনো গোষ্ঠীর ‘দাসে’ পরিণত হওয়ার রেকর্ড যদিও আছে, কিন্তু সেটা হাতে গোনা বলা চলে। বাকি গণমাধ্যমগুলো সমাজকে সঠিক পথ দেখাতেই নিরন্তর কাজ করে চলেছে। উদাহরণও আছে ভূরি ভূরি। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে ওয়াশিংটন পোস্ট ও দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ভূমিকা রেখেছিল, তা যুগ যুগ ধরে আলোচনা হবে। কিংবা হাল আমলে যুক্তরাজ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের করোনাকালীন ভূমিকা বিবিসি, গার্ডিয়ানসহ সে দেশের গণমাধ্যমগুলো যেভাবে প্রকাশ করেছিল, সেটাও বড় উদাহরণ।
একটি জাতি গঠন কিংবা সমাজ গঠন—যে গঠনের কথাই বলা হোক না কেন, গণমাধ্যমের ভূমিকা কিছুতেই খাটো করে দেখা যাবে না। সমাজের ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরাই সাংবাদিকের কাজ। এমনকি শাসক দল যখন বিরোধী দলের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়, তখন গণমাধ্যমই তাদের কথা সবার সামনে তুলে ধরে। অথচ এমনও দেখা গেছে, সেই বিরোধী দল যখন সরকারে যায়, তারাও গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করেছে। এভাবেই যুগে যুগে সংবাদমাধ্যমকে বাকরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, এখনো হচ্ছে।
আমরা যদি একটু গভীরে ভাবি, তাহলে দেখব, সাংবাদিক যে পারিশ্রমিক পান, সে তুলনায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যে ঝুঁকি নেন, তা অনেক অনেক বেশি। কার এমন দায় পড়েছে নগণ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি জীবনের ঝুঁকি নেবেন। তারপরও তিনি ঝুঁকি নেন দায়িত্বের জায়গা থেকে, তিনি ঝুঁকি নেন জনসাধারণকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার নেশা থেকে। এই নেশাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া উচিত, দমন করা উচিত নয়। গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ মানে একটি সমাজের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া। সেটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
একবার ভাবুন, একটি দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ যদি পুরোদমে রোধ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রের অবস্থা কী হবে। কেবল ‘বাতাবি লেবুর রেকর্ড ফলনেরই’ গান শুনতে হবে পত্রিকার পাতায়, টেলিভিশনের পর্দায়। কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে কেউ থাকবে না কথা বলার।
কাজেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সবার জন্যই জরুরি। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে গণমাধ্যমের সেই স্বাধীনতার সুযোগে সে দূর করতে পারে সমাজের পঙ্কিলতা। বিরোধীরা চাইলে সেই স্বাধীনতার সুযোগে সরকারের অন্ধকার দিকগুলো সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারবে। এভাবে পুরো সমাজ-রাষ্ট্রে নিশ্চিত হতে পারে জবাবদিহি।
কিন্তু বিশ্বে গণমাধ্যম নিয়ে এমন নীতি খুব কমই দেখা যায়। বরং উল্টো ঘটনাই বেশি ঘটছে। তারপরও গণমাধ্যম তার কাজ করে চলেছে, যাবে। কারণ, গণমাধ্যম হলো ফিনিক্স পাখির মতো। সে আক্রান্ত হবে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, তারপর সেখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। গণমাধ্যম এমন একটি শিল্প, এমন একটি দায়বদ্ধতা, যা কখনো কোনো দিন কোনো হামলা, হুমকি, ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না।

গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে চোখ রাখলে সমাজ তার অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করতে পারে, ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পায়। এ কারণেই যুগে যুগে সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা গণমাধ্যমকে ‘শত্রু’ মনে করে এসেছে। অর্থশক্তি, পেশিশক্তি দিয়ে তারা সমাজের এই দর্পণের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে। সেই ধারাবাহিকতা ২০২৫ সালেও ছিল। এ বছরেও গণমাধ্যম আক্রান্ত হয়েছে, সাংবাদিকদের প্রাণ গেছে।
সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা ফ্রান্সের প্যারিসভিত্তিক আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডাসের তথ্য বলছে, বিদ্বেষ ও দায়মুক্তির সংস্কৃতির কারণে ২০২৫ সালেও সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। এ বছর পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিক শুধু প্রাণই দেননি, তাঁরা হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তুও হয়েছেন।
সংগঠনটির তথ্য বলছে, বিগত ১২ মাসে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকসহ ৬৭ জন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৩ জনই প্রাণ দিয়েছেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অপরাধী চক্রের লক্ষ্যবস্তু হয়ে। এই ৬৭ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরই প্রাণ গেছে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে। এ ছাড়া ইউক্রেন যুদ্ধেও সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে সাংবাদিকদের। আফ্রিকার দেশ সুদান সাংবাদিকদের জন্য হয়ে উঠেছে প্রাণঘাতী যুদ্ধক্ষেত্র। মেক্সিকোয় অপরাধী চক্রের হাতে প্রাণ গেছে ৯ সাংবাদিকের। উত্তর আমেরিকার এই দেশটিকে বলা হয় সাংবাদিকদের জন্য বিশ্বের দ্বিতীয় বিপজ্জনক রাষ্ট্র।
সাংবাদিকেরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শুধু প্রাণই দিচ্ছেন না, তাঁরা আটক-গ্রেপ্তারেরও শিকার হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে অন্তত ৫০৩ জন সাংবাদিক কারান্তরীণ হয়ে আছেন।
কেবল অপরাধ চক্রের উৎপাতে অতিষ্ঠ দেশ কিংবা যুদ্ধকবলিত দেশই নয়, গণতন্ত্রের চর্চার দাবি করা দেশেও সাংবাদিকেরা দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকের ওপর সহিংসতা বেড়ে গেছে। ফ্রিডম অব দ্য প্রেস ফাউন্ডেশন নামের অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যত সাংবাদিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তা গত তিন বছরের মোট সাংবাদিক নিপীড়নের ঘটনার সংখ্যার বেশি।
ফ্রিডম অব দ্য প্রেস ফাউন্ডেশন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে নিপীড়নের শিকার সাংবাদিকদের বেশির ভাগই আক্রান্ত হয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা।
প্রশ্ন উঠতে পারে, সাংবাদিক কেন আক্রান্ত হন? বিশ্বজুড়েই দেখা যায়, যখন কোথাও অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয়, সাংবাদিক সেখানে যান পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করতে। তিনি কারও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করেন না। শুধু জনসাধারণকে সঠিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টায় কোনো না কোনো পক্ষ ক্ষুব্ধ হয় সেই পক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশ হওয়ার ভয়ে।
আবার অপরাধী চক্র সাংবাদিককে আক্রমণ করে তাদের গোমর ফাঁসের ভয়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আরও বেশি থাকে। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে মানবাধিকারের বালাই থাকে না। মাঠের পরিস্থিতি যেন বিশ্বমানবতা জানতে না পারে, সে চেষ্টার অংশ হিসেবে আক্রমণ করা হয় সাংবাদিককে।
কখনো কখনো শুধু রোষের বশেও সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করা হয়। শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী না, কখনো কখনো রাষ্ট্রও গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরে। সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, এর উদাহরণ বিশ্বজুড়েই রয়েছে। নতুন করে আর কোনো দেশের নামোল্লেখ করতে চাই না।
কিন্তু গণমাধ্যম সরকার ও সমাজের বন্ধু হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল সমাজের নানা ত্রুটি তুলে ধরে গণমাধ্যম রাষ্ট্র গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। গণমাধ্যম সে প্রচেষ্টা করেও যাচ্ছে। গণমাধ্যমের শাসক কিংবা কোনো গোষ্ঠীর ‘দাসে’ পরিণত হওয়ার রেকর্ড যদিও আছে, কিন্তু সেটা হাতে গোনা বলা চলে। বাকি গণমাধ্যমগুলো সমাজকে সঠিক পথ দেখাতেই নিরন্তর কাজ করে চলেছে। উদাহরণও আছে ভূরি ভূরি। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে ওয়াশিংটন পোস্ট ও দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ভূমিকা রেখেছিল, তা যুগ যুগ ধরে আলোচনা হবে। কিংবা হাল আমলে যুক্তরাজ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের করোনাকালীন ভূমিকা বিবিসি, গার্ডিয়ানসহ সে দেশের গণমাধ্যমগুলো যেভাবে প্রকাশ করেছিল, সেটাও বড় উদাহরণ।
একটি জাতি গঠন কিংবা সমাজ গঠন—যে গঠনের কথাই বলা হোক না কেন, গণমাধ্যমের ভূমিকা কিছুতেই খাটো করে দেখা যাবে না। সমাজের ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরাই সাংবাদিকের কাজ। এমনকি শাসক দল যখন বিরোধী দলের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়, তখন গণমাধ্যমই তাদের কথা সবার সামনে তুলে ধরে। অথচ এমনও দেখা গেছে, সেই বিরোধী দল যখন সরকারে যায়, তারাও গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করেছে। এভাবেই যুগে যুগে সংবাদমাধ্যমকে বাকরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, এখনো হচ্ছে।
আমরা যদি একটু গভীরে ভাবি, তাহলে দেখব, সাংবাদিক যে পারিশ্রমিক পান, সে তুলনায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যে ঝুঁকি নেন, তা অনেক অনেক বেশি। কার এমন দায় পড়েছে নগণ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি জীবনের ঝুঁকি নেবেন। তারপরও তিনি ঝুঁকি নেন দায়িত্বের জায়গা থেকে, তিনি ঝুঁকি নেন জনসাধারণকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার নেশা থেকে। এই নেশাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া উচিত, দমন করা উচিত নয়। গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ মানে একটি সমাজের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া। সেটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
একবার ভাবুন, একটি দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ যদি পুরোদমে রোধ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেই রাষ্ট্রের অবস্থা কী হবে। কেবল ‘বাতাবি লেবুর রেকর্ড ফলনেরই’ গান শুনতে হবে পত্রিকার পাতায়, টেলিভিশনের পর্দায়। কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে কেউ থাকবে না কথা বলার।
কাজেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সবার জন্যই জরুরি। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে গণমাধ্যমের সেই স্বাধীনতার সুযোগে সে দূর করতে পারে সমাজের পঙ্কিলতা। বিরোধীরা চাইলে সেই স্বাধীনতার সুযোগে সরকারের অন্ধকার দিকগুলো সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারবে। এভাবে পুরো সমাজ-রাষ্ট্রে নিশ্চিত হতে পারে জবাবদিহি।
কিন্তু বিশ্বে গণমাধ্যম নিয়ে এমন নীতি খুব কমই দেখা যায়। বরং উল্টো ঘটনাই বেশি ঘটছে। তারপরও গণমাধ্যম তার কাজ করে চলেছে, যাবে। কারণ, গণমাধ্যম হলো ফিনিক্স পাখির মতো। সে আক্রান্ত হবে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, তারপর সেখান থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। গণমাধ্যম এমন একটি শিল্প, এমন একটি দায়বদ্ধতা, যা কখনো কোনো দিন কোনো হামলা, হুমকি, ত্রাসের কাছে মাথা নত করবে না।
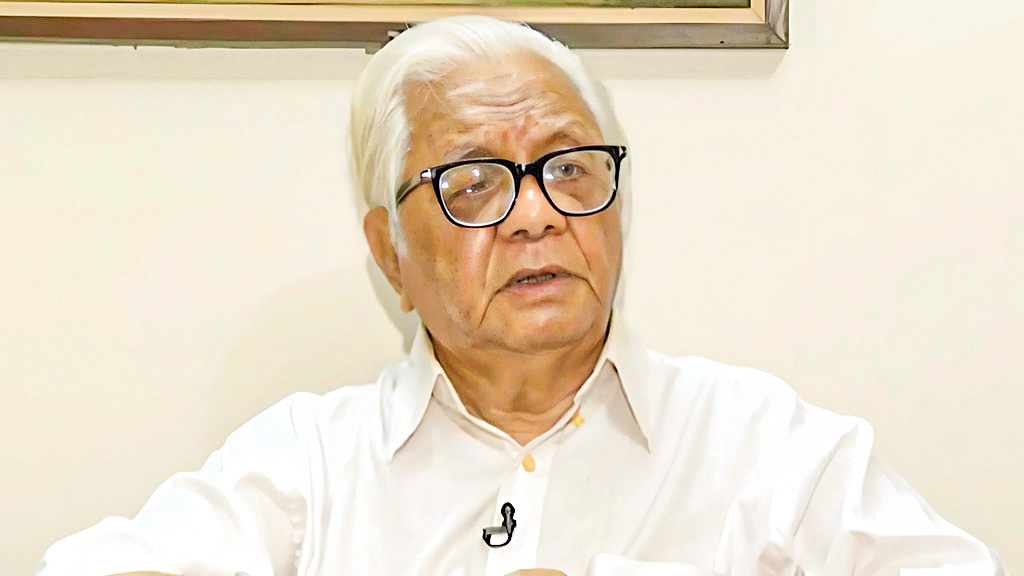
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দেখতে দেখতেই যেন বছরটা শেষ হয়ে আসছে। ২০২৫ সালের হতাশা-প্রত্যাশার হিসাব কষতে কষতে বড়দিন কড়া নেড়ে দিল দরজায়। সব হতাশা ভুলে প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগমন হয়, ভালোবাসা ও একতার বাণী ছড়িয়ে।
১৩ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় যুদ্ধের ধারণা আমূল বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সীমান্ত, সেনাবাহিনী কিংবা প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র আর একমাত্র ক্ষমতার মানদণ্ড নয়; বরং অদৃশ্য, নীরব ও প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাইবার স্পেস।
১৩ ঘণ্টা আগে
আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে তুরস্কের ভূমিকা বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল হলো, এটিকে নস্টালজিক ‘নব্য ওসমানি খেলাফত’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। বাস্তবে তুরস্ক আজ যে রাজনীতি করছে, তা আবেগের নয়, সুচিন্তিত হিসাবের। তুরস্কের এই রাজনীতি সাম্রাজ্য ফেরানোর চেষ্টা নয়, বরং শক্তির শূন্যতা কাজে লাগিয়ে...
১৩ ঘণ্টা আগেড. জাহাঙ্গীর আলম সরকার

একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় যুদ্ধের ধারণা আমূল বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সীমান্ত, সেনাবাহিনী কিংবা প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র আর একমাত্র ক্ষমতার মানদণ্ড নয়; বরং অদৃশ্য, নীরব ও প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাইবার স্পেস। আজ তথ্যই শক্তি, ডেটাই অস্ত্র এবং নেটওয়ার্কই নতুন ফ্রন্টলাইন। রাষ্ট্রের অর্থনীতি, সামরিক সক্ষমতা, কূটনীতি, এমনকি নাগরিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে উঠছে ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর।
সাইবার যুদ্ধ এখন আর কল্পবিজ্ঞান নয়; এটি বাস্তব, চলমান এবং ক্রমাগত বিস্তৃত এক বৈশ্বিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা অচল করা, ব্যাংকিং সিস্টেমে অনুপ্রবেশ, নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ, ভুয়া তথ্য ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ—সবকিছুই আজ সাইবার আক্রমণের আওতায় পড়ে। এসব আক্রমণ কোনো যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই, কোনো গুলির শব্দ ছাড়াই একটি রাষ্ট্রকে কার্যত অচল করে দিতে পারে। ফলে সামরিক শক্তির পাশাপাশি সাইবার সক্ষমতা এখন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।
এরই সঙ্গে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে নজরদারি প্রযুক্তি। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ, যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ডেটা বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকছে। ক্যামেরা, বায়োমেট্রিক ডেটা, মেটাডেটা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—সবকিছুই নজরদারির আওতায় চলে আসছে। এতে একদিকে সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধ দমনের সম্ভাবনা তৈরি হলেও, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, গোপনীয়তা ও মানবাধিকারের প্রশ্নও তীব্র হয়ে উঠছে।
এই প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কোন পথে যাচ্ছে—সে প্রশ্ন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। সাইবার অস্ত্র প্রতিযোগিতা, ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব, তথ্যনির্ভর আধিপত্য এবং প্রযুক্তিগত অসমতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করছে। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যেখানে প্রযুক্তিকে আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে, সেখানে উন্নয়নশীল ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো পড়ছে নতুন ধরনের ঝুঁকির মুখে।
এই কলামে সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তির উদ্ভব, রাষ্ট্রীয় কৌশলে এর প্রভাব এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তাকাঠামোর ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা হবে। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হবে—নিরাপত্তার নামে কতটা নজরদারি গ্রহণযোগ্য এবং এই অদৃশ্য যুদ্ধের যুগে মানবিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক নৈতিকতা আদৌ টিকে থাকবে কি না।
আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থার কৌশলগত আচরণে সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সামরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রচলিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে এই অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য, ডেটা এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণই হয়ে উঠেছে প্রভাব বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বহুজাতিক করপোরেশন, হ্যাকার গোষ্ঠী, সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এবং রাষ্ট্র-সমর্থিত সাইবার ইউনিটগুলোও সাইবার স্পেসকে ব্যবহার করছে কৌশলগত সুবিধা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে।
এই প্রেক্ষাপটে সাইবার হামলা, ডিজিটাল স্পাইয়িং, তথ্য চুরি, গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কে ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রোপাগান্ডা আধুনিক সংঘাতের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কোনো একটি দেশের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা, আর্থিক খাত, সামরিক যোগাযোগ বা নির্বাচনব্যবস্থায় সামান্য ডিজিটাল হস্তক্ষেপও তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই ধরনের আক্রমণ প্রায়ই অজ্ঞাতনামা, সীমান্তহীন এবং যুদ্ধ ঘোষণার বাইরে সংঘটিত হয়, যা প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন ও নিরাপত্তাকাঠামোকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে।
ফলস্বরূপ, সাইবার যুদ্ধ এবং নজরদারি প্রযুক্তি আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত সক্ষমতা, প্রতিরক্ষা নীতি এবং নিরাপত্তা পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রগুলো শুধু আক্রমণ প্রতিরোধেই নয়, বরং আগাম হুমকি শনাক্তকরণ, প্রতিপক্ষের দুর্বলতা বিশ্লেষণ এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই প্রযুক্তির ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভর করছে। এর পাশাপাশি, সাইবার সক্ষমতা এখন আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব, সামরিক জোট এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
তবে এই বাস্তবতা শুধু প্রযুক্তিগত বা সামরিক সক্ষমতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তির বিস্তার জিওপলিটিকসের সামগ্রিক কাঠামো, রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা স্থিতিশীলতার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। ক্ষমতার ভারসাম্য, সার্বভৌমত্বের ধারণা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা—সবকিছুই নতুন করে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে এই ডিজিটাল যুগে।
এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক সাইবার ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব রাষ্ট্রগুলোর জন্য কৌশলগত সতর্কতা, নীতি সমন্বয় এবং বহুপক্ষীয় নিরাপত্তা অংশীদারত্বের প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। বৈশ্বিক নিরাপত্তা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই কলামে সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তির বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
সাইবার যুদ্ধ এবং নজরদারি প্রযুক্তি আধুনিক জিওপলিটিকসের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এটি আর শুধু প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের হাতিয়ার নয়; বরং রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত প্রভাব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা স্থিতিশীলতার মূল নির্ধারণকারী। প্রতিটি ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, তথ্যপ্রবাহ এবং নজরদারি সক্ষমতা আজ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী বা দুর্বল করতে পারে—এটি শুধু প্রযুক্তির নয়, ক্ষমতারও খেলা।
এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রগুলোর জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে কৌশলগত সতর্কতা, তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ এবং বহুপক্ষীয় অংশীদারত্বের মাধ্যমে বৈশ্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ন্যায্য এবং নিয়ন্ত্রিত সাইবার ক্ষমতার ব্যবহার আজ শুধু প্রতিরক্ষা নয়; এটি রাষ্ট্রের কূটনীতি, শক্তি ভারসাম্য এবং আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার রক্ষাকবচে পরিণত হয়েছে।
ফলস্বরূপ আধুনিক জিওপলিটিকসে সাইবার যুদ্ধ এবং নজরদারি প্রযুক্তি শুধু এক হাতিয়ার নয়; এটি রাষ্ট্রগুলোর ভবিষ্যৎ, বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি রক্ষার এক অদৃশ্য, কিন্তু শক্তিশালী ভিত্তি। প্রযুক্তির অদৃশ্য স্রোতগুলোর মধ্যে আজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং প্রভাবের মান নির্ধারিত হচ্ছে—এটি আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা, যা দীর্ঘদিন আমাদের স্মৃতিতে এবং নীতিতে টেকসই রেশ রেখে যাবে।

একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় যুদ্ধের ধারণা আমূল বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সীমান্ত, সেনাবাহিনী কিংবা প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র আর একমাত্র ক্ষমতার মানদণ্ড নয়; বরং অদৃশ্য, নীরব ও প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাইবার স্পেস। আজ তথ্যই শক্তি, ডেটাই অস্ত্র এবং নেটওয়ার্কই নতুন ফ্রন্টলাইন। রাষ্ট্রের অর্থনীতি, সামরিক সক্ষমতা, কূটনীতি, এমনকি নাগরিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে উঠছে ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর।
সাইবার যুদ্ধ এখন আর কল্পবিজ্ঞান নয়; এটি বাস্তব, চলমান এবং ক্রমাগত বিস্তৃত এক বৈশ্বিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ। বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা অচল করা, ব্যাংকিং সিস্টেমে অনুপ্রবেশ, নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ, ভুয়া তথ্য ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ—সবকিছুই আজ সাইবার আক্রমণের আওতায় পড়ে। এসব আক্রমণ কোনো যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই, কোনো গুলির শব্দ ছাড়াই একটি রাষ্ট্রকে কার্যত অচল করে দিতে পারে। ফলে সামরিক শক্তির পাশাপাশি সাইবার সক্ষমতা এখন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।
এরই সঙ্গে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে নজরদারি প্রযুক্তি। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে রাষ্ট্রগুলো নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ, যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ডেটা বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকছে। ক্যামেরা, বায়োমেট্রিক ডেটা, মেটাডেটা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—সবকিছুই নজরদারির আওতায় চলে আসছে। এতে একদিকে সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধ দমনের সম্ভাবনা তৈরি হলেও, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, গোপনীয়তা ও মানবাধিকারের প্রশ্নও তীব্র হয়ে উঠছে।
এই প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কোন পথে যাচ্ছে—সে প্রশ্ন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। সাইবার অস্ত্র প্রতিযোগিতা, ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব, তথ্যনির্ভর আধিপত্য এবং প্রযুক্তিগত অসমতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করছে। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো যেখানে প্রযুক্তিকে আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে, সেখানে উন্নয়নশীল ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো পড়ছে নতুন ধরনের ঝুঁকির মুখে।
এই কলামে সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তির উদ্ভব, রাষ্ট্রীয় কৌশলে এর প্রভাব এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তাকাঠামোর ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা হবে। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হবে—নিরাপত্তার নামে কতটা নজরদারি গ্রহণযোগ্য এবং এই অদৃশ্য যুদ্ধের যুগে মানবিক মূল্যবোধ ও আন্তর্জাতিক নৈতিকতা আদৌ টিকে থাকবে কি না।
আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থার কৌশলগত আচরণে সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সামরিক শক্তি প্রদর্শনের প্রচলিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে এই অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে তথ্য, ডেটা এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর নিয়ন্ত্রণই হয়ে উঠেছে প্রভাব বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বহুজাতিক করপোরেশন, হ্যাকার গোষ্ঠী, সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এবং রাষ্ট্র-সমর্থিত সাইবার ইউনিটগুলোও সাইবার স্পেসকে ব্যবহার করছে কৌশলগত সুবিধা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে।
এই প্রেক্ষাপটে সাইবার হামলা, ডিজিটাল স্পাইয়িং, তথ্য চুরি, গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কে ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রোপাগান্ডা আধুনিক সংঘাতের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কোনো একটি দেশের বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা, আর্থিক খাত, সামরিক যোগাযোগ বা নির্বাচনব্যবস্থায় সামান্য ডিজিটাল হস্তক্ষেপও তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই ধরনের আক্রমণ প্রায়ই অজ্ঞাতনামা, সীমান্তহীন এবং যুদ্ধ ঘোষণার বাইরে সংঘটিত হয়, যা প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন ও নিরাপত্তাকাঠামোকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে।
ফলস্বরূপ, সাইবার যুদ্ধ এবং নজরদারি প্রযুক্তি আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত সক্ষমতা, প্রতিরক্ষা নীতি এবং নিরাপত্তা পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রগুলো শুধু আক্রমণ প্রতিরোধেই নয়, বরং আগাম হুমকি শনাক্তকরণ, প্রতিপক্ষের দুর্বলতা বিশ্লেষণ এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই প্রযুক্তির ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভর করছে। এর পাশাপাশি, সাইবার সক্ষমতা এখন আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব, সামরিক জোট এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
তবে এই বাস্তবতা শুধু প্রযুক্তিগত বা সামরিক সক্ষমতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তির বিস্তার জিওপলিটিকসের সামগ্রিক কাঠামো, রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা স্থিতিশীলতার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে। ক্ষমতার ভারসাম্য, সার্বভৌমত্বের ধারণা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা—সবকিছুই নতুন করে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে এই ডিজিটাল যুগে।
এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক সাইবার ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব রাষ্ট্রগুলোর জন্য কৌশলগত সতর্কতা, নীতি সমন্বয় এবং বহুপক্ষীয় নিরাপত্তা অংশীদারত্বের প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। বৈশ্বিক নিরাপত্তা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই কলামে সাইবার যুদ্ধ ও নজরদারি প্রযুক্তির বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
সাইবার যুদ্ধ এবং নজরদারি প্রযুক্তি আধুনিক জিওপলিটিকসের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এটি আর শুধু প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের হাতিয়ার নয়; বরং রাষ্ট্রগুলোর কৌশলগত প্রভাব, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা স্থিতিশীলতার মূল নির্ধারণকারী। প্রতিটি ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, তথ্যপ্রবাহ এবং নজরদারি সক্ষমতা আজ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী বা দুর্বল করতে পারে—এটি শুধু প্রযুক্তির নয়, ক্ষমতারও খেলা।
এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রগুলোর জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে কৌশলগত সতর্কতা, তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ এবং বহুপক্ষীয় অংশীদারত্বের মাধ্যমে বৈশ্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ন্যায্য এবং নিয়ন্ত্রিত সাইবার ক্ষমতার ব্যবহার আজ শুধু প্রতিরক্ষা নয়; এটি রাষ্ট্রের কূটনীতি, শক্তি ভারসাম্য এবং আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার রক্ষাকবচে পরিণত হয়েছে।
ফলস্বরূপ আধুনিক জিওপলিটিকসে সাইবার যুদ্ধ এবং নজরদারি প্রযুক্তি শুধু এক হাতিয়ার নয়; এটি রাষ্ট্রগুলোর ভবিষ্যৎ, বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তি রক্ষার এক অদৃশ্য, কিন্তু শক্তিশালী ভিত্তি। প্রযুক্তির অদৃশ্য স্রোতগুলোর মধ্যে আজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং প্রভাবের মান নির্ধারিত হচ্ছে—এটি আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা, যা দীর্ঘদিন আমাদের স্মৃতিতে এবং নীতিতে টেকসই রেশ রেখে যাবে।
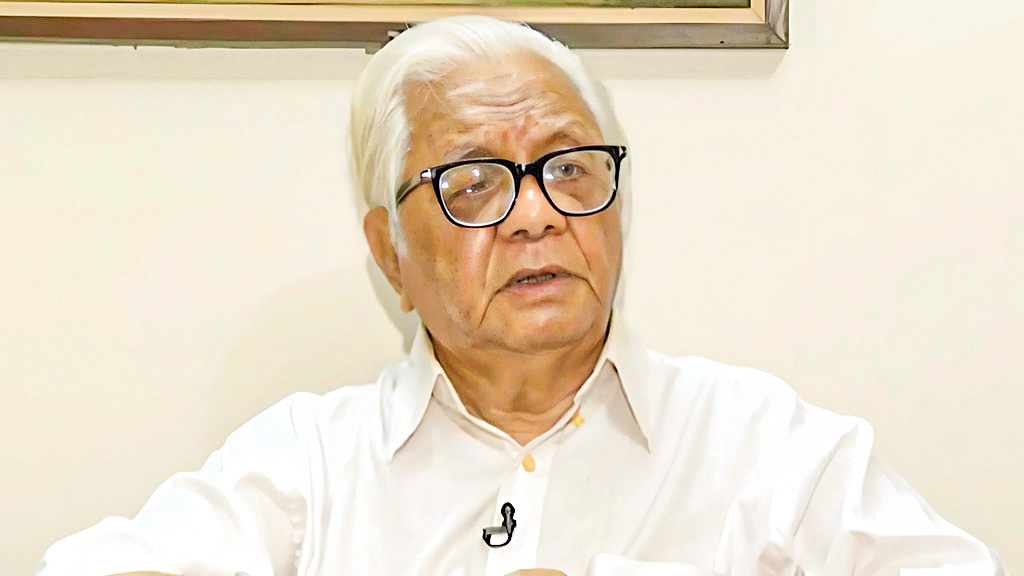
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দেখতে দেখতেই যেন বছরটা শেষ হয়ে আসছে। ২০২৫ সালের হতাশা-প্রত্যাশার হিসাব কষতে কষতে বড়দিন কড়া নেড়ে দিল দরজায়। সব হতাশা ভুলে প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগমন হয়, ভালোবাসা ও একতার বাণী ছড়িয়ে।
১৩ ঘণ্টা আগে
গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে চোখ রাখলে সমাজ তার অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করতে পারে, ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পায়। এ কারণেই যুগে যুগে সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা গণমাধ্যমকে ‘শত্রু’ মনে করে এসেছে। অর্থশক্তি, পেশিশক্তি দিয়ে তারা সমাজের এই দর্পণের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে।
১৩ ঘণ্টা আগে
আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে তুরস্কের ভূমিকা বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল হলো, এটিকে নস্টালজিক ‘নব্য ওসমানি খেলাফত’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। বাস্তবে তুরস্ক আজ যে রাজনীতি করছে, তা আবেগের নয়, সুচিন্তিত হিসাবের। তুরস্কের এই রাজনীতি সাম্রাজ্য ফেরানোর চেষ্টা নয়, বরং শক্তির শূন্যতা কাজে লাগিয়ে...
১৩ ঘণ্টা আগেআব্দুর রহমান

আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে তুরস্কের ভূমিকা বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল হলো, এটিকে নস্টালজিক ‘নব্য ওসমানি খেলাফত’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। বাস্তবে তুরস্ক আজ যে রাজনীতি করছে, তা আবেগের নয়, সুচিন্তিত হিসাবের। তুরস্কের এই রাজনীতি সাম্রাজ্য ফেরানোর চেষ্টা নয়, বরং শক্তির শূন্যতা কাজে লাগিয়ে প্রভাব বাড়ানোর একধরনের নিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা কমে আসা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৌশলগত দ্বিধা এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভেতর তুরস্ক নিজেকে এমন এক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করাও কঠিন, আবার উপেক্ষা করাও অসম্ভব। গাজা থেকে লিবিয়া, কাতার থেকে সুদান—সর্বত্রই এখন তুরস্কের প্রভাব রয়েছে।
উত্তর আফ্রিকার দেশ সুদানের ক্ষেত্রে তুরস্কের ভূমিকা সরাসরি সামরিক নয়, কিন্তু কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লোহিতসাগর অঞ্চলে সুদানের অবস্থান তুরস্ককে দীর্ঘদিন আকর্ষণ করে আসছে। সাওয়াকিন দ্বীপ পুনর্গঠনের আগ্রহ, মানবিক সহায়তা এবং অবকাঠামো সহযোগিতার মাধ্যমে আঙ্কারা সেখানে একটি উপস্থিতি তৈরি করেছে। কেবল তা-ই নয়, সুদানে চলমান গৃহযুদ্ধেও তুরস্ক সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। দেশটিতে আঙ্কারা বিদ্যমান সরকার ও সেনাবাহিনীর—যা সুদান আর্মড ফোর্সেস বা এসএএফ নামে পরিচিত—পক্ষ নিয়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এসএএফ এখন তুরস্ক ও মিসরের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার আশা করছে।
গত বছর থেকেই তুরস্ক সুদানের সেনাবাহিনীকে ড্রোন, আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ও কমান্ড সেন্টার সরবরাহ করছে। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এমনকি তুর্কি ড্রোনচালকেরাও বর্তমানে সুদানের ভেতরে কাজ করছেন। তবে এটি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য অস্বস্তিকর। কারণ, তারা সুদানকে নিজেদের নিরাপত্তাবলয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। তুরস্ক এখানে সংঘাতে না গিয়ে ভবিষ্যতের বিকল্প তৈরি করছে, যা দেশটিকে সরাসরি হুমকি নয়, কিন্তু সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
গাজা ইস্যুতে তুরস্কের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হলেও সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত। আঙ্কারা ফিলিস্তিন প্রশ্নে উচ্চকিত অবস্থান নিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং মানবিক সহায়তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। এতে আরব জনমতের বড় অংশে তুরস্ক নৈতিকভাবে জায়গা করে নিয়েছে। বাস্তবে তুরস্ক গাজায় সামরিকভাবে জড়ায়নি এবং জড়াতে চায়ও না। কারণ, সরাসরি সামরিক সম্পৃক্ততা মানে ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণমাত্রার সংঘাত, যা তুরস্কের বৃহত্তর আঞ্চলিক কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
কিন্তু গাজায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে যে যুদ্ধবিরতি অর্জিত হয়েছে, তাতে তুরস্কের সক্রিয় ভূমিকা আছে। ফলে গাজা তুরস্কের জন্য নৈতিক পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্র, সামরিক আধিপত্য বিস্তারের নয়। এই অবস্থান মিসর ও জর্ডানের জন্য অস্বস্তিকর, কারণ তারা গাজা ইস্যুতে ঐতিহাসিক মধ্যস্থতার ভূমিকা হারানোর ঝুঁকি অনুভব করে। এই অবস্থায় গাজায় তুরস্কের ভূমিকা শুধু ত্রাণ নয়, এটি তুরস্ককে মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্গঠনে একটি কেন্দ্রীয় কূটনৈতিক ভূমিকায় বসাবে। এতে এই অঞ্চলে তুরস্কের নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়াবে।
লিবিয়ায় তুরস্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করেছে। এখানে আঙ্কারা প্রমাণ করেছে যে, দেশটি কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত। ২০১৯-২০ সালে জাতিসংঘ স্বীকৃত ত্রিপোলিভিত্তিক সরকারকে তুরস্কের ড্রোন, সামরিক উপদেষ্টা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বায়রাকতার টিবি-২ ড্রোন ব্যবহার করে মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত হাফতার বাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয় তুরস্ক। এটি শুধু লিবিয়ার যুদ্ধের ফলাফল বদলায়নি, বরং পুরো আরব বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে তুরস্ক চাইলে আঞ্চলিক সংঘাতে নির্ধারক ভূমিকা নিতে পারে। এই কারণেই লিবিয়ায় তুরস্ক অনেক আরব শাসকের চোখে সরাসরি হুমকি।
মিসরের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ছিল তীব্র বৈরিতায় ভরা। মুসলিম ব্রাদারহুড প্রশ্ন, লিবিয়ার যুদ্ধ এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের গ্যাসকেন্দ্রিক রাজনীতি এই দ্বন্দ্বকে গভীর করে তোলে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে এগিয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, নিরাপত্তা সংলাপ এবং যৌথ নৌ-মহড়ার আলোচনা দেখায় যে উভয় পক্ষই বুঝেছে—স্থায়ী বৈরিতা উভয়ের কৌশলগত স্বার্থের বিরুদ্ধে। এটি কোনো আদর্শগত সমঝোতা নয়, বরং শীতল বাস্তববাদ। মিসর তুরস্ককে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, তুরস্কও মিসরকে বন্ধু মনে করে না, কিন্তু উভয়ই জানে সংঘাতের ব্যয় অনেক বেশি।
ইরানের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক আরও জটিল। একদিকে পশ্চিমা চাপ মোকাবিলায় বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সমন্বয়, অন্যদিকে সিরিয়া, ইরাক ও ককেশাসে প্রভাব বিস্তার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইরান তুরস্ককে সুন্নি প্রভাব বিস্তারের একটি সম্ভাব্য বাহক হিসেবে দেখে, যা শিয়া-বলয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তবু দুই দেশই সরাসরি সংঘাতে যায় না, কারণ সংঘাত মানে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বহিরাগত শক্তির জন্য সুযোগ তৈরি করা। এই কারণে ইরান-তুরস্ক সম্পর্ক সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে সাম্প্রতিক সময়ে।
তবে তুরস্কের আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সিরিয়ায় দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল-আসাদের পতন ঘটিয়ে বিদ্রোহী নেতা আহমেদ আল-শারাকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করার মাধ্যমে। ২০১৭ সাল থেকেই তুরস্ক আল-শারার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। তারপর ক্রমান্বয়ে আল-শারার বাহিনীকে সামরিক ও কৌশলগত সহায়তা দিয়ে সিরিয়ার মসনদ পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দেয় আঙ্কারা। তুরস্ক মূলত দুটি কারণে আল-শারার বাহিনীকে সমর্থন দিয়েছে। এক. সিরিয়ায় নিজের কৌশলগত অবস্থান দৃঢ় করা এবং দুই. দেশটি থেকে বিশেষ করে আল-শারার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা ইদলিব থেকে যেন শরণার্থীর ঢেউ নিজ ভূখণ্ডে প্রবেশ না করে, তা নিশ্চিত করা। তুরস্ক কেবল আল-শারা এবং তাঁর বাহিনীকে সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতেই সহায়তা করেনি, পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার যোগাযোগেরও মাধ্যম ছিল তারা।
আরব দুনিয়াজুড়ে এই ভূমিকাগুলোকে একসূত্রে বাঁধে তুরস্কের সামরিক শিল্প। গত এক দশকে তুরস্ক প্রতিরক্ষা খাতে যে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে, সেটিই তার ভূরাজনৈতিক সক্রিয়তার ভিত্তি। কাতার, মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া এমনকি কিছু উপসাগরীয় দেশ তুরস্কের ড্রোন ও সাঁজোয়া যান কিনেছে বা কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে। এর কারণ কেবল দাম নয়, পশ্চিমা অস্ত্র কেনার সঙ্গে রাজনৈতিক শর্ত, মানবাধিকার প্রশ্ন ও দীর্ঘ ডেলিভারি সময় জড়িত থাকে। তুরস্ক এই জায়গায় নিজেকে একটি বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে, যেখানে প্রযুক্তি যথেষ্ট আধুনিক, দাম তুলনামূলক কম এবং রাজনৈতিক শর্ত সীমিত। এতে আরব রাষ্ট্রগুলোর কাছে তুরস্ক শুধু অস্ত্র সরবরাহকারী নয়, বরং কৌশলগত বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
এই সামরিক শিল্পের প্রভাব আরব বিশ্বে দ্বিমুখী। একদিকে কিছু রাষ্ট্র তুরস্ককে অংশীদার হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। কাতারের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। কাতারে তুর্কি সামরিক ঘাঁটি, যৌথ মহড়া এবং অস্ত্র সরবরাহ একটি গভীর নিরাপত্তা অংশীদারত্ব তৈরি করেছে। অন্যদিকে মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো তুরস্কের সামরিক শিল্পকে একটি সুপ্ত হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ, এই শিল্প তুরস্ককে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যের শক্তি দেয় না, বরং প্রয়োজনে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করার সক্ষমতাও দেয়, যেমনটি লিবিয়ায় দেখা গেছে।
আরব বিশ্বে তুরস্কের সামরিক শিল্পের আরেকটি প্রভাব হলো আত্মবিশ্বাসের রাজনীতি। বহু দশক ধরে আরব রাষ্ট্রগুলো সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তুরস্কের উত্থান দেখিয়েছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশও পরিকল্পিত বিনিয়োগ, রাষ্ট্রীয় সমর্থন এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বমানের সামরিক প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে। এটি আরব সমাজের ভেতরে একধরনের অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে, যদিও শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা সব সময় স্বস্তিকর নয়।
তুরস্ক ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির শূন্যতা পূরণের একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। বিশেষ করে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে যখন ইরানের প্রভাব কিছুটা ক্ষয়ের দিকে, তখন সেই জায়গা দখলে তুরস্ক দ্রুতলয়ে এগিয়ে আসছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইরানের প্রভাব যখন কমে গেছে, তুরস্ক তা ব্যবহার করে পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে নিজের অভিলাষ জাহির করছে। এটি শুধুই প্রতিরক্ষা নয়; সমগ্র অঞ্চলই নিজ প্রভাববলয়ে আনার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান তুরস্ক নতুন করে কোনো অটোমান বা ওসমানি সালতানাত গড়ছে না, কিন্তু প্রভাব বিস্তার করছে। দেশটি পুরো ব্যবস্থাকে ভাঙছে না, কিন্তু নিয়ম বদলাচ্ছে। এই নিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সক্ষমতাই তুরস্ককে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে।

আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে তুরস্কের ভূমিকা বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল হলো, এটিকে নস্টালজিক ‘নব্য ওসমানি খেলাফত’ বলে উড়িয়ে দেওয়া। বাস্তবে তুরস্ক আজ যে রাজনীতি করছে, তা আবেগের নয়, সুচিন্তিত হিসাবের। তুরস্কের এই রাজনীতি সাম্রাজ্য ফেরানোর চেষ্টা নয়, বরং শক্তির শূন্যতা কাজে লাগিয়ে প্রভাব বাড়ানোর একধরনের নিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
আরব বিশ্ব ও মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা কমে আসা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কৌশলগত দ্বিধা এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভেতর তুরস্ক নিজেকে এমন এক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করাও কঠিন, আবার উপেক্ষা করাও অসম্ভব। গাজা থেকে লিবিয়া, কাতার থেকে সুদান—সর্বত্রই এখন তুরস্কের প্রভাব রয়েছে।
উত্তর আফ্রিকার দেশ সুদানের ক্ষেত্রে তুরস্কের ভূমিকা সরাসরি সামরিক নয়, কিন্তু কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লোহিতসাগর অঞ্চলে সুদানের অবস্থান তুরস্ককে দীর্ঘদিন আকর্ষণ করে আসছে। সাওয়াকিন দ্বীপ পুনর্গঠনের আগ্রহ, মানবিক সহায়তা এবং অবকাঠামো সহযোগিতার মাধ্যমে আঙ্কারা সেখানে একটি উপস্থিতি তৈরি করেছে। কেবল তা-ই নয়, সুদানে চলমান গৃহযুদ্ধেও তুরস্ক সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। দেশটিতে আঙ্কারা বিদ্যমান সরকার ও সেনাবাহিনীর—যা সুদান আর্মড ফোর্সেস বা এসএএফ নামে পরিচিত—পক্ষ নিয়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এসএএফ এখন তুরস্ক ও মিসরের কাছ থেকে অস্ত্র পাওয়ার আশা করছে।
গত বছর থেকেই তুরস্ক সুদানের সেনাবাহিনীকে ড্রোন, আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ও কমান্ড সেন্টার সরবরাহ করছে। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে। এমনকি তুর্কি ড্রোনচালকেরাও বর্তমানে সুদানের ভেতরে কাজ করছেন। তবে এটি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য অস্বস্তিকর। কারণ, তারা সুদানকে নিজেদের নিরাপত্তাবলয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। তুরস্ক এখানে সংঘাতে না গিয়ে ভবিষ্যতের বিকল্প তৈরি করছে, যা দেশটিকে সরাসরি হুমকি নয়, কিন্তু সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।
গাজা ইস্যুতে তুরস্কের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হলেও সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রিত। আঙ্কারা ফিলিস্তিন প্রশ্নে উচ্চকিত অবস্থান নিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং মানবিক সহায়তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। এতে আরব জনমতের বড় অংশে তুরস্ক নৈতিকভাবে জায়গা করে নিয়েছে। বাস্তবে তুরস্ক গাজায় সামরিকভাবে জড়ায়নি এবং জড়াতে চায়ও না। কারণ, সরাসরি সামরিক সম্পৃক্ততা মানে ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণমাত্রার সংঘাত, যা তুরস্কের বৃহত্তর আঞ্চলিক কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
কিন্তু গাজায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে যে যুদ্ধবিরতি অর্জিত হয়েছে, তাতে তুরস্কের সক্রিয় ভূমিকা আছে। ফলে গাজা তুরস্কের জন্য নৈতিক পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্র, সামরিক আধিপত্য বিস্তারের নয়। এই অবস্থান মিসর ও জর্ডানের জন্য অস্বস্তিকর, কারণ তারা গাজা ইস্যুতে ঐতিহাসিক মধ্যস্থতার ভূমিকা হারানোর ঝুঁকি অনুভব করে। এই অবস্থায় গাজায় তুরস্কের ভূমিকা শুধু ত্রাণ নয়, এটি তুরস্ককে মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্গঠনে একটি কেন্দ্রীয় কূটনৈতিক ভূমিকায় বসাবে। এতে এই অঞ্চলে তুরস্কের নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়াবে।
লিবিয়ায় তুরস্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করেছে। এখানে আঙ্কারা প্রমাণ করেছে যে, দেশটি কেবল কথায় সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তব সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত। ২০১৯-২০ সালে জাতিসংঘ স্বীকৃত ত্রিপোলিভিত্তিক সরকারকে তুরস্কের ড্রোন, সামরিক উপদেষ্টা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বায়রাকতার টিবি-২ ড্রোন ব্যবহার করে মিসর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থিত হাফতার বাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয় তুরস্ক। এটি শুধু লিবিয়ার যুদ্ধের ফলাফল বদলায়নি, বরং পুরো আরব বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে তুরস্ক চাইলে আঞ্চলিক সংঘাতে নির্ধারক ভূমিকা নিতে পারে। এই কারণেই লিবিয়ায় তুরস্ক অনেক আরব শাসকের চোখে সরাসরি হুমকি।
মিসরের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ছিল তীব্র বৈরিতায় ভরা। মুসলিম ব্রাদারহুড প্রশ্ন, লিবিয়ার যুদ্ধ এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের গ্যাসকেন্দ্রিক রাজনীতি এই দ্বন্দ্বকে গভীর করে তোলে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে এগিয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, নিরাপত্তা সংলাপ এবং যৌথ নৌ-মহড়ার আলোচনা দেখায় যে উভয় পক্ষই বুঝেছে—স্থায়ী বৈরিতা উভয়ের কৌশলগত স্বার্থের বিরুদ্ধে। এটি কোনো আদর্শগত সমঝোতা নয়, বরং শীতল বাস্তববাদ। মিসর তুরস্ককে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না, তুরস্কও মিসরকে বন্ধু মনে করে না, কিন্তু উভয়ই জানে সংঘাতের ব্যয় অনেক বেশি।
ইরানের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক আরও জটিল। একদিকে পশ্চিমা চাপ মোকাবিলায় বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সমন্বয়, অন্যদিকে সিরিয়া, ইরাক ও ককেশাসে প্রভাব বিস্তার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইরান তুরস্ককে সুন্নি প্রভাব বিস্তারের একটি সম্ভাব্য বাহক হিসেবে দেখে, যা শিয়া-বলয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তবু দুই দেশই সরাসরি সংঘাতে যায় না, কারণ সংঘাত মানে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বহিরাগত শক্তির জন্য সুযোগ তৈরি করা। এই কারণে ইরান-তুরস্ক সম্পর্ক সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে সাম্প্রতিক সময়ে।
তবে তুরস্কের আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সিরিয়ায় দীর্ঘদিনের শাসক বাশার আল-আসাদের পতন ঘটিয়ে বিদ্রোহী নেতা আহমেদ আল-শারাকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করার মাধ্যমে। ২০১৭ সাল থেকেই তুরস্ক আল-শারার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। তারপর ক্রমান্বয়ে আল-শারার বাহিনীকে সামরিক ও কৌশলগত সহায়তা দিয়ে সিরিয়ার মসনদ পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দেয় আঙ্কারা। তুরস্ক মূলত দুটি কারণে আল-শারার বাহিনীকে সমর্থন দিয়েছে। এক. সিরিয়ায় নিজের কৌশলগত অবস্থান দৃঢ় করা এবং দুই. দেশটি থেকে বিশেষ করে আল-শারার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা ইদলিব থেকে যেন শরণার্থীর ঢেউ নিজ ভূখণ্ডে প্রবেশ না করে, তা নিশ্চিত করা। তুরস্ক কেবল আল-শারা এবং তাঁর বাহিনীকে সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিতেই সহায়তা করেনি, পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার যোগাযোগেরও মাধ্যম ছিল তারা।
আরব দুনিয়াজুড়ে এই ভূমিকাগুলোকে একসূত্রে বাঁধে তুরস্কের সামরিক শিল্প। গত এক দশকে তুরস্ক প্রতিরক্ষা খাতে যে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে, সেটিই তার ভূরাজনৈতিক সক্রিয়তার ভিত্তি। কাতার, মরক্কো, তিউনিসিয়া, লিবিয়া এমনকি কিছু উপসাগরীয় দেশ তুরস্কের ড্রোন ও সাঁজোয়া যান কিনেছে বা কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে। এর কারণ কেবল দাম নয়, পশ্চিমা অস্ত্র কেনার সঙ্গে রাজনৈতিক শর্ত, মানবাধিকার প্রশ্ন ও দীর্ঘ ডেলিভারি সময় জড়িত থাকে। তুরস্ক এই জায়গায় নিজেকে একটি বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছে, যেখানে প্রযুক্তি যথেষ্ট আধুনিক, দাম তুলনামূলক কম এবং রাজনৈতিক শর্ত সীমিত। এতে আরব রাষ্ট্রগুলোর কাছে তুরস্ক শুধু অস্ত্র সরবরাহকারী নয়, বরং কৌশলগত বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
এই সামরিক শিল্পের প্রভাব আরব বিশ্বে দ্বিমুখী। একদিকে কিছু রাষ্ট্র তুরস্ককে অংশীদার হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। কাতারের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। কাতারে তুর্কি সামরিক ঘাঁটি, যৌথ মহড়া এবং অস্ত্র সরবরাহ একটি গভীর নিরাপত্তা অংশীদারত্ব তৈরি করেছে। অন্যদিকে মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো তুরস্কের সামরিক শিল্পকে একটি সুপ্ত হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ, এই শিল্প তুরস্ককে কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যের শক্তি দেয় না, বরং প্রয়োজনে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করার সক্ষমতাও দেয়, যেমনটি লিবিয়ায় দেখা গেছে।
আরব বিশ্বে তুরস্কের সামরিক শিল্পের আরেকটি প্রভাব হলো আত্মবিশ্বাসের রাজনীতি। বহু দশক ধরে আরব রাষ্ট্রগুলো সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তুরস্কের উত্থান দেখিয়েছে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশও পরিকল্পিত বিনিয়োগ, রাষ্ট্রীয় সমর্থন এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বমানের সামরিক প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে। এটি আরব সমাজের ভেতরে একধরনের অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে, যদিও শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা সব সময় স্বস্তিকর নয়।
তুরস্ক ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির শূন্যতা পূরণের একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। বিশেষ করে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে যখন ইরানের প্রভাব কিছুটা ক্ষয়ের দিকে, তখন সেই জায়গা দখলে তুরস্ক দ্রুতলয়ে এগিয়ে আসছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইরানের প্রভাব যখন কমে গেছে, তুরস্ক তা ব্যবহার করে পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে নিজের অভিলাষ জাহির করছে। এটি শুধুই প্রতিরক্ষা নয়; সমগ্র অঞ্চলই নিজ প্রভাববলয়ে আনার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান তুরস্ক নতুন করে কোনো অটোমান বা ওসমানি সালতানাত গড়ছে না, কিন্তু প্রভাব বিস্তার করছে। দেশটি পুরো ব্যবস্থাকে ভাঙছে না, কিন্তু নিয়ম বদলাচ্ছে। এই নিয়ন্ত্রিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সক্ষমতাই তুরস্ককে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ে পরিণত করেছে।
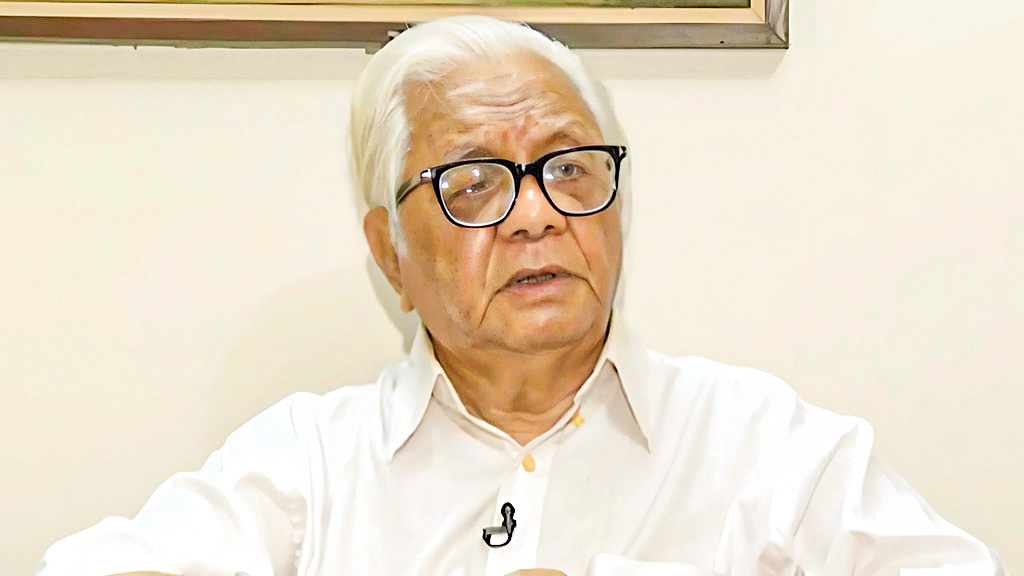
৭ সেপ্টেম্বর বদরুদ্দীন উমরের জীবনের প্রস্থান হয়েছে। তাঁর এই প্রস্থানের মধ্য দিয়ে তিন পুরুষের রাজনৈতিক ধারারও সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর দাদা আবুল কাসেম ছিলেন তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান বোর্ডের সদস্য। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। আর তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ধারার নেতা।
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দেখতে দেখতেই যেন বছরটা শেষ হয়ে আসছে। ২০২৫ সালের হতাশা-প্রত্যাশার হিসাব কষতে কষতে বড়দিন কড়া নেড়ে দিল দরজায়। সব হতাশা ভুলে প্রত্যাশা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগমন হয়, ভালোবাসা ও একতার বাণী ছড়িয়ে।
১৩ ঘণ্টা আগে
গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এই দর্পণে চোখ রাখলে সমাজ তার অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করতে পারে, ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ পায়। এ কারণেই যুগে যুগে সমাজকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ব্যক্তিরা গণমাধ্যমকে ‘শত্রু’ মনে করে এসেছে। অর্থশক্তি, পেশিশক্তি দিয়ে তারা সমাজের এই দর্পণের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে।
১৩ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় যুদ্ধের ধারণা আমূল বদলে গেছে। রাষ্ট্রের সীমান্ত, সেনাবাহিনী কিংবা প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র আর একমাত্র ক্ষমতার মানদণ্ড নয়; বরং অদৃশ্য, নীরব ও প্রযুক্তিনির্ভর এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে সাইবার স্পেস।
১৩ ঘণ্টা আগে