নজরুল জাহিদ
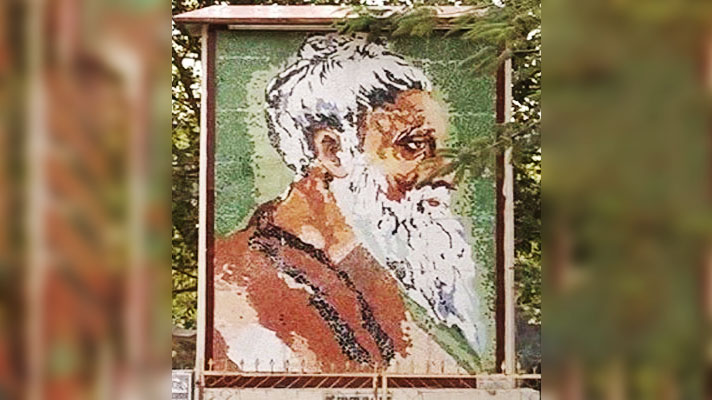
লালনের গান কেন ভালো লাগে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী হিসেবে এই ভালো লাগায় আমার কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাত আছে কি-না, লালনের গানে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ ও উচ্চারণ জানা থাকায় আমার বাড়তি সুবিধার কারণে এই ভালো লাগা কি-না, কিংবা অতি শৈশব থেকে সাধুগুরুদের আখড়ায় বসে গান শোনার, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আড্ডার কারণে আমার মনে কোনো অযৌক্তিক আগ্রহ তৈরি হয়েছে কি-না ইত্যাদি নিয়ে অনেক ভেবেছি। সেসব ভাবনার ফলাফল নিয়েই আজকের এই লেখা।
লেখাপড়া, চাকরি, আর পারিবারিক কারণে বারবার বিদেশে গেছি। কখনো অল্প সময়, কখনো-বা দু-তিন বছর একটানা বসবাস করেছি; বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে মিশেছি। অজান্তেই তুলনা করেছি নিজেদের সঙ্গে। কী আছে আমাদের, যা ওঁদের নেই? কী আমাকে আলাদা উচ্চতা দিয়েছে? কী আমাকে বিশেষ করে রাখবে আগামীতে? অনেক কিছুর মধ্যে যে বিষয়টা প্রধান বলে মনে হয়েছে, তা হলো বাংলার লোকজ সম্পদ।
এই লোকজ সম্পদই বাঙালির শক্তির আধার। সম্প্রীতির এবং আত্মোন্নতির অমীয় বাণীসমৃদ্ধ ভাববাদি ভক্তিগীতি বা দেহতত্ত্বের গানগুলো হলো এই লোকজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম। এই সম্পদই বাঙালিকে পৃথিবীর অন্য সব জাতি থেকে বিশেষ করে রেখেছে। আর লালন শাহ ফকির হলেন বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রধানতম অংশভাক।
আলাদা করে বাউল বা লালন অনুসারীদের চিনতে হয়নি। এঁদের সম্পর্কে আলাদা করে পড়তেও হয়নি। গ্রামে, পাড়ায় বা এমনকি পরিবারে এঁরা আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। এঁদেরকে চিনতাম ‘নাড়ার ফকির’ হিসেবে। ‘নাড়া’ বলতে গ্রামে গাছের ডালপালা কেটে ছেঁটে তাঁকে ছোট করাও বোঝাত। মাথা টাক করাটাও ছিল ‘মাথা নাড়া’ করা। ধান কাটা শেষে মাঠে পড়ে থাকা ধানের অবশিষ্ট অংশকে ‘ধানের নাড়া’ বলত। জসিম উদ্দীনের ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতায় আছে—
‘তুমি যদি যাও সে–সব কুড়ায়ে
নাড়ার আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে,
খাব আর যত গেঁয়ো–চাষীদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে,
হাসিয়া হাসিয়া মুঠি মুঠি তাহা বিলাইব দুইজনে।’
নিঃসন্তান বিধবা নারীদের ‘নাড়া-খাড়া বিধবা’; অর্থাৎ, পিছুটানহীন বিধবা বলা হতো। রাগসংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিষ্যের ডান হাতে লাল রংয়ের সুতা; অর্থাৎ, ‘নাড়া’ বেঁধে দিয়ে নিজ ঘরানায় গ্রহণের রেওয়াজটি আজও চালু আছে। গ্রামের বাচ্চাদের কোমরে তাবিজ বাঁধার চিকন সুতাকেও ‘নাড়া’ বলা হতো।
আমাকে একবার দিদার শাহ ফকির* ‘নাড়া’ শব্দের অর্থের সঙ্গে পবিত্র কোরআনের সুরা এখলাসের প্রসঙ্গে বলেছিলেন। তাঁর মতে, এই সুরায় আল্লাহ নিজেকে অমুখাপেক্ষী, কারও সঙ্গে সম্পৃক্ত নন অর্থে পরিচয় দিয়েছেন, যার সঙ্গে ‘নাড়া’ অর্থের মিল আছে। লালনের গানেও বেশ কয়েক স্থানে এই নাড়া শব্দের উল্লেখ আছে, যা শুনলে লালন ও তাঁর অনুসারীরা নাড়া বলতে কী বোঝেন, তা বোঝা যায়। লালন নিজেকেও নাড়া হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি আত্মাকেও নাড়া হিসেবে পরিচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন—
-‘একজন নাড়া জগৎ জোড়া, কাজটি তাহার জগৎ ছাড়া’
-‘নাড়ার সঙ্গে হয়ে নাড়ি, পরণে পরেছি ডুরি, দেবনা আঁচির কড়ি, বেড়াবো চৈতন্যের পথে’
-‘কুলের বউ ছিলাম বাড়ি/হলাম ন্যাড়ি ন্যাড়ার সাথে/কুলের আচার কুলের বিচার/আর কি ভুলি সেই ভোলাতে’
-‘দিসনে আর আঁচাই কড়ি, নাড়ার নাড়ি হও যেইরে; থাকবি ভালো, সর্বকাল যাবে দূরে’
-‘তিল পরিমাণ জায়গাতে কী কুদরতিময়! জগতজোড়া নাড়া সেথায় বারাম দেয়, বলবো কী সেই নাড়ার গুন বিচার অমাবস্যা পূর্ণিমা সদায় দীপ্তকার...’
সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হলো—লালনের মতে, ‘নাড়া’ শব্দটির অর্থ হলো শাখাহীন বা সন্তানহীন। রক্ষণশীল মুসলমানদের কাছে এঁরা গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তবে সাধারণ অর্থে এঁদের সবাই নির্বিবাদী নিরীহ ভাবুক ধরনের মানুষ মনে করত। ফলে এক ধরনের সাধারণ প্রশ্রয়ের আশ্রয়েই তাঁদের থাকতে দেখেছি, যা ইদানীং কমে গেছে।
আমার চাচির ভাই ‘নাড়ার ফকির’ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে চাচির আড়ালে অন্যরা যখন কথা বলত, তখন তাতে খুব একটা শ্রদ্ধা দেখেছি, তা নয়। বরং নাড়ার ফকির হয়ে বংশের মান নষ্ট করেছে—এমন অভিযোগ শোনা যেত। কিন্তু উনি যখন বোনের বাড়িতে আসতেন, সাদা আলখেল্লা পরা, কাঁধে একটা ঝোলা, হাতে একটা একতারা, সারাক্ষণ মুখে হাসি, আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন, যেন আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। এটা আমার ভালো লাগত। শিশুকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব আশ্চর্যের ছিল। তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।
গানের গলা ভালো ছিল না। কিন্তু প্রায় সারাক্ষণই গান গাইতেন। পরে জেনেছি, এসব গানকে ভক্তিগান, ভাবগান, বাউলগান যে নামেই ডাকি না কেন, সাধুগুরুদের জীবনে এগুলো এক অনিবার্য উপাদান। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, অর্থ বা সম্মানের জন্য তাঁরা গান করেন না। তাঁরা গান করেন আরাধনা বা সাধনার মাধ্যম হিসেবে, জীবনাচরণের অংশ হিসেবে। গানই তাঁদের মন্ত্র, স্তোত্র বা ধর্মবাণী।
জীবন কেমনভাবে যাপন করা হবে, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য বা পরিণতি কী, ভালো বা মন্দ কী দিয়ে নির্ধারিত হবে—এমন দার্শনিক বিষয় ছাড়াও এমনকি আহার-নিদ্রা-মৈথুন-সংক্রান্ত প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রশ্নের জবাবও তাঁরা গানের মাধ্যমে অনুসন্ধান করেন। তাই দেখা যায়, নিছক আনন্দ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে গান গাইতে বসেও ভক্তি আর উপলব্ধির আবেশে তাঁদের চোখ জলে ভরে ওঠে; ভক্তিরসের স্রোতধারায় আনন্দ আর বেদনার অপূর্ব মিলন ঘটে।
সেই আমার লালনের গান শোনা শুরু। আলমডাঙ্গার দিদার শাহ, রইচ উদ্দিনসহ অনেকের গান শুনতাম। আমাদের বাড়ির পাশেই মতলেব নামে এক সাধুর ছোট খুপড়ি ঘরে প্রায় সন্ধ্যায় গানের আসর বসত। আমিই ছিলাম সেই আসরের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। একসময় একুশে পদকপ্রাপ্ত খোদাবক্স সাঁইয়ের স্নেহ-সান্নিধ্য পেলাম। লালন গবেষক ড. ক্যারল সলোমনের সঙ্গে আমেরিকায় বন্ধুত্ব হলো। তাঁর আমেরিকার বাসায় মকছেদ আলী সাঁইয়ের রেকর্ডেড গান শুনলাম। এসব ‘সোনার ধানে’ আমার জীবনের গোলা ভরে গেল। লালনের গানকে প্রতিদিন যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে বুঝলাম এই গানের সুর ও বাণীর ভেতর দিয়ে নিজস্ব জীবন দর্শন ও ভাববাদী ঔদার্যমণ্ডিত অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাবাদ প্রচারিত হয়েছে। গানের মধ্যে লালন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক-দৈহিক সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন, করেছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের জয়গান।
ক্রমবর্ধমান ভেদ-বিভক্তি অসহিষ্ণুতার এই সময়ে মানুষে-মানুষে মিলনের জয়গান গাওয়ার অংশ হিসেবেই লালনের গান এখন বেশি করে শোনা ও শোনানো দরকার। তবে খেয়াল রাখা দরকার, যেন ‘বাজার’ এই গানের মরমী মাধুর্য নষ্ট না করে।
কারণ ইদানীং লক্ষ্য করছি, একদিকে এই গানের মাহাত্ম্য দেশি-বিদেশি গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে, শাহরিক সমাজে এই গান জনপ্রিয় হচ্ছে।
অন্যদিকে, জনপ্রিয়তা বাড়াতে গানগুলো নিয়ে ফিউশন ম্যাশআপ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হচ্ছে। তাতে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে গানের সুরের, আর আদর্শের। ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত বলা দরকার।
উচ্চপ্রযুক্তি ও উচ্চ তাল-লয়-মাত্রা প্রয়োগ করায় গানগুলো থেকে ভক্তিরস, আর মরমী ঔদার্য যেন হারিয়ে যাচ্ছে। লালনের গানের কথা, আর সুরের পরিবর্তন হচ্ছে। দীর্ঘকাল কপিরাইট থাকার কারণে রবীন্দ্রসংগীতের একটা মান বা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের কান তৈরি হয়ে গেছে। তাই বেসুরো রবীন্দ্রসংগীত ‘বাজার’ পায় না।
কিন্তু লালনের গান ছাপার অক্ষরে সংকলিত এবং স্বরলিপিতে নিবন্ধিত না থাকায় গানের কথায় গরমিল দেখা যাচ্ছে। নিবেদনের ভাব, ভঙ্গি বা সুরেও পরিবর্তন হচ্ছে। এ ছাড়া লালনের গানে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ আঞ্চলিক উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েছে, যা অন্য কারও দ্বারা উচ্চারণ করা কঠিন, ঠিকভাবে লেখাও সম্ভব না এবং ওই বিশেষ শব্দ বা শব্দমালার অর্থ জানা না থাকায় এসব শব্দ ঠিকভাবে গীত বা উচ্চারিত হচ্ছে না। তাই পুরো গানের রসভঙ্গ এবং অনর্থ ঘটছে। এই প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ শ্রোতা ও সমর্থক তৈরি করা এবং সত্যিকারের সাধুগুরুদের পরিবারে গান যেভাবে চর্চিত এবং গীত হয়, তা শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার বলে মনে হয়।
পাশাপাশি আরও দুটি কাজ শুরু করা দরকার। প্রথমটি হলো—সাধুগুরুদের সম্পর্কে অনেকে ভাবেন যে, তাঁদের সংসার নেই, তাঁরা অবৈজ্ঞানিক, অস্বাস্থ্যকর, নেশাসক্ত, আয়-উপার্জনহীন পরাশ্রয়ী এবং অসামাজিক ও অযাচারী। এমনকি তাঁদের পোশাক আশাক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও ভুল ধারণা আছে। যেমন—তাঁরা কমলা বা গেরুয়া রঙের আলখেল্লা ধরনের কাপড় পরেন এবং তাঁদের লম্বা চুল বা মাথায় জট আছে।
আসলে এ রকম ধারণা ভুল। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তাঁদের জীবন আমাদের আর সবার মতোই। কেউ কৃষি করেন, কেউ চাকরি বা ব্যবসা। তাঁদের ঘর-সংসার, সমাজ, সামাজিকতা—সব আছে। সাধারণ গৃহী অ-বাউলদের তুলনায় তাঁরা বরং সমাজের জন্য উপকারী। কারণ, তাঁরা যুগে যুগে কেবল আক্রান্তই হয়েছেন, কখনো আক্রমণ করেননি। যে এলাকায় তাঁদের বসবাস, সেখানকার থানায় খোঁজ নিয়ে জানা যাবে—কোনো সাধুগুরুর নামে মামলা বা অভিযোগ নেই। যে গ্রামে বা মহল্লায় তাঁদের বসবাস, সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা যাবে—তাঁরা কোনো ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত নন। তাঁরা নির্লোভ, তাই নির্বিরোধী। এমনকি পশুর গায়েও তাঁরা হাত তোলেন না। বরং, একটি নির্মল জীবনধারার মধ্যে সংগীতের সুর আর পূর্ববর্তী গুরুদের রচিত গানের বাণীর নির্দেশনা মেনে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র নির্মোহ, তথা ‘জিন্দা মরা’ হয়ে জীবনকে উপভোগ করা এবং তা অনেকের সেবায় নিযুক্ত করে শুধু মানুষ হিসেবে নয়, প্রাণী হিসেবেও প্রকৃতির সংসারে মিশে থাকা।
সাধক ও লালন সংগীতজ্ঞ খোদাবক্স সাঁইয়ের ভাষায়, ‘লালনের মূল কথা হলো মানবপ্রেম। মানুষ ভজতে হবে, গুরুর মাধ্যমে দেহ মোকামের খবর জানতে হবে, আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব—এসব বুঝতে হবে। মুর্শিদের স্বরূপ চিনে শুদ্ধ মানুষ হতে হবে।’
আরেকটি জরুরি কাজ হলো—অশান্ত-অসুখী দেশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাধুগুরুদের জীবনাদর্শের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তা প্রচার করে বিশ্বশান্তি অর্জনের পথ প্রতিষ্ঠা করা।
আমরা সবাই জন্মেই যুদ্ধ দেখেছি। আমাদের আগে যারা এই গ্রহে জন্মেছেন, তারাও যুদ্ধ দেখেছেন, যুদ্ধের শিকার হয়েছেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা এবং তাঁদের সন্তানও কি হিংসা, লোভ, আর নির্যাতনের দুনিয়া থেকে রেহাই পাবে না? যুদ্ধই কি মানবজাতির নিয়তি? শান্তি নয়? বহুবার বহুভাবে পৃথিবীতে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে।
উনিশ পিপে নস্যি ফুরিয়েছে সেই কবে, জাতিপুঞ্জ জাতিসঙ্ঘসহ হাজারো সংস্থার জন্ম হয়েছে, ব্যয়িত হয়েছে অজস্র অর্থ, রচিত হয়েছে ফরমুলা, খচিত হয়েছে তারকার পর তারকা, কিন্তু শান্তির ললিতবাণীর পাথরের মূর্তিতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়নি। অবশেষে মানবজাতি উপলব্ধি করেছে যে, ব্যক্তিজীবনে লোভ হিংসা অহং বর্জন করে মানুষ যদি ‘মানুষ’ হয়ে উঠতে পারত, যদি অন্য মানুষ ও প্রাণীকূলের অধিকার মেনে নিত, তাহলে সামষ্টিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা পেত। তাই নানা শাস্ত্র-ধর্মের বিধান প্রয়োগ করে মানুষকে মানুষ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তিজীবনে এবং ফলশ্রুতিতে সামষ্টিক জীবনে শান্তি আসেনি। এখানেই সাধুগুরুদের সাফল্য।
রবীন্দ্রনাথের ‘জুতা আবিষ্কার’-এর মতো পাদপ্রদীপের বাইরে, যাকে আমরা ‘অন্ধকার’ বলি, সেই অন্ধকারে থেকেই, বাংলার সাধুগুরু বাউল ফকিরেরা নিজেদের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, সুস্থ-নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবী সকর্মক জীবন, আত্মোন্নয়ন—এই যদি বিশ্বশান্তির মৌলিক প্যারামিটার বা মানমাত্রা হয়ে থাকে, প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে সুখসৃষ্টি করাই যদি অধুনা উন্নত নেতৃত্ব বা সংস্থার কর্মপরিকল্পনা হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেও কেবল বাংলার সাধুগুরুদের মধ্যেই সেই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটেছে। সাধুগুরুরা অতি নীরবে নিজ জীবনে এবং সেই সূত্রে তাঁর নিজ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সফল হয়েছেন। বিশ্বকে এই খবরটি জানিয়ে দেওয়াও আমাদের কর্তব্য বৈকি।
লেখক: বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির কার্যালয়ের মানবাধিকার বিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা
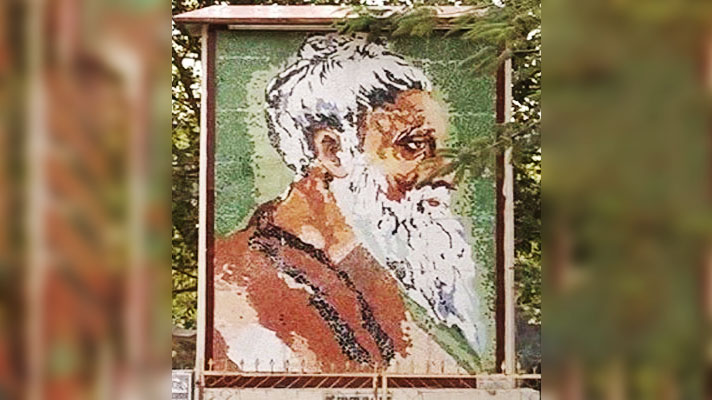
লালনের গান কেন ভালো লাগে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী হিসেবে এই ভালো লাগায় আমার কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাত আছে কি-না, লালনের গানে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ ও উচ্চারণ জানা থাকায় আমার বাড়তি সুবিধার কারণে এই ভালো লাগা কি-না, কিংবা অতি শৈশব থেকে সাধুগুরুদের আখড়ায় বসে গান শোনার, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আড্ডার কারণে আমার মনে কোনো অযৌক্তিক আগ্রহ তৈরি হয়েছে কি-না ইত্যাদি নিয়ে অনেক ভেবেছি। সেসব ভাবনার ফলাফল নিয়েই আজকের এই লেখা।
লেখাপড়া, চাকরি, আর পারিবারিক কারণে বারবার বিদেশে গেছি। কখনো অল্প সময়, কখনো-বা দু-তিন বছর একটানা বসবাস করেছি; বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে মিশেছি। অজান্তেই তুলনা করেছি নিজেদের সঙ্গে। কী আছে আমাদের, যা ওঁদের নেই? কী আমাকে আলাদা উচ্চতা দিয়েছে? কী আমাকে বিশেষ করে রাখবে আগামীতে? অনেক কিছুর মধ্যে যে বিষয়টা প্রধান বলে মনে হয়েছে, তা হলো বাংলার লোকজ সম্পদ।
এই লোকজ সম্পদই বাঙালির শক্তির আধার। সম্প্রীতির এবং আত্মোন্নতির অমীয় বাণীসমৃদ্ধ ভাববাদি ভক্তিগীতি বা দেহতত্ত্বের গানগুলো হলো এই লোকজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম। এই সম্পদই বাঙালিকে পৃথিবীর অন্য সব জাতি থেকে বিশেষ করে রেখেছে। আর লালন শাহ ফকির হলেন বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রধানতম অংশভাক।
আলাদা করে বাউল বা লালন অনুসারীদের চিনতে হয়নি। এঁদের সম্পর্কে আলাদা করে পড়তেও হয়নি। গ্রামে, পাড়ায় বা এমনকি পরিবারে এঁরা আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। এঁদেরকে চিনতাম ‘নাড়ার ফকির’ হিসেবে। ‘নাড়া’ বলতে গ্রামে গাছের ডালপালা কেটে ছেঁটে তাঁকে ছোট করাও বোঝাত। মাথা টাক করাটাও ছিল ‘মাথা নাড়া’ করা। ধান কাটা শেষে মাঠে পড়ে থাকা ধানের অবশিষ্ট অংশকে ‘ধানের নাড়া’ বলত। জসিম উদ্দীনের ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতায় আছে—
‘তুমি যদি যাও সে–সব কুড়ায়ে
নাড়ার আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে,
খাব আর যত গেঁয়ো–চাষীদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে,
হাসিয়া হাসিয়া মুঠি মুঠি তাহা বিলাইব দুইজনে।’
নিঃসন্তান বিধবা নারীদের ‘নাড়া-খাড়া বিধবা’; অর্থাৎ, পিছুটানহীন বিধবা বলা হতো। রাগসংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিষ্যের ডান হাতে লাল রংয়ের সুতা; অর্থাৎ, ‘নাড়া’ বেঁধে দিয়ে নিজ ঘরানায় গ্রহণের রেওয়াজটি আজও চালু আছে। গ্রামের বাচ্চাদের কোমরে তাবিজ বাঁধার চিকন সুতাকেও ‘নাড়া’ বলা হতো।
আমাকে একবার দিদার শাহ ফকির* ‘নাড়া’ শব্দের অর্থের সঙ্গে পবিত্র কোরআনের সুরা এখলাসের প্রসঙ্গে বলেছিলেন। তাঁর মতে, এই সুরায় আল্লাহ নিজেকে অমুখাপেক্ষী, কারও সঙ্গে সম্পৃক্ত নন অর্থে পরিচয় দিয়েছেন, যার সঙ্গে ‘নাড়া’ অর্থের মিল আছে। লালনের গানেও বেশ কয়েক স্থানে এই নাড়া শব্দের উল্লেখ আছে, যা শুনলে লালন ও তাঁর অনুসারীরা নাড়া বলতে কী বোঝেন, তা বোঝা যায়। লালন নিজেকেও নাড়া হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি আত্মাকেও নাড়া হিসেবে পরিচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন—
-‘একজন নাড়া জগৎ জোড়া, কাজটি তাহার জগৎ ছাড়া’
-‘নাড়ার সঙ্গে হয়ে নাড়ি, পরণে পরেছি ডুরি, দেবনা আঁচির কড়ি, বেড়াবো চৈতন্যের পথে’
-‘কুলের বউ ছিলাম বাড়ি/হলাম ন্যাড়ি ন্যাড়ার সাথে/কুলের আচার কুলের বিচার/আর কি ভুলি সেই ভোলাতে’
-‘দিসনে আর আঁচাই কড়ি, নাড়ার নাড়ি হও যেইরে; থাকবি ভালো, সর্বকাল যাবে দূরে’
-‘তিল পরিমাণ জায়গাতে কী কুদরতিময়! জগতজোড়া নাড়া সেথায় বারাম দেয়, বলবো কী সেই নাড়ার গুন বিচার অমাবস্যা পূর্ণিমা সদায় দীপ্তকার...’
সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায়, তা হলো—লালনের মতে, ‘নাড়া’ শব্দটির অর্থ হলো শাখাহীন বা সন্তানহীন। রক্ষণশীল মুসলমানদের কাছে এঁরা গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তবে সাধারণ অর্থে এঁদের সবাই নির্বিবাদী নিরীহ ভাবুক ধরনের মানুষ মনে করত। ফলে এক ধরনের সাধারণ প্রশ্রয়ের আশ্রয়েই তাঁদের থাকতে দেখেছি, যা ইদানীং কমে গেছে।
আমার চাচির ভাই ‘নাড়ার ফকির’ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে চাচির আড়ালে অন্যরা যখন কথা বলত, তখন তাতে খুব একটা শ্রদ্ধা দেখেছি, তা নয়। বরং নাড়ার ফকির হয়ে বংশের মান নষ্ট করেছে—এমন অভিযোগ শোনা যেত। কিন্তু উনি যখন বোনের বাড়িতে আসতেন, সাদা আলখেল্লা পরা, কাঁধে একটা ঝোলা, হাতে একটা একতারা, সারাক্ষণ মুখে হাসি, আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন, যেন আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। এটা আমার ভালো লাগত। শিশুকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব আশ্চর্যের ছিল। তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।
গানের গলা ভালো ছিল না। কিন্তু প্রায় সারাক্ষণই গান গাইতেন। পরে জেনেছি, এসব গানকে ভক্তিগান, ভাবগান, বাউলগান যে নামেই ডাকি না কেন, সাধুগুরুদের জীবনে এগুলো এক অনিবার্য উপাদান। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, অর্থ বা সম্মানের জন্য তাঁরা গান করেন না। তাঁরা গান করেন আরাধনা বা সাধনার মাধ্যম হিসেবে, জীবনাচরণের অংশ হিসেবে। গানই তাঁদের মন্ত্র, স্তোত্র বা ধর্মবাণী।
জীবন কেমনভাবে যাপন করা হবে, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য বা পরিণতি কী, ভালো বা মন্দ কী দিয়ে নির্ধারিত হবে—এমন দার্শনিক বিষয় ছাড়াও এমনকি আহার-নিদ্রা-মৈথুন-সংক্রান্ত প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রশ্নের জবাবও তাঁরা গানের মাধ্যমে অনুসন্ধান করেন। তাই দেখা যায়, নিছক আনন্দ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে গান গাইতে বসেও ভক্তি আর উপলব্ধির আবেশে তাঁদের চোখ জলে ভরে ওঠে; ভক্তিরসের স্রোতধারায় আনন্দ আর বেদনার অপূর্ব মিলন ঘটে।
সেই আমার লালনের গান শোনা শুরু। আলমডাঙ্গার দিদার শাহ, রইচ উদ্দিনসহ অনেকের গান শুনতাম। আমাদের বাড়ির পাশেই মতলেব নামে এক সাধুর ছোট খুপড়ি ঘরে প্রায় সন্ধ্যায় গানের আসর বসত। আমিই ছিলাম সেই আসরের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। একসময় একুশে পদকপ্রাপ্ত খোদাবক্স সাঁইয়ের স্নেহ-সান্নিধ্য পেলাম। লালন গবেষক ড. ক্যারল সলোমনের সঙ্গে আমেরিকায় বন্ধুত্ব হলো। তাঁর আমেরিকার বাসায় মকছেদ আলী সাঁইয়ের রেকর্ডেড গান শুনলাম। এসব ‘সোনার ধানে’ আমার জীবনের গোলা ভরে গেল। লালনের গানকে প্রতিদিন যেন নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে বুঝলাম এই গানের সুর ও বাণীর ভেতর দিয়ে নিজস্ব জীবন দর্শন ও ভাববাদী ঔদার্যমণ্ডিত অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতাবাদ প্রচারিত হয়েছে। গানের মধ্যে লালন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক-দৈহিক সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন, করেছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের জয়গান।
ক্রমবর্ধমান ভেদ-বিভক্তি অসহিষ্ণুতার এই সময়ে মানুষে-মানুষে মিলনের জয়গান গাওয়ার অংশ হিসেবেই লালনের গান এখন বেশি করে শোনা ও শোনানো দরকার। তবে খেয়াল রাখা দরকার, যেন ‘বাজার’ এই গানের মরমী মাধুর্য নষ্ট না করে।
কারণ ইদানীং লক্ষ্য করছি, একদিকে এই গানের মাহাত্ম্য দেশি-বিদেশি গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে, শাহরিক সমাজে এই গান জনপ্রিয় হচ্ছে।
অন্যদিকে, জনপ্রিয়তা বাড়াতে গানগুলো নিয়ে ফিউশন ম্যাশআপ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হচ্ছে। তাতে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে গানের সুরের, আর আদর্শের। ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত বলা দরকার।
উচ্চপ্রযুক্তি ও উচ্চ তাল-লয়-মাত্রা প্রয়োগ করায় গানগুলো থেকে ভক্তিরস, আর মরমী ঔদার্য যেন হারিয়ে যাচ্ছে। লালনের গানের কথা, আর সুরের পরিবর্তন হচ্ছে। দীর্ঘকাল কপিরাইট থাকার কারণে রবীন্দ্রসংগীতের একটা মান বা স্ট্যান্ডার্ড দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের কান তৈরি হয়ে গেছে। তাই বেসুরো রবীন্দ্রসংগীত ‘বাজার’ পায় না।
কিন্তু লালনের গান ছাপার অক্ষরে সংকলিত এবং স্বরলিপিতে নিবন্ধিত না থাকায় গানের কথায় গরমিল দেখা যাচ্ছে। নিবেদনের ভাব, ভঙ্গি বা সুরেও পরিবর্তন হচ্ছে। এ ছাড়া লালনের গানে যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের বেশ কিছু আঞ্চলিক শব্দ আঞ্চলিক উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েছে, যা অন্য কারও দ্বারা উচ্চারণ করা কঠিন, ঠিকভাবে লেখাও সম্ভব না এবং ওই বিশেষ শব্দ বা শব্দমালার অর্থ জানা না থাকায় এসব শব্দ ঠিকভাবে গীত বা উচ্চারিত হচ্ছে না। তাই পুরো গানের রসভঙ্গ এবং অনর্থ ঘটছে। এই প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ শ্রোতা ও সমর্থক তৈরি করা এবং সত্যিকারের সাধুগুরুদের পরিবারে গান যেভাবে চর্চিত এবং গীত হয়, তা শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার বলে মনে হয়।
পাশাপাশি আরও দুটি কাজ শুরু করা দরকার। প্রথমটি হলো—সাধুগুরুদের সম্পর্কে অনেকে ভাবেন যে, তাঁদের সংসার নেই, তাঁরা অবৈজ্ঞানিক, অস্বাস্থ্যকর, নেশাসক্ত, আয়-উপার্জনহীন পরাশ্রয়ী এবং অসামাজিক ও অযাচারী। এমনকি তাঁদের পোশাক আশাক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও ভুল ধারণা আছে। যেমন—তাঁরা কমলা বা গেরুয়া রঙের আলখেল্লা ধরনের কাপড় পরেন এবং তাঁদের লম্বা চুল বা মাথায় জট আছে।
আসলে এ রকম ধারণা ভুল। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তাঁদের জীবন আমাদের আর সবার মতোই। কেউ কৃষি করেন, কেউ চাকরি বা ব্যবসা। তাঁদের ঘর-সংসার, সমাজ, সামাজিকতা—সব আছে। সাধারণ গৃহী অ-বাউলদের তুলনায় তাঁরা বরং সমাজের জন্য উপকারী। কারণ, তাঁরা যুগে যুগে কেবল আক্রান্তই হয়েছেন, কখনো আক্রমণ করেননি। যে এলাকায় তাঁদের বসবাস, সেখানকার থানায় খোঁজ নিয়ে জানা যাবে—কোনো সাধুগুরুর নামে মামলা বা অভিযোগ নেই। যে গ্রামে বা মহল্লায় তাঁদের বসবাস, সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা যাবে—তাঁরা কোনো ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত নন। তাঁরা নির্লোভ, তাই নির্বিরোধী। এমনকি পশুর গায়েও তাঁরা হাত তোলেন না। বরং, একটি নির্মল জীবনধারার মধ্যে সংগীতের সুর আর পূর্ববর্তী গুরুদের রচিত গানের বাণীর নির্দেশনা মেনে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র নির্মোহ, তথা ‘জিন্দা মরা’ হয়ে জীবনকে উপভোগ করা এবং তা অনেকের সেবায় নিযুক্ত করে শুধু মানুষ হিসেবে নয়, প্রাণী হিসেবেও প্রকৃতির সংসারে মিশে থাকা।
সাধক ও লালন সংগীতজ্ঞ খোদাবক্স সাঁইয়ের ভাষায়, ‘লালনের মূল কথা হলো মানবপ্রেম। মানুষ ভজতে হবে, গুরুর মাধ্যমে দেহ মোকামের খবর জানতে হবে, আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব—এসব বুঝতে হবে। মুর্শিদের স্বরূপ চিনে শুদ্ধ মানুষ হতে হবে।’
আরেকটি জরুরি কাজ হলো—অশান্ত-অসুখী দেশিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাধুগুরুদের জীবনাদর্শের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তা প্রচার করে বিশ্বশান্তি অর্জনের পথ প্রতিষ্ঠা করা।
আমরা সবাই জন্মেই যুদ্ধ দেখেছি। আমাদের আগে যারা এই গ্রহে জন্মেছেন, তারাও যুদ্ধ দেখেছেন, যুদ্ধের শিকার হয়েছেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা এবং তাঁদের সন্তানও কি হিংসা, লোভ, আর নির্যাতনের দুনিয়া থেকে রেহাই পাবে না? যুদ্ধই কি মানবজাতির নিয়তি? শান্তি নয়? বহুবার বহুভাবে পৃথিবীতে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে।
উনিশ পিপে নস্যি ফুরিয়েছে সেই কবে, জাতিপুঞ্জ জাতিসঙ্ঘসহ হাজারো সংস্থার জন্ম হয়েছে, ব্যয়িত হয়েছে অজস্র অর্থ, রচিত হয়েছে ফরমুলা, খচিত হয়েছে তারকার পর তারকা, কিন্তু শান্তির ললিতবাণীর পাথরের মূর্তিতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়নি। অবশেষে মানবজাতি উপলব্ধি করেছে যে, ব্যক্তিজীবনে লোভ হিংসা অহং বর্জন করে মানুষ যদি ‘মানুষ’ হয়ে উঠতে পারত, যদি অন্য মানুষ ও প্রাণীকূলের অধিকার মেনে নিত, তাহলে সামষ্টিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা পেত। তাই নানা শাস্ত্র-ধর্মের বিধান প্রয়োগ করে মানুষকে মানুষ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যক্তিজীবনে এবং ফলশ্রুতিতে সামষ্টিক জীবনে শান্তি আসেনি। এখানেই সাধুগুরুদের সাফল্য।
রবীন্দ্রনাথের ‘জুতা আবিষ্কার’-এর মতো পাদপ্রদীপের বাইরে, যাকে আমরা ‘অন্ধকার’ বলি, সেই অন্ধকারে থেকেই, বাংলার সাধুগুরু বাউল ফকিরেরা নিজেদের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, সুস্থ-নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবী সকর্মক জীবন, আত্মোন্নয়ন—এই যদি বিশ্বশান্তির মৌলিক প্যারামিটার বা মানমাত্রা হয়ে থাকে, প্রতিটি ব্যক্তিজীবনে সুখসৃষ্টি করাই যদি অধুনা উন্নত নেতৃত্ব বা সংস্থার কর্মপরিকল্পনা হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেও কেবল বাংলার সাধুগুরুদের মধ্যেই সেই কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটেছে। সাধুগুরুরা অতি নীরবে নিজ জীবনে এবং সেই সূত্রে তাঁর নিজ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সফল হয়েছেন। বিশ্বকে এই খবরটি জানিয়ে দেওয়াও আমাদের কর্তব্য বৈকি।
লেখক: বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির কার্যালয়ের মানবাধিকার বিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।
৭ ঘণ্টা আগে
স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।
৭ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক
৭ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।
৭ ঘণ্টা আগেসিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।
সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।
স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।
কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।
আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।
বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।
এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।
একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।
ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।
লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।
সেটা যেন শুধু মাটির বিভাজন নয়, মানুষেরও বিভাজন হলো প্রথম। এই বিভাজন একদা অখণ্ড বঙ্গদেশের একাংশকে যুক্ত করে দিল ভারতের সঙ্গে। সেখানকার বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় দাঁড়াল ভারতীয় বলে; আরেক অংশকে শামিল করে দিল পাকিস্তানের সঙ্গে, সেখানকার বাঙালির পরিচয় দাঁড়াল পাকিস্তানি বলে। এপারের মানুষ ওপারে গেছে, ওপারের মানুষ এসেছে এপারে, মানুষের রক্তে রঙিন হয়েছে বিভক্ত মাটি ও নদী। দুই রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। দেশ দুটি মিত্র হলো না পরস্পরের এবং সেই বৈরিতা ছড়িয়ে পড়ল দুই পাশের বাঙালির মনেও। ভারতের অংশ হয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি যতটা না অসন্তুষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গের বাঙালি অসন্তুষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সে আরও এক বিভাজন ঘটিয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ত্যাগ-আত্মত্যাগে, রক্তের বিনিময়ে।
স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক কাঠামো আসলে সাতচল্লিশেই তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ইদানীং বেশি করে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী এবং আধা মৌলবাদীরা তথাকথিত লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলতে পছন্দ করে। কথাটা মিথ্যা, আদতেই।
কেননা, লাহোর প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট, হয়তো তাকে ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছিল। তাতে পাকিস্তানের কিংবা ভারত বিভাজনের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি এবং দুই অঞ্চলে দুটি ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও পরে দিল্লি সম্মেলনে প্রস্তাবটি সংশোধন করে একটা রাষ্ট্রের পক্ষেই বক্তব্য দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে একটা পাকিস্তান ভেঙে দুটি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে রক্তের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটা করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।
আমরা বলি এবং মিথ্যা বলি না যে বঙ্গবিভাগের পেছনে ইংরেজদের কারসাজি ছিল। যেমন সেটা ১৯০৫ সালে, তেমনি ১৯৪৭ সালেও বোঝা গেছে। সে সময়ের ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি তাঁর নোটে লিখেছিলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ বঙ্গ একটা শক্তি, বিভক্ত বঙ্গ নানা দিকে টানবে এবং সেটাই হবে ওই পরিকল্পনার (বঙ্গবিভাগের) একটা বড় গুণ।’ এ ছিল ইংরেজের অভিপ্রায়, কিন্তু বঙ্গদেশের নিজের মধ্যেও নিশ্চয় সেই উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল, যাদের অস্তিত্ব ওই আশাবাদকে সমর্থন করেছে। নানা দিকে টানাপোড়েন ছিল। আর তার কারণ অন্য কিছু নয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণি। মধ্যবিত্ত সর্বত্রই একটা অগোছালো ব্যাপার। তার একেক অংশে একেক প্রবণতা, তার একদিকের সঙ্গে অপর দিকের বিরোধ; পরাধীন বাংলায় পরাধীনতার কারণেই পরস্পর বিরোধিতাটা ছিল বরং বেশি। এই মধ্যবিত্ত মোটেই স্বাধীন ছিল না। তার ভিত প্রোথিত ছিল চাকরিতে, পেশায় এবং কিছুটা ভূমিরাজস্বে। শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। দুর্বল মেরুদণ্ডের এই শ্রেণির একাংশ তাই আত্মসমর্পণ করেছিল। আত্মসমর্পণকারীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ সাহেবমুখী; অপর ভাগ ইয়ং বেঙ্গল। অর্থাৎ একই সঙ্গে সাহেবমুখী ও সামন্তবাদবিরোধী। আর যে অংশটি ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী, সেটা ছিল অধীনতার বিষয়ে সচেতন এবং তাদেরকে জাতীয়তাবাদীও বলতে হবে। কিন্তু এরা মূলত সংস্কারপন্থী এবং চূড়ান্ত বিচারে, নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের জন্য আপসপন্থী ছিল। এর সূত্রপাতে আছেন রামমোহন এবং মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র।
বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে করতে হয়, কেননা তিনি ছিলেন মধ্যবিত্তের এই ধারার সবচেয়ে উজ্জ্বল ও প্রভাবশালী মুখপাত্র। বঙ্কিম ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক এবং পরাধীনতার গ্লানিতে অত্যধিক পীড়িত। কিন্তু শ্রেণিগত কারণেই তিনিও আটকা পড়ে গেলেন একটা গণ্ডিতে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি’। তাঁর এই বক্তব্য ছিল বড় স্পষ্ট। এই অনুমোদন ছিল না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হৃদয়হীনতার কথা জেনেও তার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাননি। ইংরেজ অসন্তুষ্ট হবে ভেবে, স্বাধীনতার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেননি। ইংরেজের বদলে তিনি যবনকে দাঁড় করালেন এবং সেই মৃত অশ্বকে যখন প্রহার শুরু করলেন, তখন সেই প্রহারের ভেতরে ইংরেজের প্রতি অক্ষম অসন্তোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। বিকাশে আগ্রহী মুসলমান বাঙালি মনে করল এ আর এমন কিছু নয়, তার প্রতি ঘৃণা বটে।
এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা কৃষকদের মধ্যে ছিল না, তা ছিল মধ্যবিত্তেরই ব্যাধি। তবে পরাধীন বঙ্গে জাতীয়তাবাদীরা আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ছিলেন না, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অংশের জন্য হিন্দু জাতি, আরেক অংশের জন্য মুসলিম জাতি। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তবে সেটা ছিল জনগণের সঙ্গে নয়। তা ছিল দুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে—যাদের একটা উঠেছে, আরেকটা উঠতে চাইছে।
একটা দ্বন্দ্ব ছিল ইংরেজের সঙ্গে বাঙালির; আরেকটা দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছিল বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের। প্রথম দ্বন্দ্বটা তার তীব্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের কারণে। আর হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ছিল বলেই দেশভাগ হলো। না হলে বাইরে থেকে চতুর ইংরেজ যতই কলকাঠি নাডুক না কেন, ঘটনাটি ঘটত না। ১৯০৫-এ কাজ হয়নি, তখন অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্ত এটা চায়নি। তারা অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির ব্যবচ্ছেদের আশঙ্কা করেছে। সে আশঙ্কা মোটেই অন্যায় ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল আরও এক গভীর শঙ্কা, সে হচ্ছে খণ্ডিত বঙ্গে পেশাগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জমির মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কা। ১৯৪৭ সালে সেই শ্রেণিই আবার বঙ্গভঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে পড়ল, মূলত সেই অর্থনৈতিক শঙ্কাতেই। এবারের ভয়টা ছিল অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের। অপর দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের যে অংশ উঠতে চাচ্ছিল, তারা ১৯০৫ সালেও বঙ্গভঙ্গ চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে সাতচল্লিশেও। সেটা ছিল নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে।
ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর হিন্দির চাপ কম পোহায়নি। ওই চাপ, বলা বাহুল্য, ক্রমাগত বেড়েছে। কংগ্রেসের শাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃশাসনই ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির শাসনামল তো দুঃশাসনের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রের পথে এগোতে চাচ্ছে।
লক্ষ করার বিষয়, অবিভক্ত বঙ্গে নেতৃত্ব ছিল মধ্যবিত্তের হাতেই। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত বাংলার রাজনীতিকে ভারতবর্ষের রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে পারেনি। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন গান্ধী, আরেক দিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার রাজনীতি অংশ হয়ে গেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির এবং তার চাবিকাঠি বাংলার এ কে ফজলুল হক কিংবা সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে থাকেনি, থেকেছে অবাঙালিদের হাতেই। এর কারণও শ্রেণিগত। বাঙালি মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল, অবাঙালি মধ্যবিত্তের তুলনায়। শ্রেণি অবস্থান এসব ঘটনার সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
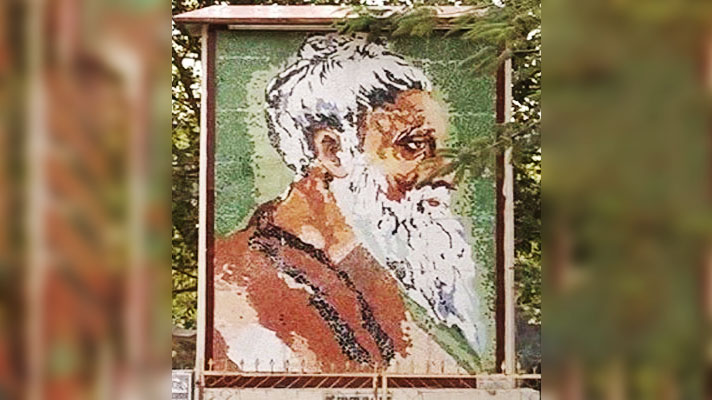
লালনের গান কেন ভালো লাগে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী হিসেবে এই ভালো লাগায় আমার কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাত আছে কি-না, লালনের গানে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ ও উচ্চারণ জানা থাকায় আমার বাড়তি সুবিধার কারণে এই ভালো
২১ অক্টোবর ২০২২
স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।
৭ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক
৭ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।
৭ ঘণ্টা আগেমাসুদ-উর রহমান

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গঠিত হওয়া অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল—এই সরকার শুধু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে না, বরং দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থেকে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।
কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অগ্রসর হওয়া গেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধীরগতিতে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। যেমন ধরা যাক, আমাদের সবচেয়ে গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা উপভোগের স্বাদ। কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ নিয়ে বিগত সরকারের সময়ে নানা অপকর্ম করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার নামের পাশে মিথ্যা সনদ জুড়ে দেওয়া শুধু প্রতারণা নয়, এটি একধরনের অপরাধ—ইতিহাস ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।
এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ বাতিল ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে’।
এটি এমন এক ঘোষণা ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি বলা যায়। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বছর পেরিয়েছে, অথচ বাস্তব অগ্রগতি দেখা যায়নি। আজও বহু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিচ্ছেন, বিপরীতে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিই পাননি। একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি যদি মিথ্যার ওপর দাঁড়ায়, তাহলে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করতে পারলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিটি যেমন মজবুত হতো, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হতো না।
২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকগুলোর খবর ছিল—‘প্রাথমিকভাবে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের কথা নিশ্চিত করেছে মিয়ানমার।’ সেই সময় অনেকে মনে করেছিলেন, অবশেষে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেল, একজন রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; বরং আরও অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে।
কক্সবাজার ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোতে এখন ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে, যাদের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নিরাপত্তা—সবই চাপে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে মিয়ানমারের প্রতি চাপ অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই জটিল সমস্যার সমাধান করা কঠিন। তবু জনগণের প্রত্যাশা ছিল—সরকার অন্তত প্রত্যাবাসনের দৃশ্যমান সূচনা করবে। কিন্তু তা হয়নি।
প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি, নদী দূষিত হচ্ছে, বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রাম ও শহর প্লাস্টিকে ভরে যাচ্ছে। পরিবেশের এই সংকট রোধে ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, ‘কাঁচাবাজারেও আজ থেকে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ’। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবায়নে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এখন বহাল তবিয়তে প্রতিটি বাজারে, এমনকি পাড়ার ছোট দোকানেও পলিথিন ব্যাগ আগের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে।
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে। অথচ কর্মসংস্থানের অভাব আজ তরুণদের সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে একটি দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘২৬ লাখ শিক্ষিত বেকারের দেশে ২৬ লাখ ভারতীয় কী করে চাকরি করে’। প্রতিবেদকের ভাষ্যমতে, ‘একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আরেকটি রাষ্ট্র কি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের “দুরভিসন্ধির” পরিকল্পনাগুলোর একটি এটি। এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে ভারতীয়দের সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ দেশে শিক্ষিত বেকার ২৬ লাখ ৪০ হাজার!’ এমন প্রতিবেদন কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি এক তীব্র প্রশ্ন—দেশে যদি এত বেকার তরুণ থাকে, তবে বিদেশিরা কেন চাকরি পাবে? এমন বাস্তবতায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশে এমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে বিদেশি কর্মীদের আর সুযোগ না থাকে। এক বছর পার হয়ে গেলেও ২৬ লাখ ভারতীয়কে চাকরিচ্যুত করার কোনো খবর এখনো গণমাধ্যমে দেখা যায়নি।
এরপর একটি স্বাধীন দেশের জন্য সার্বভৌমত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, ‘হাসিনা সরকারের আমলে করা সকল গোপন চুক্তি বাতিল করা হবে।’ কিন্তু এ বছরের ২১ অক্টোবর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা দেন, ‘ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিলের দাবি সত্য নয়’। এরপর ২৬ অক্টোবরের আরেকটি সংবাদ থেকে জানা গেল, ‘দ্বিগুণ মূল্যে কমলাপুর মেট্রোরেলের কাজ পেয়েছে ভারতীয় কোম্পানি’। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই সম্পর্ক যেন কখনোই সমমর্যাদার বাইরে না যায়। দেশের স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা রক্ষা করার জন্য বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহি অপরিহার্য।
তারপর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশে, বিশেষত ভারতে যায়। এই পরিস্থিতি বদলানোর আশায় সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, চীন বাংলাদেশে চারটি বৃহৎ বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল, ‘বড় হাসপাতাল করতে চায় চীন’। এই হাসপাতালগুলোর একটি নামও ঠিক করা হয়েছিল ‘চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল’। প্রতিশ্রুতি ছিল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল নির্মিত হবে, যাতে জনগণ উন্নত চিকিৎসা পায় এবং আর বিদেশে যেতে না হয়। কিন্তু আজও সেই হাসপাতালের জমি নির্ধারণের কাজই শুরু হয়নি, হাসপাতাল তো দূরের কথা!
এই তালিকা এখানেই শেষ নয়। এমন আরও অনেক প্রতিশ্রুতি আছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক কিছুই পরিকল্পনার স্তর পেরোতে পারছে না। অথচ এসব কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দৃঢ়তা
আর দায়িত্ববোধ।
তবু হতাশ হইনি। কারণ, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এক দিনে ঘটে না, সময় লাগে। হয়তো সরকার এখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো নীতিগত বাধা কাটানোর চেষ্টা করছে। তাই বিশ্বাস রাখতে চাই, একদিন এই ‘হতে পারত’গুলো সত্যি হবে, বাস্তবে রূপ নেবে সেই সব প্রতিশ্রুতি।
আমরা যারা এই দেশের নাগরিক, আমাদেরও দায়িত্ব শুধু সমালোচনা নয়, সচেতন থাকা, দাবি জানানো এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি করা। কারণ, সরকার, রাষ্ট্র, জাতি—সবই আমাদের সম্মিলিত সত্তা।

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে গঠিত হওয়া অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল—এই সরকার শুধু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে না, বরং দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত থেকে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবে।
কিন্তু এক বছরের বেশি সময় পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অগ্রসর হওয়া গেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ধীরগতিতে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। যেমন ধরা যাক, আমাদের সবচেয়ে গর্বের অর্জন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা উপভোগের স্বাদ। কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ নিয়ে বিগত সরকারের সময়ে নানা অপকর্ম করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার নামের পাশে মিথ্যা সনদ জুড়ে দেওয়া শুধু প্রতারণা নয়, এটি একধরনের অপরাধ—ইতিহাস ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।
এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ বাতিল ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে’।
এটি এমন এক ঘোষণা ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি বলা যায়। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বছর পেরিয়েছে, অথচ বাস্তব অগ্রগতি দেখা যায়নি। আজও বহু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিচ্ছেন, বিপরীতে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিই পাননি। একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি যদি মিথ্যার ওপর দাঁড়ায়, তাহলে সেই ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করতে পারলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তিটি যেমন মজবুত হতো, তেমনি রাষ্ট্রের অর্থের অপচয় হতো না।
২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল দেশের প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকগুলোর খবর ছিল—‘প্রাথমিকভাবে ১ লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের কথা নিশ্চিত করেছে মিয়ানমার।’ সেই সময় অনেকে মনে করেছিলেন, অবশেষে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। কিন্তু বছরের শেষে দেখা গেল, একজন রোহিঙ্গাকেও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি; বরং আরও অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে।
কক্সবাজার ও টেকনাফের আশ্রয়শিবিরগুলোতে এখন ১২ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে, যাদের কারণে স্থানীয় অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নিরাপত্তা—সবই চাপে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে মিয়ানমারের প্রতি চাপ অব্যাহত থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় এই জটিল সমস্যার সমাধান করা কঠিন। তবু জনগণের প্রত্যাশা ছিল—সরকার অন্তত প্রত্যাবাসনের দৃশ্যমান সূচনা করবে। কিন্তু তা হয়নি।
প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি, নদী দূষিত হচ্ছে, বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে, গ্রাম ও শহর প্লাস্টিকে ভরে যাচ্ছে। পরিবেশের এই সংকট রোধে ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয়, ‘কাঁচাবাজারেও আজ থেকে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ’। সেই ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবায়নে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এখন বহাল তবিয়তে প্রতিটি বাজারে, এমনকি পাড়ার ছোট দোকানেও পলিথিন ব্যাগ আগের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে।
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে। অথচ কর্মসংস্থানের অভাব আজ তরুণদের সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে একটি দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ‘২৬ লাখ শিক্ষিত বেকারের দেশে ২৬ লাখ ভারতীয় কী করে চাকরি করে’। প্রতিবেদকের ভাষ্যমতে, ‘একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আরেকটি রাষ্ট্র কি এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের “দুরভিসন্ধির” পরিকল্পনাগুলোর একটি এটি। এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে ভারতীয়দের সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। অথচ দেশে শিক্ষিত বেকার ২৬ লাখ ৪০ হাজার!’ এমন প্রতিবেদন কেবল পরিসংখ্যান নয়, এটি এক তীব্র প্রশ্ন—দেশে যদি এত বেকার তরুণ থাকে, তবে বিদেশিরা কেন চাকরি পাবে? এমন বাস্তবতায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস তখন ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশে এমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে বিদেশি কর্মীদের আর সুযোগ না থাকে। এক বছর পার হয়ে গেলেও ২৬ লাখ ভারতীয়কে চাকরিচ্যুত করার কোনো খবর এখনো গণমাধ্যমে দেখা যায়নি।
এরপর একটি স্বাধীন দেশের জন্য সার্বভৌমত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, ‘হাসিনা সরকারের আমলে করা সকল গোপন চুক্তি বাতিল করা হবে।’ কিন্তু এ বছরের ২১ অক্টোবর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ঘোষণা দেন, ‘ভারতের সঙ্গে ১০ চুক্তি বাতিলের দাবি সত্য নয়’। এরপর ২৬ অক্টোবরের আরেকটি সংবাদ থেকে জানা গেল, ‘দ্বিগুণ মূল্যে কমলাপুর মেট্রোরেলের কাজ পেয়েছে ভারতীয় কোম্পানি’। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই সম্পর্ক যেন কখনোই সমমর্যাদার বাইরে না যায়। দেশের স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা রক্ষা করার জন্য বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও জবাবদিহি অপরিহার্য।
তারপর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিদেশে, বিশেষত ভারতে যায়। এই পরিস্থিতি বদলানোর আশায় সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, চীন বাংলাদেশে চারটি বৃহৎ বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল, ‘বড় হাসপাতাল করতে চায় চীন’। এই হাসপাতালগুলোর একটি নামও ঠিক করা হয়েছিল ‘চায়না-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ জেনারেল হাসপাতাল’। প্রতিশ্রুতি ছিল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গে হাসপাতাল নির্মিত হবে, যাতে জনগণ উন্নত চিকিৎসা পায় এবং আর বিদেশে যেতে না হয়। কিন্তু আজও সেই হাসপাতালের জমি নির্ধারণের কাজই শুরু হয়নি, হাসপাতাল তো দূরের কথা!
এই তালিকা এখানেই শেষ নয়। এমন আরও অনেক প্রতিশ্রুতি আছে, যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক কিছুই পরিকল্পনার স্তর পেরোতে পারছে না। অথচ এসব কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দৃঢ়তা
আর দায়িত্ববোধ।
তবু হতাশ হইনি। কারণ, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এক দিনে ঘটে না, সময় লাগে। হয়তো সরকার এখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে, হয়তো নীতিগত বাধা কাটানোর চেষ্টা করছে। তাই বিশ্বাস রাখতে চাই, একদিন এই ‘হতে পারত’গুলো সত্যি হবে, বাস্তবে রূপ নেবে সেই সব প্রতিশ্রুতি।
আমরা যারা এই দেশের নাগরিক, আমাদেরও দায়িত্ব শুধু সমালোচনা নয়, সচেতন থাকা, দাবি জানানো এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি করা। কারণ, সরকার, রাষ্ট্র, জাতি—সবই আমাদের সম্মিলিত সত্তা।
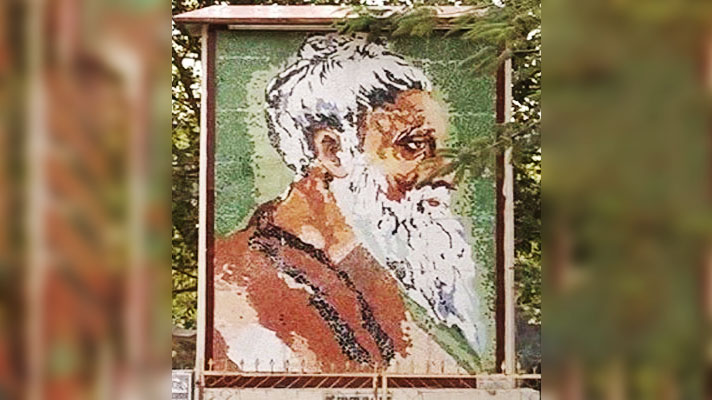
লালনের গান কেন ভালো লাগে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী হিসেবে এই ভালো লাগায় আমার কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাত আছে কি-না, লালনের গানে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ ও উচ্চারণ জানা থাকায় আমার বাড়তি সুবিধার কারণে এই ভালো
২১ অক্টোবর ২০২২
গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।
৭ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক
৭ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।
৭ ঘণ্টা আগেহেনা শিকদার

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক ধারণা নয়, একটি সর্বগ্রাসী জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে, যার করাল গ্রাসে আমাদের শত শত বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।
‘ভোগবাদ’ আমাদের শেখায়, তোমার পরিচয় তোমার অধিকারে, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিধেয় ব্র্যান্ডে, আর তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সে। এই দর্শন অনুযায়ী, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভোগ করা, আরও বেশি সঞ্চয় করা নয় এবং আরও বেশি ক্রয় করা। আমাদের এই অন্তহীন ‘আরও চাই’ সংস্কৃতি এমন এক মরীচিকার পেছনে ধাবিত করছে, যেখানে তৃষ্ণা মেটে না, কেবল বাড়ে। আর এই উন্মত্ত দৌড়ে আমরা যা কিছু পেছনে ফেলে আসছি, তা হলো আমাদের মনুষ্যত্বের অলংকার—আমাদের মূল্যবোধ।
মূল্যবোধের এই মৃত্যুর প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন। যে সমাজে একজন মানুষের মূল্যায়ন তার চরিত্র, প্রজ্ঞা বা সহানুভূতির পরিবর্তে তার ব্যবহৃত গাড়ি, দামি মোবাইল ফোন অথবা বাড়ির আকার দিয়ে নির্ধারিত হয়, সে সমাজে সম্পর্কের উষ্ণতা আশা করা বৃথা। সম্পর্কগুলো ক্রমেই যেন ‘লেনদেনভিত্তিক’ হয়ে উঠছে। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার মতো পবিত্র বন্ধনগুলোও আজ লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে মাপা হয়। ‘আমার এতে কী লাভ?’—এ প্রশ্নই যখন সবকিছুর আগে চলে আসে, তখন নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বা মমত্ববোধের মতো শব্দগুলো অভিধান থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য।
ভোগবাদী সমাজ আত্মকেন্দ্রিকতাকে উসকে দেয়। ‘আমি’ এবং ‘আমার’—এই দুটি শব্দ আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে ‘আমরা’ বা ‘সমাজ’ ধারণাটি ফিকে হয়ে যায়। অন্যের প্রতি সহানুভূতি কিংবা সহমর্মিতা প্রদর্শনের অবকাশ কোথায়, যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজের সুখের নীড় নির্মাণে ব্যস্ত? এই সমাজ আমাদের শিখিয়ে দেয়, পাশের বাড়ির মানুষটি অনাহারে থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না, যদি তোমার ফ্রিজ ভর্তি থাকে। এই যে সামষ্টিক চেতনার মৃত্যু, এটাই মূল্যবোধের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।
নৈতিকতা ও সততার ধারণাটিও এই ভোগবাদী দর্শনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। যখন সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হয় অর্থ ও প্রতিপত্তি, তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটি বৈধ না অবৈধ, তা বিবেচ্য বিষয় থাকে না। ‘দ্য ইন্ড জাস্টিফাইস দ্য মিনস’ অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সফল হলেই উপায় যেকোনো কিছু হতে পারে। ফলে দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার সামাজিক ব্যাধি থেকে একধরনের ‘স্মার্টনেস’ বা ‘দক্ষতা’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যে তরুণসমাজ সততাকে ‘বোকামি’ এবং অসদুপায় অবলম্বনকে ‘চালাকি’ বলে মনে করে, তাদের হাতে ভবিষ্যতের মূল্যবোধ কতটা সুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমেয়।
ভোগবাদ আমাদের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটেও নিমজ্জিত করছে। বিজ্ঞাপনের মায়াজাল আর সোশ্যাল মিডিয়ার লোকদেখানো জীবনের চাকচিক্য আমাদের মধ্যে একধরনের স্থায়ী অতৃপ্তি তৈরি করছে। নিজের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে অন্যের যা আছে, তা না পাওয়ার হতাশায় আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি। এই অন্তহীন তুলনা আর প্রতিযোগিতার ফলে বাড়ছে বিষণ্ণতা, একাকিত্ব ও মানসিক অস্থিরতা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, জীবনের প্রকৃত সুখ বস্তুগত প্রাপ্তিতে নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, জ্ঞানার্জন এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।
পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনেও এই ভোগবাদী সংস্কৃতির দায় অপরিসীম। আরও নতুন পণ্য, আরও নতুন ফ্যাশনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির ওপর যে অপরিসীম অত্যাচার চালাচ্ছি, তার ফল আমরা এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি। যে মূল্যবোধ আমাদের শেখাত প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে, সেই মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমরা এক আত্মঘাতী খেলায় মেতেছি।
তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়? আমরা কি শুধুই পণ্যের দাস হয়ে থাকব? এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। ভোগবাদ হলো জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণমাত্র, তাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা এক বিরাট প্রমাদ। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে, জীবনের সার্থকতা দামি পোশাকে নয়, পরিচ্ছন্ন চরিত্রে; বিলাসবহুল বাড়িতে নয়, ভালোবাসাপূর্ণ পরিবারে; এবং অফুরন্ত সম্পদে নয়, অন্যের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিতে।
আমাদের উচিত বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং আত্মিক বা মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজা। অন্যথায়, আমরা এমন এক ‘সোনার খাঁচা’ তৈরি করব, যেখানে সব থাকবে, শুধু থাকবে না সেই পাখি—যার নাম ‘মানবতা’। কিন্তু এই ভোগবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে পুঁজির দাসত্বের কারণে। কোনোভাবেই এটাকে এড়ানোর সুযোগ নেই। মূল্যবোধের এই মৃত্যু রোধ করতে না পারলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক বিত্তশালী কিন্তু দেউলিয়া সমাজে বাস করবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক ধারণা নয়, একটি সর্বগ্রাসী জীবনদর্শনে পরিণত হয়েছে, যার করাল গ্রাসে আমাদের শত শত বছরের সঞ্চিত মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।
‘ভোগবাদ’ আমাদের শেখায়, তোমার পরিচয় তোমার অধিকারে, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার পরিধেয় ব্র্যান্ডে, আর তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার ব্যাংক ব্যালেন্সে। এই দর্শন অনুযায়ী, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশি ভোগ করা, আরও বেশি সঞ্চয় করা নয় এবং আরও বেশি ক্রয় করা। আমাদের এই অন্তহীন ‘আরও চাই’ সংস্কৃতি এমন এক মরীচিকার পেছনে ধাবিত করছে, যেখানে তৃষ্ণা মেটে না, কেবল বাড়ে। আর এই উন্মত্ত দৌড়ে আমরা যা কিছু পেছনে ফেলে আসছি, তা হলো আমাদের মনুষ্যত্বের অলংকার—আমাদের মূল্যবোধ।
মূল্যবোধের এই মৃত্যুর প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন। যে সমাজে একজন মানুষের মূল্যায়ন তার চরিত্র, প্রজ্ঞা বা সহানুভূতির পরিবর্তে তার ব্যবহৃত গাড়ি, দামি মোবাইল ফোন অথবা বাড়ির আকার দিয়ে নির্ধারিত হয়, সে সমাজে সম্পর্কের উষ্ণতা আশা করা বৃথা। সম্পর্কগুলো ক্রমেই যেন ‘লেনদেনভিত্তিক’ হয়ে উঠছে। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার মতো পবিত্র বন্ধনগুলোও আজ লাভ-ক্ষতির নিক্তিতে মাপা হয়। ‘আমার এতে কী লাভ?’—এ প্রশ্নই যখন সবকিছুর আগে চলে আসে, তখন নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বা মমত্ববোধের মতো শব্দগুলো অভিধান থেকে নির্বাসিত হতে বাধ্য।
ভোগবাদী সমাজ আত্মকেন্দ্রিকতাকে উসকে দেয়। ‘আমি’ এবং ‘আমার’—এই দুটি শব্দ আমাদের চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে ‘আমরা’ বা ‘সমাজ’ ধারণাটি ফিকে হয়ে যায়। অন্যের প্রতি সহানুভূতি কিংবা সহমর্মিতা প্রদর্শনের অবকাশ কোথায়, যখন আমরা প্রত্যেকেই নিজের সুখের নীড় নির্মাণে ব্যস্ত? এই সমাজ আমাদের শিখিয়ে দেয়, পাশের বাড়ির মানুষটি অনাহারে থাকলেও তোমার কিছু যায় আসে না, যদি তোমার ফ্রিজ ভর্তি থাকে। এই যে সামষ্টিক চেতনার মৃত্যু, এটাই মূল্যবোধের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়।
নৈতিকতা ও সততার ধারণাটিও এই ভোগবাদী দর্শনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত। যখন সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি হয় অর্থ ও প্রতিপত্তি, তখন সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটি বৈধ না অবৈধ, তা বিবেচ্য বিষয় থাকে না। ‘দ্য ইন্ড জাস্টিফাইস দ্য মিনস’ অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সফল হলেই উপায় যেকোনো কিছু হতে পারে। ফলে দুর্নীতি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার সামাজিক ব্যাধি থেকে একধরনের ‘স্মার্টনেস’ বা ‘দক্ষতা’ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যে তরুণসমাজ সততাকে ‘বোকামি’ এবং অসদুপায় অবলম্বনকে ‘চালাকি’ বলে মনে করে, তাদের হাতে ভবিষ্যতের মূল্যবোধ কতটা সুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমেয়।
ভোগবাদ আমাদের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটেও নিমজ্জিত করছে। বিজ্ঞাপনের মায়াজাল আর সোশ্যাল মিডিয়ার লোকদেখানো জীবনের চাকচিক্য আমাদের মধ্যে একধরনের স্থায়ী অতৃপ্তি তৈরি করছে। নিজের যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে অন্যের যা আছে, তা না পাওয়ার হতাশায় আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি। এই অন্তহীন তুলনা আর প্রতিযোগিতার ফলে বাড়ছে বিষণ্ণতা, একাকিত্ব ও মানসিক অস্থিরতা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, জীবনের প্রকৃত সুখ বস্তুগত প্রাপ্তিতে নয়, বরং আত্মিক প্রশান্তি, জ্ঞানার্জন এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত।
পরিবেশগত বিপর্যয়ের পেছনেও এই ভোগবাদী সংস্কৃতির দায় অপরিসীম। আরও নতুন পণ্য, আরও নতুন ফ্যাশনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির ওপর যে অপরিসীম অত্যাচার চালাচ্ছি, তার ফল আমরা এরই মধ্যে পেতে শুরু করেছি। যে মূল্যবোধ আমাদের শেখাত প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে, সেই মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমরা এক আত্মঘাতী খেলায় মেতেছি।
তাহলে প্রশ্ন হলো, এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায়? আমরা কি শুধুই পণ্যের দাস হয়ে থাকব? এর উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। ভোগবাদ হলো জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণমাত্র, তাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা এক বিরাট প্রমাদ। আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে, জীবনের সার্থকতা দামি পোশাকে নয়, পরিচ্ছন্ন চরিত্রে; বিলাসবহুল বাড়িতে নয়, ভালোবাসাপূর্ণ পরিবারে; এবং অফুরন্ত সম্পদে নয়, অন্যের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তিতে।
আমাদের উচিত বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং আত্মিক বা মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজা। অন্যথায়, আমরা এমন এক ‘সোনার খাঁচা’ তৈরি করব, যেখানে সব থাকবে, শুধু থাকবে না সেই পাখি—যার নাম ‘মানবতা’। কিন্তু এই ভোগবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে পুঁজির দাসত্বের কারণে। কোনোভাবেই এটাকে এড়ানোর সুযোগ নেই। মূল্যবোধের এই মৃত্যু রোধ করতে না পারলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক বিত্তশালী কিন্তু দেউলিয়া সমাজে বাস করবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।
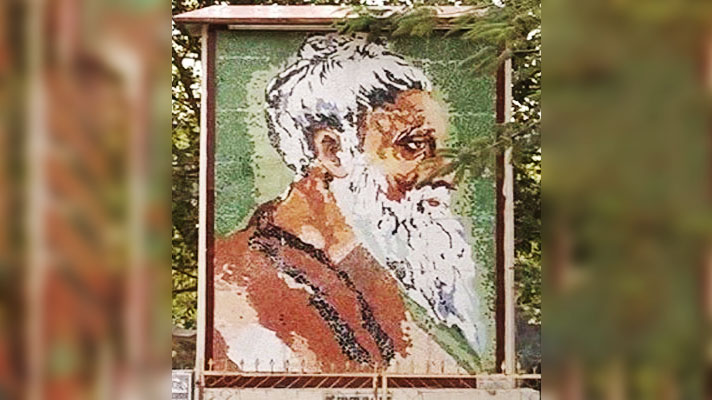
লালনের গান কেন ভালো লাগে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী হিসেবে এই ভালো লাগায় আমার কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাত আছে কি-না, লালনের গানে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ ও উচ্চারণ জানা থাকায় আমার বাড়তি সুবিধার কারণে এই ভালো
২১ অক্টোবর ২০২২
গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।
৭ ঘণ্টা আগে
স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।
৭ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল।
৭ ঘণ্টা আগেসম্পাদকীয়

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল। জানাজানি হলে বাড়ির লোকজন এবং পাড়াপড়শিরা একত্র হয়ে পিকআপটিকে ধাওয়া করে।
একপর্যায়ে পিকআপ থেকে তিন চোর পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এরপর তারা ধরা পড়ে এবং মার খায়। উত্তেজিত লোকজন তাদের এমন মার দেয় যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।
যে তিনজনকে হত্যা করা হলো, তারা যদি সত্যিই গরু চুরি করতে এসে থাকে, তাহলে শাস্তি তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। যে কেউ জানেন, এ রকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল। যে যেভাবে পেরেছে, সেভাবেই তাদের শরীরে আঘাত করেছে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে দুজনের মৃত্যু হয়, এবং একজন মৃত্যুবরণ করে হাসপাতালে নেওয়ার পর।
লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষ দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তারা আইন নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে? কেন মানুষ পুলিশ কিংবা আদালতের কাজকে নিজের কাজ হিসেবে মনে করবে?
একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেই আর কোনো দিক বিবেচনা না করে তাকে আঘাত করা শুরু হয়ে যায়। কোনো একজন কাউকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ার অপেক্ষা শুধু, এরপর দলেবলে পেটানোর সুখ খুঁজে ফেরা!
আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই অন্যায়। আমরা গত শতাব্দীর সিনেমাগুলোয় দেখেছি, মেলোড্রামার শেষ দৃশ্যে পুলিশ সংলাপ আওড়াচ্ছে, ‘আইন নিজের হাতে কোনোভাবেই তুলে নেবেন না।’ এই সংলাপ নিয়ে বহু হাসাহাসি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যেসব কারণ মানুষকে নিষ্ঠুর, নির্মম, অভদ্র, অসহিষ্ণু, অমানবিক করে তুলছে, সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করা দরকার সবার আগে। ‘আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া’ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমরা এ রকম এক অমানবিক পরিস্থিতি কেন তৈরি করলাম, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও জরুরি।
মানুষ কতটা অমানুষ হয়ে উঠেছে, ভিন্ন দুটি উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখার চেষ্টা করব। ২০২৪ সালের ২৭ মার্চের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একটি ছাগল কলা খেয়ে ফেলেছে। তাই ছাগলটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল এক কলাবিক্রেতা।
মৃত ছাগল-মাতার আশপাশে ঘুরছিল তখন দুই অবোধ ছাগলছানা। দ্বিতীয়টিও ছাগল হত্যার ঘটনা। বগুড়ার শেরপুরে গাছের পাতা খাওয়ার কারণে রামদা দিয়ে কুপিয়ে একটি ছাগলকে মেরে ফেললেন এক যুবক। ২০২৫ সালের ১৪ আগস্টের ঘটনা এটি। ঘটেছিল চকধলী গ্রামে।
এবার তিনটি অপরাধে যে ধরনের শাস্তি পেল অপরাধীরা, তা বিবেচনা করে দেখুন। আর ভাবুন, কোন পথে আমরা চলেছি!

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার উত্তেজিত জনতা। গত শনিবার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
এলাকাবাসী বলছেন, তিনটি গরু চুরি করে এরা পিকআপে তুলে নিয়েছিল। জানাজানি হলে বাড়ির লোকজন এবং পাড়াপড়শিরা একত্র হয়ে পিকআপটিকে ধাওয়া করে।
একপর্যায়ে পিকআপ থেকে তিন চোর পুকুরে ঝাঁপ দেয়। এরপর তারা ধরা পড়ে এবং মার খায়। উত্তেজিত লোকজন তাদের এমন মার দেয় যে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।
যে তিনজনকে হত্যা করা হলো, তারা যদি সত্যিই গরু চুরি করতে এসে থাকে, তাহলে শাস্তি তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। যে কেউ জানেন, এ রকম ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল। যে যেভাবে পেরেছে, সেভাবেই তাদের শরীরে আঘাত করেছে। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে তাৎক্ষণিকভাবে দুজনের মৃত্যু হয়, এবং একজন মৃত্যুবরণ করে হাসপাতালে নেওয়ার পর।
লক্ষ করলে দেখা যায়, মানুষ দিন দিন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তারা আইন নিজের হাতেই তুলে নিচ্ছে। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে? কেন মানুষ পুলিশ কিংবা আদালতের কাজকে নিজের কাজ হিসেবে মনে করবে?
একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে যে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেললেই আর কোনো দিক বিবেচনা না করে তাকে আঘাত করা শুরু হয়ে যায়। কোনো একজন কাউকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়ার অপেক্ষা শুধু, এরপর দলেবলে পেটানোর সুখ খুঁজে ফেরা!
আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই অন্যায়। আমরা গত শতাব্দীর সিনেমাগুলোয় দেখেছি, মেলোড্রামার শেষ দৃশ্যে পুলিশ সংলাপ আওড়াচ্ছে, ‘আইন নিজের হাতে কোনোভাবেই তুলে নেবেন না।’ এই সংলাপ নিয়ে বহু হাসাহাসি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে যেসব কারণ মানুষকে নিষ্ঠুর, নির্মম, অভদ্র, অসহিষ্ণু, অমানবিক করে তুলছে, সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করা দরকার সবার আগে। ‘আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া’ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমরা এ রকম এক অমানবিক পরিস্থিতি কেন তৈরি করলাম, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও জরুরি।
মানুষ কতটা অমানুষ হয়ে উঠেছে, ভিন্ন দুটি উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখার চেষ্টা করব। ২০২৪ সালের ২৭ মার্চের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একটি ছাগল কলা খেয়ে ফেলেছে। তাই ছাগলটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল এক কলাবিক্রেতা।
মৃত ছাগল-মাতার আশপাশে ঘুরছিল তখন দুই অবোধ ছাগলছানা। দ্বিতীয়টিও ছাগল হত্যার ঘটনা। বগুড়ার শেরপুরে গাছের পাতা খাওয়ার কারণে রামদা দিয়ে কুপিয়ে একটি ছাগলকে মেরে ফেললেন এক যুবক। ২০২৫ সালের ১৪ আগস্টের ঘটনা এটি। ঘটেছিল চকধলী গ্রামে।
এবার তিনটি অপরাধে যে ধরনের শাস্তি পেল অপরাধীরা, তা বিবেচনা করে দেখুন। আর ভাবুন, কোন পথে আমরা চলেছি!
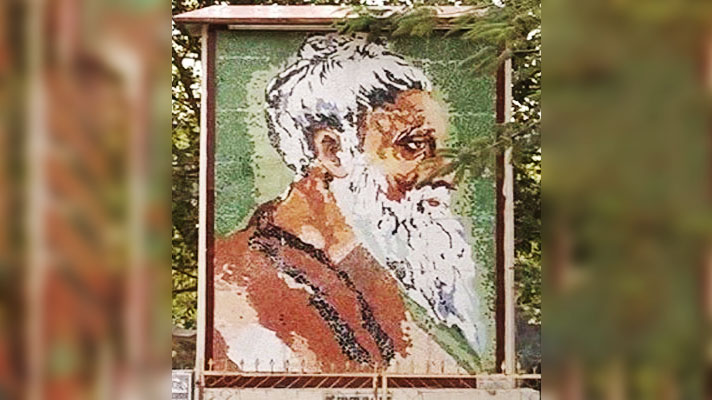
লালনের গান কেন ভালো লাগে, বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার অধিবাসী হিসেবে এই ভালো লাগায় আমার কোনো ব্যক্তিগত পক্ষপাত আছে কি-না, লালনের গানে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ, অর্থ ও উচ্চারণ জানা থাকায় আমার বাড়তি সুবিধার কারণে এই ভালো
২১ অক্টোবর ২০২২
গত এক শতাব্দীতে বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কম কিছু ঘটেনি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে ১৯৪৭ সালে, বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশভাগের চেষ্টা আগেও একবার হয়েছিল, ১৯০৫ সালে; তখন তা কার্যকর হয়নি। ৪২ বছর পরে আবার চেষ্টা হলো, এবার তা সফল হলো। সাতচল্লিশে ভঙ্গ হলো বঙ্গ।
৭ ঘণ্টা আগে
স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও মেট্রোরেল—অবকাঠামোগত উন্নয়নের এ দৃশ্যপট আজ অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। তবু উন্নয়নের এই ঝলমলে রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি, কিছু অপূর্ণ আশার গল্প।
৭ ঘণ্টা আগে
একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে যেন এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, শপিং মলের উজ্জ্বল আলো আর বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি; অন্যদিকে এক গভীর অন্ধকার, যা নিঃশব্দে গ্রাস করছে আমাদের মানবিক সত্তাকে। এই অন্ধকারের নাম ‘ভোগবাদ’। এটি শুধু সামাজিক
৭ ঘণ্টা আগে