
ফওজিয়া মোসলেম বাংলাদেশের নারী মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন নিরলস যোদ্ধা। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি। পেশায় চিকিৎসক ছিলেন।’ ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধসহ প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক সব আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। একসময় সিপিবিতেও সক্রিয় ছিলেন। মৃদুভাষী, সদালাপি ফওজিয়া মোসলেমের সঙ্গে নারীর অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে কথা বলেছেন আজকের পত্রিকার বিভুরঞ্জন সরকার।
আপনার জীবনের শুরু এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পেছনের প্রেরণা কী ছিল?
আমার বেড়ে ওঠা ঢাকায়। ষাটের দশকে যখন ছাত্ররাজনীতির পরিবেশ গড়ে উঠছিল, চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধ্যয়নের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমি ভর্তি হই ১৯৬৪ সালে। তখন চারদিকে উত্তাল সময়—ভাষা, স্বাধিকার, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলন। সেই পরিবেশে রাজনৈতিক চেতনা জন্মানো খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষ করে আমার ছোট মামা ডাক্তার সৈয়দ খলিলউল্লাহ বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করেন।
তৎকালীন পাকিস্তানে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের নৈতিক দায়বোধ থেকেই আমি রাজনীতিতে সক্রিয় হই। সময়ের পরিক্রমায় আমিও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হই। এখন অবশ্য আমার কোনো রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ততা নাই।
আপনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই সময়কালে কী পরিবর্তন দেখেছেন?
হ্যাঁ, মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আমি এর সঙ্গে যুক্ত। প্রথম দিকে আমাদের মূল লড়াই ছিল সাংবিধানিক অধিকার, নারী শিক্ষা, যৌতুকবিরোধী আইন, বাল্যবিবাহের অভিঘাত বিষয়ে নারী সমাজকে সচেতন করা ও সংগঠিত করা। পরের দশকে আমরা নারী নির্যাতনবিরোধী আইন, পারিবারিক আইন সংস্কার, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আন্দোলনে অগ্রসর হই। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার মানব অধিকার হিসেবে পরিচিতি পায়।
নারীর জীবনে পরিবর্তন অবশ্যই এসেছে। মূল পরিবর্তন ঘটেছে নারীর চিন্তা জগতে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মের নারীর মধ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী মুক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে এবং নারীর শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, মিডিয়া ও সামাজিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমানতা বেড়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রতি সহিংসতাও বেড়েছে। যেমন এখন নারী শিক্ষা বাড়লেও কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকা কঠিন; আইন থাকলেও প্রয়োগ হয় না। সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা আগের তুলনায় সহিংস ও আরও নিষ্ঠুর রূপ নিচ্ছে, যা ঘটছে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আবার পরোক্ষভাবে। সাম্প্রতিক সময়ে নারী বিদ্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক সমাজের মধ্যে নারী বিদ্বেষ প্রচারের অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে।
নারী সংস্কার কমিশনের সুপারিশকে ঘিরে সাম্প্রতিক যে ধর্মীয় বিরোধিতা দেখা গেছে, আপনি সেটিকে কীভাবে দেখছেন?
এটি নতুন নয়। আমরা যখনই নারীর অধিকার নিয়ে কোনো আইনি সংস্কারের কথা বলি, তখন একটি গোষ্ঠী ধর্মের ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নারী আন্দোলনকে আঘাত করার চেষ্টা করে। নারী সংস্কার কমিশন মূলত বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুপারিশ করেছে, বিশেষ করে নারীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত অধিকার বিষয়ে আইনের অসামঞ্জস্যতা দূর করে মানবিক ও সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: উত্তরাধিকার, বিবাহ ও তালাক, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। কিন্তু কিছু সংগঠন একে ‘ধর্মবিরোধী’ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং অত্যন্ত অশোভন, অশ্লীল ও কুৎসিতভাবে তা প্রকাশ করছে যা কখনো রাজনীতি ও গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। এইসব দলের বক্তব্য সংবিধানের সমতা ও মর্যাদার লক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
তাহলে আপনি বলছেন, ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কেবল মতভিন্নতা নয়, বরং সাংগঠনিকভাবে অধিকার হরণ?
সাংগঠনিক অধিকার হরণ এভাবে আমি বলতে চাই না, কিন্তু নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। যারা নারী সংস্কার কমিশনের বিরোধিতা করছে তারা কেবল নারীর বিরুদ্ধে নয়, প্রগতিশীল সমাজের বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছে। আমরা বলি, ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মানবাধিকারের বিরোধ নেই। আপনি যখন বলছেন, মেয়েরা সমান উত্তরাধিকার পাবে, কিংবা বিবাহে যৌক্তিক শর্ত থাকবে, তখন আপনি মূলত সামাজিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন। আপনি মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করুন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে রাষ্ট্রীয় আইনে একজন নারী দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক থাকবে। সংবিধানও সমতার কথাই বলে। এই কথাটিই আমরা আবার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি।
কর্মক্ষেত্রে নারীরা এখনো বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে। এটা আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
প্রশ্নটি বর্তমান সময়োপযোগী। আজকে যে নারী বিভিন্ন অফিসে ব্যাংকে, স্কুলে, মেডিকেল বা আইটি সেক্টরে কাজ করছেন তাঁকে দেখে মনে হতে পারে যে ‘সব ঠিক আছে’। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাঁকে প্রতিদিন প্রমাণ করতে হয় যে সে ‘পুরুষের সমান’ কাজ করতে পারে। এই প্রমাণের চাপ পুরুষদের ওপর থাকে না।
নারীরা সমান কাজে কম মজুরি পাওয়া বৈশ্বিক সমস্যা হলেও বাংলাদেশে তা আরও প্রকট। ২০২৩ সালের একটি জরিপ বলছে, বেসরকারি সেক্টরে নারীরা পুরুষদের তুলনায় গড়ে ২১% কম পারিশ্রমিক পান। এ ছাড়া কর্মস্থলে যৌন হয়রানির ভয়, মাতৃত্বকালীন ছুটিতে চাকরি হারানোর ঝুঁকি, পদোন্নতিতে বঞ্চনা ইত্যাদি তো আছেই।
যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে যে নীতিমালা আছে, তাও কি কার্যকরভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না?
২০০৯ সালে উচ্চ আদালত যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, সব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে খুব কম প্রতিষ্ঠানে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। তদুপরি কমিটি গঠিত হলেও পিতৃতান্ত্রিক প্রথা ও সংস্কৃতির কারণে সেগুলো নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে কাজ করতে পারছে না। এ ছাড়া হাইকোর্টের নীতিমালার ভিত্তিতে এখনো কোনো আইন প্রণয়ন করা হয় নাই। নারী আন্দোলন এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তাগিদ দিয়ে আসছে। ফলে অনেক নারী অভিযোগ করেও বিচার পান না, বরং উল্টো হেনস্তার শিকার হন। এই অবস্থায় নারী আত্মরক্ষার ও চাকরির স্বার্থে চুপ করে থাকার সংস্কৃতি অনুসরণ করে। এটা ভীষণ ভয়ংকর পরিস্থিতি। আমরা চাই এই নীতিমালাকে আইন হিসেবে প্রণয়ন করা হোক এবং বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মনিটরিং সেল গঠিত হোক।
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নারীকে পদায়ন করার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। গণতান্ত্রিক পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও ইতিবাচক নীতি-সক্ষমতা এগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত। নারী বলতে আমরা শুধু সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী বুঝি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, ব্যাংকের বোর্ড, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দলের কার্যনির্বাহী কমিটিতে কোথাও নারীর প্রকৃত অংশগ্রহণ নেই।
সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন আছে, কিন্তু সেটা মনোনয়ননির্ভর। রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের মাঠে ব্যবহার করে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষদেরই আধিপত্য। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছি, দলীয় পদে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এটি রাষ্ট্রের দায়।
নারীর চলাচলে, নিরাপত্তায় যে প্রতিবন্ধকতা, আপনি কি মনে করেন তা রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা?
খুব পরিষ্কারভাবে বলি হ্যাঁ, এটি রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা। আপনি যদি একটি মেয়ে হয়ে বাসে উঠে নিরাপদ না বোধ করেন, রাতের শহরে হাঁটতে ভয় পান, এতে নারীর ব্যক্তিগত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় যা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। বিচারহীনতার সংস্কৃতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সংস্কৃতি এবং নারীর অভিযোগকে তুচ্ছ করার প্রবণতা এসব মিলে নারীর চলাচল, আত্মবিশ্বাস, কর্মপরিসর সংকুচিত করে ফেলেছে।
তাহলে ভবিষ্যৎটা আপনি কেমন দেখছেন?
আমি আশাবাদী। কারণ, তৃণমূল থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে এ প্রজন্মের নারী মানসিকভাবে অগ্রসর, শক্তিশালী। ধারাবাহিক নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর মধ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে তা নারীকে সাহসী করে তুলেছে। বর্তমান প্রজন্মের নারীরা সব কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী, দক্ষ। আর এখনকার মেয়েরা টেকনোলজি, ব্যবসা, সাংবাদিকতা, খেলাধুলা সব জায়গায় আত্মপ্রকাশ করছে। তবে আমাদের এই পথচলা এখনো ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা যদি রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এই ত্রিপক্ষীয় কাঠামোয় সমতা না আনতে পারি, তাহলে ব্যক্তি অর্জন সমাজে প্রভাব ফেলবে না।
নারী শিক্ষা এখন অনেক এগিয়েছে। তাহলে শিক্ষার এই বিস্তৃত সুযোগ নারীর অবস্থানকে কতটা বদলাতে পেরেছে?
আমাদের সময়ে, বিশেষ করে ষাট-সত্তরের দশকে, মেয়েদের মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করাটাই ছিল বিশেষ কিছু। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সাহস কিংবা সুযোগ অনেকেই পেত না। এখন গ্রামের মেয়েরাও কলেজে যায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে বড় অগ্রগতি।
কিন্তু শুধু শিক্ষার পরিসংখ্যান দিয়ে নারীর অবস্থান নির্ধারণ করা যায় না। আজকে আপনি একজন নারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে দেখবেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সে যখন পদোন্নতির সময় নিজের যোগ্যতার বদলে ‘নারী হওয়া’কে বাধা হিসেবে পায়, তখন বুঝতে পারবেন, শিক্ষা সমাজের চেতনাকে কতটুকু বদলাতে পেরেছে। শিক্ষা মানেই ক্ষমতায়ন নয়, যদি সেই শিক্ষায় নারীর আত্মমর্যাদা, সমতা ও অধিকারবোধ না থাকে। আর এটিই হলো আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ।
তাহলে আপনি বলছেন, শিক্ষা সত্ত্বেও নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না?
ঠিক সেটাই। আপনি মেয়েটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন, সে পড়ালেখা করল কিন্তু তার কর্মস্থলে যেতে নিরাপত্তা নেই, বাসে উঠে হয়রানির শিকার হয়, পরিবারে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাহলে এই শিক্ষার সুফল কোথায়? দীর্ঘকালব্যাপী আমরা যে যে সামাজিক প্রথা কাঠামো গড়ে তুলেছি, আইন প্রণয়ন করেছি তা নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূলে না। সুতরাং আমরা যখন ‘নারী উন্নয়ন’ বলি, তখন শুধু সংখ্যার উন্নয়ন দিয়ে কাজ হবে না, প্রয়োজন নারীবান্ধব সামাজিক কাঠামো, যা নারীর অধিকার।
বাংলাদেশের নগর জীবনে নারীর চলাচলের ওপর যেসব প্রতিবন্ধকতা, বিশেষত গণপরিবহনে, তা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন চিন্তার বড় ত্রুটি। আপনি নগরায়ণের কথা বলছেন, কিন্তু নগরবাসীর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন হয় না। সেখানে নারী আরও প্রান্তিক। নারীর নিরাপদ চলাচল এই মৌলিক বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয় না। আজকে একজন মেয়ে সকালে অফিসে যাবে, সন্ধ্যায় ফিরবে, সে জানে না সে কোন বাসে উঠলে নিরাপদ থাকবে।
গণপরিবহনে যৌন হয়রানি এখন একটি নিরন্তর বাস্তবতা। শুধু শারীরিক হেনস্তা নয়, মানসিক যন্ত্রণাও প্রচণ্ড। আমরা বহু মেয়েকে পেয়েছি যারা হয়রানির ভয়ে পড়ালেখা বা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এটা কেবল একজন ব্যক্তির ক্ষতি নয়, রাষ্ট্রের সম্পদের অপচয়।
এ ছাড়া, নারীর চলাচলের জন্য শহরে নারীবান্ধব অবকাঠামো নেই। না আছে নারীবান্ধব ফুটপাত, না পর্যাপ্ত আলো বা নিরাপত্তাব্যবস্থা। এটা রাষ্ট্রীয় অবহেলার নমুনা।
রাজনৈতিক দলগুলো নারীর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দেয়, বাস্তবে তার প্রতিফলন কতটা দেখছেন?
রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নারীর প্রশ্নে এখনো দায়বদ্ধতার নিদর্শন দেখা যায় না। নির্বাচনের আগে তারা নারী ভোটের কথা বলে, সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নিয়ে গর্ব করে, কিন্তু বাস্তবে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিসরে নারীর ভূমিকা নেই।
দলীয় কাউন্সিল, সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক পদে নারীদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। শুধু পোস্টারে মুখ থাকলেই ‘উন্নয়ন’ হয় না। আমরা চাই রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রকৃত, নির্বাচিত, জবাবদিহিমূলক নারী নেতৃত্ব।
আর সংরক্ষিত আসনের নারী এমপিদের আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁরা যদি দলনির্ভর হন এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না থাকেন, তবে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যায়। এটা শুধু একটি প্রতীক হয়ে থাকে। সেই কারণে আমরা সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন চাই।
আপনি একাধিকবার বলেছেন, রাষ্ট্র নারীকে দয়া নয়, অধিকার দিক। এই বার্তাটা যদি আপনি সরাসরি রাষ্ট্রকে দিতে চান, কী বলবেন?
আমি রাষ্ট্রকে আহ্বান জানাব নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দায়বদ্ধ হওয়ার জন্য। সংবিধানে সমতার যে কথা বলা হয়েছে, তা যেন কাগজে না থাকে, বাস্তবেও প্রতিফলিত হয়। একটি মেয়ে শিশুকে জন্মের পর থেকেই যেন রাষ্ট্রীয় সমান মর্যাদার আশ্বাস দিতে পারে—এই হোক রাষ্ট্রের নৈতিক দায়।
আমাদের নারীসুলভ কাজ বা ‘মা-বোন’ ভেবে সহানুভূতির দরকার নেই, আমাদের নাগরিক, সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার চাই। একজন পুরুষের মতো একজন নারীও মানুষ হিসেবে পরিচিত হবে, রাষ্ট্রের নাগরিক হবে এবং সেই মর্যাদায় বাঁচবে এটাই রাষ্ট্রের নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। নারী ও পুরুষ উভয়কে মানবিক সমান অধিকার দিতে হবে।
তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে তরুণ নারীরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায়, ফিল্ম, লেখালেখিতে, প্রতিবাদে অনেক দৃঢ় অবস্থানে আসছে। আপনি এটাকে কীভাবে দেখছেন?
আমি এটা অনেক ইতিবাচকভাবে দেখি। একসময় নারীরা সাহস করত না প্রতিবাদ করার, কিন্তু এখন তারা শুধু প্রতিবাদ করছে না, নিজের কণ্ঠও নির্মাণ করছে। তারা লিখছে, ছবি তুলছে, গান বানাচ্ছে, প্রতিবাদ করছে।
তবে এই চেতনার বিস্তার যেন শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। গ্রাম, শ্রমজীবী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুবিধাবঞ্চিত মেয়েরা যেন এই আন্দোলনের আওতায় আসে, এই সংযোগটা আমাদের করতে হবে।
আপনি যে সংগ্রাম করেছেন, যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকে তরুণদের উদ্দেশে কোনো বার্তা দিতে চান?
আমরা যারা আগের প্রজন্ম, তারা শুধু একটা কাঠামো তৈরি করে দিয়েছি। নতুন প্রজন্মকে তার গঠন, নির্মাণ ও পুনর্গঠন করতে হবে। তাদের বলব, পিছিয়ে পড়া নারীকে খুঁজে নাও, তাকে সঙ্গে নাও। নিজের উন্নয়নে আত্মতুষ্ট না হয়ে, অন্য নারীর অনুপস্থিতি বা সমস্যা চিহ্নিত করে সেখানেই কাজ শুরু করো। আর রাষ্ট্রের কাছে দাবি করতে শেখো—দয়া নয়, অধিকার চাও। একই সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। অধিকার এবং দায়িত্ব একে অপরের সহযোগী। যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে অধিকার হাতছাড়া হয়ে যায়।
আপনি দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে অভিজ্ঞতা নারী প্রশ্নে কেমন ছিল?
কমিউনিস্ট রাজনীতি আমাকে শিখিয়েছে সংগ্রাম করতে, সংহতি গড়তে। কিন্তু সত্য বলতেই হয়, বাম রাজনীতির ভেতরেও নারীর প্রশ্ন সব সময় প্রাধান্য পায়নি। অনেক সময় ‘বৃহত্তর বিপ্লব’-এর কথা বলতে গিয়ে নারী বিষয়কে গৌণ করা হয়েছে। এখনো তাদের কমিটিগুলোতে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।
তবুও বলব, সেখান থেকে আমি রাজনৈতিক চেতনা পেয়েছি, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি গড়েছি। পরবর্তী সময়ে যখন আমি মহিলা পরিষদে কাজ শুরু করি, তখন সেই চেতনা কাজে লেগেছে।
আপনি যখন মহিলা পরিষদে কাজ শুরু করেন, তখন কি ভেবেছিলেন এই পথটা এত দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ হবে?
শুরুতে বুঝি নাই যে নারী মুক্তির পথ এতটাই দীর্ঘ, জটিল ও বন্ধুর। আমাদের মানব সভ্যতার আদিতে যখন শ্রমের বিভাজন এবং সম্পদের মালিকানা ছিল না, তখন সমাজ ছিল নারীপ্রধান। পরবর্তী সময়ে শ্রমের এবং সম্পদের মালিকানাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত নারীবিরোধী আইন, কাঠামো, প্রথার অবসান ঘটিয়ে সমতাভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে নারী মুক্তির পথ। সেই পথে নারী ও পুরুষকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাঠামো পুরুষে-পুরুষেও বৈষম্য সৃষ্টি করে। অতীতের আন্দোলন এবং বর্তমান আন্দোলনকে এক ধারায় গ্রথিত করতে হবে। তাই আজও আমি আশাবাদী। এই যে এত প্রতিবন্ধকতার মাঝেও মেয়েরা লড়ছে, নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসছে, তাদের দেখে মনে হয়, পথটা কণ্টকাকীর্ণ হলেও, হাঁটতে হবেই।
আপনি নিজে একজন চিকিৎসক, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, সংগঠক। এত পরিচয়ের ভেতর নারী হিসেবে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন?
খুব স্পষ্ট করে যদি বলি অবশ্যই আমার পরিচয় আমি একজন নারী, একজন চিকিৎসক, একজন শিক্ষক এবং একজন রাজনৈতিক কর্মী। তবে আমার কর্মজীবনের সব ক্ষেত্রে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে। আমার কাজ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা। আমার পরিবার এবং সহকর্মীরা আমার যাত্রায় যেভাবে সহায়তা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।
আপনি কি মনে করেন, এই দেশ একদিন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সত্যিকারের রাষ্ট্র হবে?
আমি স্বপ্ন দেখি সে স্বপ্ন ঘুমিয়ে নয়, জাগরণে, কর্মজগতে। আমি মনে করি, স্বপ্ন না থাকলে সংগ্রাম অর্থহীন হয়ে যায়। আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা রাষ্ট্রের, যেখানে নারী স্বাধীনভাবে হাঁটবে, সিদ্ধান্ত নেবে এবং নিজের চাহিদা ও জীবনের অধিকার নিজেই স্থির করবে। সেই রাষ্ট্র এখনো আসেনি, তবে তার দিগন্ত দেখা গেছে। যদি নতুন প্রজন্ম এই স্বপ্নকে ধারণ করে, প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তবে একদিন এই দেশ নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হলো, বিশ্বের কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তাদের আনুগত্য না মানলে সেখানে যেকোনো উপায়ে তাঁকে উৎখাত করা। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাস তা-ই বলে। সেই
২ ঘণ্টা আগে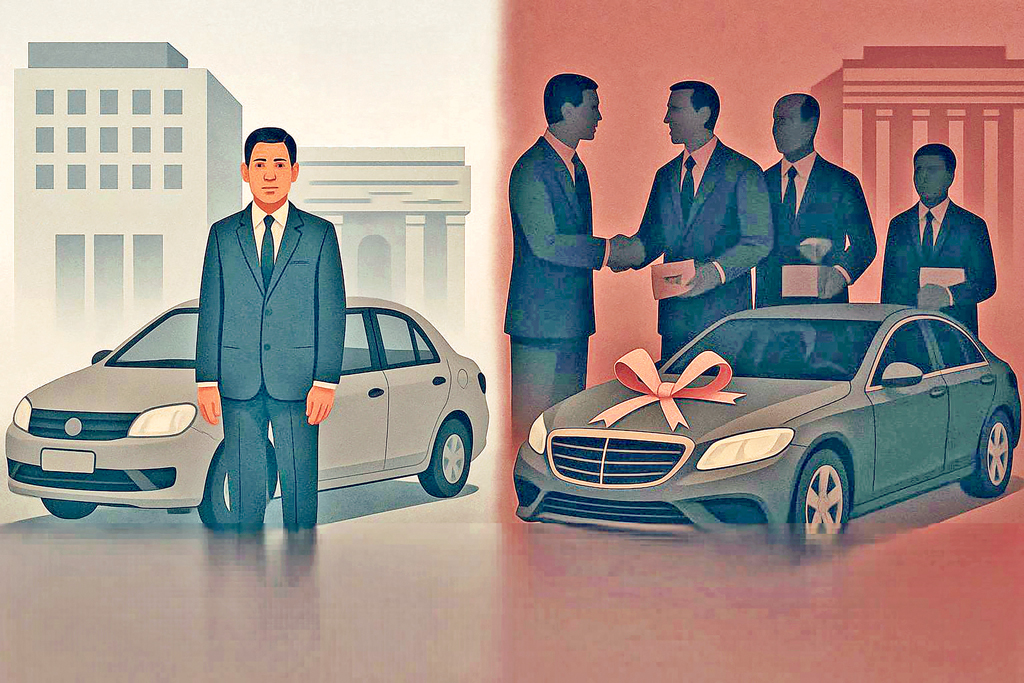
দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন সরকারের মধ্যে দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ব্যক্তিগত কিছু কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বিএনপি ও তার নেতাদের গতানুগতিক কাজকর্ম। এই দুই ধারার মধ্যে মিলের চেয়ে যেন অমিলই বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না, আগামী দিনগুলোতে ঠিক...
৩ ঘণ্টা আগে
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে চোখ মধ্যপ্রাচ্যের ওপর। প্রশ্ন একটাই, এখন কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যবস্তু ইরানের ইসলামি শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে কি? হলে কী হবে সেই ইরানের চেহারা! মুহুর্মুহু হামলার মুখে কতক্ষণ...
৩ ঘণ্টা আগে
আলতাফ পারভেজ লেখক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর। ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ‘মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনঃপাঠ’, ‘বার্মা: জাতিগত সংঘাতের সাত দশক’, ‘শ্রীলঙ্কার তামিল ইলম’, ‘গ্রামসি ও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা’ প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বই।
১ দিন আগে