সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

লন্ডনে যে সময়ে সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল তৈরি হয়, প্রায় সেই সময়েই আগ্রায় তৈরি হয়েছে তাজমহল। এই দুটি সৌধ মানুষের নির্মাণকুশলতার অসামান্য নিদর্শন। তাজমহল বোধ হয় অধিকতর বিস্ময়কর সৃষ্টি সেন্ট পলস্-এর তুলনায়। কিন্তু যে সভ্যতা সেন্ট পলস্ তৈরি করেছে, তার সঙ্গে তাজমহল সৃষ্টিকারী সভ্যতার ব্যবধান ছিল একেবারে মৌলিক।
তাজমহল মৃত্যুর স্মারক। পিরামিডের সঙ্গে তাজমহলের প্রধান দূরত্ব সময়ের, নইলে নির্মাণকুশলতার বিস্ময়করতার দিক দিয়ে যেমন, উদ্দেশ্যের দিক দিয়েও তেমনি তারা সন্নিকটবর্তী। সেটা একটা কথা, তার চেয়েও বড় কথা, তাজমহল ব্যক্তির স্বার্থে তৈরি, একজন ব্যক্তিকে সে রক্ষা করতে চেয়েছে কালের অমোঘ অবলুপ্তির হাত থেকে, অথবা দুজন ব্যক্তিকে। তাজমহলে-পিরামিডে প্রধান ঐক্য এই অভিপ্রায়ে। আর ওই যে মৃত্যুকে ও ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে তাজমহলের সভ্যতা, তা থেকে বোঝা যায় তার অগ্রগতি ঘটছিল না জীবনের দিকে, বরং সে পিছিয়ে আসছিল মৃত্যুর অভিমুখে।
সেন্ট পলস্ জীবনের জন্য তৈরি। ধর্ম সেকালে জীবনেরই অঙ্গ ছিল। এই অট্টালিকার স্থপতি যিনি, তিনি শুধু গির্জাই তৈরি করেননি, তৈরি করেছেন হাসপাতাল ও ছাত্র-পাঠগৃহ, তৈরি করেছেন বাগান এবং নকশা করেছিলেন লন্ডন শহরের পুনর্নির্মাণের, যে লন্ডন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল অগ্নিকাণ্ডে, সেই লন্ডন শহরের। ক্যাথিড্রাল আলাদা কিছু নয়, তাঁর অনেক পরিকল্পনারই একটি। গির্জাকে ক্রিস্টোফার রেন আলাদা করে দেখেননি জীবন থেকে। সমাজ থেকেও নয়। ক্যাথিড্রাল রাজার স্বার্থে, স্থপতির স্বার্থে বা কোনো ব্যক্তির স্বার্থে নির্মিত হয়নি, নির্মিত হয়েছে সমাজের স্বার্থে, সবার প্রয়োজনে। সেইখানে, অট্টালিকার সেই সামাজিকতায়, উদ্দেশ্যের সেই সর্বজনস্বার্থ চেতনায় ও উদ্যমের সেই সমবায়ে জীবন ছিল পরিব্যাপ্ত, ছিল সর্বক্ষণ জীবন্ত।
ক্যাথিড্রালটি তৈরি করা হয়েছিল একটা পুরোনো ভিতের ওপর, কিন্তু এর আরও একটা ভিত্তি ছিল, অত্যন্ত দৃঢ় একটি ভিত্তি। সেই ভিত্তিটা সামাজিক। সেন্ট পলস্ শুধু যে মাটির ওপর তৈরি হয়েছে তা-ই নয়, তৈরি হয়েছে একটা সমাজের ওপরেও বটে। বড় গৃহ সব সময়ই সেইভাবে তৈরি হতো, তাজমহলও তা-ই হয়েছে। কিন্তু তাজমহলের সামাজিক ভিত্তিটা ছিল দুর্বল, তাজমহলের নিচে লন্ডন শহর ছিল না, তার মাটিতে বাজেনি শিল্পবিপ্লবের পদধ্বনি, তাজমহলের আশপাশে অগ্রাভিযান চলছিল না পার্লামেন্টের, অর্থাৎ সমগ্র সমাজের। তাজমহল সমাজজীবনের দিকে এগোয়নি, স্থির হয়েও থাকতে পারেনি, কেননা স্থিতাবস্থা বলে কিছু নেই, সমাজ হয় অগ্রসর হচ্ছে জীবনের দিকে, নয়তো পিছিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর অভিমুখে। সেন্ট পলসের সমাজের কাছে অনিবার্য পরাজয় ঘটেছে তাজমহলের সমাজের। ইংরেজের ভারত বিজয় একটা দেশের কাছে অন্য দেশের পরাজয় নয়, একটা সমাজের কাছে পরাজয় আরেকটা সমাজের।
ইংরেজের যে শক্তি ছিল, তার প্রকৃত উৎস কী? সে কি গোলাবারুদ, নাকি সাদা চামড়া, নাকি সে ইংরেজি ভাষা? প্রকৃত শক্তি এমনকি গোলাবারুদেরও নয়, গোলাবারুদ ভারতবর্ষীয়দেরও ছিল, প্রকৃত শক্তি এসেছে ইংরেজের সমাজ থেকে। ইংরেজের প্রবল, সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তি দুর্বল, বিশৃঙ্খল ও বিভক্ত ভারতবর্ষীয় সামাজিক শক্তিকে পরাভূত করেছে। রবার্ট ক্লাইভ রাজা ছিলেন না, ছিলেন মধ্যবিত্ত কেরানি। সেই কেরানি সাম্রাজ্যের ভিত পত্তন যদি করে থাকেন, তবে নিজের শক্তিতে, একক শক্তিতে করেননি, করেছেন যে সমাজ থেকে এসেছেন, সেই সমাজের শক্তিতে।
নইলে কেরানির সাধ্য কী রাজ্য গড়ে? নইলে সুতার ব্যবসায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরইবা সাধ্য কী দেশ জয় করে? সমাজের শক্তিতেই সেই সুতা শক্তিশালী হয়েছে, শক্তিশালী হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, ভারতবর্ষকে বেঁধে ফেলেছে। যে শক্তি সেন্ট পলস্ তৈরি করেছে, সফল করেছে শিল্পবিপ্লব, জন্ম দিয়েছে শেক্সপিয়ার ও নিউটনের, সেই একই শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে; শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র।
সমাজের এই শক্তি এল কোথা থেকে? এল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। ইংরেজের সামাজিক শক্তি রাজারা তৈরি করেননি, তৈরি করেনি বিলাসী অভিজাত শ্রেণি, তৈরি করেছে ইংল্যান্ডের কমন্স, তার পার্লামেন্ট। রাজা ও রাজার সঙ্গীদের ক্ষমতা খর্ব করেই অভ্যুদয় ঘটেছে এই সামাজিক শক্তির। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একবার ম্যাগনাকার্টা আদায় করে নিয়েছিল জনসাধারণ অনিচ্ছুক রাজার কম্পিত হস্ত থেকে। পরে তারা দেখল কাজ হচ্ছে না পুরোপুরি। তাই দেখে আরও পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে শিরশ্ছেদ করল তারা অন্য এক রাজার। শুধু রাজার নয়, বস্তুত রাজার ক্ষমতার। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন যিনি ক্রমওয়েল, তিনি প্রতিনিধি ছিলেন নতুন মধ্যবিত্তের, রাজতন্ত্রের বিনাশে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি, লোকে চেয়েছিল তাঁকে রাজা করবে, কিন্তু তিনি মাথা নোয়াননি মুকুটের কাছে। রাজা অবশ্য পরে ফিরে এসেছেন। কিন্তু সেই আগের রাজা নন আদপেই, তিনি এসেছেন বন্দী হয়ে, কমন্স তাঁকে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে নিয়মতান্ত্রিকতার কঠিন দড়ি দিয়ে। বেঁধে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সমাজের শক্তিকে। আর সেই মুক্তিই জীবনের সব ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য সৃজন-দক্ষতার মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই রকমেরই একটি অভিব্যক্তি। তাজমহলের সভ্যতার মধ্যে এই শক্তি ছিল না।
সেন্ট পলস্ যখন তৈরি হয় তখনকার সামাজিক অবস্থাটা কী রূপ ছিল ইংল্যান্ডে? তার আগে ‘গৌরবজনক বিপ্লব’ সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। রয়্যাল সোসাইটি ব্যস্ত তখন বিজ্ঞানের গবেষণায়। শিল্পবিপ্লবের তখন প্রস্তুতি চলছে, বড় কোনো জায়গায় নয়, বলা যায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির ঘরে। আগুন লেগে পুড়ে গেছে লন্ডন তার আগে, কিন্তু সেই ধ্বংসে পরাভূত হয়নি মানুষ। ক্রিস্টোফার রেন নতুন নতুন অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরেই। ধ্বংস ছিল সৃষ্টির অজুহাত।
মূল কথাটা ঘুরেফিরে দাঁড়াল, এই জনগণের জীবনই সমাজের জীবন, শক্তি আছে সেইখানেই। সমাজের শক্তি যদি হয় বন্ধনপীড়িত, তবে সমাজ কিছুতেই এগোবে না জীবনের দিকে, বরং তাকে নামতে হবে মৃত্যুর অভিমুখে। আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সমাজের শক্তি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেছে। আমেরিকার মতো বৃহৎ শক্তি যে ‘অনুন্নত’ ভিয়েতনামিদের হাতে পরাভূত হলো, সে ওই সামাজিক শক্তির কারণেই। আলজেরিয়াতেও তা-ই।
বাংলাদেশে সমাজের শক্তি উন্মোচিত হয়নি কখনো। এই দেশে পরিবর্তন এসেছে সময়-সময়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে; কিন্তু যে পরিবর্তন মূল পরিবর্তন, যা এলে অন্য সব পরিবর্তন আসে আপনা থেকেই, সেই পরিবর্তন ঘটতে পারেনি এই দেশে। এই সমাজের ভেতরে-বাইরে কঠিন দাসত্ব—বাইরে আছে শাসন, ভেতরেও তাই। ভেতরে মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রভু ও দাসের, সেই সম্পর্কে শক্তি নেই, আছে অবিশ্বাস ও ঈর্ষা। বিদ্রোহ ঘটেছে বাংলাদেশে, কিন্তু বিপ্লব ঘটেনি। বরং বিপ্লবকে ভয় করেছে মানুষ, এখনো করে। ফলে মুক্ত হলে যে শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারত, শত শত বছর ধরে নিরুপায় সেই শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে আটকা পড়ে আছে, দিনে দিনে সে আরও দুর্বল হচ্ছে, রুগ্ণ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।
যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল বাংলাদেশে, সেই ৯ মাসে পুরোনো সমাজটা ভাঙছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেনেড ও বোমা শুধু ব্রিজ ভাঙছিল না, ভাঙছিল সমাজকেও। সেই সঙ্গে প্রভু-দাসের অভিপুরাতন সম্পর্কের স্থলে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠছিল, সমবায়ী সম্পর্ক, সাম্যের ও সহযোগিতার সম্পর্ক। কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি, না ভাঙার কাজ, না গড়ার কাজ। পুরোনো সম্পর্কটা আবার, প্রায় অলক্ষ্যে, কিন্তু অতিদ্রুত ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে, কিন্তু আগের আকার নিয়ে আসতে পারেনি। অক্ষত আসেনি, দুমড়ে-মুচড়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে। আজ না আছে তার নিজের শক্তি, না আছে তার প্রতি অন্যের আস্থা। আস্থা একটা বড় কথা, আস্থা না থাকলে এমনকি দাস ব্যবস্থারও শক্তি থাকে না। ভৃত্য যদি প্রভুকে না মান্য করে, তবে প্রভুর আসন বিচলিত হয়। বাংলাদেশে প্রভুদের আসন বিচলিত হয়েছে মাত্র, আসন ভূলুণ্ঠিত হয়নি এখনো। পুরোনো সম্পর্ক দুমড়ে-মুচড়ে নড়বড়ে হয়ে গেল। কিন্তু নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল না। বিপদ এইখানেই। সমাজ রুগ্ণ আগেও ছিল, আজ তার অসামান্য স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে আরও ব্যাপকভাবে।
এই অবস্থার যদি আমরা পরিবর্তন চাই, তবে নীরব ক্রন্দন কি সরব হুংকার, উত্তেজিত উপদেশ কি বিরূপ সমালোচনা, কিছুতেই কিছু হবে না। আসল কাজ জীবনকে মুক্ত করা। তার জন্য চাই মানুষে-মানুষে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা। সাধারণ মানুষের মুক্তি ছাড়া জীবনের মুক্তি নেই, সবার উদ্যম ভিন্ন অবসান নেই দৈন্যের। আমাদের সব প্রচেষ্টার-রাজনীতির, শিক্ষার, শিল্পকলার, অর্থনীতির সব কর্মোদ্যমের মাঝখানে বিবেকের মতো, নিয়ামক শক্তির মতো স্থাপন করা আবশ্যক এই সত্যটিকে।
তাজমহলের পথ জীবনের পথ নয়। তাজমহল মানুষের নির্মাণকুশলতার যত বড় নিদর্শনই হোক না কেন।

লন্ডনে যে সময়ে সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল তৈরি হয়, প্রায় সেই সময়েই আগ্রায় তৈরি হয়েছে তাজমহল। এই দুটি সৌধ মানুষের নির্মাণকুশলতার অসামান্য নিদর্শন। তাজমহল বোধ হয় অধিকতর বিস্ময়কর সৃষ্টি সেন্ট পলস্-এর তুলনায়। কিন্তু যে সভ্যতা সেন্ট পলস্ তৈরি করেছে, তার সঙ্গে তাজমহল সৃষ্টিকারী সভ্যতার ব্যবধান ছিল একেবারে মৌলিক।
তাজমহল মৃত্যুর স্মারক। পিরামিডের সঙ্গে তাজমহলের প্রধান দূরত্ব সময়ের, নইলে নির্মাণকুশলতার বিস্ময়করতার দিক দিয়ে যেমন, উদ্দেশ্যের দিক দিয়েও তেমনি তারা সন্নিকটবর্তী। সেটা একটা কথা, তার চেয়েও বড় কথা, তাজমহল ব্যক্তির স্বার্থে তৈরি, একজন ব্যক্তিকে সে রক্ষা করতে চেয়েছে কালের অমোঘ অবলুপ্তির হাত থেকে, অথবা দুজন ব্যক্তিকে। তাজমহলে-পিরামিডে প্রধান ঐক্য এই অভিপ্রায়ে। আর ওই যে মৃত্যুকে ও ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে তাজমহলের সভ্যতা, তা থেকে বোঝা যায় তার অগ্রগতি ঘটছিল না জীবনের দিকে, বরং সে পিছিয়ে আসছিল মৃত্যুর অভিমুখে।
সেন্ট পলস্ জীবনের জন্য তৈরি। ধর্ম সেকালে জীবনেরই অঙ্গ ছিল। এই অট্টালিকার স্থপতি যিনি, তিনি শুধু গির্জাই তৈরি করেননি, তৈরি করেছেন হাসপাতাল ও ছাত্র-পাঠগৃহ, তৈরি করেছেন বাগান এবং নকশা করেছিলেন লন্ডন শহরের পুনর্নির্মাণের, যে লন্ডন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল অগ্নিকাণ্ডে, সেই লন্ডন শহরের। ক্যাথিড্রাল আলাদা কিছু নয়, তাঁর অনেক পরিকল্পনারই একটি। গির্জাকে ক্রিস্টোফার রেন আলাদা করে দেখেননি জীবন থেকে। সমাজ থেকেও নয়। ক্যাথিড্রাল রাজার স্বার্থে, স্থপতির স্বার্থে বা কোনো ব্যক্তির স্বার্থে নির্মিত হয়নি, নির্মিত হয়েছে সমাজের স্বার্থে, সবার প্রয়োজনে। সেইখানে, অট্টালিকার সেই সামাজিকতায়, উদ্দেশ্যের সেই সর্বজনস্বার্থ চেতনায় ও উদ্যমের সেই সমবায়ে জীবন ছিল পরিব্যাপ্ত, ছিল সর্বক্ষণ জীবন্ত।
ক্যাথিড্রালটি তৈরি করা হয়েছিল একটা পুরোনো ভিতের ওপর, কিন্তু এর আরও একটা ভিত্তি ছিল, অত্যন্ত দৃঢ় একটি ভিত্তি। সেই ভিত্তিটা সামাজিক। সেন্ট পলস্ শুধু যে মাটির ওপর তৈরি হয়েছে তা-ই নয়, তৈরি হয়েছে একটা সমাজের ওপরেও বটে। বড় গৃহ সব সময়ই সেইভাবে তৈরি হতো, তাজমহলও তা-ই হয়েছে। কিন্তু তাজমহলের সামাজিক ভিত্তিটা ছিল দুর্বল, তাজমহলের নিচে লন্ডন শহর ছিল না, তার মাটিতে বাজেনি শিল্পবিপ্লবের পদধ্বনি, তাজমহলের আশপাশে অগ্রাভিযান চলছিল না পার্লামেন্টের, অর্থাৎ সমগ্র সমাজের। তাজমহল সমাজজীবনের দিকে এগোয়নি, স্থির হয়েও থাকতে পারেনি, কেননা স্থিতাবস্থা বলে কিছু নেই, সমাজ হয় অগ্রসর হচ্ছে জীবনের দিকে, নয়তো পিছিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর অভিমুখে। সেন্ট পলসের সমাজের কাছে অনিবার্য পরাজয় ঘটেছে তাজমহলের সমাজের। ইংরেজের ভারত বিজয় একটা দেশের কাছে অন্য দেশের পরাজয় নয়, একটা সমাজের কাছে পরাজয় আরেকটা সমাজের।
ইংরেজের যে শক্তি ছিল, তার প্রকৃত উৎস কী? সে কি গোলাবারুদ, নাকি সাদা চামড়া, নাকি সে ইংরেজি ভাষা? প্রকৃত শক্তি এমনকি গোলাবারুদেরও নয়, গোলাবারুদ ভারতবর্ষীয়দেরও ছিল, প্রকৃত শক্তি এসেছে ইংরেজের সমাজ থেকে। ইংরেজের প্রবল, সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তি দুর্বল, বিশৃঙ্খল ও বিভক্ত ভারতবর্ষীয় সামাজিক শক্তিকে পরাভূত করেছে। রবার্ট ক্লাইভ রাজা ছিলেন না, ছিলেন মধ্যবিত্ত কেরানি। সেই কেরানি সাম্রাজ্যের ভিত পত্তন যদি করে থাকেন, তবে নিজের শক্তিতে, একক শক্তিতে করেননি, করেছেন যে সমাজ থেকে এসেছেন, সেই সমাজের শক্তিতে।
নইলে কেরানির সাধ্য কী রাজ্য গড়ে? নইলে সুতার ব্যবসায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরইবা সাধ্য কী দেশ জয় করে? সমাজের শক্তিতেই সেই সুতা শক্তিশালী হয়েছে, শক্তিশালী হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, ভারতবর্ষকে বেঁধে ফেলেছে। যে শক্তি সেন্ট পলস্ তৈরি করেছে, সফল করেছে শিল্পবিপ্লব, জন্ম দিয়েছে শেক্সপিয়ার ও নিউটনের, সেই একই শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে; শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র।
সমাজের এই শক্তি এল কোথা থেকে? এল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। ইংরেজের সামাজিক শক্তি রাজারা তৈরি করেননি, তৈরি করেনি বিলাসী অভিজাত শ্রেণি, তৈরি করেছে ইংল্যান্ডের কমন্স, তার পার্লামেন্ট। রাজা ও রাজার সঙ্গীদের ক্ষমতা খর্ব করেই অভ্যুদয় ঘটেছে এই সামাজিক শক্তির। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একবার ম্যাগনাকার্টা আদায় করে নিয়েছিল জনসাধারণ অনিচ্ছুক রাজার কম্পিত হস্ত থেকে। পরে তারা দেখল কাজ হচ্ছে না পুরোপুরি। তাই দেখে আরও পরে, সপ্তদশ শতাব্দীতে শিরশ্ছেদ করল তারা অন্য এক রাজার। শুধু রাজার নয়, বস্তুত রাজার ক্ষমতার। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন যিনি ক্রমওয়েল, তিনি প্রতিনিধি ছিলেন নতুন মধ্যবিত্তের, রাজতন্ত্রের বিনাশে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি, লোকে চেয়েছিল তাঁকে রাজা করবে, কিন্তু তিনি মাথা নোয়াননি মুকুটের কাছে। রাজা অবশ্য পরে ফিরে এসেছেন। কিন্তু সেই আগের রাজা নন আদপেই, তিনি এসেছেন বন্দী হয়ে, কমন্স তাঁকে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে নিয়মতান্ত্রিকতার কঠিন দড়ি দিয়ে। বেঁধে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সমাজের শক্তিকে। আর সেই মুক্তিই জীবনের সব ক্ষেত্রে অত্যাশ্চর্য সৃজন-দক্ষতার মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই রকমেরই একটি অভিব্যক্তি। তাজমহলের সভ্যতার মধ্যে এই শক্তি ছিল না।
সেন্ট পলস্ যখন তৈরি হয় তখনকার সামাজিক অবস্থাটা কী রূপ ছিল ইংল্যান্ডে? তার আগে ‘গৌরবজনক বিপ্লব’ সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। রয়্যাল সোসাইটি ব্যস্ত তখন বিজ্ঞানের গবেষণায়। শিল্পবিপ্লবের তখন প্রস্তুতি চলছে, বড় কোনো জায়গায় নয়, বলা যায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির ঘরে। আগুন লেগে পুড়ে গেছে লন্ডন তার আগে, কিন্তু সেই ধ্বংসে পরাভূত হয়নি মানুষ। ক্রিস্টোফার রেন নতুন নতুন অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরেই। ধ্বংস ছিল সৃষ্টির অজুহাত।
মূল কথাটা ঘুরেফিরে দাঁড়াল, এই জনগণের জীবনই সমাজের জীবন, শক্তি আছে সেইখানেই। সমাজের শক্তি যদি হয় বন্ধনপীড়িত, তবে সমাজ কিছুতেই এগোবে না জীবনের দিকে, বরং তাকে নামতে হবে মৃত্যুর অভিমুখে। আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সমাজের শক্তি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেছে। আমেরিকার মতো বৃহৎ শক্তি যে ‘অনুন্নত’ ভিয়েতনামিদের হাতে পরাভূত হলো, সে ওই সামাজিক শক্তির কারণেই। আলজেরিয়াতেও তা-ই।
বাংলাদেশে সমাজের শক্তি উন্মোচিত হয়নি কখনো। এই দেশে পরিবর্তন এসেছে সময়-সময়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে; কিন্তু যে পরিবর্তন মূল পরিবর্তন, যা এলে অন্য সব পরিবর্তন আসে আপনা থেকেই, সেই পরিবর্তন ঘটতে পারেনি এই দেশে। এই সমাজের ভেতরে-বাইরে কঠিন দাসত্ব—বাইরে আছে শাসন, ভেতরেও তাই। ভেতরে মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রভু ও দাসের, সেই সম্পর্কে শক্তি নেই, আছে অবিশ্বাস ও ঈর্ষা। বিদ্রোহ ঘটেছে বাংলাদেশে, কিন্তু বিপ্লব ঘটেনি। বরং বিপ্লবকে ভয় করেছে মানুষ, এখনো করে। ফলে মুক্ত হলে যে শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারত, শত শত বছর ধরে নিরুপায় সেই শক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে আটকা পড়ে আছে, দিনে দিনে সে আরও দুর্বল হচ্ছে, রুগ্ণ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।
যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিল বাংলাদেশে, সেই ৯ মাসে পুরোনো সমাজটা ভাঙছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেনেড ও বোমা শুধু ব্রিজ ভাঙছিল না, ভাঙছিল সমাজকেও। সেই সঙ্গে প্রভু-দাসের অভিপুরাতন সম্পর্কের স্থলে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠছিল, সমবায়ী সম্পর্ক, সাম্যের ও সহযোগিতার সম্পর্ক। কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি, না ভাঙার কাজ, না গড়ার কাজ। পুরোনো সম্পর্কটা আবার, প্রায় অলক্ষ্যে, কিন্তু অতিদ্রুত ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে, কিন্তু আগের আকার নিয়ে আসতে পারেনি। অক্ষত আসেনি, দুমড়ে-মুচড়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে। আজ না আছে তার নিজের শক্তি, না আছে তার প্রতি অন্যের আস্থা। আস্থা একটা বড় কথা, আস্থা না থাকলে এমনকি দাস ব্যবস্থারও শক্তি থাকে না। ভৃত্য যদি প্রভুকে না মান্য করে, তবে প্রভুর আসন বিচলিত হয়। বাংলাদেশে প্রভুদের আসন বিচলিত হয়েছে মাত্র, আসন ভূলুণ্ঠিত হয়নি এখনো। পুরোনো সম্পর্ক দুমড়ে-মুচড়ে নড়বড়ে হয়ে গেল। কিন্তু নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠল না। বিপদ এইখানেই। সমাজ রুগ্ণ আগেও ছিল, আজ তার অসামান্য স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে আরও ব্যাপকভাবে।
এই অবস্থার যদি আমরা পরিবর্তন চাই, তবে নীরব ক্রন্দন কি সরব হুংকার, উত্তেজিত উপদেশ কি বিরূপ সমালোচনা, কিছুতেই কিছু হবে না। আসল কাজ জীবনকে মুক্ত করা। তার জন্য চাই মানুষে-মানুষে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা। সাধারণ মানুষের মুক্তি ছাড়া জীবনের মুক্তি নেই, সবার উদ্যম ভিন্ন অবসান নেই দৈন্যের। আমাদের সব প্রচেষ্টার-রাজনীতির, শিক্ষার, শিল্পকলার, অর্থনীতির সব কর্মোদ্যমের মাঝখানে বিবেকের মতো, নিয়ামক শক্তির মতো স্থাপন করা আবশ্যক এই সত্যটিকে।
তাজমহলের পথ জীবনের পথ নয়। তাজমহল মানুষের নির্মাণকুশলতার যত বড় নিদর্শনই হোক না কেন।
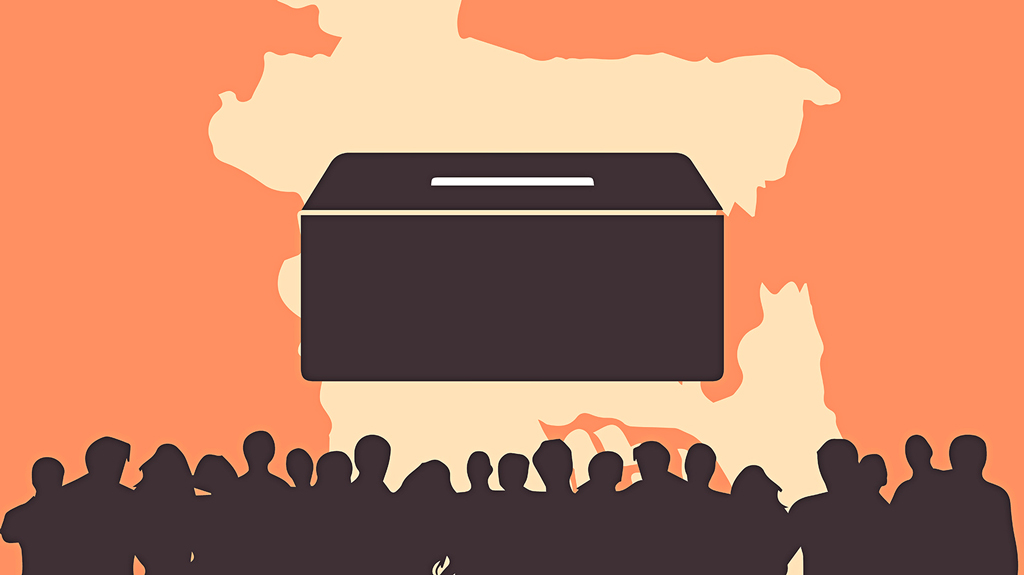
অনেকেরই সংশয় ছিল। কারও কিছুটা হালকা, কারও আবার গভীর। কেউ কেউ শঙ্কিতও ছিলেন। দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা নিয়ে। এদের সবার সেই সব সংশয় ও শঙ্কা এখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ফলে দেশের শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তরকামী সাধারণ মানুষের জন্য তা হয়ে উঠেছে অশনিসংকেত। হ্যাঁ, এই কথাগুলো হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয়
৩ ঘণ্টা আগে
ন্যায়বিচার, সংস্কার ও বৈষম্য বিলোপের দাবি থেকে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অনেকেই অপরাধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) নেতার উন্মুক্ত চাঁদাবাজির ঘটনা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
৩ ঘণ্টা আগে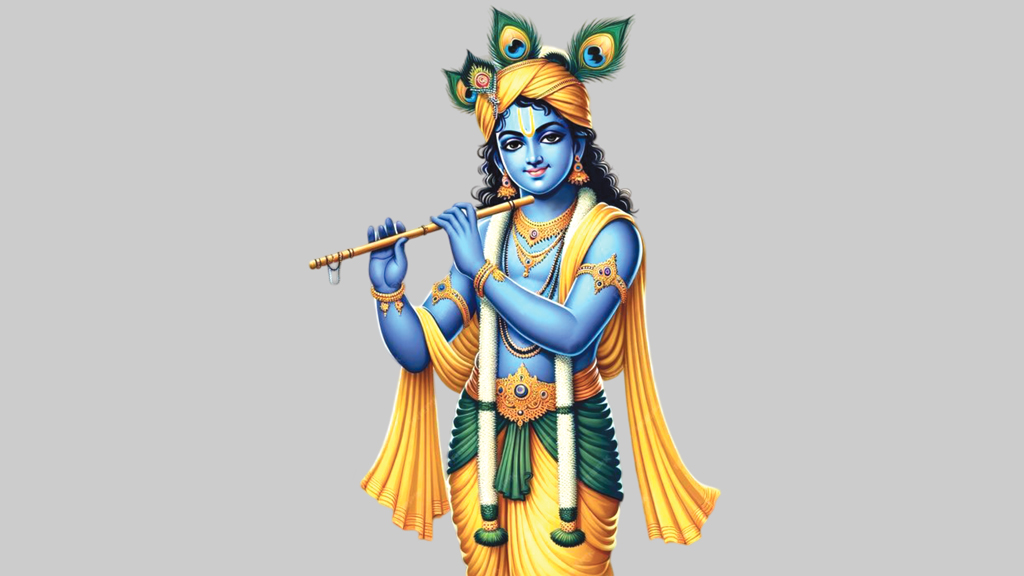
আমাদের সর্বসাধারণের মনে একটা প্রশ্ন সব সময়ই ঘুরপাক খায়—ভগবান যেহেতু অজ, তাহলে তাঁর আবার জন্ম কিসের? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান নিজেই গীতায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও এই জড়জগতে জন্মগ্রহণ করেন। কেন তিনি জন্মগ্রহণ
৩ ঘণ্টা আগে
একসময় ভরা মৌসুমে এ দেশের সাধারণ মানুষও ইলিশ কিনতে পারত। কিন্তু অনেক বছর থেকে ইলিশ শুধু উচ্চবিত্ত মানুষেরাই কিনতে পারছে। বাজারে ইলিশের সরবরাহ কম থাকায় এর আকাশছোঁয়া দামের কারণে এখন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের নাগালের মধ্যে নেই ইলিশ। এখন ভরা মৌসুমে ইলিশের দাম বাড়া নিয়ে ১৫ আগস্ট আজকের পত্রিকায় একটি সংবাদ
৩ ঘণ্টা আগে