শহিদুল ইসলাম
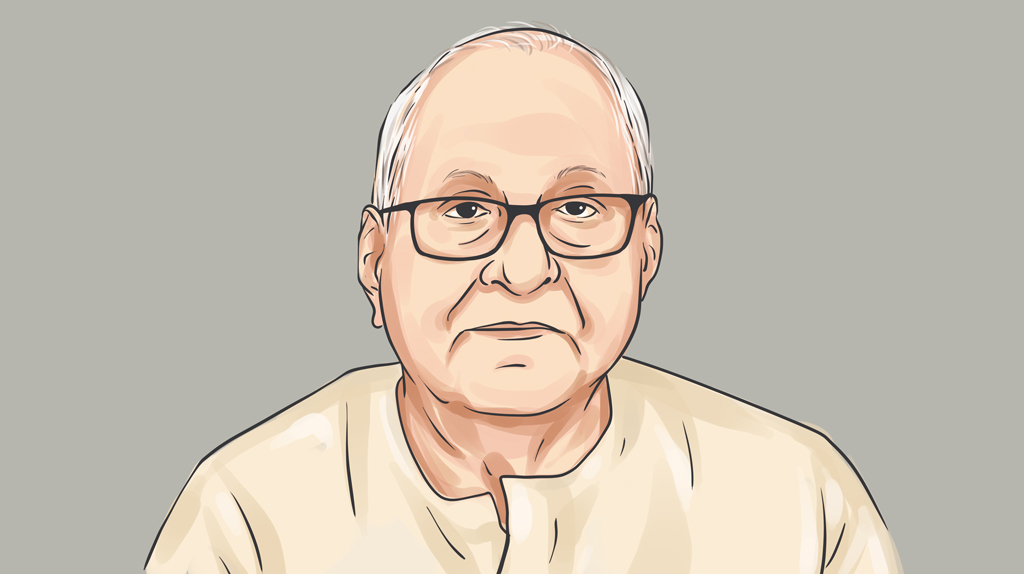
সারা জীবন তো বিজ্ঞান, প্রযুক্তির জয়গানই গেয়েছি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র পৃথিবী আজ নিওনের আলোয় উদ্ভাসিত। পৃথিবীর সম্পদ আজ কত গুণ বেড়েছে, গুগলে একটা স্পর্শ করলে জানা যাবে। কিন্তু সাহিত্য, সংগীত, নাটক, ছায়াছবি, নৃত্যসহ সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে জোরের সঙ্গে কি সে কথা বলা যাবে? সমাজ বদলেছে। সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি সমাজেরই প্রতিফলন। তাই সংস্কৃতি সেই পুরোনো যুগের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, সেটা আমরা আশা করি না। করলেও তা হবে না; হতে পারে না। পুরোনো যুগের মানুষকে তা মেনে নিতে হয়। কষ্ট হলেও মানতে হয়।
আজকের লেখাটি লিখতে অনুপ্রাণিত হলাম ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খানের বড় বড় কয়েকটি সাক্ষাৎকার শুনে। সম্ভবত ১৯৬০-৬৩ সালে দিল্লির দূরদর্শনে সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল। নতুন করে খান সাহেবের পরিচয় দেওয়ার দরকার পড়ে না। ভারতের জনগণ তাঁকে বিশ শতকের ‘তানসেন’ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর সব কথা নিয়ে লেখা সম্ভব নয়। কারণ উর্দু ভালো বুঝি না।
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি যাঁদের কাছে তালিম নিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।’ উত্তরে খান সাহেব বলেন, ‘তাঁরা সবাই অন্য জগতের মানুষ ছিলেন। খোদ আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট। আমি তাঁদের কাছেই পৌঁছাতে পারিনি।’ খান সাহেব পাঁচ বছর বয়সে চাচা কালে খানের কাছে নাড়া বাঁধেন। বিংশ শতাব্দীর তানসেনের কী গভীর শ্রদ্ধা তাঁর ওস্তাদের প্রতি। আরেক প্রশ্নের জবাবে এখনকার গায়কদের প্রতি সেই একই অভিযোগ। যেসব গুণের কথা বললেন, এখনকার শিল্পীদের মধ্যে তার অভাব লক্ষ করেন। এখনকার মানে ষাটের দশকের প্রথমে। বড়ে গোলাম আলী খানের শিষ্য সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকর একই কথা বলেছেন।
কেবল গান গেয়ে তাঁদের কীভাবে চলত? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজা-মহারাজাদের সংগীতপ্রীতির কথা বলেন; অর্থাৎ সামন্ত যুগের কথা চলে আসে। তানসেন ছিলেন সম্রাট আকবরের নবরত্নের একজন; অর্থাৎ সামন্ত যুগীয় অর্থনীতির এটা একটা সুফল। আমরা কেবল সামন্ত যুগীয় শ্রেণিবিভাজন ও নির্যাতনের কথাই জানি। কিন্তু সামন্ত যুগীয় শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটকের এক শক্তিশালী ধারা গড়ে উঠেছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল সামন্ত যুগীয় শ্রেণিবিভাজনের কারণে।
আজ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোয় কে ওই ওস্তাদদের অর্থনৈতিক সাহায্য করবে? আজ সেদিনের মতো কেউ কি কেবল সংগীতের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে? সে যুগে বড় শিল্পীরা যেভাবে রাষ্ট্রের সম্মান পেয়েছেন এবং জনগণের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা লাভ করেছিলেন, আজ কেবল সংগীতের ওপর নির্ভরশীল শিল্পীরা তা পান?
যদি পেট চালানোর জন্য আমাদের অন্য কাজ করতে হয়, তাহলে সেকালের মতো ওস্তাদের জন্ম কি সম্ভব? ওস্তাদ আলী আকবর খান দিনে ১৮ ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন। অন্নপূর্ণা দেবী ও রবিশঙ্কর দিনে ১২ ঘণ্টা। এটা কি এই যুগে সম্ভব? যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কি আজ তাঁদের মতো শিল্পীর জন্ম সম্ভব? সম্ভব যে নয়, আজ তা পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরি, গজল, ভজন বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত। আধুনিক গান ও সিনেমার গানে সুরারোপ করা খুব কঠিন। আমাদের দেশে কজন সুরকার আছেন, যাঁরা নিয়মিত রেওয়াজ করেন? ভারতে আজ উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রসার ঘটছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।
সাহিত্যের দিকে তাকালেও একই চিত্র চোখে পড়ে। আমি পশ্চিমের জগতের কথা বলব না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভাষণে বলেছেন, প্রাচীন ও মধ্য যুগে যদি ব্রাহ্মণ শ্রেণির উদ্ভব না হতো, তাহলে সে সময়ের সাহিত্য সৃষ্টি হতো কীভাবে? প্রতিটি মানুষকে যদি বেঁচে থাকার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, তাহলে মানুষের মনের খোরাক কে সৃষ্টি করবে? অর্থাৎ মানুষের সত্তায় নিহিত সৃজনশীলতা বিকশিত হওয়ার জন্য কিছু মুক্ত সময় তাকে দিতে হবে। সামন্ত যুগের পতনের সময় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পুঁজিবাদের প্রগতিশীল উত্থানে যে অমর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আজকের সমাজ বাস্তবতায় তেমন সাহিত্য কোথায়? আজকেরপ্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী সমাজে যা সৃষ্টি হচ্ছে, তা তারই সঙ্গে সংগতিশীল।
তাহলে এমন সিদ্ধান্তে আসা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চোখঝলসানো উন্নয়ন আমাদের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার জন্য সহায়ক নয়। প্রচুর বই লেখা হচ্ছে। এর মধ্যে কটা বই মৌলিক, যা আগে কখনো লেখা হয়নি। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায় প্রায় সবই আগের কোনো মৌলিক সাহিত্যের টীকাটিপ্পনী। যেমনটা দেখা গিয়েছিল অষ্টম-দশম শতাব্দীর মুসলিম পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে। সেগুলো ছিল প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মৌলিক রচনার টীকাভাষ্য।
তাই এ কথা মিথ্যা নয় যে সাহিত্য হচ্ছে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। যেমন চিত্রশিল্প, সংগীত, নৃত্য। অর্থনৈতিক অবকাঠামো এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আজকের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তদনুরূপ সংস্কৃতির জন্ম হয়।
পরিবর্তন নিয়ে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। বর্তমানের করপোরেট পুঁজিবাদের দোকানে সবকিছুই কিনতে হয়, একটি গোলাপের সৌন্দর্যও তখন হারিয়ে যায়। মোনালিসা তখন বাজারি সৌন্দর্যে পরিণত হয়। দ্য ভিঞ্চি, তানসেন, সত্যজিৎ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেটোফেন, বাখ, শেক্সপিয়ার, উদয়শংকর, আলাউদ্দিন খান, বড়ে গোলাম আলী খান, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি তখন বাজারের সেলফগুলো ভরিয়ে তোলেন। সেখানেই মূল্যবান শোপিস হিসেবে তাঁরা কেনাবেচার সামগ্রী। কিন্তু সেখানে থাকে না সুর-তাল-লয়-ঝুমুর লহরি-নাটক-সাহিত্য ইত্যাদি মানুষের কোনো সৃজনশীলতার স্পর্শ।
তৈরি হয় বর্তমান সমাজেরই ‘রত্নসম্ভার’।
লেখক: সাবেক অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
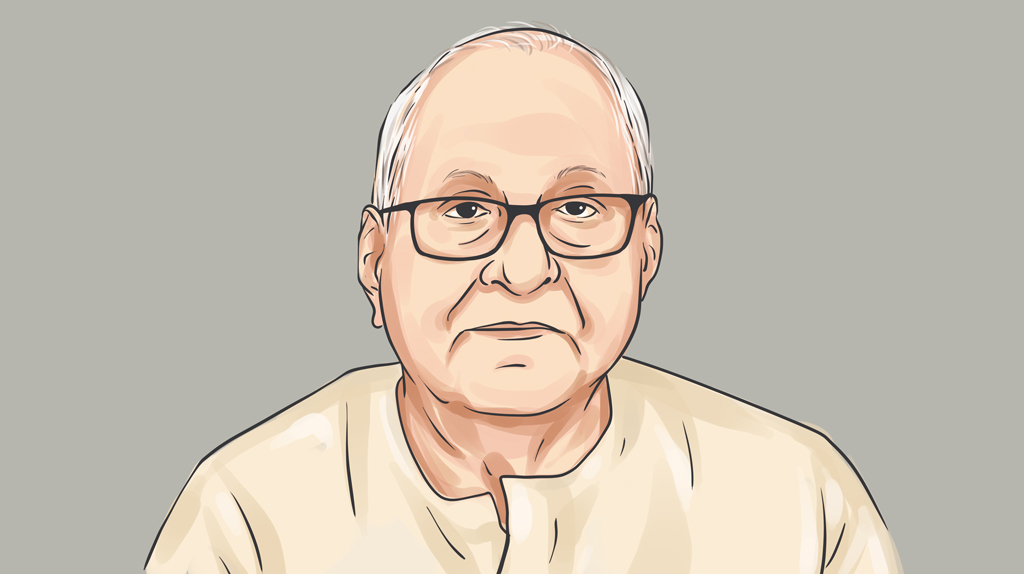
সারা জীবন তো বিজ্ঞান, প্রযুক্তির জয়গানই গেয়েছি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র পৃথিবী আজ নিওনের আলোয় উদ্ভাসিত। পৃথিবীর সম্পদ আজ কত গুণ বেড়েছে, গুগলে একটা স্পর্শ করলে জানা যাবে। কিন্তু সাহিত্য, সংগীত, নাটক, ছায়াছবি, নৃত্যসহ সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে জোরের সঙ্গে কি সে কথা বলা যাবে? সমাজ বদলেছে। সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি সমাজেরই প্রতিফলন। তাই সংস্কৃতি সেই পুরোনো যুগের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে, সেটা আমরা আশা করি না। করলেও তা হবে না; হতে পারে না। পুরোনো যুগের মানুষকে তা মেনে নিতে হয়। কষ্ট হলেও মানতে হয়।
আজকের লেখাটি লিখতে অনুপ্রাণিত হলাম ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খানের বড় বড় কয়েকটি সাক্ষাৎকার শুনে। সম্ভবত ১৯৬০-৬৩ সালে দিল্লির দূরদর্শনে সেগুলো গ্রহণ করা হয়েছিল। নতুন করে খান সাহেবের পরিচয় দেওয়ার দরকার পড়ে না। ভারতের জনগণ তাঁকে বিশ শতকের ‘তানসেন’ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর সব কথা নিয়ে লেখা সম্ভব নয়। কারণ উর্দু ভালো বুঝি না।
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি যাঁদের কাছে তালিম নিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।’ উত্তরে খান সাহেব বলেন, ‘তাঁরা সবাই অন্য জগতের মানুষ ছিলেন। খোদ আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট। আমি তাঁদের কাছেই পৌঁছাতে পারিনি।’ খান সাহেব পাঁচ বছর বয়সে চাচা কালে খানের কাছে নাড়া বাঁধেন। বিংশ শতাব্দীর তানসেনের কী গভীর শ্রদ্ধা তাঁর ওস্তাদের প্রতি। আরেক প্রশ্নের জবাবে এখনকার গায়কদের প্রতি সেই একই অভিযোগ। যেসব গুণের কথা বললেন, এখনকার শিল্পীদের মধ্যে তার অভাব লক্ষ করেন। এখনকার মানে ষাটের দশকের প্রথমে। বড়ে গোলাম আলী খানের শিষ্য সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকর একই কথা বলেছেন।
কেবল গান গেয়ে তাঁদের কীভাবে চলত? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি রাজা-মহারাজাদের সংগীতপ্রীতির কথা বলেন; অর্থাৎ সামন্ত যুগের কথা চলে আসে। তানসেন ছিলেন সম্রাট আকবরের নবরত্নের একজন; অর্থাৎ সামন্ত যুগীয় অর্থনীতির এটা একটা সুফল। আমরা কেবল সামন্ত যুগীয় শ্রেণিবিভাজন ও নির্যাতনের কথাই জানি। কিন্তু সামন্ত যুগীয় শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটকের এক শক্তিশালী ধারা গড়ে উঠেছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল সামন্ত যুগীয় শ্রেণিবিভাজনের কারণে।
আজ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোয় কে ওই ওস্তাদদের অর্থনৈতিক সাহায্য করবে? আজ সেদিনের মতো কেউ কি কেবল সংগীতের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে? সে যুগে বড় শিল্পীরা যেভাবে রাষ্ট্রের সম্মান পেয়েছেন এবং জনগণের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা লাভ করেছিলেন, আজ কেবল সংগীতের ওপর নির্ভরশীল শিল্পীরা তা পান?
যদি পেট চালানোর জন্য আমাদের অন্য কাজ করতে হয়, তাহলে সেকালের মতো ওস্তাদের জন্ম কি সম্ভব? ওস্তাদ আলী আকবর খান দিনে ১৮ ঘণ্টা রেওয়াজ করতেন। অন্নপূর্ণা দেবী ও রবিশঙ্কর দিনে ১২ ঘণ্টা। এটা কি এই যুগে সম্ভব? যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কি আজ তাঁদের মতো শিল্পীর জন্ম সম্ভব? সম্ভব যে নয়, আজ তা পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরি, গজল, ভজন বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত। আধুনিক গান ও সিনেমার গানে সুরারোপ করা খুব কঠিন। আমাদের দেশে কজন সুরকার আছেন, যাঁরা নিয়মিত রেওয়াজ করেন? ভারতে আজ উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রসার ঘটছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।
সাহিত্যের দিকে তাকালেও একই চিত্র চোখে পড়ে। আমি পশ্চিমের জগতের কথা বলব না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভাষণে বলেছেন, প্রাচীন ও মধ্য যুগে যদি ব্রাহ্মণ শ্রেণির উদ্ভব না হতো, তাহলে সে সময়ের সাহিত্য সৃষ্টি হতো কীভাবে? প্রতিটি মানুষকে যদি বেঁচে থাকার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, তাহলে মানুষের মনের খোরাক কে সৃষ্টি করবে? অর্থাৎ মানুষের সত্তায় নিহিত সৃজনশীলতা বিকশিত হওয়ার জন্য কিছু মুক্ত সময় তাকে দিতে হবে। সামন্ত যুগের পতনের সময় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং পুঁজিবাদের প্রগতিশীল উত্থানে যে অমর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আজকের সমাজ বাস্তবতায় তেমন সাহিত্য কোথায়? আজকেরপ্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী সমাজে যা সৃষ্টি হচ্ছে, তা তারই সঙ্গে সংগতিশীল।
তাহলে এমন সিদ্ধান্তে আসা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চোখঝলসানো উন্নয়ন আমাদের সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার জন্য সহায়ক নয়। প্রচুর বই লেখা হচ্ছে। এর মধ্যে কটা বই মৌলিক, যা আগে কখনো লেখা হয়নি। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায় প্রায় সবই আগের কোনো মৌলিক সাহিত্যের টীকাটিপ্পনী। যেমনটা দেখা গিয়েছিল অষ্টম-দশম শতাব্দীর মুসলিম পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে। সেগুলো ছিল প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মৌলিক রচনার টীকাভাষ্য।
তাই এ কথা মিথ্যা নয় যে সাহিত্য হচ্ছে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। যেমন চিত্রশিল্প, সংগীত, নৃত্য। অর্থনৈতিক অবকাঠামো এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আজকের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা গেল যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তদনুরূপ সংস্কৃতির জন্ম হয়।
পরিবর্তন নিয়ে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। বর্তমানের করপোরেট পুঁজিবাদের দোকানে সবকিছুই কিনতে হয়, একটি গোলাপের সৌন্দর্যও তখন হারিয়ে যায়। মোনালিসা তখন বাজারি সৌন্দর্যে পরিণত হয়। দ্য ভিঞ্চি, তানসেন, সত্যজিৎ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেটোফেন, বাখ, শেক্সপিয়ার, উদয়শংকর, আলাউদ্দিন খান, বড়ে গোলাম আলী খান, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি তখন বাজারের সেলফগুলো ভরিয়ে তোলেন। সেখানেই মূল্যবান শোপিস হিসেবে তাঁরা কেনাবেচার সামগ্রী। কিন্তু সেখানে থাকে না সুর-তাল-লয়-ঝুমুর লহরি-নাটক-সাহিত্য ইত্যাদি মানুষের কোনো সৃজনশীলতার স্পর্শ।
তৈরি হয় বর্তমান সমাজেরই ‘রত্নসম্ভার’।
লেখক: সাবেক অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...
১২ জুন ২০২৫
ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।
১৯ মে ২০২৫
আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
০৮ মে ২০২৫
পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...
০৮ মে ২০২৫