কাশফিয়া আলম ঝিলিক

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে? এসব বিষয়ে জানতে চেয়ে আমরা লিখিত প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম তিন নারীনেত্রীর কাছে। কী বলছেন তাঁরা? জানাচ্ছেন কাশফিয়া আলম ঝিলিক।

নারীকে পিছিয়ে রাখা মানে সমাজকেই পিছিয়ে রাখা
নারীবিষয়ক প্রতিবাদী পদক্ষেপগুলো বেশির ভাগ সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। কারণ, বৈষম্যমূলক এই সমাজে ক্ষমতাসীনেরা সব সময় মানুষকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে রাখে। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। শহরের নারীদের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই, কর্মজীবী নারীর সন্তানকে দেখাশোনার জন্য ডে কেয়ার নেই। অথচ এগুলো নিয়ে আলোচনা কম। গুটিকয়েক সেনসেশনাল ইস্যু, যেগুলো বাংলাদেশের বেশির ভাগ সাধারণ নারীর মূল ইস্যু নয়, সেগুলো নিয়েই মিডিয়া সয়লাব। মূল আলোচনা চাপা পড়ে যায়।
নারীকে নিয়ে আজেবাজে কথা বললেও রাষ্ট্র কখনোই তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না; বরং পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে নারীকে গৃহে বন্দী করতে চায়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইতিবাচক প্রভাব যেমন ফেলছে, তেমনি নেতিবাচক প্রভাবও। তবে সরকারের অবহেলার কারণে নেতিবাচক প্রভাবই বেশি পড়ছে। একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে নারী অবাধে তার মত প্রকাশ করতে পারবে। সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে জনপরিসরে হেয় করে বক্তব্য ছড়িয়ে নারীজীবনকে খুব সহজে আক্রান্ত করা যায়। শোষণের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে, তাই নারী এবং ধর্মকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভেদ তৈরি করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জনমনে নারী সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে
নারী অধিকার বলতে, শ্রম থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কিংবা সম্পত্তি নিয়ে যেসব প্রতিবাদ হয়ে থাকে, সেগুলো সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারে কি না, সেটা একটা প্রশ্ন। কারণ, বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, নারীরা এক্সট্রিম কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে হাজির হয়ে যায়। ফলে সমাজে যারা সাধারণ নারী, যারা অ্যাকটিভিজম করে না, তারা আসলে নিজেদের এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না। এ কারণে নারীর বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও কথাবার্তা কম হতে দেখা যায়।
নারীকে আজেবাজে মন্তব্য করার বিষয়ে অনেকে বলেন, আমরা তো অন্য নারীকে বলছি, সবাইকে না। তখন আজেবাজে কথাকে ইস্যু বানানো হয় না। যদি জনসমক্ষে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করা শুরু হয়, যারা এ ধরনের মন্তব্য করে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হলে এসব বন্ধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে দেখা যায়, নারীকে হেয় করার জন্য সব ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্যের আশ্রয় নেওয়া হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীরা যেমন ভোকাল হয়, তেমনই নারীর প্রতি অবমাননাও করা হয়। দেখা যায়, নেতিবাচক বিষয়গুলোই এখানে বেশি প্রচারিত হয়। তাই এখানে নারীবিদ্বেষ মোটাদাগে বেশি চোখে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে আরও বেশি নারীকে হেনস্তার প্রবণতা বাড়ছে। অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় যে নারীরা যেহেতু সমান অধিকার চাচ্ছে, তাহলে সমান হেনস্তার শিকার তারা কেন হবে না। এ ধরনের একটা কনসেপ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে গড়ে উঠছে। এসব নারীর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নারী বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই হয় না
নারী নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা কোনো নতুন বিষয় নয়। দেশ-কালের পরিবর্তনের ফলে এর ফর্ম পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো ইস্যু এলে এটা আমাদের চোখে পড়ে বেশি। কিন্তু নারীবিদ্বেষী মন্তব্য এখানে চলমান। কারণ, আমরা যে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে বাস করি, সেখানে নারীকে অতি ক্ষমতাহীন ও দুর্বল ভাবা হয়। তাই তাদের প্রতি যেকোনো মন্তব্য করা যায় বলে তারা মনে করে। আবার যে নারী এগিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে এই মিসোজেনিস্ট আলাপ করে দাবিয়ে রাখতে চায়। কখনো দেখেছেন, এই ধরনের কথা বললে কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে হয়! তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কোনো অ্যাকশন থাকে? এর মানে কি এই নয় যে রাষ্ট্র নিজেও নারীবিদ্বেষী এই প্রবণতা উৎপাদনের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তার নানা অ্যাকশন দিয়ে।
নারীর যেকোনো বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই তো হয় না। নারী হচ্ছে লিটমাসের মতো। এই প্রসঙ্গের অবস্থান দিয়েই চিহ্নিত করা যায়, রাষ্ট্র জনগণের পক্ষে না বিপক্ষে। তাই এ-সংক্রান্ত প্রতিবাদ যত ধামাচাপা দেওয়া যাবে, তা রাষ্ট্রের জন্য তত স্বস্তির।
চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদের মূল থিম হচ্ছে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যৌথ কণ্ঠস্বর গড়ে তোলা। ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীরা বিভিন্ন ফর্মে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, ঠিক তেমনি নারীবাদীদের বহুমুখী ডিজিটাল অ্যাকটিভিজম গড়ে উঠেছে। প্রযুক্তিকে অস্বীকার না করে চতুর্থ ওয়েভ নারীবাদ কিন্তু প্রযুক্তির মধ্যেই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে একে শক্তি হিসেবে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেও আমি মনে করি নারীবাদী অ্যাকটিভিজমের শক্তিশালী টুল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই আমি ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীর নব কৌশলে হয়রানির শিকার হওয়া দেখছি, তেমনি তার বিপরীতে প্রচুর নারীর সঞ্চরণশীল কার্যক্রমকেও পাঠ করছি।

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে? এসব বিষয়ে জানতে চেয়ে আমরা লিখিত প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম তিন নারীনেত্রীর কাছে। কী বলছেন তাঁরা? জানাচ্ছেন কাশফিয়া আলম ঝিলিক।

নারীকে পিছিয়ে রাখা মানে সমাজকেই পিছিয়ে রাখা
নারীবিষয়ক প্রতিবাদী পদক্ষেপগুলো বেশির ভাগ সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। কারণ, বৈষম্যমূলক এই সমাজে ক্ষমতাসীনেরা সব সময় মানুষকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে রাখে। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। শহরের নারীদের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই, কর্মজীবী নারীর সন্তানকে দেখাশোনার জন্য ডে কেয়ার নেই। অথচ এগুলো নিয়ে আলোচনা কম। গুটিকয়েক সেনসেশনাল ইস্যু, যেগুলো বাংলাদেশের বেশির ভাগ সাধারণ নারীর মূল ইস্যু নয়, সেগুলো নিয়েই মিডিয়া সয়লাব। মূল আলোচনা চাপা পড়ে যায়।
নারীকে নিয়ে আজেবাজে কথা বললেও রাষ্ট্র কখনোই তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না; বরং পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে নারীকে গৃহে বন্দী করতে চায়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইতিবাচক প্রভাব যেমন ফেলছে, তেমনি নেতিবাচক প্রভাবও। তবে সরকারের অবহেলার কারণে নেতিবাচক প্রভাবই বেশি পড়ছে। একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে নারী অবাধে তার মত প্রকাশ করতে পারবে। সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে জনপরিসরে হেয় করে বক্তব্য ছড়িয়ে নারীজীবনকে খুব সহজে আক্রান্ত করা যায়। শোষণের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে, তাই নারী এবং ধর্মকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভেদ তৈরি করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জনমনে নারী সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে
নারী অধিকার বলতে, শ্রম থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কিংবা সম্পত্তি নিয়ে যেসব প্রতিবাদ হয়ে থাকে, সেগুলো সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারে কি না, সেটা একটা প্রশ্ন। কারণ, বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, নারীরা এক্সট্রিম কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে হাজির হয়ে যায়। ফলে সমাজে যারা সাধারণ নারী, যারা অ্যাকটিভিজম করে না, তারা আসলে নিজেদের এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না। এ কারণে নারীর বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও কথাবার্তা কম হতে দেখা যায়।
নারীকে আজেবাজে মন্তব্য করার বিষয়ে অনেকে বলেন, আমরা তো অন্য নারীকে বলছি, সবাইকে না। তখন আজেবাজে কথাকে ইস্যু বানানো হয় না। যদি জনসমক্ষে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করা শুরু হয়, যারা এ ধরনের মন্তব্য করে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হলে এসব বন্ধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে দেখা যায়, নারীকে হেয় করার জন্য সব ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্যের আশ্রয় নেওয়া হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীরা যেমন ভোকাল হয়, তেমনই নারীর প্রতি অবমাননাও করা হয়। দেখা যায়, নেতিবাচক বিষয়গুলোই এখানে বেশি প্রচারিত হয়। তাই এখানে নারীবিদ্বেষ মোটাদাগে বেশি চোখে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে আরও বেশি নারীকে হেনস্তার প্রবণতা বাড়ছে। অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় যে নারীরা যেহেতু সমান অধিকার চাচ্ছে, তাহলে সমান হেনস্তার শিকার তারা কেন হবে না। এ ধরনের একটা কনসেপ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে গড়ে উঠছে। এসব নারীর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নারী বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই হয় না
নারী নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা কোনো নতুন বিষয় নয়। দেশ-কালের পরিবর্তনের ফলে এর ফর্ম পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো ইস্যু এলে এটা আমাদের চোখে পড়ে বেশি। কিন্তু নারীবিদ্বেষী মন্তব্য এখানে চলমান। কারণ, আমরা যে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে বাস করি, সেখানে নারীকে অতি ক্ষমতাহীন ও দুর্বল ভাবা হয়। তাই তাদের প্রতি যেকোনো মন্তব্য করা যায় বলে তারা মনে করে। আবার যে নারী এগিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে এই মিসোজেনিস্ট আলাপ করে দাবিয়ে রাখতে চায়। কখনো দেখেছেন, এই ধরনের কথা বললে কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে হয়! তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কোনো অ্যাকশন থাকে? এর মানে কি এই নয় যে রাষ্ট্র নিজেও নারীবিদ্বেষী এই প্রবণতা উৎপাদনের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তার নানা অ্যাকশন দিয়ে।
নারীর যেকোনো বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই তো হয় না। নারী হচ্ছে লিটমাসের মতো। এই প্রসঙ্গের অবস্থান দিয়েই চিহ্নিত করা যায়, রাষ্ট্র জনগণের পক্ষে না বিপক্ষে। তাই এ-সংক্রান্ত প্রতিবাদ যত ধামাচাপা দেওয়া যাবে, তা রাষ্ট্রের জন্য তত স্বস্তির।
চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদের মূল থিম হচ্ছে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যৌথ কণ্ঠস্বর গড়ে তোলা। ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীরা বিভিন্ন ফর্মে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, ঠিক তেমনি নারীবাদীদের বহুমুখী ডিজিটাল অ্যাকটিভিজম গড়ে উঠেছে। প্রযুক্তিকে অস্বীকার না করে চতুর্থ ওয়েভ নারীবাদ কিন্তু প্রযুক্তির মধ্যেই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে একে শক্তি হিসেবে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেও আমি মনে করি নারীবাদী অ্যাকটিভিজমের শক্তিশালী টুল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই আমি ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীর নব কৌশলে হয়রানির শিকার হওয়া দেখছি, তেমনি তার বিপরীতে প্রচুর নারীর সঞ্চরণশীল কার্যক্রমকেও পাঠ করছি।
কাশফিয়া আলম ঝিলিক

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে? এসব বিষয়ে জানতে চেয়ে আমরা লিখিত প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম তিন নারীনেত্রীর কাছে। কী বলছেন তাঁরা? জানাচ্ছেন কাশফিয়া আলম ঝিলিক।

নারীকে পিছিয়ে রাখা মানে সমাজকেই পিছিয়ে রাখা
নারীবিষয়ক প্রতিবাদী পদক্ষেপগুলো বেশির ভাগ সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। কারণ, বৈষম্যমূলক এই সমাজে ক্ষমতাসীনেরা সব সময় মানুষকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে রাখে। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। শহরের নারীদের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই, কর্মজীবী নারীর সন্তানকে দেখাশোনার জন্য ডে কেয়ার নেই। অথচ এগুলো নিয়ে আলোচনা কম। গুটিকয়েক সেনসেশনাল ইস্যু, যেগুলো বাংলাদেশের বেশির ভাগ সাধারণ নারীর মূল ইস্যু নয়, সেগুলো নিয়েই মিডিয়া সয়লাব। মূল আলোচনা চাপা পড়ে যায়।
নারীকে নিয়ে আজেবাজে কথা বললেও রাষ্ট্র কখনোই তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না; বরং পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে নারীকে গৃহে বন্দী করতে চায়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইতিবাচক প্রভাব যেমন ফেলছে, তেমনি নেতিবাচক প্রভাবও। তবে সরকারের অবহেলার কারণে নেতিবাচক প্রভাবই বেশি পড়ছে। একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে নারী অবাধে তার মত প্রকাশ করতে পারবে। সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে জনপরিসরে হেয় করে বক্তব্য ছড়িয়ে নারীজীবনকে খুব সহজে আক্রান্ত করা যায়। শোষণের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে, তাই নারী এবং ধর্মকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভেদ তৈরি করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জনমনে নারী সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে
নারী অধিকার বলতে, শ্রম থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কিংবা সম্পত্তি নিয়ে যেসব প্রতিবাদ হয়ে থাকে, সেগুলো সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারে কি না, সেটা একটা প্রশ্ন। কারণ, বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, নারীরা এক্সট্রিম কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে হাজির হয়ে যায়। ফলে সমাজে যারা সাধারণ নারী, যারা অ্যাকটিভিজম করে না, তারা আসলে নিজেদের এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না। এ কারণে নারীর বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও কথাবার্তা কম হতে দেখা যায়।
নারীকে আজেবাজে মন্তব্য করার বিষয়ে অনেকে বলেন, আমরা তো অন্য নারীকে বলছি, সবাইকে না। তখন আজেবাজে কথাকে ইস্যু বানানো হয় না। যদি জনসমক্ষে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করা শুরু হয়, যারা এ ধরনের মন্তব্য করে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হলে এসব বন্ধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে দেখা যায়, নারীকে হেয় করার জন্য সব ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্যের আশ্রয় নেওয়া হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীরা যেমন ভোকাল হয়, তেমনই নারীর প্রতি অবমাননাও করা হয়। দেখা যায়, নেতিবাচক বিষয়গুলোই এখানে বেশি প্রচারিত হয়। তাই এখানে নারীবিদ্বেষ মোটাদাগে বেশি চোখে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে আরও বেশি নারীকে হেনস্তার প্রবণতা বাড়ছে। অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় যে নারীরা যেহেতু সমান অধিকার চাচ্ছে, তাহলে সমান হেনস্তার শিকার তারা কেন হবে না। এ ধরনের একটা কনসেপ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে গড়ে উঠছে। এসব নারীর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নারী বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই হয় না
নারী নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা কোনো নতুন বিষয় নয়। দেশ-কালের পরিবর্তনের ফলে এর ফর্ম পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো ইস্যু এলে এটা আমাদের চোখে পড়ে বেশি। কিন্তু নারীবিদ্বেষী মন্তব্য এখানে চলমান। কারণ, আমরা যে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে বাস করি, সেখানে নারীকে অতি ক্ষমতাহীন ও দুর্বল ভাবা হয়। তাই তাদের প্রতি যেকোনো মন্তব্য করা যায় বলে তারা মনে করে। আবার যে নারী এগিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে এই মিসোজেনিস্ট আলাপ করে দাবিয়ে রাখতে চায়। কখনো দেখেছেন, এই ধরনের কথা বললে কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে হয়! তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কোনো অ্যাকশন থাকে? এর মানে কি এই নয় যে রাষ্ট্র নিজেও নারীবিদ্বেষী এই প্রবণতা উৎপাদনের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তার নানা অ্যাকশন দিয়ে।
নারীর যেকোনো বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই তো হয় না। নারী হচ্ছে লিটমাসের মতো। এই প্রসঙ্গের অবস্থান দিয়েই চিহ্নিত করা যায়, রাষ্ট্র জনগণের পক্ষে না বিপক্ষে। তাই এ-সংক্রান্ত প্রতিবাদ যত ধামাচাপা দেওয়া যাবে, তা রাষ্ট্রের জন্য তত স্বস্তির।
চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদের মূল থিম হচ্ছে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যৌথ কণ্ঠস্বর গড়ে তোলা। ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীরা বিভিন্ন ফর্মে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, ঠিক তেমনি নারীবাদীদের বহুমুখী ডিজিটাল অ্যাকটিভিজম গড়ে উঠেছে। প্রযুক্তিকে অস্বীকার না করে চতুর্থ ওয়েভ নারীবাদ কিন্তু প্রযুক্তির মধ্যেই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে একে শক্তি হিসেবে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেও আমি মনে করি নারীবাদী অ্যাকটিভিজমের শক্তিশালী টুল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই আমি ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীর নব কৌশলে হয়রানির শিকার হওয়া দেখছি, তেমনি তার বিপরীতে প্রচুর নারীর সঞ্চরণশীল কার্যক্রমকেও পাঠ করছি।

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে? এসব বিষয়ে জানতে চেয়ে আমরা লিখিত প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম তিন নারীনেত্রীর কাছে। কী বলছেন তাঁরা? জানাচ্ছেন কাশফিয়া আলম ঝিলিক।

নারীকে পিছিয়ে রাখা মানে সমাজকেই পিছিয়ে রাখা
নারীবিষয়ক প্রতিবাদী পদক্ষেপগুলো বেশির ভাগ সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। কারণ, বৈষম্যমূলক এই সমাজে ক্ষমতাসীনেরা সব সময় মানুষকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে রাখে। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করে। শহরের নারীদের স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই, কর্মজীবী নারীর সন্তানকে দেখাশোনার জন্য ডে কেয়ার নেই। অথচ এগুলো নিয়ে আলোচনা কম। গুটিকয়েক সেনসেশনাল ইস্যু, যেগুলো বাংলাদেশের বেশির ভাগ সাধারণ নারীর মূল ইস্যু নয়, সেগুলো নিয়েই মিডিয়া সয়লাব। মূল আলোচনা চাপা পড়ে যায়।
নারীকে নিয়ে আজেবাজে কথা বললেও রাষ্ট্র কখনোই তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় না; বরং পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক রাষ্ট্রনায়কেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে নারীকে গৃহে বন্দী করতে চায়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইতিবাচক প্রভাব যেমন ফেলছে, তেমনি নেতিবাচক প্রভাবও। তবে সরকারের অবহেলার কারণে নেতিবাচক প্রভাবই বেশি পড়ছে। একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে নারী অবাধে তার মত প্রকাশ করতে পারবে। সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে জনপরিসরে হেয় করে বক্তব্য ছড়িয়ে নারীজীবনকে খুব সহজে আক্রান্ত করা যায়। শোষণের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে, তাই নারী এবং ধর্মকে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভেদ তৈরি করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জনমনে নারী সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে
নারী অধিকার বলতে, শ্রম থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কিংবা সম্পত্তি নিয়ে যেসব প্রতিবাদ হয়ে থাকে, সেগুলো সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারে কি না, সেটা একটা প্রশ্ন। কারণ, বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, নারীরা এক্সট্রিম কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে হাজির হয়ে যায়। ফলে সমাজে যারা সাধারণ নারী, যারা অ্যাকটিভিজম করে না, তারা আসলে নিজেদের এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না। এ কারণে নারীর বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও কথাবার্তা কম হতে দেখা যায়।
নারীকে আজেবাজে মন্তব্য করার বিষয়ে অনেকে বলেন, আমরা তো অন্য নারীকে বলছি, সবাইকে না। তখন আজেবাজে কথাকে ইস্যু বানানো হয় না। যদি জনসমক্ষে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করা শুরু হয়, যারা এ ধরনের মন্তব্য করে, তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হলে এসব বন্ধ করা সম্ভব। বাংলাদেশে দেখা যায়, নারীকে হেয় করার জন্য সব ক্ষেত্রে এ ধরনের মন্তব্যের আশ্রয় নেওয়া হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীরা যেমন ভোকাল হয়, তেমনই নারীর প্রতি অবমাননাও করা হয়। দেখা যায়, নেতিবাচক বিষয়গুলোই এখানে বেশি প্রচারিত হয়। তাই এখানে নারীবিদ্বেষ মোটাদাগে বেশি চোখে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে আরও বেশি নারীকে হেনস্তার প্রবণতা বাড়ছে। অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় যে নারীরা যেহেতু সমান অধিকার চাচ্ছে, তাহলে সমান হেনস্তার শিকার তারা কেন হবে না। এ ধরনের একটা কনসেপ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে গড়ে উঠছে। এসব নারীর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিকে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

নারী বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই হয় না
নারী নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা কোনো নতুন বিষয় নয়। দেশ-কালের পরিবর্তনের ফলে এর ফর্ম পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো ইস্যু এলে এটা আমাদের চোখে পড়ে বেশি। কিন্তু নারীবিদ্বেষী মন্তব্য এখানে চলমান। কারণ, আমরা যে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে বাস করি, সেখানে নারীকে অতি ক্ষমতাহীন ও দুর্বল ভাবা হয়। তাই তাদের প্রতি যেকোনো মন্তব্য করা যায় বলে তারা মনে করে। আবার যে নারী এগিয়ে যেতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে এই মিসোজেনিস্ট আলাপ করে দাবিয়ে রাখতে চায়। কখনো দেখেছেন, এই ধরনের কথা বললে কাউকে কোনো জবাবদিহি করতে হয়! তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় কোনো অ্যাকশন থাকে? এর মানে কি এই নয় যে রাষ্ট্র নিজেও নারীবিদ্বেষী এই প্রবণতা উৎপাদনের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে তার নানা অ্যাকশন দিয়ে।
নারীর যেকোনো বিষয়ের প্রতিবাদকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই তো হয় না। নারী হচ্ছে লিটমাসের মতো। এই প্রসঙ্গের অবস্থান দিয়েই চিহ্নিত করা যায়, রাষ্ট্র জনগণের পক্ষে না বিপক্ষে। তাই এ-সংক্রান্ত প্রতিবাদ যত ধামাচাপা দেওয়া যাবে, তা রাষ্ট্রের জন্য তত স্বস্তির।
চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদের মূল থিম হচ্ছে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যৌথ কণ্ঠস্বর গড়ে তোলা। ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীরা বিভিন্ন ফর্মে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে, ঠিক তেমনি নারীবাদীদের বহুমুখী ডিজিটাল অ্যাকটিভিজম গড়ে উঠেছে। প্রযুক্তিকে অস্বীকার না করে চতুর্থ ওয়েভ নারীবাদ কিন্তু প্রযুক্তির মধ্যেই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে একে শক্তি হিসেবে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেও আমি মনে করি নারীবাদী অ্যাকটিভিজমের শক্তিশালী টুল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তাই আমি ডিজিটাল স্পেসে যেমন নারীর নব কৌশলে হয়রানির শিকার হওয়া দেখছি, তেমনি তার বিপরীতে প্রচুর নারীর সঞ্চরণশীল কার্যক্রমকেও পাঠ করছি।

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিনের কথা মনে হলে কিছু জনপ্রিয় গানের কথা সামনে আসে। জানেন কি, হিমেল হাওয়ার পরশ আর আলোকসজ্জার রোশনাইয়ের মধ্যে যে সুরগুলো আমাদের কানে বাজে, সেগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে একদল নারী। তাঁদের লেখা, কণ্ঠ আর সুরের জাদুকরী মিশেলে বড়দিন পেয়েছে এক অনন্য রূপ।...
২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরে শুধু নয়, পুরো দেশে নারীরা ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরব অবদান রেখে চলেছেন। আমরা সেই সব নারীকে ‘উদ্যোক্তা’ হিসেবে দেখছি। এই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বছরজুড়ে অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন ধরনের মেলা, সেটাও শুধু ঢাকায় নয়; বরং পুরো দেশে। সেই মেলাগুলো শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়...
১ দিন আগে
ব্যর্থতা কখনো কখনো সাফল্যের মোড়কে ফিরে আসে। রোজাইয়া রাব্বি রোজের গল্পটা তেমনই। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা শেষ করে ২০১৭ সালে ভর্তি হন গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। তবে বাবার অসুস্থতার কারণে বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে বসতে হয় বিয়ের...
১ দিন আগে
পোখারা শহরের এক বাড়ির ছাদ। রাতের নিস্তব্ধতায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক কিশোরী। সঙ্গে আছেন তার মা, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক। কিশোরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওই দুটো নক্ষত্র কি এখনই ধাক্কা খাবে?’ মা হেসে বুঝিয়ে দেন, ওরা একে অপরের থেকে কত দূরে কিংবা ওই যে ছুটন্ত বিন্দুটি দেখছ, ওটা আসলে নক্ষত্র...
২ দিন আগেফিচার ডেস্ক, ঢাকা

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিনের কথা মনে হলে কিছু জনপ্রিয় গানের কথা সামনে আসে। জানেন কি, হিমেল হাওয়ার পরশ আর আলোকসজ্জার রোশনাইয়ের মধ্যে যে সুরগুলো আমাদের কানে বাজে, সেগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে একদল নারী। তাঁদের লেখা, কণ্ঠ আর সুরের জাদুকরী মিশেলে বড়দিন পেয়েছে এক অনন্য রূপ।
কুইন অব ক্রিসমাস মারায়া
বড়দিনের গানের কথা উঠলে যে নামটি সবার আগে স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে, তিনি হলেন মারায়া কেরি। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় বড়দিনের অলিখিত অ্যানথাম, ‘অল আই ওয়ান্ট ফর ক্রিসমাস ইজ ইউ...’ গানটি। এটি যৌথভাবে লিখেছিলেন মারায়া কেরি ও ওয়াল্টার এন আফানাসিফ। এর কণ্ঠশিল্পী ছিলেন মারায়া। এই গানের প্রতিটি ছত্রে মিশে রয়েছে এক চিরন্তন আর্তি। তাঁর গানের কথায় ফুটে ওঠে সেই সত্য, ‘বড়দিনে খুব বেশি কিছু চাওয়ার নেই আমার,/ শুধু একটি জিনিসেরই বড় প্রয়োজন... বড়দিনে শুধু তোমাকেই চাই আমি!’ এর অর্থ, উৎসবের জাঁকজমক বা দামি উপহারের চেয়ে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যই আসল।

মারায়া কেরি ও ওয়াল্টার এ গানটি লিখতে ও সুর করতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র ১৫ মিনিট। গান লেখা ও কণ্ঠ দেওয়াই নয়, মারায়া ছিলেন এই গানের সুরকার। প্রতিবছরের ডিসেম্বরে বিলবোর্ড চার্টের শীর্ষে ফিরে আসা এই এক গান থেকে তিনি কোটি কোটি টাকা রয়্যালটি পান, যা তাঁকে এনে দিয়েছে কুইন অব ক্রিসমাস বা বড়দিনের রানি উপাধি।
ড্রামের শব্দে ধ্রুপদি সুর

এক দরিদ্র শিশু, যার কাছে যিশুর জন্মের আনন্দ উৎসবে দেওয়ার মতো কোনো দামি উপহার ছিল না। তাই সে তার ছোট্ট ড্রামটি বাজিয়ে সম্মান জানাতে চেয়েছিল। এমনই একটি ঘটনাকে সুরে-তালে মিলিয়েছিলেন আমেরিকান সংগীত শিক্ষক ক্যাথরিন কেনিকট ডেভিস। ১৯৪১ সালের অনন্য সৃষ্টি ‘দ্য লিটিল ড্রামার বয়’ গানটি। প্রথমে এর নাম ছিল ‘দ্য ক্যারল অব দ্য ড্রাম’। গানটি একটি চেক গানের অনুকরণে তৈরি বলে ধারণা করা হয়। তবে এর সুর এবং কথা দুটোরই মূল কারিগর ছিলেন ক্যাথরিন। গানের সেই বিখ্যাত ‘পা-রাম-পাম-পাম-পাম’ সুরটি মূলত ক্যাথরিনেরই করা। আজও বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে বড়দিনের ক্যারল হিসেবে এ সুরটি মানুষের হৃদয়ে অনুরণিত হয়।
চঞ্চলতা ও শাশ্বত আবেদন
বড়দিনের উৎসবে কেবল ভক্তি বা আবেগ নয়, মিশে থাকে কিছুটা চঞ্চলতা আর কৌতুকও। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘স্যান্টা বেবি’ গানটি তারই প্রমাণ। এর নেপথ্যে ছিলেন প্রতিভাবান গীতিকার জোয়ান জাভিটস। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন সিনেটর জ্যাকব জাভিটসের ভাইয়ের মেয়ে। সে সময়ে দাঁড়িয়ে এক নারীর এমন চটুল ও আধুনিক কথার গান লেখা ছিল বেশ সাহসী পদক্ষেপ। ফিল স্প্রিংগার ও টনি স্প্রিংগারের সঙ্গে মিলে জোয়ান এ গানটি লিখেছিলেন। গানটি আর্থ কিটের কণ্ঠে অমর হয়ে আছে। দশকের পর দশক পার হলেও গানটির আবেদন একটুও কমেনি। ম্যাডোনা থেকে শুরু করে কাইলি মিনোগ, টেইলর সুইফট এবং আরিয়ানা গ্রান্দের মতো বর্তমান সময়ের পপতারকারাও এ গানটি নতুন করে গেয়েছেন।
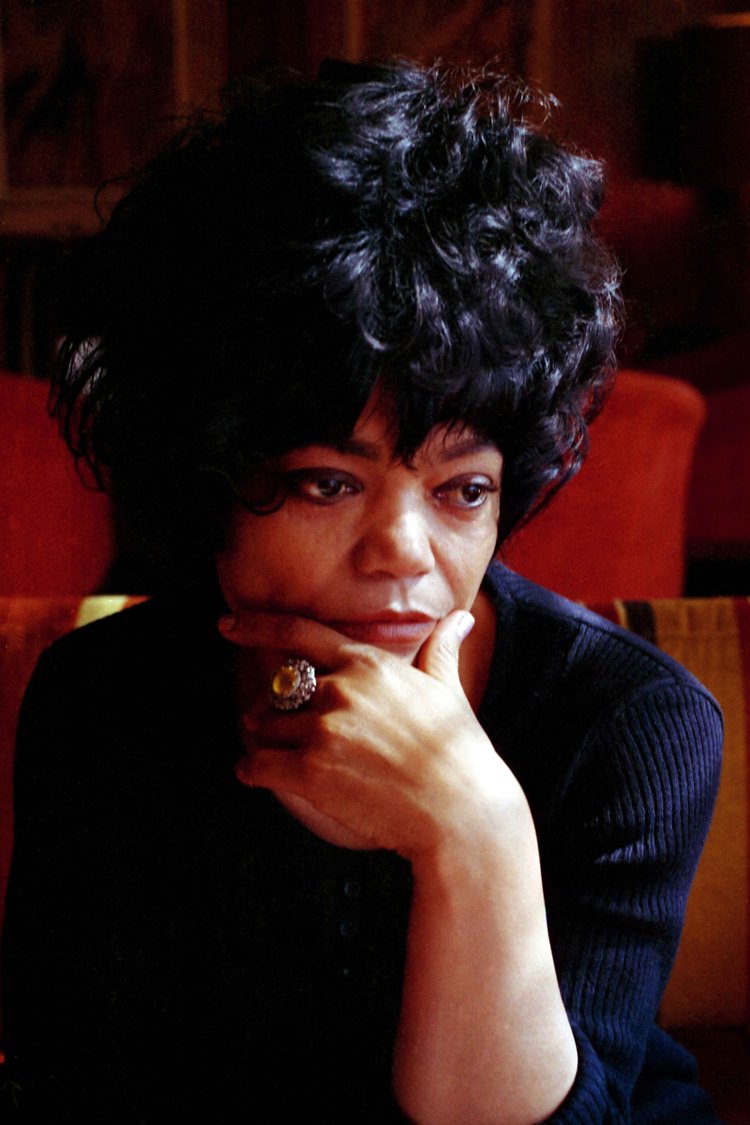
কিংবদন্তির সুর ও আধুনিকতার ছোঁয়া
কান্ট্রি মিউজিকের কিংবদন্তি ডলি পার্টন বড়দিনের উৎসবকে রাঙিয়েছেন নিজের মেধা দিয়ে। তিনি বড়দিন উপলক্ষে একাধিক সফল অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশ গানই ছিল তাঁর নিজের লেখা। তাঁর অমর সৃষ্টি ‘হার্ড ক্যান্ডি ক্রিসমাস’ ও ‘ক্রিসমাস অব মেনি কালার্স’ গানগুলো আজও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।
সিয়ার কণ্ঠে বড়দিনের আনন্দের স্রোত

সময়ের স্রোতে বড়দিনের গানে যোগ হয়েছে আধুনিকতার নতুন মাত্রা। তরুণ প্রজন্মের কাছে বড়দিন মানেই যেন অস্ট্রেলিয়ান সংগীতশিল্পী ও গীতিকার সিয়া। ২০১৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘এভরিডে ইজ ক্রিসমাস’ অ্যালবামটি। সিয়া প্রমাণ করেছেন, বড়দিনের গানের জন্য কেবল পুরোনো ক্ল্যাসিকের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। তাঁর নিজের লেখা ‘স্নো ম্যান’ ও ‘স্যান্টা ইজ কামিং ফর আস’ গানগুলো এখনকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়।
বড়দিনের সুরের মূর্ছনা কেবল সুর নয়; বরং এক অদৃশ্য মিলনমেলা। পর্দার আড়ালে থাকা এই নারী কারিগরদের লেখনী আর সুরের মায়ায় বড়দিন হয়ে ওঠে আরও মধুময়, আরও প্রাণবন্ত। প্রিয়জন আর আত্মীয়স্বজনের সে মিলনমেলায় এ গানগুলোই হয়ে থাকে আত্মার খোরাক।
সূত্র: বিবিসি, ওয়েব্যাক মেশিন, কনকর্ড ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরি, ভ্যানিটি ফেয়ার

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিনের কথা মনে হলে কিছু জনপ্রিয় গানের কথা সামনে আসে। জানেন কি, হিমেল হাওয়ার পরশ আর আলোকসজ্জার রোশনাইয়ের মধ্যে যে সুরগুলো আমাদের কানে বাজে, সেগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে একদল নারী। তাঁদের লেখা, কণ্ঠ আর সুরের জাদুকরী মিশেলে বড়দিন পেয়েছে এক অনন্য রূপ।
কুইন অব ক্রিসমাস মারায়া
বড়দিনের গানের কথা উঠলে যে নামটি সবার আগে স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে, তিনি হলেন মারায়া কেরি। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় বড়দিনের অলিখিত অ্যানথাম, ‘অল আই ওয়ান্ট ফর ক্রিসমাস ইজ ইউ...’ গানটি। এটি যৌথভাবে লিখেছিলেন মারায়া কেরি ও ওয়াল্টার এন আফানাসিফ। এর কণ্ঠশিল্পী ছিলেন মারায়া। এই গানের প্রতিটি ছত্রে মিশে রয়েছে এক চিরন্তন আর্তি। তাঁর গানের কথায় ফুটে ওঠে সেই সত্য, ‘বড়দিনে খুব বেশি কিছু চাওয়ার নেই আমার,/ শুধু একটি জিনিসেরই বড় প্রয়োজন... বড়দিনে শুধু তোমাকেই চাই আমি!’ এর অর্থ, উৎসবের জাঁকজমক বা দামি উপহারের চেয়ে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যই আসল।

মারায়া কেরি ও ওয়াল্টার এ গানটি লিখতে ও সুর করতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র ১৫ মিনিট। গান লেখা ও কণ্ঠ দেওয়াই নয়, মারায়া ছিলেন এই গানের সুরকার। প্রতিবছরের ডিসেম্বরে বিলবোর্ড চার্টের শীর্ষে ফিরে আসা এই এক গান থেকে তিনি কোটি কোটি টাকা রয়্যালটি পান, যা তাঁকে এনে দিয়েছে কুইন অব ক্রিসমাস বা বড়দিনের রানি উপাধি।
ড্রামের শব্দে ধ্রুপদি সুর

এক দরিদ্র শিশু, যার কাছে যিশুর জন্মের আনন্দ উৎসবে দেওয়ার মতো কোনো দামি উপহার ছিল না। তাই সে তার ছোট্ট ড্রামটি বাজিয়ে সম্মান জানাতে চেয়েছিল। এমনই একটি ঘটনাকে সুরে-তালে মিলিয়েছিলেন আমেরিকান সংগীত শিক্ষক ক্যাথরিন কেনিকট ডেভিস। ১৯৪১ সালের অনন্য সৃষ্টি ‘দ্য লিটিল ড্রামার বয়’ গানটি। প্রথমে এর নাম ছিল ‘দ্য ক্যারল অব দ্য ড্রাম’। গানটি একটি চেক গানের অনুকরণে তৈরি বলে ধারণা করা হয়। তবে এর সুর এবং কথা দুটোরই মূল কারিগর ছিলেন ক্যাথরিন। গানের সেই বিখ্যাত ‘পা-রাম-পাম-পাম-পাম’ সুরটি মূলত ক্যাথরিনেরই করা। আজও বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে বড়দিনের ক্যারল হিসেবে এ সুরটি মানুষের হৃদয়ে অনুরণিত হয়।
চঞ্চলতা ও শাশ্বত আবেদন
বড়দিনের উৎসবে কেবল ভক্তি বা আবেগ নয়, মিশে থাকে কিছুটা চঞ্চলতা আর কৌতুকও। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘স্যান্টা বেবি’ গানটি তারই প্রমাণ। এর নেপথ্যে ছিলেন প্রতিভাবান গীতিকার জোয়ান জাভিটস। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মার্কিন সিনেটর জ্যাকব জাভিটসের ভাইয়ের মেয়ে। সে সময়ে দাঁড়িয়ে এক নারীর এমন চটুল ও আধুনিক কথার গান লেখা ছিল বেশ সাহসী পদক্ষেপ। ফিল স্প্রিংগার ও টনি স্প্রিংগারের সঙ্গে মিলে জোয়ান এ গানটি লিখেছিলেন। গানটি আর্থ কিটের কণ্ঠে অমর হয়ে আছে। দশকের পর দশক পার হলেও গানটির আবেদন একটুও কমেনি। ম্যাডোনা থেকে শুরু করে কাইলি মিনোগ, টেইলর সুইফট এবং আরিয়ানা গ্রান্দের মতো বর্তমান সময়ের পপতারকারাও এ গানটি নতুন করে গেয়েছেন।
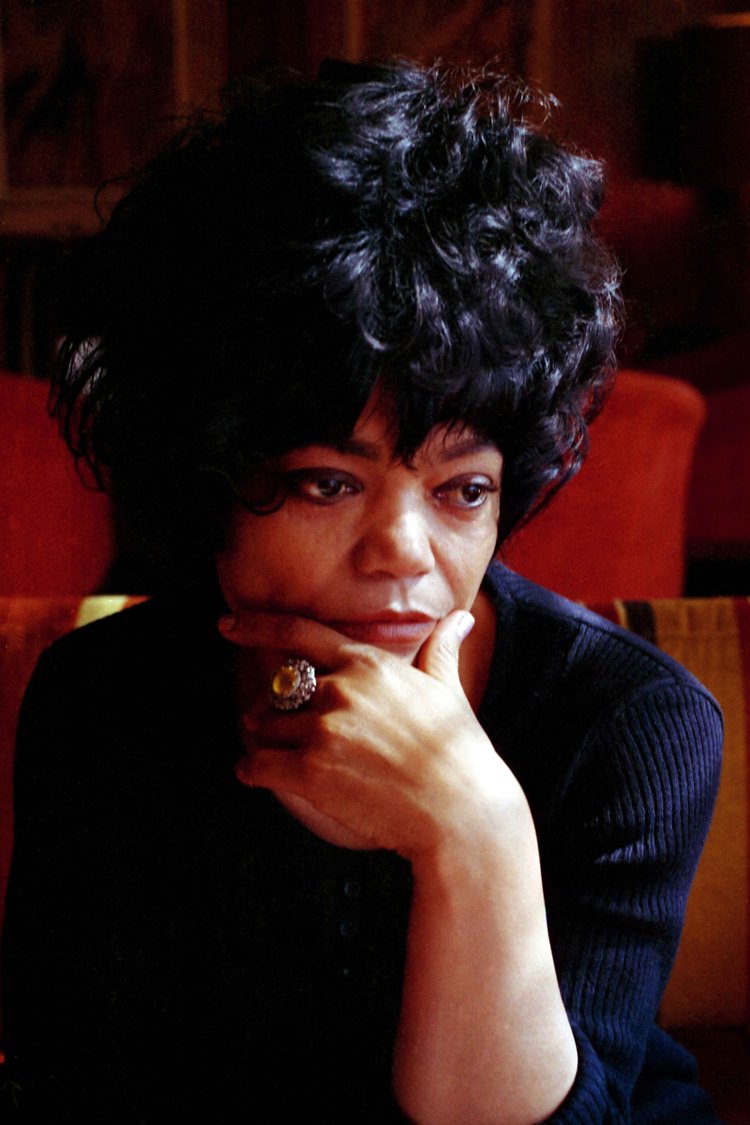
কিংবদন্তির সুর ও আধুনিকতার ছোঁয়া
কান্ট্রি মিউজিকের কিংবদন্তি ডলি পার্টন বড়দিনের উৎসবকে রাঙিয়েছেন নিজের মেধা দিয়ে। তিনি বড়দিন উপলক্ষে একাধিক সফল অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশ গানই ছিল তাঁর নিজের লেখা। তাঁর অমর সৃষ্টি ‘হার্ড ক্যান্ডি ক্রিসমাস’ ও ‘ক্রিসমাস অব মেনি কালার্স’ গানগুলো আজও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।
সিয়ার কণ্ঠে বড়দিনের আনন্দের স্রোত

সময়ের স্রোতে বড়দিনের গানে যোগ হয়েছে আধুনিকতার নতুন মাত্রা। তরুণ প্রজন্মের কাছে বড়দিন মানেই যেন অস্ট্রেলিয়ান সংগীতশিল্পী ও গীতিকার সিয়া। ২০১৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘এভরিডে ইজ ক্রিসমাস’ অ্যালবামটি। সিয়া প্রমাণ করেছেন, বড়দিনের গানের জন্য কেবল পুরোনো ক্ল্যাসিকের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। তাঁর নিজের লেখা ‘স্নো ম্যান’ ও ‘স্যান্টা ইজ কামিং ফর আস’ গানগুলো এখনকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়।
বড়দিনের সুরের মূর্ছনা কেবল সুর নয়; বরং এক অদৃশ্য মিলনমেলা। পর্দার আড়ালে থাকা এই নারী কারিগরদের লেখনী আর সুরের মায়ায় বড়দিন হয়ে ওঠে আরও মধুময়, আরও প্রাণবন্ত। প্রিয়জন আর আত্মীয়স্বজনের সে মিলনমেলায় এ গানগুলোই হয়ে থাকে আত্মার খোরাক।
সূত্র: বিবিসি, ওয়েব্যাক মেশিন, কনকর্ড ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরি, ভ্যানিটি ফেয়ার

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে...
২১ মে ২০২৫
ঢাকা শহরে শুধু নয়, পুরো দেশে নারীরা ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরব অবদান রেখে চলেছেন। আমরা সেই সব নারীকে ‘উদ্যোক্তা’ হিসেবে দেখছি। এই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বছরজুড়ে অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন ধরনের মেলা, সেটাও শুধু ঢাকায় নয়; বরং পুরো দেশে। সেই মেলাগুলো শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়...
১ দিন আগে
ব্যর্থতা কখনো কখনো সাফল্যের মোড়কে ফিরে আসে। রোজাইয়া রাব্বি রোজের গল্পটা তেমনই। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা শেষ করে ২০১৭ সালে ভর্তি হন গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। তবে বাবার অসুস্থতার কারণে বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে বসতে হয় বিয়ের...
১ দিন আগে
পোখারা শহরের এক বাড়ির ছাদ। রাতের নিস্তব্ধতায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক কিশোরী। সঙ্গে আছেন তার মা, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক। কিশোরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওই দুটো নক্ষত্র কি এখনই ধাক্কা খাবে?’ মা হেসে বুঝিয়ে দেন, ওরা একে অপরের থেকে কত দূরে কিংবা ওই যে ছুটন্ত বিন্দুটি দেখছ, ওটা আসলে নক্ষত্র...
২ দিন আগেকাশফিয়া আলম ঝিলিক, ঢাকা

ঢাকা শহরে শুধু নয়, পুরো দেশে নারীরা ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরব অবদান রেখে চলেছেন। আমরা সেই সব নারীকে ‘উদ্যোক্তা’ হিসেবে দেখছি। এই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বছরজুড়ে অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন ধরনের মেলা, সেটাও শুধু ঢাকায় নয়; বরং পুরো দেশে। সেই মেলাগুলো শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়; বরং নেটওয়ার্কিং, নতুন আইডিয়া বিনিময় এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশাল খোলা বই। তবে চলতি বছর সেই মেলাগুলোর চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন; বিশেষ করে উদ্যোক্তা মেলার সংখ্যা কমে যাওয়া এবং এর প্রভাব নিয়ে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
মেলার গুরুত্ব ও বর্তমান সংকট
এসএমই ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, নতুন উদ্যোক্তাদের ৬০ শতাংশ নারী। ফাউন্ডেশনটি এ পর্যন্ত ৫০ হাজারের বেশি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আর্টেমিস লাইফস্টাইলের স্বত্বাধিকারী ফায়জা আহমেদ রাফা বলেন, ‘আমরা যারা অনলাইন বিজনেসের সঙ্গে জড়িত, তারা বছরে বেশ কিছু মেলায় অংশ নেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে সরাসরি ভোক্তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করা যায়।
এ ছাড়া উদ্যোক্তা মেলাগুলোতে পরিচিতি পাওয়ার সুযোগ থাকে। অনলাইন উদ্যোগ নিয়ে ভোক্তাদের অনেক সময় বিশ্বাস তৈরি করতে অসুবিধা হয়। মেলা করলে তাঁরা সরাসরি এসে পণ্য যাচাই করতে পারেন। এর ফলে অনেকে নিশ্চিন্তে অনলাইনে অর্ডার করেন।’ রাফা আরও জানান, সাধারণত ঈদ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা দুর্গাপূজার মতো উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়। তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ‘লাস্ট দু-এক বছরে তুলনামূলক মেলার আয়োজন কিছুটা কম।’
কেন কমছে মেলার সংখ্যা
নারী উদ্যোক্তা ফোরামের সভাপতি রাফিয়া আক্তার, যিনি ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে কাজ করছেন, তিনি এ বছর বড় কোনো মেলার আয়োজন করতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে তিনি দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। রাফিয়া আক্তার বলেন, ‘আসলে দেশের পরিস্থিতির কারণে এ বছর মেলা আয়োজন করা হয়নি। যে কারণে অর্থনৈতিক দিকেও প্রভাব পড়েছে। এ মুহূর্তে ইনভেস্ট করে মেলায় কেউ অংশ নেবেন কি না, সেসব দিক বিবেচনা করে বড় কোনো মেলার আয়োজন করা হয়নি এবার।’
রাফিয়া আক্তার আরও যোগ করেন, ‘গত বছরের আগেও দেখা গেছে, সব সময় ফোন আসত, এখানে মেলা সেখানে মেলা। সেটা কমে গেছে। এটা আমার কাছে কম এসেছে কি না জানি না। মনে হয়, মেলার আয়োজন তুলনামূলক কমে গেছে।’
তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন
মাইসারার স্বত্বাধিকারী এলমা খন্দকার এষা। তিনি বলেন, ‘গত কয়েক বছর আমি মেলা করিনি। তবে চলতি বছর বেশ কিছু মেলা করেছি। সেটা যদি হিসাব করি, তাহলে আমার চোখে মেলা কম মনে হয়নি।’
অর্থনীতিতে নারীর অবদান ও আগামীর প্রত্যাশা অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, দেশের ১ কোটি ১৮ লাখ এসএমইর মধ্যে মাত্র ৬ দশমিক ৪৭ শতাংশ নারী মালিকানাধীন হলেও উদ্যোক্তা হওয়ার হার দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে দেশের ৩ কোটি ৭ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) একটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দারিদ্র্যসীমায় নতুন করে কোনো নারী যুক্ত হননি, যেখানে ১ লাখ ৬০ হাজার পুরুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন।
সৌন্দর্যশিল্প, হস্তশিল্প, বুটিক ও ব্লক প্রিন্টের মতো খাতে নারীদের জয়জয়কার। এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে মেলার মতো প্ল্যাটফর্মগুলো অপরিহার্য। এতে ঢাকাসহ বড় শহরের ভোক্তাদের সঙ্গে সারা দেশের নারী উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়। এতে পণ্য ও ক্রয়বৈচিত্র্য বাড়ে, ভোক্তা এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা তৈরি
হয়। সর্বোপরি অর্থনৈতিক গতিশীলতা ঠিক থাকে। কিন্তু এ বছর দৃশ্যমানভাবে মেলার সংখ্যা কিছুটা কমে গেছে। তবু উদ্যোক্তারা অনেক আশাবাদী। এই আশাবাদ দেশের অর্থনীতির জন্যই।

ঢাকা শহরে শুধু নয়, পুরো দেশে নারীরা ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরব অবদান রেখে চলেছেন। আমরা সেই সব নারীকে ‘উদ্যোক্তা’ হিসেবে দেখছি। এই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বছরজুড়ে অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন ধরনের মেলা, সেটাও শুধু ঢাকায় নয়; বরং পুরো দেশে। সেই মেলাগুলো শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়; বরং নেটওয়ার্কিং, নতুন আইডিয়া বিনিময় এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের বিশাল খোলা বই। তবে চলতি বছর সেই মেলাগুলোর চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন; বিশেষ করে উদ্যোক্তা মেলার সংখ্যা কমে যাওয়া এবং এর প্রভাব নিয়ে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
মেলার গুরুত্ব ও বর্তমান সংকট
এসএমই ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, নতুন উদ্যোক্তাদের ৬০ শতাংশ নারী। ফাউন্ডেশনটি এ পর্যন্ত ৫০ হাজারের বেশি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আর্টেমিস লাইফস্টাইলের স্বত্বাধিকারী ফায়জা আহমেদ রাফা বলেন, ‘আমরা যারা অনলাইন বিজনেসের সঙ্গে জড়িত, তারা বছরে বেশ কিছু মেলায় অংশ নেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে সরাসরি ভোক্তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করা যায়।
এ ছাড়া উদ্যোক্তা মেলাগুলোতে পরিচিতি পাওয়ার সুযোগ থাকে। অনলাইন উদ্যোগ নিয়ে ভোক্তাদের অনেক সময় বিশ্বাস তৈরি করতে অসুবিধা হয়। মেলা করলে তাঁরা সরাসরি এসে পণ্য যাচাই করতে পারেন। এর ফলে অনেকে নিশ্চিন্তে অনলাইনে অর্ডার করেন।’ রাফা আরও জানান, সাধারণত ঈদ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা দুর্গাপূজার মতো উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়। তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ‘লাস্ট দু-এক বছরে তুলনামূলক মেলার আয়োজন কিছুটা কম।’
কেন কমছে মেলার সংখ্যা
নারী উদ্যোক্তা ফোরামের সভাপতি রাফিয়া আক্তার, যিনি ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে কাজ করছেন, তিনি এ বছর বড় কোনো মেলার আয়োজন করতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে তিনি দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। রাফিয়া আক্তার বলেন, ‘আসলে দেশের পরিস্থিতির কারণে এ বছর মেলা আয়োজন করা হয়নি। যে কারণে অর্থনৈতিক দিকেও প্রভাব পড়েছে। এ মুহূর্তে ইনভেস্ট করে মেলায় কেউ অংশ নেবেন কি না, সেসব দিক বিবেচনা করে বড় কোনো মেলার আয়োজন করা হয়নি এবার।’
রাফিয়া আক্তার আরও যোগ করেন, ‘গত বছরের আগেও দেখা গেছে, সব সময় ফোন আসত, এখানে মেলা সেখানে মেলা। সেটা কমে গেছে। এটা আমার কাছে কম এসেছে কি না জানি না। মনে হয়, মেলার আয়োজন তুলনামূলক কমে গেছে।’
তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন
মাইসারার স্বত্বাধিকারী এলমা খন্দকার এষা। তিনি বলেন, ‘গত কয়েক বছর আমি মেলা করিনি। তবে চলতি বছর বেশ কিছু মেলা করেছি। সেটা যদি হিসাব করি, তাহলে আমার চোখে মেলা কম মনে হয়নি।’
অর্থনীতিতে নারীর অবদান ও আগামীর প্রত্যাশা অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুযায়ী, দেশের ১ কোটি ১৮ লাখ এসএমইর মধ্যে মাত্র ৬ দশমিক ৪৭ শতাংশ নারী মালিকানাধীন হলেও উদ্যোক্তা হওয়ার হার দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে দেশের ৩ কোটি ৭ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) একটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দারিদ্র্যসীমায় নতুন করে কোনো নারী যুক্ত হননি, যেখানে ১ লাখ ৬০ হাজার পুরুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছেন।
সৌন্দর্যশিল্প, হস্তশিল্প, বুটিক ও ব্লক প্রিন্টের মতো খাতে নারীদের জয়জয়কার। এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে মেলার মতো প্ল্যাটফর্মগুলো অপরিহার্য। এতে ঢাকাসহ বড় শহরের ভোক্তাদের সঙ্গে সারা দেশের নারী উদ্যোক্তাদের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হয়। এতে পণ্য ও ক্রয়বৈচিত্র্য বাড়ে, ভোক্তা এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা তৈরি
হয়। সর্বোপরি অর্থনৈতিক গতিশীলতা ঠিক থাকে। কিন্তু এ বছর দৃশ্যমানভাবে মেলার সংখ্যা কিছুটা কমে গেছে। তবু উদ্যোক্তারা অনেক আশাবাদী। এই আশাবাদ দেশের অর্থনীতির জন্যই।

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে...
২১ মে ২০২৫
খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিনের কথা মনে হলে কিছু জনপ্রিয় গানের কথা সামনে আসে। জানেন কি, হিমেল হাওয়ার পরশ আর আলোকসজ্জার রোশনাইয়ের মধ্যে যে সুরগুলো আমাদের কানে বাজে, সেগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে একদল নারী। তাঁদের লেখা, কণ্ঠ আর সুরের জাদুকরী মিশেলে বড়দিন পেয়েছে এক অনন্য রূপ।...
২ ঘণ্টা আগে
ব্যর্থতা কখনো কখনো সাফল্যের মোড়কে ফিরে আসে। রোজাইয়া রাব্বি রোজের গল্পটা তেমনই। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা শেষ করে ২০১৭ সালে ভর্তি হন গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। তবে বাবার অসুস্থতার কারণে বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে বসতে হয় বিয়ের...
১ দিন আগে
পোখারা শহরের এক বাড়ির ছাদ। রাতের নিস্তব্ধতায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক কিশোরী। সঙ্গে আছেন তার মা, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক। কিশোরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওই দুটো নক্ষত্র কি এখনই ধাক্কা খাবে?’ মা হেসে বুঝিয়ে দেন, ওরা একে অপরের থেকে কত দূরে কিংবা ওই যে ছুটন্ত বিন্দুটি দেখছ, ওটা আসলে নক্ষত্র...
২ দিন আগেআল আমিন

ব্যর্থতা কখনো কখনো সাফল্যের মোড়কে ফিরে আসে। রোজাইয়া রাব্বি রোজের গল্পটা তেমনই। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা শেষ করে ২০১৭ সালে ভর্তি হন গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। তবে বাবার অসুস্থতার কারণে বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি আজ অন্য নারীদের কাছে হয়ে উঠেছেন আদর্শ।
২০১৯ সালে একটি সেলাই মেশিন দিয়ে শুরু করেন নিজের ভুবনে যাত্রা। কিছু গজ কাপড় কিনে পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেন প্রথমে। সেলাই মেশিনের আওয়াজের চেয়ে তখন বেশি শোনা যেত মানুষের কটূক্তির আওয়াজ। তাই ছোটবেলার রান্না করার শখ থেকে ছোট্ট পরিসরে শুরু করলেন ক্যাটারিং সার্ভিস। সেখানেও ডেলিভারি, প্রমোশনসহ নানা সমস্যার মুখে পড়লেন তিনি। তবে দমে গেলেন না। কয়েকজন নারীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করলেন উদ্যোক্তা উন্নয়ন আবাসন নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ। তাঁর নিজের তৈরি পণ্যের পাশাপাশি শহরের নারীদের উৎপাদিত পণ্য সেই ফেসবুক গ্রুপে বিক্রি করতে শুরু করেন তিনি। এরপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহের কাজ শুরু করেন রোজ।
খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রে অল্প দিনেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন পঞ্চগড় শহরের চাউলহাটির নিউমার্কেট এলাকায় তাঁর ‘প্রত্যাশা’ ব্র্যান্ডের নিজস্ব একটি আউটলেট আছে। সেখানে বুটিকস ও হ্যান্ডপেইন্টের বিভিন্ন পণ্য তিনি পাইকারি বিক্রি করেন। এখন তাঁর অধীনে নিয়মিত কাজ করছেন ১০ জন নারী।
উদ্যোক্তা জীবনের শুরুতে নানা প্রতিবন্ধকতা পার করে তিনি জেলা পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে সফলতা অর্জনকারী নারী হিসেবে পেয়েছেন এ বছরের শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী পুরস্কার। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে তাঁকে অদম্য নারী পুরস্কারে ভূষিত করেন পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান।
রোজাইয়া রাব্বি রোজের স্বপ্ন, তাঁর পণ্য যেন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নে তিনি কাজ করে যেতে চান অন্য নারীদের সঙ্গে নিয়ে।

ব্যর্থতা কখনো কখনো সাফল্যের মোড়কে ফিরে আসে। রোজাইয়া রাব্বি রোজের গল্পটা তেমনই। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা শেষ করে ২০১৭ সালে ভর্তি হন গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। তবে বাবার অসুস্থতার কারণে বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে বসতে হয় বিয়ের পিঁড়িতে। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি আজ অন্য নারীদের কাছে হয়ে উঠেছেন আদর্শ।
২০১৯ সালে একটি সেলাই মেশিন দিয়ে শুরু করেন নিজের ভুবনে যাত্রা। কিছু গজ কাপড় কিনে পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেন প্রথমে। সেলাই মেশিনের আওয়াজের চেয়ে তখন বেশি শোনা যেত মানুষের কটূক্তির আওয়াজ। তাই ছোটবেলার রান্না করার শখ থেকে ছোট্ট পরিসরে শুরু করলেন ক্যাটারিং সার্ভিস। সেখানেও ডেলিভারি, প্রমোশনসহ নানা সমস্যার মুখে পড়লেন তিনি। তবে দমে গেলেন না। কয়েকজন নারীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করলেন উদ্যোক্তা উন্নয়ন আবাসন নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ। তাঁর নিজের তৈরি পণ্যের পাশাপাশি শহরের নারীদের উৎপাদিত পণ্য সেই ফেসবুক গ্রুপে বিক্রি করতে শুরু করেন তিনি। এরপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহের কাজ শুরু করেন রোজ।
খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রে অল্প দিনেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন পঞ্চগড় শহরের চাউলহাটির নিউমার্কেট এলাকায় তাঁর ‘প্রত্যাশা’ ব্র্যান্ডের নিজস্ব একটি আউটলেট আছে। সেখানে বুটিকস ও হ্যান্ডপেইন্টের বিভিন্ন পণ্য তিনি পাইকারি বিক্রি করেন। এখন তাঁর অধীনে নিয়মিত কাজ করছেন ১০ জন নারী।
উদ্যোক্তা জীবনের শুরুতে নানা প্রতিবন্ধকতা পার করে তিনি জেলা পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে সফলতা অর্জনকারী নারী হিসেবে পেয়েছেন এ বছরের শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী পুরস্কার। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে তাঁকে অদম্য নারী পুরস্কারে ভূষিত করেন পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান।
রোজাইয়া রাব্বি রোজের স্বপ্ন, তাঁর পণ্য যেন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নে তিনি কাজ করে যেতে চান অন্য নারীদের সঙ্গে নিয়ে।

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে...
২১ মে ২০২৫
খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিনের কথা মনে হলে কিছু জনপ্রিয় গানের কথা সামনে আসে। জানেন কি, হিমেল হাওয়ার পরশ আর আলোকসজ্জার রোশনাইয়ের মধ্যে যে সুরগুলো আমাদের কানে বাজে, সেগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে একদল নারী। তাঁদের লেখা, কণ্ঠ আর সুরের জাদুকরী মিশেলে বড়দিন পেয়েছে এক অনন্য রূপ।...
২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরে শুধু নয়, পুরো দেশে নারীরা ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরব অবদান রেখে চলেছেন। আমরা সেই সব নারীকে ‘উদ্যোক্তা’ হিসেবে দেখছি। এই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বছরজুড়ে অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন ধরনের মেলা, সেটাও শুধু ঢাকায় নয়; বরং পুরো দেশে। সেই মেলাগুলো শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়...
১ দিন আগে
পোখারা শহরের এক বাড়ির ছাদ। রাতের নিস্তব্ধতায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক কিশোরী। সঙ্গে আছেন তার মা, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক। কিশোরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওই দুটো নক্ষত্র কি এখনই ধাক্কা খাবে?’ মা হেসে বুঝিয়ে দেন, ওরা একে অপরের থেকে কত দূরে কিংবা ওই যে ছুটন্ত বিন্দুটি দেখছ, ওটা আসলে নক্ষত্র...
২ দিন আগেফিচার ডেস্ক

পোখারা শহরের এক বাড়ির ছাদ। রাতের নিস্তব্ধতায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক কিশোরী। সঙ্গে আছেন তার মা, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক। কিশোরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওই দুটো নক্ষত্র কি এখনই ধাক্কা খাবে?’ মা হেসে বুঝিয়ে দেন, ওরা একে অপরের থেকে কত দূরে কিংবা ওই যে ছুটন্ত বিন্দুটি দেখছ, ওটা আসলে নক্ষত্র নয়—একটি স্যাটেলাইট। সেই কৌতূহলী কিশোরীটি আজকের মনীষা শ্রেষ্ঠা—নেপালের সফল জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিঃপদার্থবিদ এবং দেশটির প্রথম নারী অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফার। তিনি এখন হাই-এনার্জি অ্যাস্ট্রোফিজিকস বিষয়ে পিএইচডি করছেন।
চ্যালেঞ্জের সঙ্গে শুরু যে লড়াই
মনীষার বিজ্ঞানের পথে আসাটা ছিল অনেকটা জেদের বশে। তিনি যে কলেজে পড়তেন, সেখানে পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে ছিল ১২০ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয়জন মেয়ে। অথচ জীববিজ্ঞানের চিত্রটা ছিল ঠিক উল্টো। বন্ধুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর পান, মেয়েদের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে জীববিজ্ঞান অনেক সহজ। মনীষা বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানই পড়তে হবে।
ক্লাসে ঢোকার পর শুরু হলো অন্য এক লড়াই। পুরুষশাসিত সেই পরিবেশে অনেক সময় মেয়েদের বসার জন্য কোনো আসনই দেওয়া হতো না; তাদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হতো। এমনকি ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময়ও তরুণেরা কাজ করত, আর মেয়েদের দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখার অনুমতি ছিল। মাস্টার্স পর্যায়ে এসে এই সংকট আরও বাড়ে। পড়াশোনার পদ্ধতি ছিল শুধু নোট নেওয়া আর মুখস্থ করা। একপর্যায়ে হতাশ হয়ে মনীষা ডিগ্রি শেষ না করেই পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
নেপাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির যাত্রা
২০১৩ সালে মনীষা নেপাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে (এনএএসও) প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে যোগ দেন। তখন সংগঠনটির কোনো অফিস ছিল না, ছিল খুব সীমিত সুবিধা। মনীষা ও তাঁর দল মিলে বছরের পর বছর পরিশ্রম করে সেটিকে আন্তর্জাতিক উচ্চতায় নিয়ে যান।
সম্প্রতি এই সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের সদস্যপদ পেয়েছে, যা নেপালের ১০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম।
আজ এনএএসও শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার—তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল চিন্তার উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। মনীষার দল সারা দেশে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং শিক্ষার্থীদের হাতে টেলিস্কোপ ও বই তুলে দিচ্ছে। যাতে তারাও বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পারে।
অলিম্পিয়াড ও বৈশ্বিক সাফল্য
মনীষা শ্রেষ্ঠা নেপালের ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নেপালি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করেন। তাঁর হাত ধরে অনেক শিক্ষার্থী ফ্রান্স, আমেরিকা ও সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক মঞ্চে লড়াই করেছেন। এমনকি এই অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া তিন শিক্ষার্থী বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। ২০২০ সালে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে স্টারস শাইন ফর এভরিওয়ান সংস্থা তাঁকে বিশেষ সম্মাননা দেয়।
ডার্ক স্কাই বা অন্ধকার আকাশ রক্ষা
মনীষা শুধু বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন দক্ষ আলোকচিত্রীও। নেপালের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় তাঁর তোলা মহাকাশের ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমান সময়ের বড় একটি সমস্যা আলোকদূষণ নিয়ে কাজ করছেন।
২০১৬ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮০ শতাংশ মানুষ শহর ও অবকাঠামোর কৃত্রিম আলোর কারণে রাতের আকাশের আসল সৌন্দর্য দেখতে পায় না। মনীষা তাদের সতর্ক করে জানান, আগামী ২০ বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। তাই নেপালে ‘অ্যাস্ট্রো-ট্যুরিজম’ কিংবা জ্যোতি-পর্যটন বিকাশের মাধ্যমে আকাশ রক্ষার স্বপ্ন দেখেন মনীষা শ্রেষ্ঠা।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন
মনীষার স্বপ্ন নেপালে একটি নিজস্ব মানমন্দির তৈরি করা, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তিনি মনে করেন, নেপালের কাছে দামি যন্ত্রপাতি না থাকলেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় ল্যাবরেটরি আছে। সেটা হলো, মাথার ওপরের অন্ধকার আকাশ। তিনি বিশ্বাস করেন, আকাশ আমাদের সবাইকে এক সুতোয় বাঁধে। তিনি চান তাঁর জীবনের গল্প শুনে অন্য মেয়েরাও যেন বিজ্ঞানের কঠিন পথে পা বাড়াতে পিছপা না হয়।
সূত্র: এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক, দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট

পোখারা শহরের এক বাড়ির ছাদ। রাতের নিস্তব্ধতায় আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে এক কিশোরী। সঙ্গে আছেন তার মা, যিনি পেশায় একজন শিক্ষক। কিশোরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, ওই দুটো নক্ষত্র কি এখনই ধাক্কা খাবে?’ মা হেসে বুঝিয়ে দেন, ওরা একে অপরের থেকে কত দূরে কিংবা ওই যে ছুটন্ত বিন্দুটি দেখছ, ওটা আসলে নক্ষত্র নয়—একটি স্যাটেলাইট। সেই কৌতূহলী কিশোরীটি আজকের মনীষা শ্রেষ্ঠা—নেপালের সফল জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিঃপদার্থবিদ এবং দেশটির প্রথম নারী অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফার। তিনি এখন হাই-এনার্জি অ্যাস্ট্রোফিজিকস বিষয়ে পিএইচডি করছেন।
চ্যালেঞ্জের সঙ্গে শুরু যে লড়াই
মনীষার বিজ্ঞানের পথে আসাটা ছিল অনেকটা জেদের বশে। তিনি যে কলেজে পড়তেন, সেখানে পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে ছিল ১২০ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয়জন মেয়ে। অথচ জীববিজ্ঞানের চিত্রটা ছিল ঠিক উল্টো। বন্ধুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর পান, মেয়েদের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে জীববিজ্ঞান অনেক সহজ। মনীষা বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানই পড়তে হবে।
ক্লাসে ঢোকার পর শুরু হলো অন্য এক লড়াই। পুরুষশাসিত সেই পরিবেশে অনেক সময় মেয়েদের বসার জন্য কোনো আসনই দেওয়া হতো না; তাদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হতো। এমনকি ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময়ও তরুণেরা কাজ করত, আর মেয়েদের দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখার অনুমতি ছিল। মাস্টার্স পর্যায়ে এসে এই সংকট আরও বাড়ে। পড়াশোনার পদ্ধতি ছিল শুধু নোট নেওয়া আর মুখস্থ করা। একপর্যায়ে হতাশ হয়ে মনীষা ডিগ্রি শেষ না করেই পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
নেপাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির যাত্রা
২০১৩ সালে মনীষা নেপাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে (এনএএসও) প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে যোগ দেন। তখন সংগঠনটির কোনো অফিস ছিল না, ছিল খুব সীমিত সুবিধা। মনীষা ও তাঁর দল মিলে বছরের পর বছর পরিশ্রম করে সেটিকে আন্তর্জাতিক উচ্চতায় নিয়ে যান।
সম্প্রতি এই সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের সদস্যপদ পেয়েছে, যা নেপালের ১০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম।
আজ এনএএসও শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার—তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল চিন্তার উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। মনীষার দল সারা দেশে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং শিক্ষার্থীদের হাতে টেলিস্কোপ ও বই তুলে দিচ্ছে। যাতে তারাও বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পারে।
অলিম্পিয়াড ও বৈশ্বিক সাফল্য
মনীষা শ্রেষ্ঠা নেপালের ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নেপালি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করেন। তাঁর হাত ধরে অনেক শিক্ষার্থী ফ্রান্স, আমেরিকা ও সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিক মঞ্চে লড়াই করেছেন। এমনকি এই অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া তিন শিক্ষার্থী বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। ২০২০ সালে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে স্টারস শাইন ফর এভরিওয়ান সংস্থা তাঁকে বিশেষ সম্মাননা দেয়।
ডার্ক স্কাই বা অন্ধকার আকাশ রক্ষা
মনীষা শুধু বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন দক্ষ আলোকচিত্রীও। নেপালের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় তাঁর তোলা মহাকাশের ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমান সময়ের বড় একটি সমস্যা আলোকদূষণ নিয়ে কাজ করছেন।
২০১৬ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৮০ শতাংশ মানুষ শহর ও অবকাঠামোর কৃত্রিম আলোর কারণে রাতের আকাশের আসল সৌন্দর্য দেখতে পায় না। মনীষা তাদের সতর্ক করে জানান, আগামী ২০ বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। তাই নেপালে ‘অ্যাস্ট্রো-ট্যুরিজম’ কিংবা জ্যোতি-পর্যটন বিকাশের মাধ্যমে আকাশ রক্ষার স্বপ্ন দেখেন মনীষা শ্রেষ্ঠা।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন
মনীষার স্বপ্ন নেপালে একটি নিজস্ব মানমন্দির তৈরি করা, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তিনি মনে করেন, নেপালের কাছে দামি যন্ত্রপাতি না থাকলেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় ল্যাবরেটরি আছে। সেটা হলো, মাথার ওপরের অন্ধকার আকাশ। তিনি বিশ্বাস করেন, আকাশ আমাদের সবাইকে এক সুতোয় বাঁধে। তিনি চান তাঁর জীবনের গল্প শুনে অন্য মেয়েরাও যেন বিজ্ঞানের কঠিন পথে পা বাড়াতে পিছপা না হয়।
সূত্র: এশিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক, দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট

এত আন্দোলন, এত প্রতিবাদ, এত আইন! তবু নারীর অধিকার রাজপথ কিংবা কোর্টের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই হাল? প্রতিবাদগুলো কেন ধামাচাপা পড়ে থাকছে? কেন বারবার অধিকারের কথা বলতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে? নারীর প্রতি সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কেমন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে...
২১ মে ২০২৫
খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বড়দিনের কথা মনে হলে কিছু জনপ্রিয় গানের কথা সামনে আসে। জানেন কি, হিমেল হাওয়ার পরশ আর আলোকসজ্জার রোশনাইয়ের মধ্যে যে সুরগুলো আমাদের কানে বাজে, সেগুলো সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে একদল নারী। তাঁদের লেখা, কণ্ঠ আর সুরের জাদুকরী মিশেলে বড়দিন পেয়েছে এক অনন্য রূপ।...
২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা শহরে শুধু নয়, পুরো দেশে নারীরা ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরব অবদান রেখে চলেছেন। আমরা সেই সব নারীকে ‘উদ্যোক্তা’ হিসেবে দেখছি। এই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বছরজুড়ে অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন ধরনের মেলা, সেটাও শুধু ঢাকায় নয়; বরং পুরো দেশে। সেই মেলাগুলো শুধু পণ্য বিক্রির জায়গা নয়...
১ দিন আগে
ব্যর্থতা কখনো কখনো সাফল্যের মোড়কে ফিরে আসে। রোজাইয়া রাব্বি রোজের গল্পটা তেমনই। কম্পিউটার সায়েন্সে ডিপ্লোমা শেষ করে ২০১৭ সালে ভর্তি হন গ্রিন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। তবে বাবার অসুস্থতার কারণে বেশি দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। লেখাপড়া ছেড়ে তাঁকে বসতে হয় বিয়ের...
১ দিন আগে