মো. আবুল কাশেম
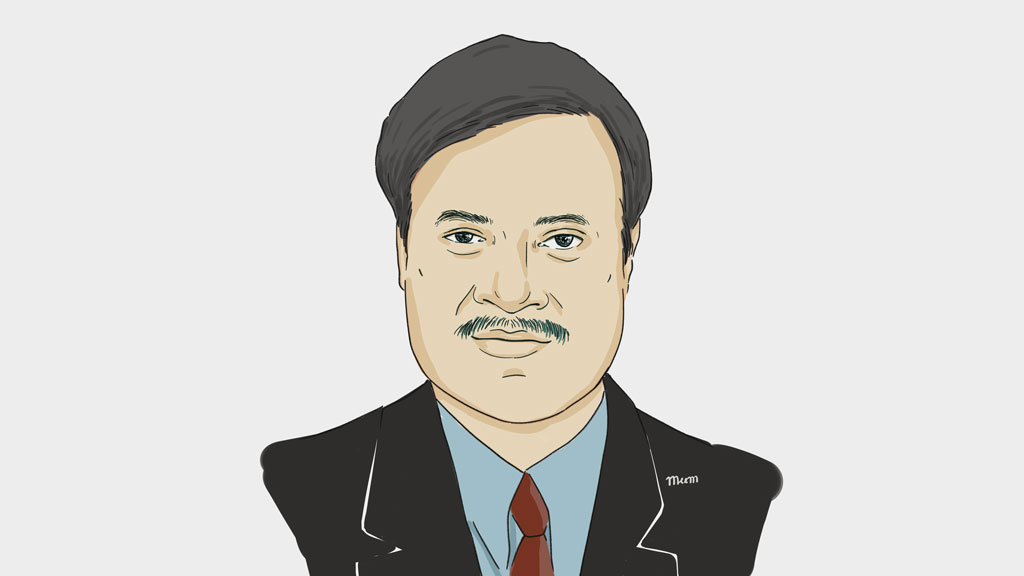
নগদ নিয়ে চারদিকে নানান কথা, আলোচনা-সমালোচনা শুনছি আর ভাবছি, পেছনের আসল কারণটা কী? পরিস্থিতি দেখে যেটা বুঝতে পারছি, তাতে অবাক না হয়ে পারছি না। সত্যিই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি।
সব দেখে-শুনে, মোদ্দাকথা, আমার কাছে যে অর্থ দাঁড়াচ্ছে তা হলো—টাকা লেনদেন, বিল পেমেন্ট এসব জায়গায় গ্রাহক যখন খানিকটা সুবিধা পেতে শুরু করলেন, তখন একটি পক্ষের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা–ছোটবেলায় এমন একটা প্রবাদ পড়েছিলাম। সেটা আজ খুব করে মনে পড়ছে। সন্দেহজনক লেনদেন দেখে ডাক বিভাগের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শরণাপন্ন হওয়ায় সাধুবাদ পাওয়ার কথা। অথচ বুঝে না বুঝে, অনেকেই তাদের সমালোচনা শুরু করেছেন। কেউ কেউ বিনা কারণেই যোগ দিচ্ছেন সেই মিছিলে। কেউবা আবার মধুর সন্ধানে ওই কাতারে তো আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন।
কেন এমনটি ঘটছে, সেটা একটু-আধটু তো বুঝতেই পারি। বিষয়টি বুঝতে একটু পেছনে যেতে হবে। মূল সমস্যাটা হয়েছে গত এক দশকে একটি পক্ষ মনোপলির যে দৌরাত্ম্য তৈরি করেছে, সেটিতে যখনই খানিকটা ধাক্কা খেয়েছে, অমনি তাদের নখদন্ত সব বেরিয়ে পড়েছে। একইভাবে একে একে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস চালু করা বেশির ভাগ উদ্যোগকেই আগে তাঁরা বাজারছাড়া করতে পেরেছেন। ফলে একসময়ের ৩০টি এমএফএস লাইসেন্স নেমে এসেছে অর্ধেকে। যার মধ্যে সত্যিকার অর্থে বলার মতো সেবা তো কেউ চালিয়ে রাখতে পারেনি। ফলে এ সেবায় প্রতিযোগিতা বলে যে একটা বিষয় থাকতে পারে, সেটা মানুষ ভুলতেই বসেছিল।
ব্যতিক্রম কেবল নগদ। সমস্যাটা এখানেই। এর আগে ভেতর থেকে দেখেছি, এখন তো বাইরে থেকে দেখছি। ভেতর থেকে দেখে আসার কারণে, বাইরে থেকেও সবকিছু যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।
চলুন, একটু অঙ্কের হিসাব থেকে ঘুরে আসি। নগদ থেকে টাকা পাঠাতে খরচ নেই। আবার এক হাজার টাকা ক্যাশ-আউটে খরচ ৯ টাকা ৯৯ পয়সা। ভ্যাটসহ সাড়ে ১১ টাকা। অথচ মনোপলির দাপট তৈরি করা এই গোষ্ঠী ১০ বছর আগে যে সাড়ে ১৮ টাকা ক্যাশ-আউট চার্জ করেছিল, সেটাই এখনো বহাল রেখেছে। সেখানে আবার টাকা পাঠাতেও খরচ ৫ টাকা। তাহলে এক হাজার টাকা লেনদেনেই পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেল ১২ টাকার বেশি। এ রকম কত কোটি কোটি ১২ টাকার হিসাব যে জমা হচ্ছে, তার হিসাব যাঁদের রাখার, যাঁদের দেখার, তারা তো ঘুমিয়ে গেছেন।
কে বলতে পারে, এই কোটি কোটি ১২ টাকার কতটা দেশে থাকছে আর কতটা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে? এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, শেষ বিচারে গ্রাহকই আসলে ঠিক করতে পারেন এই হাজার কোটি টাকা দেশে রাখবেন, নাকি বিদেশি কোম্পানিকে লুটে নিতে দেবেন?
মঙ্গলবার একটি দৈনিকে একটা রিপোর্ট দেখলাম, গত এক বছরে নগদ গ্রাহকেরা এক হাজার কোটি টাকার সুবিধা পেয়েছেন। দেশের ব্যাংকিং খাতের ক্ষুদ্র একজন সাবেক কর্মকর্তা হওয়ায় বাইরে থেকেও দেখতে ভালো লাগে, বাজারে অন্তত কিছুটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তা ছাড়া, নগদের প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে মনোপলি অপারেটরও যখন কিছুটা ছাড় দিতে শুরু করে, তখন ভালো লাগাটা আরও বাড়ে।
কিন্তু ভালো লাগাটা আবার উবেও যায় যখন চোখে পড়ে রেফারি নিজেই একটি পক্ষ নিয়ে নেন। ওই মঙ্গলবারই একটি কাগজে চোখে পড়ল ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বিষয়ে একটি হুঁশিয়ারি। আমার জানা মতে, এটি উদাহরণহীন একটি ঘটনা। পত্রিকা মারফত জেনেছি, নগদ এবং ডাক বিভাগের গাঁটছড়াকে কোম্পানি কাঠামোর আনুষ্ঠানিকতা দিতে এটি করা হচ্ছে। সেটি নিয়ে পানি ঘোলা হচ্ছে।
সবকিছুর মূলে আমার যেটা মনে হয়, তা হলো স্বার্থের আঘাত। একচেটিয়াত্বের কঠিন দেয়ালে জনগণের ভালোবাসার আঘাত সে কারণেই নগদ আজ আক্রান্ত। ওই একই কারণে দেশ-বিদেশ থেকে একসঙ্গে নগদের বিরুদ্ধে হুংকার আসছে।
অনেকেই কথা বলছেন নগদের বন্ড ছাড়া নিয়ে। রীতিমতো কড়া সমালোচনায় নেমেছেন। গাত্রদাহ তো বুঝি, প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে বড় হওয়ার শক্তি জোগাতে না পারে তার জন্য সব পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে।
নগদ একটা বন্ড ছাড়ার অনুমতি পাচ্ছে, যা পাবলিক বন্ড না। জনগণের কেনার জন্য নয়। টাকাটা আসবে বিদেশ থেকে। কেউ কি প্রশ্ন করবে না যে অনেকে যখন বিদেশে অর্থ পাচারে মত্ত, তখন নগদ বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আনছে–এর ভেদ করার কি কেউ নেই?
কেউ কি চিন্তায় আনবে না যে, একটি কোম্পানি বাংলাদেশে সব গ্রাস করার মচ্ছপে মেতেছে। একের পর এক কোম্পানি কিনে, নিজেদের মধ্যে যোগসাজশে প্রভাব বিস্তারে নেমেছে। এগুলো ভাবার সময় চলে গেলে কিন্তু পরে আর কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাবে না।
কেউ কি একবার জানতে চাইবেন, এমএফএসগুলোর মধ্যে যারা টানা কয়েক বছর লাভে ছিল, সেখান থেকে লোকসানে নেমে এল কীভাবে? সবার তো গ্রাহক বেড়েছে; তাদেরও বেড়েছে। লেনদেন বেড়েছে এবং আয়ও বেড়েছে–তারপরও লাভ থেকে লোকসানে? রেগুলেটর বা অডিটর কি নির্মোহভাবে তা দেখছে?
এসব প্রশ্ন করার লোক পাওয়া যায় না বলেই দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে যায়। ঠিক এ কারণেই আমাদের দেশে সরকারি কোনো সেবা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। নতুন কিছু করতে দেখলেই তাকে পিষে মারার আয়োজন চলে।
তারপরও আশাবাদী হই, আশাবাদী হই এই ভেবে যে, ভেতর থেকে কোনো শুভবুদ্ধির উদয় হবে হয়তো। নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টি বুঝতে পারবেন আশা করি। গ্রাহক-জনগণও বুঝতে পারবেন, তাঁরা কারও ক্রীড়নক হয়ে কাজ করবেন, নাকি দেশের পক্ষে দাঁড়াবেন?
লেখক: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর
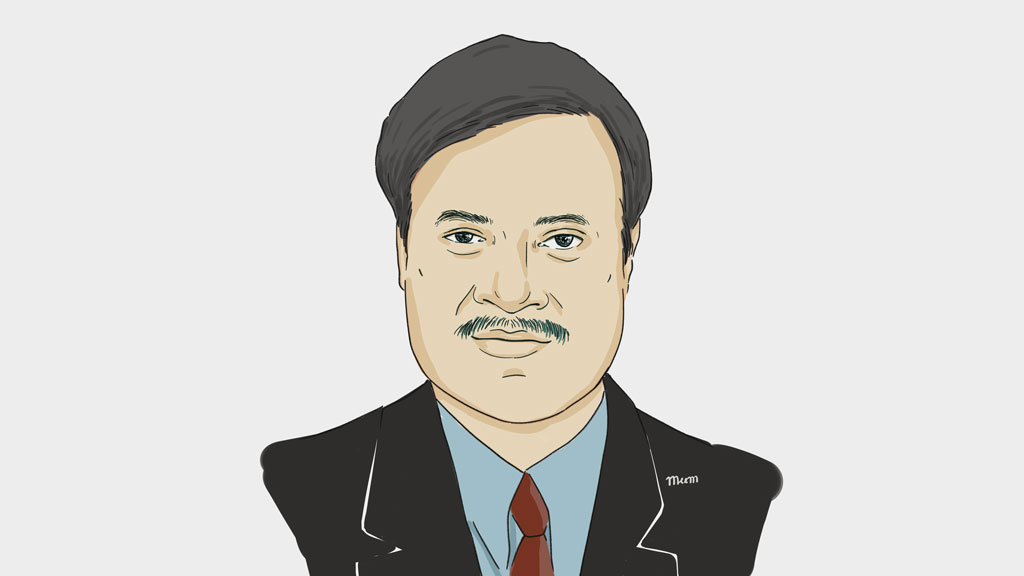
নগদ নিয়ে চারদিকে নানান কথা, আলোচনা-সমালোচনা শুনছি আর ভাবছি, পেছনের আসল কারণটা কী? পরিস্থিতি দেখে যেটা বুঝতে পারছি, তাতে অবাক না হয়ে পারছি না। সত্যিই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি।
সব দেখে-শুনে, মোদ্দাকথা, আমার কাছে যে অর্থ দাঁড়াচ্ছে তা হলো—টাকা লেনদেন, বিল পেমেন্ট এসব জায়গায় গ্রাহক যখন খানিকটা সুবিধা পেতে শুরু করলেন, তখন একটি পক্ষের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল।
ঝোপ বুঝে কোপ মারা–ছোটবেলায় এমন একটা প্রবাদ পড়েছিলাম। সেটা আজ খুব করে মনে পড়ছে। সন্দেহজনক লেনদেন দেখে ডাক বিভাগের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শরণাপন্ন হওয়ায় সাধুবাদ পাওয়ার কথা। অথচ বুঝে না বুঝে, অনেকেই তাদের সমালোচনা শুরু করেছেন। কেউ কেউ বিনা কারণেই যোগ দিচ্ছেন সেই মিছিলে। কেউবা আবার মধুর সন্ধানে ওই কাতারে তো আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন।
কেন এমনটি ঘটছে, সেটা একটু-আধটু তো বুঝতেই পারি। বিষয়টি বুঝতে একটু পেছনে যেতে হবে। মূল সমস্যাটা হয়েছে গত এক দশকে একটি পক্ষ মনোপলির যে দৌরাত্ম্য তৈরি করেছে, সেটিতে যখনই খানিকটা ধাক্কা খেয়েছে, অমনি তাদের নখদন্ত সব বেরিয়ে পড়েছে। একইভাবে একে একে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস চালু করা বেশির ভাগ উদ্যোগকেই আগে তাঁরা বাজারছাড়া করতে পেরেছেন। ফলে একসময়ের ৩০টি এমএফএস লাইসেন্স নেমে এসেছে অর্ধেকে। যার মধ্যে সত্যিকার অর্থে বলার মতো সেবা তো কেউ চালিয়ে রাখতে পারেনি। ফলে এ সেবায় প্রতিযোগিতা বলে যে একটা বিষয় থাকতে পারে, সেটা মানুষ ভুলতেই বসেছিল।
ব্যতিক্রম কেবল নগদ। সমস্যাটা এখানেই। এর আগে ভেতর থেকে দেখেছি, এখন তো বাইরে থেকে দেখছি। ভেতর থেকে দেখে আসার কারণে, বাইরে থেকেও সবকিছু যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।
চলুন, একটু অঙ্কের হিসাব থেকে ঘুরে আসি। নগদ থেকে টাকা পাঠাতে খরচ নেই। আবার এক হাজার টাকা ক্যাশ-আউটে খরচ ৯ টাকা ৯৯ পয়সা। ভ্যাটসহ সাড়ে ১১ টাকা। অথচ মনোপলির দাপট তৈরি করা এই গোষ্ঠী ১০ বছর আগে যে সাড়ে ১৮ টাকা ক্যাশ-আউট চার্জ করেছিল, সেটাই এখনো বহাল রেখেছে। সেখানে আবার টাকা পাঠাতেও খরচ ৫ টাকা। তাহলে এক হাজার টাকা লেনদেনেই পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেল ১২ টাকার বেশি। এ রকম কত কোটি কোটি ১২ টাকার হিসাব যে জমা হচ্ছে, তার হিসাব যাঁদের রাখার, যাঁদের দেখার, তারা তো ঘুমিয়ে গেছেন।
কে বলতে পারে, এই কোটি কোটি ১২ টাকার কতটা দেশে থাকছে আর কতটা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে? এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, শেষ বিচারে গ্রাহকই আসলে ঠিক করতে পারেন এই হাজার কোটি টাকা দেশে রাখবেন, নাকি বিদেশি কোম্পানিকে লুটে নিতে দেবেন?
মঙ্গলবার একটি দৈনিকে একটা রিপোর্ট দেখলাম, গত এক বছরে নগদ গ্রাহকেরা এক হাজার কোটি টাকার সুবিধা পেয়েছেন। দেশের ব্যাংকিং খাতের ক্ষুদ্র একজন সাবেক কর্মকর্তা হওয়ায় বাইরে থেকেও দেখতে ভালো লাগে, বাজারে অন্তত কিছুটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে। তা ছাড়া, নগদের প্রতিযোগিতার চাপে পড়ে মনোপলি অপারেটরও যখন কিছুটা ছাড় দিতে শুরু করে, তখন ভালো লাগাটা আরও বাড়ে।
কিন্তু ভালো লাগাটা আবার উবেও যায় যখন চোখে পড়ে রেফারি নিজেই একটি পক্ষ নিয়ে নেন। ওই মঙ্গলবারই একটি কাগজে চোখে পড়ল ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা বিষয়ে একটি হুঁশিয়ারি। আমার জানা মতে, এটি উদাহরণহীন একটি ঘটনা। পত্রিকা মারফত জেনেছি, নগদ এবং ডাক বিভাগের গাঁটছড়াকে কোম্পানি কাঠামোর আনুষ্ঠানিকতা দিতে এটি করা হচ্ছে। সেটি নিয়ে পানি ঘোলা হচ্ছে।
সবকিছুর মূলে আমার যেটা মনে হয়, তা হলো স্বার্থের আঘাত। একচেটিয়াত্বের কঠিন দেয়ালে জনগণের ভালোবাসার আঘাত সে কারণেই নগদ আজ আক্রান্ত। ওই একই কারণে দেশ-বিদেশ থেকে একসঙ্গে নগদের বিরুদ্ধে হুংকার আসছে।
অনেকেই কথা বলছেন নগদের বন্ড ছাড়া নিয়ে। রীতিমতো কড়া সমালোচনায় নেমেছেন। গাত্রদাহ তো বুঝি, প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে বড় হওয়ার শক্তি জোগাতে না পারে তার জন্য সব পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে।
নগদ একটা বন্ড ছাড়ার অনুমতি পাচ্ছে, যা পাবলিক বন্ড না। জনগণের কেনার জন্য নয়। টাকাটা আসবে বিদেশ থেকে। কেউ কি প্রশ্ন করবে না যে অনেকে যখন বিদেশে অর্থ পাচারে মত্ত, তখন নগদ বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আনছে–এর ভেদ করার কি কেউ নেই?
কেউ কি চিন্তায় আনবে না যে, একটি কোম্পানি বাংলাদেশে সব গ্রাস করার মচ্ছপে মেতেছে। একের পর এক কোম্পানি কিনে, নিজেদের মধ্যে যোগসাজশে প্রভাব বিস্তারে নেমেছে। এগুলো ভাবার সময় চলে গেলে কিন্তু পরে আর কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাবে না।
কেউ কি একবার জানতে চাইবেন, এমএফএসগুলোর মধ্যে যারা টানা কয়েক বছর লাভে ছিল, সেখান থেকে লোকসানে নেমে এল কীভাবে? সবার তো গ্রাহক বেড়েছে; তাদেরও বেড়েছে। লেনদেন বেড়েছে এবং আয়ও বেড়েছে–তারপরও লাভ থেকে লোকসানে? রেগুলেটর বা অডিটর কি নির্মোহভাবে তা দেখছে?
এসব প্রশ্ন করার লোক পাওয়া যায় না বলেই দেশ ও দেশের জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে যায়। ঠিক এ কারণেই আমাদের দেশে সরকারি কোনো সেবা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। নতুন কিছু করতে দেখলেই তাকে পিষে মারার আয়োজন চলে।
তারপরও আশাবাদী হই, আশাবাদী হই এই ভেবে যে, ভেতর থেকে কোনো শুভবুদ্ধির উদয় হবে হয়তো। নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টি বুঝতে পারবেন আশা করি। গ্রাহক-জনগণও বুঝতে পারবেন, তাঁরা কারও ক্রীড়নক হয়ে কাজ করবেন, নাকি দেশের পক্ষে দাঁড়াবেন?
লেখক: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর

জাতীয় প্রেসক্লাবে ৭ সেপ্টেম্বর গণশক্তি আয়োজন করে ‘জুলাই সনদ ও নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা। সেই সভায় নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না যে প্রশ্নটি করেছেন, তা কোটি টাকার সঙ্গে তুলনা করাই যায়। তাঁর সহজ জিজ্ঞাসা—‘ভোটের দিন যাঁর যেখানে শক্তি আছে, তাঁর যদি মনে হয় জিততে পারবেন না...
১ দিন আগে
হিমালয়কন্যা নেপালের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ভূদৃশ্যটি পর্বতমালার মতোই চড়াই-উতরাইয়ে ভরা। ১০ বছরের মাওবাদী বিদ্রোহের রক্তক্ষরণের পর ২০০৮ সালে উচ্ছেদ হয়েছিল রাজতন্ত্র। সেই থেকে ১৩ বার সরকার বদল হয়েছে। ক্ষমতার মসনদে ঘুরেফিরে দেখা যাচ্ছিল গুটিকয়েক নেতাকে।
১ দিন আগে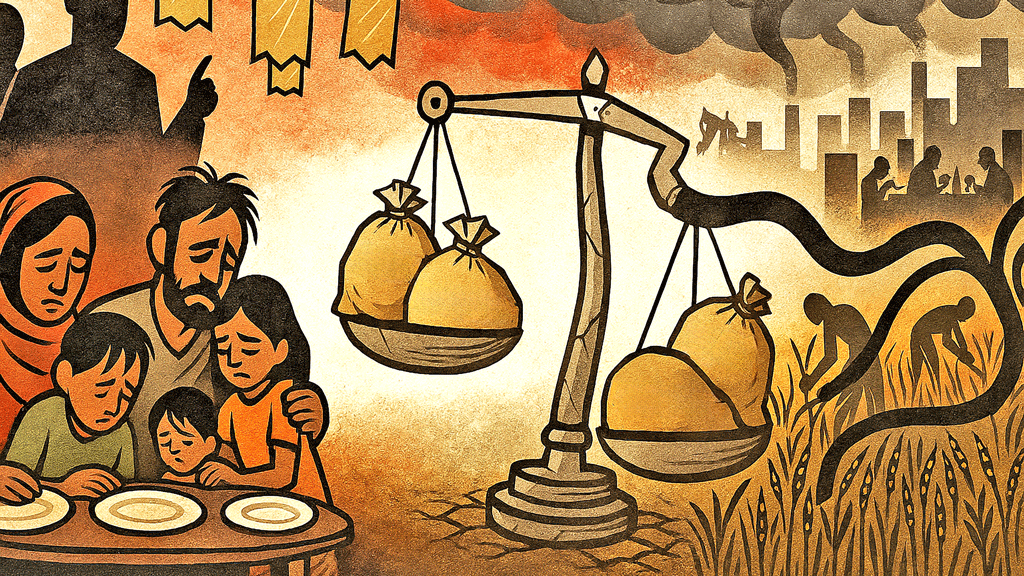
বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) পরিচালিত ‘২০২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের পরিবারসমূহের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি’ শীর্ষক সাম্প্রতিক জরিপের ফলাফলে উঠে এসেছে যে তিন বছরে (২০২২-২৫) দেশে দারিদ্র্যের হার ৯ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে এখন ২৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।
১ দিন আগে
বাংলা ভাষায় একটি পরিচিত শব্দবন্ধ হলো বায়ুচড়া। এর আভিধানিক অর্থ হলো পাগলামি। পাগলামি, উন্মাদনা বা উন্মত্ততা অর্থে আমরা ‘মাথা গরম হওয়া’র কথা কমবেশি সবাই জানি। একই অর্থে বায়ুরোগ বা বায়ুগ্রস্ততাও তুলনামূলকভাবে পরিচিত। এমনকি পাগলামি অর্থে ‘মাথা ফোরটি নাইন হওয়া’র কথাও প্রচলিত রয়েছে।
১ দিন আগে