হিল্লোল দত্ত
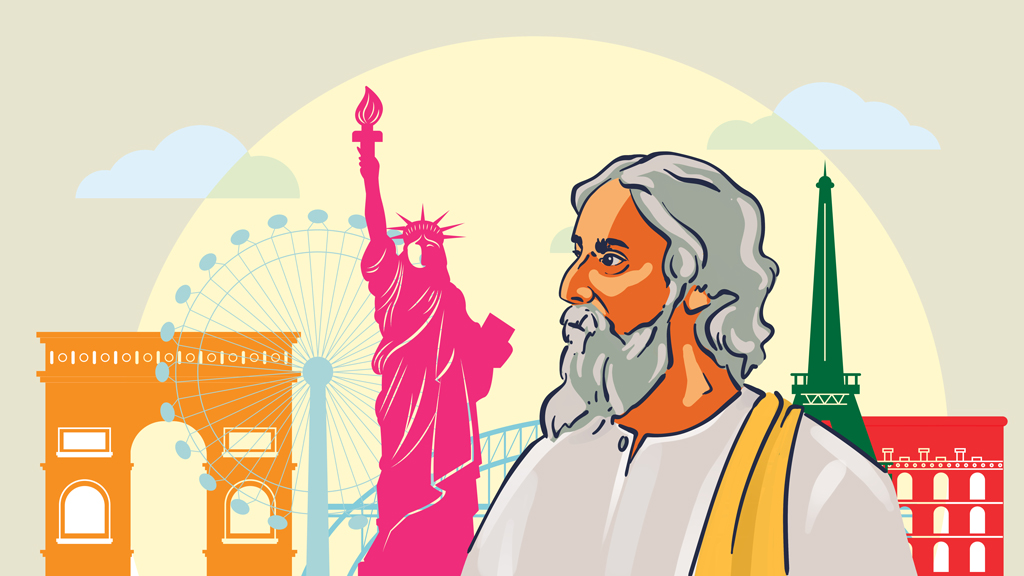
রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণপিয়াসী ছিলেন। নেহাত কম দেশ ঘোরেননি তিনি। কাজের উদ্দেশ্যে, সম্মান গ্রহণ করতে, আমন্ত্রণে সাড়া দিতে, প্রদর্শনীতে অংশ নিতে, বক্তৃতা দিতে তিনি বিভিন্ন সময়ে নানান দেশে গেছেন। এক হিসাবে জানা যায়, ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশে অন্তত ৩০টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, যার অনেকগুলো নিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনিও রয়েছে।
এত সব দেশের মধ্যে যে দেশটিতে তিনি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ভ্রমণ করেছেন, ইংল্যান্ড বাদে, আশ্চর্যজনকভাবে সেই দেশ নিয়েই আলোচনা খুব কম হয়। খোদ রবীন্দ্রনাথও তাঁর সেই দেশেতে ভ্রমণ নিয়ে কেন যেন নীরবই থেকেছেন। বই তো দূর স্থান, সেই দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর তেমন কোনো লেখালেখিই চোখে পড়ে না।
দেশটির নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে কবি পাঁচবার যাত্রা করেন। প্রায় ১৭ মাস তিনি কাটিয়েছিলেন বিশাল এই দেশে। ১৯১২ থেকে ১৯৩০ অবধি এই যাত্রা নানান প্রাপ্তি, প্রশংসা, সমালোচনা এবং অন্তত একটি অঘটনে বিজড়িত।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাধারার প্রথম পরিচয় তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অমৃতসরে গিয়ে। সেখানে বারো বছর বয়েসে তিনি ‘দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন’ পড়া শুরু করেন। পুত্রের ভাষায়, ‘পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া পিটার পার্লি'স টেলস পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্রাংকলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।’
এই হিসেবি নৈতিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ আমৃত্যুই ছিল, যা তাঁর মার্কিন দেশে ভ্রমণের সময়ও প্রতিভাত হয়েছে। তবে সাহিত্যিক হিসেবে ওয়াল্ট হুইটম্যান, রালফ এমার্সনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহ পরিস্ফুট হয়েছে নানান সময়ে।
কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে, যখন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ সেখানকার ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে যান। সে সময় প্রায় সবাই, যাঁরা উচ্চবিত্ত এবং সামাজিক স্তরে উঁচু দরের, তাঁদের সন্তানদের ইংল্যান্ডেই পড়াশোনার জন্য পাঠাতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে যান এবং ব্যর্থ হয়ে দেশে ফেরেন। রথীন্দ্রনাথ অবশ্য সফল হয়ে ফিরেছিলেন ১৯০৯ সালে।
১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মার্কিন দেশে যান ইংল্যান্ড থেকে। সে বছরই তাঁর ক্ষীণকায় গীতাঞ্জলি ‘সং অফারিংস’ নামে প্রকাশিত হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে এবং মার্কিন মুলুকের প্রখ্যাত ‘পোয়েট্রি’ সাময়িকীতে তাঁর সেই বই থেকে ছখানা কবিতাও বেরিয়েছে। তিনি সেবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাত মাসের একটি ভ্রমণ করেন, যার একটা বড় অংশ গেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার মধ্যে হার্ভার্ডও ছিল এবং নানান জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ায়। তাঁর দ্বিতীয় সফরটি নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক ছিল।
১৯১৬-১৭ সালের মধ্যে তিনি আমেরিকার নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ। বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাকমিলান তাঁর এই বক্তৃতার উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতি বক্তৃতায় তিনি তৎকালীন ৭০০ থেকে ১ হাজার মার্কিন ডলার অবধি সম্মানী পেতেন। এই নিয়ে আমেরিকায়ও তিনি সমালোচনার মুখোমুখি হন। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে তিনি সম্মানিত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে বক্তব্য রেখে হয়েছিলেন সমালোচিত, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে।
বছর তিনেক পর, ১৯২০ সালে কবি আবারও ফিরলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চার মাসের মেয়াদে। এবারও মূল উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ জোগাড়। কিন্তু এবারের সফর নিষ্ফল। আমেরিকা জড়িয়ে পড়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, কিছুটা হলেও, তাদের অনাক্রমণনীতি সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান, জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তব্য, ভোগবাদসর্বস্ব জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ নরমেধের প্রতিবাদে তাঁর নাইটহুড ত্যাগ করা, সবকিছু মিলিয়ে তিনি ইয়াংকিদের কাছে অপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য তখন। এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছেও, যাঁদের বড়সড় ব্যবসা তখনো ইংরেজদের সঙ্গে চলমান।
১৯২৯ সাঁলে কানাডার সোসাইটি অব এজুকেশনের আমন্ত্রণে তিনি কানাডা যাত্রা করেন। কিন্তু ভ্যাংকুভারের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার রূঢ় আচরণে তিনি সবকিছু বাতিল করে হপ্তা তিনেক লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকেন এবং পরে জাপানে ফেরত আসেন।
পরের বছরই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনের শেষ সফর করেন। ১৯৩০ সালের এই সফর নানান দিক থেকে বর্ণাঢ্য ছিল। মাস দুয়েকের এই সফর তাঁর জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করে। ম্যানহাটনে তিনি আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে সত্য, সৌন্দর্য নিয়ে আলাপ করেন, যা এখন বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ কবি হয়েও তিনি বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।
তবে ১৯১৬-১৭ মেয়াদে তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা মার্কিন মুলুকে ঘটেছিল, সেটা না বললেই নয়। ১ অক্টোবর, ১৯১৬ সালে তিনি নামলেন পোর্টল্যান্ড, ওরিগনে। ৪ অক্টোবর গেলেন সান ফ্র্যান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানে কলম্বিয়া থিয়েটারে তাঁর বক্তৃতার সময় নিরাপত্তার খুব কড়াকড়ি দেখা গেল। কোনো এশীয় লোকজনকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। পুলিশ কড়া নজর রাখছে চারপাশে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে লুকিয়ে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে আনেন। বক্তৃতা দিয়ে বেরোনোর সময়ও পেছনের দরজা। ট্রেনে করে সরিয়ে নেওয়া হয় ঘণ্টাখানেক দূরের পথ স্যান্টা বারবারায়। এমনকি পরের নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোও বাতিলের অনুরোধ করা হয় কবিকে।
কারণ কী?
পুলিশের কাছে গোয়েন্দা মারফত খবর এসেছে, এর আগে হিন্দুস্থান গদর পার্টি নামে আমেরিকার একটি রাজনৈতিক দল রবীন্দ্রনাথের ওপর হামলা করতে চায়। দলটি ১৯১৩ সালে আমেরিকায় নিবন্ধিত হয়। মূলত মার্কিন প্রবাসী পাঞ্জাবিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষে ভারতে সহিংস সংগ্রাম করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। দলের তৎকালীন নেতা রামচন্দ্র ভরদ্বাজ ‘হিন্দুস্থান গদর’ নামের একটি পত্রিকা চালাতেন, যা মূলত উর্দু ও পাঞ্জাবি, মাঝেমধ্যে ইংরেজিতে প্রকাশিত হতো। অক্টোবরেই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে জগদীশ চন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর ব্রিটিশ প্রশাসনের গোয়েন্দাগিরির তীব্র সমালোচনা করা হয়। কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে ৫ অক্টোবর ‘সান ফ্র্যান্সিসকো এক্সামিনার’ নামে এক পত্রিকায় রামচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড গ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন রামচন্দ্র। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এক লেখায় ‘মুঘল শাসনের চাইতে ব্রিটিশ শাসন উত্তম’ বলায় রামচন্দ্র প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানান।
৫ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের সাময়িক আবাস প্যালেস হোটেলের বাইরে গদর পার্টির দুজন সদস্য, হাতেশি সিং ও জীবন সিং খালসা দিওয়ান সোসাইটি নামের আরেকটি প্রবাসী পাঞ্জাবিদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকামী দলের দুই সদস্য বিষেণ সিং মাট্টু ও উমরাও সিংয়ের ওপর হামলা করেন। হামলার কারণে বিষেণের পাগড়ি মাথা থেকে খুলে পড়ে যায়। বিষেণ ও উমরাও রবীন্দ্রনাথকে একটি সভায় বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। যদিও হামলা হোটেলের বাইরে হয়, গোয়েন্দাদের প্রাপ্ত তথ্যমতে, গদর পার্টির লোক রবীন্দ্রনাথের ওপরই হামলা চালাতে এসেছিল। কারণ তো আগেই বলা হলো। গদর পার্টির ভেতরে একজন মার্কিন গোয়েন্দাও চুপিসারে নিজের কাজ চালাচ্ছিলেন। তাঁর নাম উইলিয়াম মান্ডেল। তিনি সান ফ্র্যান্সিসকোর প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর নজরদারি করতেন, যারা ব্রিটিশ ভারতে সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভে মদদ দিতেন। মজার বিষয় হলো, তাঁকে গদর পার্টিরই একজন রামচন্দ্র ও তাঁর সাথিদের ওপর অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিয়োগ করেছিলেন। তিনি একসঙ্গে দুটো কাজই চালাচ্ছিলেন সুবিধামতো। সম্ভবত তিনিই রবীন্দ্রনাথের ওপর গদর পার্টির সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে পুলিশকে জানান।
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি এবং তিনি বলেন যে, এই রাজনৈতিক মতভেদের বিষয়াশয় নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন। দেশবাসীর ওপরেই তিনি ভরসা রাখবেন।
এই হামলার আতঙ্ক মোটেও ছায়া ফেলেনি তাঁর সফরে। সান ফ্র্যান্সিসকো ও লস অ্যাঞ্জেলেসে সেবার অভূতপূর্ব সাফল্য ও সম্মান লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ। ‘সান ফ্র্যান্সিসকো এক্সামিনারেই’ লেখা হয়, স্থাপিত হয়েছে দ্য কাল্ট অব রবীন্দ্রনাথ। ‘লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস’ গর্বভরে ঘোষণা করে, লস অ্যাঞ্জেলেসে অন্য যেকোনো মার্কিন নগরীর চাইতেই রবীন্দ্রনাথের বই বেশি বিক্রি হয়। ১৯১৭ সালে তিনি ‘ন্যাশনালিজম’ নামের বইটি লিখে শেষ করেন। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে তিনি বইটি উৎসর্গ করতে চান। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ডামাডোলের মধ্যে এবং অন্যান্য বৈশ্বিক রাজনৈতিক গোলযোগে সেটা আর হয়নি।
এ ঘটনার একটি করুণ পরিণতি আছে। রামচন্দ্রকে তাঁর দলেরই রাম সিং নামে এক তরুণ ১৯১৫ সালে আদালতকক্ষে গুলি করে হত্যা করেন ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগসাজশের সন্দেহে। সেই আদালতে চলছিল হিন্দুস্থান-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি। ঘটনাচক্রে তাতে উঠে এসেছিল রবীন্দ্রনাথেরও নাম। কিন্তু সে আরেক কাহিনি।
লেখক: আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অনুবাদক ও ব্লগার।
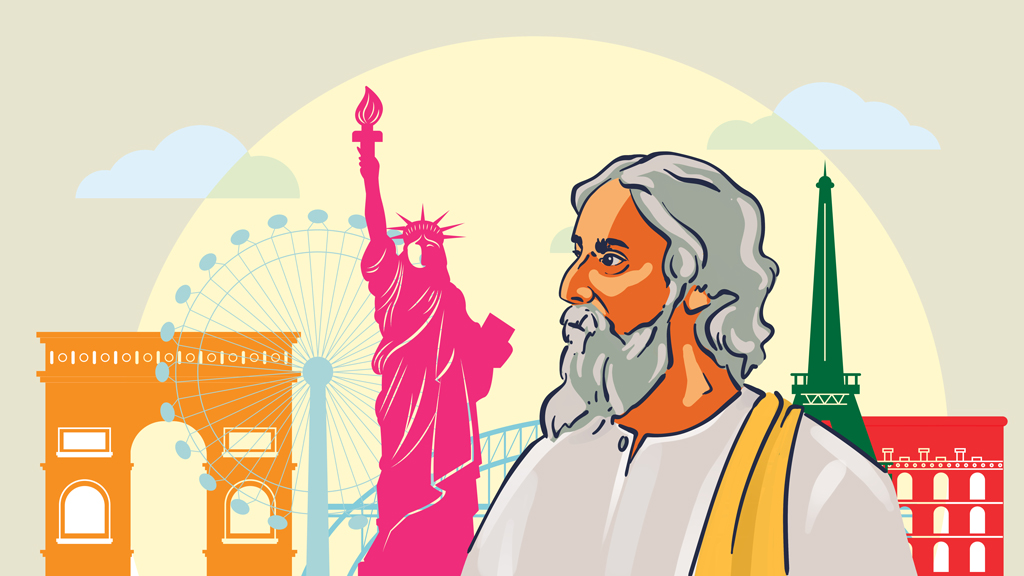
রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণপিয়াসী ছিলেন। নেহাত কম দেশ ঘোরেননি তিনি। কাজের উদ্দেশ্যে, সম্মান গ্রহণ করতে, আমন্ত্রণে সাড়া দিতে, প্রদর্শনীতে অংশ নিতে, বক্তৃতা দিতে তিনি বিভিন্ন সময়ে নানান দেশে গেছেন। এক হিসাবে জানা যায়, ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশে অন্তত ৩০টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, যার অনেকগুলো নিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনিও রয়েছে।
এত সব দেশের মধ্যে যে দেশটিতে তিনি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ভ্রমণ করেছেন, ইংল্যান্ড বাদে, আশ্চর্যজনকভাবে সেই দেশ নিয়েই আলোচনা খুব কম হয়। খোদ রবীন্দ্রনাথও তাঁর সেই দেশেতে ভ্রমণ নিয়ে কেন যেন নীরবই থেকেছেন। বই তো দূর স্থান, সেই দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর তেমন কোনো লেখালেখিই চোখে পড়ে না।
দেশটির নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে কবি পাঁচবার যাত্রা করেন। প্রায় ১৭ মাস তিনি কাটিয়েছিলেন বিশাল এই দেশে। ১৯১২ থেকে ১৯৩০ অবধি এই যাত্রা নানান প্রাপ্তি, প্রশংসা, সমালোচনা এবং অন্তত একটি অঘটনে বিজড়িত।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাধারার প্রথম পরিচয় তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অমৃতসরে গিয়ে। সেখানে বারো বছর বয়েসে তিনি ‘দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন’ পড়া শুরু করেন। পুত্রের ভাষায়, ‘পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া পিটার পার্লি'স টেলস পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন জীবনী অনেকটা গল্পের মতো লাগিবে এবং তাহা পড়িয়া আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে গিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিল। বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন নিতান্তই সুবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। তাঁহার হিসাব করা কেজো ধর্মনীতির সংকীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্রাংকলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।’
এই হিসেবি নৈতিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ আমৃত্যুই ছিল, যা তাঁর মার্কিন দেশে ভ্রমণের সময়ও প্রতিভাত হয়েছে। তবে সাহিত্যিক হিসেবে ওয়াল্ট হুইটম্যান, রালফ এমার্সনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহ পরিস্ফুট হয়েছে নানান সময়ে।
কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে, যখন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ সেখানকার ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে যান। সে সময় প্রায় সবাই, যাঁরা উচ্চবিত্ত এবং সামাজিক স্তরে উঁচু দরের, তাঁদের সন্তানদের ইংল্যান্ডেই পড়াশোনার জন্য পাঠাতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে যান এবং ব্যর্থ হয়ে দেশে ফেরেন। রথীন্দ্রনাথ অবশ্য সফল হয়ে ফিরেছিলেন ১৯০৯ সালে।
১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মার্কিন দেশে যান ইংল্যান্ড থেকে। সে বছরই তাঁর ক্ষীণকায় গীতাঞ্জলি ‘সং অফারিংস’ নামে প্রকাশিত হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে এবং মার্কিন মুলুকের প্রখ্যাত ‘পোয়েট্রি’ সাময়িকীতে তাঁর সেই বই থেকে ছখানা কবিতাও বেরিয়েছে। তিনি সেবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাত মাসের একটি ভ্রমণ করেন, যার একটা বড় অংশ গেছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যার মধ্যে হার্ভার্ডও ছিল এবং নানান জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ায়। তাঁর দ্বিতীয় সফরটি নানান দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক ছিল।
১৯১৬-১৭ সালের মধ্যে তিনি আমেরিকার নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ। বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাকমিলান তাঁর এই বক্তৃতার উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতি বক্তৃতায় তিনি তৎকালীন ৭০০ থেকে ১ হাজার মার্কিন ডলার অবধি সম্মানী পেতেন। এই নিয়ে আমেরিকায়ও তিনি সমালোচনার মুখোমুখি হন। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে তিনি সম্মানিত ও জনপ্রিয় হয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে বক্তব্য রেখে হয়েছিলেন সমালোচিত, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে।
বছর তিনেক পর, ১৯২০ সালে কবি আবারও ফিরলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চার মাসের মেয়াদে। এবারও মূল উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ জোগাড়। কিন্তু এবারের সফর নিষ্ফল। আমেরিকা জড়িয়ে পড়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, কিছুটা হলেও, তাদের অনাক্রমণনীতি সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান, জাতীয়তাবাদবিরোধী বক্তব্য, ভোগবাদসর্বস্ব জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ নরমেধের প্রতিবাদে তাঁর নাইটহুড ত্যাগ করা, সবকিছু মিলিয়ে তিনি ইয়াংকিদের কাছে অপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য তখন। এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছেও, যাঁদের বড়সড় ব্যবসা তখনো ইংরেজদের সঙ্গে চলমান।
১৯২৯ সাঁলে কানাডার সোসাইটি অব এজুকেশনের আমন্ত্রণে তিনি কানাডা যাত্রা করেন। কিন্তু ভ্যাংকুভারের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার রূঢ় আচরণে তিনি সবকিছু বাতিল করে হপ্তা তিনেক লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকেন এবং পরে জাপানে ফেরত আসেন।
পরের বছরই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনের শেষ সফর করেন। ১৯৩০ সালের এই সফর নানান দিক থেকে বর্ণাঢ্য ছিল। মাস দুয়েকের এই সফর তাঁর জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করে। ম্যানহাটনে তিনি আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে সত্য, সৌন্দর্য নিয়ে আলাপ করেন, যা এখন বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ কবি হয়েও তিনি বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।
তবে ১৯১৬-১৭ মেয়াদে তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা মার্কিন মুলুকে ঘটেছিল, সেটা না বললেই নয়। ১ অক্টোবর, ১৯১৬ সালে তিনি নামলেন পোর্টল্যান্ড, ওরিগনে। ৪ অক্টোবর গেলেন সান ফ্র্যান্সিসকো, ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানে কলম্বিয়া থিয়েটারে তাঁর বক্তৃতার সময় নিরাপত্তার খুব কড়াকড়ি দেখা গেল। কোনো এশীয় লোকজনকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। পুলিশ কড়া নজর রাখছে চারপাশে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে লুকিয়ে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে আনেন। বক্তৃতা দিয়ে বেরোনোর সময়ও পেছনের দরজা। ট্রেনে করে সরিয়ে নেওয়া হয় ঘণ্টাখানেক দূরের পথ স্যান্টা বারবারায়। এমনকি পরের নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোও বাতিলের অনুরোধ করা হয় কবিকে।
কারণ কী?
পুলিশের কাছে গোয়েন্দা মারফত খবর এসেছে, এর আগে হিন্দুস্থান গদর পার্টি নামে আমেরিকার একটি রাজনৈতিক দল রবীন্দ্রনাথের ওপর হামলা করতে চায়। দলটি ১৯১৩ সালে আমেরিকায় নিবন্ধিত হয়। মূলত মার্কিন প্রবাসী পাঞ্জাবিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্রিটিশ শাসনের বিপক্ষে ভারতে সহিংস সংগ্রাম করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। দলের তৎকালীন নেতা রামচন্দ্র ভরদ্বাজ ‘হিন্দুস্থান গদর’ নামের একটি পত্রিকা চালাতেন, যা মূলত উর্দু ও পাঞ্জাবি, মাঝেমধ্যে ইংরেজিতে প্রকাশিত হতো। অক্টোবরেই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে জগদীশ চন্দ্র বসু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর ব্রিটিশ প্রশাসনের গোয়েন্দাগিরির তীব্র সমালোচনা করা হয়। কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে ৫ অক্টোবর ‘সান ফ্র্যান্সিসকো এক্সামিনার’ নামে এক পত্রিকায় রামচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড গ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন রামচন্দ্র। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এক লেখায় ‘মুঘল শাসনের চাইতে ব্রিটিশ শাসন উত্তম’ বলায় রামচন্দ্র প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানান।
৫ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের সাময়িক আবাস প্যালেস হোটেলের বাইরে গদর পার্টির দুজন সদস্য, হাতেশি সিং ও জীবন সিং খালসা দিওয়ান সোসাইটি নামের আরেকটি প্রবাসী পাঞ্জাবিদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকামী দলের দুই সদস্য বিষেণ সিং মাট্টু ও উমরাও সিংয়ের ওপর হামলা করেন। হামলার কারণে বিষেণের পাগড়ি মাথা থেকে খুলে পড়ে যায়। বিষেণ ও উমরাও রবীন্দ্রনাথকে একটি সভায় বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। যদিও হামলা হোটেলের বাইরে হয়, গোয়েন্দাদের প্রাপ্ত তথ্যমতে, গদর পার্টির লোক রবীন্দ্রনাথের ওপরই হামলা চালাতে এসেছিল। কারণ তো আগেই বলা হলো। গদর পার্টির ভেতরে একজন মার্কিন গোয়েন্দাও চুপিসারে নিজের কাজ চালাচ্ছিলেন। তাঁর নাম উইলিয়াম মান্ডেল। তিনি সান ফ্র্যান্সিসকোর প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর নজরদারি করতেন, যারা ব্রিটিশ ভারতে সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভে মদদ দিতেন। মজার বিষয় হলো, তাঁকে গদর পার্টিরই একজন রামচন্দ্র ও তাঁর সাথিদের ওপর অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিয়োগ করেছিলেন। তিনি একসঙ্গে দুটো কাজই চালাচ্ছিলেন সুবিধামতো। সম্ভবত তিনিই রবীন্দ্রনাথের ওপর গদর পার্টির সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে পুলিশকে জানান।
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি এবং তিনি বলেন যে, এই রাজনৈতিক মতভেদের বিষয়াশয় নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন। দেশবাসীর ওপরেই তিনি ভরসা রাখবেন।
এই হামলার আতঙ্ক মোটেও ছায়া ফেলেনি তাঁর সফরে। সান ফ্র্যান্সিসকো ও লস অ্যাঞ্জেলেসে সেবার অভূতপূর্ব সাফল্য ও সম্মান লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ। ‘সান ফ্র্যান্সিসকো এক্সামিনারেই’ লেখা হয়, স্থাপিত হয়েছে দ্য কাল্ট অব রবীন্দ্রনাথ। ‘লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস’ গর্বভরে ঘোষণা করে, লস অ্যাঞ্জেলেসে অন্য যেকোনো মার্কিন নগরীর চাইতেই রবীন্দ্রনাথের বই বেশি বিক্রি হয়। ১৯১৭ সালে তিনি ‘ন্যাশনালিজম’ নামের বইটি লিখে শেষ করেন। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে তিনি বইটি উৎসর্গ করতে চান। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ডামাডোলের মধ্যে এবং অন্যান্য বৈশ্বিক রাজনৈতিক গোলযোগে সেটা আর হয়নি।
এ ঘটনার একটি করুণ পরিণতি আছে। রামচন্দ্রকে তাঁর দলেরই রাম সিং নামে এক তরুণ ১৯১৫ সালে আদালতকক্ষে গুলি করে হত্যা করেন ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগসাজশের সন্দেহে। সেই আদালতে চলছিল হিন্দুস্থান-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি। ঘটনাচক্রে তাতে উঠে এসেছিল রবীন্দ্রনাথেরও নাম। কিন্তু সে আরেক কাহিনি।
লেখক: আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অনুবাদক ও ব্লগার।

কোথাও নেই কোনো ইট-পাথরের রাস্তা। চারপাশে শুধু থইথই পানি। সেই পানির বুকেই গড়ে উঠেছে বসতি—পুরো একটি গ্রাম। ঘরবাড়ি, দোকানপাট, স্কুল, উপাসনালয়—সবই আছে সেই গ্রামে। কিন্তু পানির ওপর! মোটরগাড়ি নেই, নেই বাহারি মোটরবাইক। ফলে শব্দদূষণ নেই। আর নেই দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ার বুকে অ
১১ ঘণ্টা আগে
‘শক্ত মনের মানুষ’ বলে একটি কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু সেই মানুষের বৈশিষ্ট্য কী? আর করেই বা কী? খেয়াল করলে দেখবেন, সেই মানুষ সাফল্যে খুব বেশি উচ্ছ্বাস দেখায় না, ব্যর্থতায় কারও কাছে সহানুভূতি চায় না, শোকে কাতর হয় না, প্রায় সব দায়িত্ব নীরবে পালন করে, কোনো কাজে অজুহাত দেখায় না ইত্যাদি।
১২ ঘণ্টা আগে
রোজ লিপস্টিক ব্যবহারের ফলে ঠোঁটের রং স্বাভাবিক গোলাপি থাকে না। লিপস্টিক ভালোভাবে না তুললে বা এটির মান ভালো না হলেও ঠোঁটের রং কালচে হয়ে যেতে পারে। ঠোঁটের শুষ্কতা দূর করে একে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে কিছু ঘরোয়া টিপস মেনে চলতে পারেন। এতে ঠোঁটের কালচে ভাব দূর হবে। সেই সঙ্গে ঠোঁটে ফিরবে গোলাপি আভা।
১৩ ঘণ্টা আগে
বাজারে এখন যেসব সবজি পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্য়ে পটোল আর ঢ্যাঁড়স বলতে গেলে দু-এক দিন পরপরই কিনছেন প্রায় সবাই। কিন্তু সব সময় কি এগুলোর ভাজা আর তরকারি খেতে ভালো লাগে? মাঝেমধ্যে একটু ভিন্ন কায়দায় রান্না করলে এসব সবজিও একঘেয়ে অবস্থা কাটিয়ে হয়ে উঠতে পারে মুখরোচক।
১৭ ঘণ্টা আগে