রাজীব কুমার সাহা
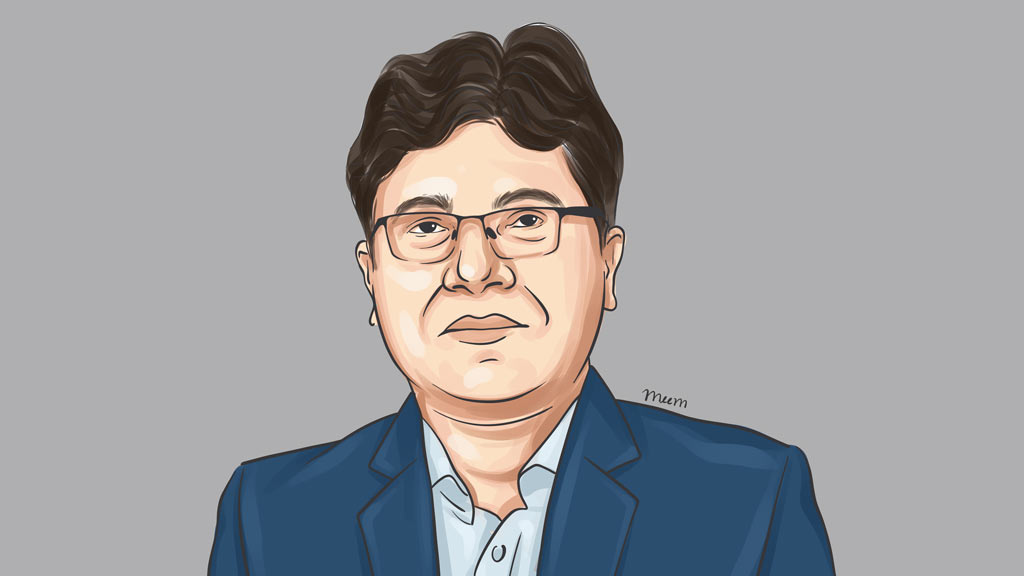
বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি শব্দবন্ধ হলো ‘অর্ধচন্দ্র’। শব্দবন্ধটিকে সঙ্গী করে প্রচলিত বাগধারায় আমরা পাই ‘অর্ধচন্দ্র দেওয়া’, যার মানে হলো ‘গলাধাক্কা দেওয়া’। কিন্তু অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে গলাধাক্কার আসলে সম্পর্ক কী? শরীরের অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়া এই গলাধাক্কার প্রসঙ্গটিকেই কেন অর্ধচন্দ্রের অর্থরূপে গ্রহণ করা হলো?
আবার একই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, যেহেতু অর্ধচন্দ্রের ব্যাপার রয়েছে, সে হিসাবে নিশ্চয় আভিধানিক বা আলংকারিকভাবে পূর্ণচন্দ্র বলে কোনো বিষয় হয়তো রয়েছে? আসলে কি তাই? তবে চলুন চন্দনচর্চিত চারুনেত্রে অর্ধচন্দ্রের চন্দ্রালাপে চিত্তশুদ্ধি করি।
সংস্কৃত ‘অর্ধ’ এবং ‘চন্দ্র’ শব্দসহযোগে গঠিত হয়েছে ‘অর্ধচন্দ্র’ শব্দটি। এটি বিশেষ্য পদ। আর অর্ধচন্দ্র দেওয়া বাগধারাটি ক্রিয়া বিশেষ্য পদ। অভিধান অনুসারে ‘অর্ধচন্দ্র’ শব্দের অর্থ হলো অর্ধ বা অর্ধেক প্রকাশিত চন্দ্র বা চাঁদ; সেনা সমাবেশের একটি কৌশলবিশেষ প্রভৃতি।
আলংকারিকভাবে অর্ধচন্দ্র শব্দের অর্থ হলো গলাধাক্কা। এখন প্রশ্ন হলো, এই অর্ধচন্দ্রের অর্থরূপে গলাধাক্কা কীভাবে স্থান করে নিল?
আগেই বলা হয়েছে, অর্ধচন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো অর্ধ প্রকাশিত চন্দ্র বা চাঁদ। কিন্তু আমাদের যাপিত জীবনের প্রচলিত অর্থে অর্ধচন্দ্র বলতে চাঁদের অর্ধাংশকে কমই বোঝায়। আলংকারিক অর্থ হিসেবে বোঝায় গলাধাক্কা।
এর মূলত কারণটি হলো কাউকে গলাধাক্কা দিতে হলে হাতের আকৃতি হয়ে যায় অনেকটা অর্ধচন্দ্রের ন্যায় অর্ধবৃত্তাকার। কাউকে গলাধাক্কা দেওয়ার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যকার যে অর্ধবৃত্তাকার আকৃতি তৈরি হয়, সেটিই অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুল্য। সাধারণত অর্ধচন্দ্রের এই চিত্রকল্পই গলাধাক্কার বিকল্প হিসেবে বাক্ভঙ্গিতে স্থান করে নিয়েছে।
অর্ধচন্দ্রের সূত্র সন্ধানে চাঁদ সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা জেনে নিতে পারি। সূর্যের মতোই চাঁদ পূর্ব দিকে ওঠে আর পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। চাঁদের এক দিন (অর্থাৎ, চাঁদ নিজের অক্ষের ওপর একবার ঘুরতে যে সময় নেয়) পৃথিবীর প্রায় এক মাসের সমান।
চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের পিঠে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। পৃথিবীর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা চাঁদ দেখি, সেখান থেকে চাঁদের যে আলোকিত অংশটি দেখতে পাই, সেটাকেই সেই সময়ের চাঁদের একটা নির্দিষ্ট তিথি বলছি। তাই চাঁদ দেখা সর্বদাই চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের পারস্পরিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল।
চাঁদের আকারের পরিবর্তন বলতে অনেকে মনে করেন যে দৃশ্যান্তরে চাঁদ আসলেই ছোট বা বড় হয়ে যায়। আসলে তা নয়, চাঁদ একই থাকে। তার ওপর আলো পড়ে যতটুকু দেখা যায়, সেটারই পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরো চাঁদ দৃশ্যমান হলে পূর্ণিমা আর একটুও দৃশ্যমান না হলে হয় অমাবস্যা। দিনের বেলায়ও চাঁদ থাকে, তবে সূর্যের আলোর কারণে তা দৃশ্যমান হয় না।
চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারটি খুবই প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চলে আসে, তখন চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে থাকে, সেটাতে কোনো আলো পড়ে না। ফলে সেদিকে পুরোটাই অন্ধকার। তখন চাঁদের অমাবস্যা। পরের দিন চাঁদ কিছুটা ঘুরে যায় তার কক্ষপথে।
পৃথিবী থেকে আমরা তার কাস্তের মতো চিকন একটা অংশ দেখতে পাই। শুরু হয় শুক্লপক্ষ। চাঁদ যখন অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার দিকে যায়, তখন শুক্লপক্ষ, আবার যখন পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যার দিকে যায় তখন হয় কৃষ্ণপক্ষ। পনেরো দিনে এক পক্ষ ধরা হয়। অমাবস্যার পরদিন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ বা প্রথমা, তারপর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, এভাবে ত্রয়োদশী, চতুর্দশীর পরদিন পূর্ণিমা হয়। তার পরের দিন হয় কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ (প্রথমা), দ্বিতীয়া, তৃতীয়া। এভাবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর পর হয় অমাবস্যা। শুক্লপক্ষের সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে চাঁদের অর্ধেক আলোকিত হয়। তখনই আক্ষরিকভাবে অর্ধচন্দ্র দৃশ্যমান হয়।
প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় আমরা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ অনুসারে ‘অর্ধচন্দ্র দেওয়া’ বলতে ‘গলাধাক্কা দেওয়া’কেই স্পষ্টরূপে বুঝে থাকি। এই পরম্পরা অনুসারে অনেকে আবার মনে করতে পারেন, তাহলে ‘পূর্ণচন্দ্র’ বলতে বোধ হয় আমরা ‘গলা টিপে ধরা’কে ইঙ্গিত করতে পারি।
প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি তা নয়। পূর্ণচন্দ্র শব্দের এমন কোনো আলংকারিক অর্থ নেই। যদি কেউ করে থাকেন, তবে সেটি পূর্ণচন্দ্র শব্দের সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ। সুতরাং, আসুন যাপিত জীবনের সব অশুভকে অব্যাজে অর্ধচন্দ্র দিয়ে অন্তরিত করি।
লেখক: আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক
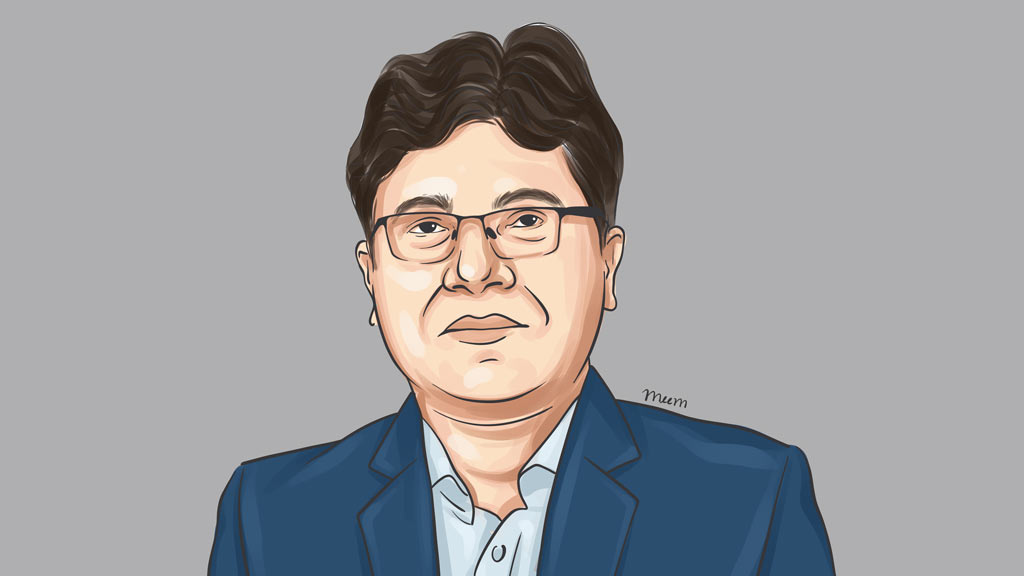
বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি শব্দবন্ধ হলো ‘অর্ধচন্দ্র’। শব্দবন্ধটিকে সঙ্গী করে প্রচলিত বাগধারায় আমরা পাই ‘অর্ধচন্দ্র দেওয়া’, যার মানে হলো ‘গলাধাক্কা দেওয়া’। কিন্তু অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে গলাধাক্কার আসলে সম্পর্ক কী? শরীরের অপরাপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়া এই গলাধাক্কার প্রসঙ্গটিকেই কেন অর্ধচন্দ্রের অর্থরূপে গ্রহণ করা হলো?
আবার একই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, যেহেতু অর্ধচন্দ্রের ব্যাপার রয়েছে, সে হিসাবে নিশ্চয় আভিধানিক বা আলংকারিকভাবে পূর্ণচন্দ্র বলে কোনো বিষয় হয়তো রয়েছে? আসলে কি তাই? তবে চলুন চন্দনচর্চিত চারুনেত্রে অর্ধচন্দ্রের চন্দ্রালাপে চিত্তশুদ্ধি করি।
সংস্কৃত ‘অর্ধ’ এবং ‘চন্দ্র’ শব্দসহযোগে গঠিত হয়েছে ‘অর্ধচন্দ্র’ শব্দটি। এটি বিশেষ্য পদ। আর অর্ধচন্দ্র দেওয়া বাগধারাটি ক্রিয়া বিশেষ্য পদ। অভিধান অনুসারে ‘অর্ধচন্দ্র’ শব্দের অর্থ হলো অর্ধ বা অর্ধেক প্রকাশিত চন্দ্র বা চাঁদ; সেনা সমাবেশের একটি কৌশলবিশেষ প্রভৃতি।
আলংকারিকভাবে অর্ধচন্দ্র শব্দের অর্থ হলো গলাধাক্কা। এখন প্রশ্ন হলো, এই অর্ধচন্দ্রের অর্থরূপে গলাধাক্কা কীভাবে স্থান করে নিল?
আগেই বলা হয়েছে, অর্ধচন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো অর্ধ প্রকাশিত চন্দ্র বা চাঁদ। কিন্তু আমাদের যাপিত জীবনের প্রচলিত অর্থে অর্ধচন্দ্র বলতে চাঁদের অর্ধাংশকে কমই বোঝায়। আলংকারিক অর্থ হিসেবে বোঝায় গলাধাক্কা।
এর মূলত কারণটি হলো কাউকে গলাধাক্কা দিতে হলে হাতের আকৃতি হয়ে যায় অনেকটা অর্ধচন্দ্রের ন্যায় অর্ধবৃত্তাকার। কাউকে গলাধাক্কা দেওয়ার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যকার যে অর্ধবৃত্তাকার আকৃতি তৈরি হয়, সেটিই অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুল্য। সাধারণত অর্ধচন্দ্রের এই চিত্রকল্পই গলাধাক্কার বিকল্প হিসেবে বাক্ভঙ্গিতে স্থান করে নিয়েছে।
অর্ধচন্দ্রের সূত্র সন্ধানে চাঁদ সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা জেনে নিতে পারি। সূর্যের মতোই চাঁদ পূর্ব দিকে ওঠে আর পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। চাঁদের এক দিন (অর্থাৎ, চাঁদ নিজের অক্ষের ওপর একবার ঘুরতে যে সময় নেয়) পৃথিবীর প্রায় এক মাসের সমান।
চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের পিঠে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। পৃথিবীর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা চাঁদ দেখি, সেখান থেকে চাঁদের যে আলোকিত অংশটি দেখতে পাই, সেটাকেই সেই সময়ের চাঁদের একটা নির্দিষ্ট তিথি বলছি। তাই চাঁদ দেখা সর্বদাই চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যের পারস্পরিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল।
চাঁদের আকারের পরিবর্তন বলতে অনেকে মনে করেন যে দৃশ্যান্তরে চাঁদ আসলেই ছোট বা বড় হয়ে যায়। আসলে তা নয়, চাঁদ একই থাকে। তার ওপর আলো পড়ে যতটুকু দেখা যায়, সেটারই পরিবর্তন সূচিত হয়। পুরো চাঁদ দৃশ্যমান হলে পূর্ণিমা আর একটুও দৃশ্যমান না হলে হয় অমাবস্যা। দিনের বেলায়ও চাঁদ থাকে, তবে সূর্যের আলোর কারণে তা দৃশ্যমান হয় না।
চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারটি খুবই প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চলে আসে, তখন চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে থাকে, সেটাতে কোনো আলো পড়ে না। ফলে সেদিকে পুরোটাই অন্ধকার। তখন চাঁদের অমাবস্যা। পরের দিন চাঁদ কিছুটা ঘুরে যায় তার কক্ষপথে।
পৃথিবী থেকে আমরা তার কাস্তের মতো চিকন একটা অংশ দেখতে পাই। শুরু হয় শুক্লপক্ষ। চাঁদ যখন অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার দিকে যায়, তখন শুক্লপক্ষ, আবার যখন পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যার দিকে যায় তখন হয় কৃষ্ণপক্ষ। পনেরো দিনে এক পক্ষ ধরা হয়। অমাবস্যার পরদিন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ বা প্রথমা, তারপর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, এভাবে ত্রয়োদশী, চতুর্দশীর পরদিন পূর্ণিমা হয়। তার পরের দিন হয় কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ (প্রথমা), দ্বিতীয়া, তৃতীয়া। এভাবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর পর হয় অমাবস্যা। শুক্লপক্ষের সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে চাঁদের অর্ধেক আলোকিত হয়। তখনই আক্ষরিকভাবে অর্ধচন্দ্র দৃশ্যমান হয়।
প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় আমরা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ অনুসারে ‘অর্ধচন্দ্র দেওয়া’ বলতে ‘গলাধাক্কা দেওয়া’কেই স্পষ্টরূপে বুঝে থাকি। এই পরম্পরা অনুসারে অনেকে আবার মনে করতে পারেন, তাহলে ‘পূর্ণচন্দ্র’ বলতে বোধ হয় আমরা ‘গলা টিপে ধরা’কে ইঙ্গিত করতে পারি।
প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি তা নয়। পূর্ণচন্দ্র শব্দের এমন কোনো আলংকারিক অর্থ নেই। যদি কেউ করে থাকেন, তবে সেটি পূর্ণচন্দ্র শব্দের সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ। সুতরাং, আসুন যাপিত জীবনের সব অশুভকে অব্যাজে অর্ধচন্দ্র দিয়ে অন্তরিত করি।
লেখক: আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...
১২ জুন ২০২৫
ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।
১৯ মে ২০২৫
আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
০৮ মে ২০২৫
পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...
০৮ মে ২০২৫