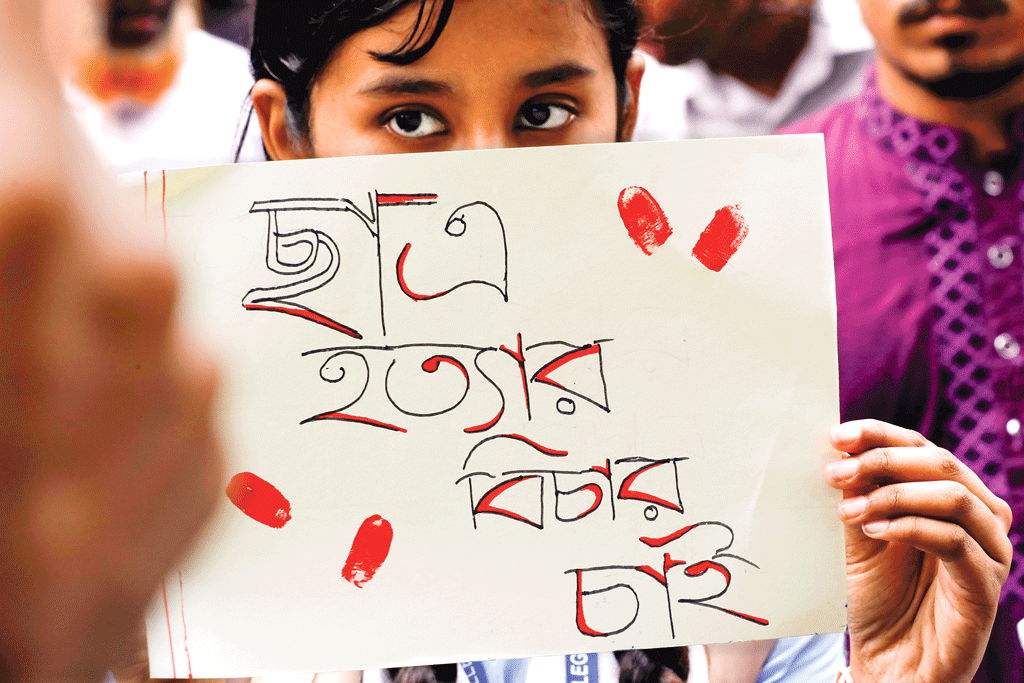
সামাজিক পরিবর্তনের ওপর রোমান কার্জনারিকের বই ‘হিস্ট্রি ফর টুমরো: ইন্সপিরেশন ফ্রম দ্য পাস্ট ফর দ্য ফিউচার অব হিউম্যানিটি’ বইটিতে রোমান কার্জনারিক তুলে ধরেছেন কীভাবে অতীত আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারে। সহজ কথায়, এই বই বলে আমরা কে এবং আমরা কী হতে পারি।
বৈশ্বিক চালচিত্রে একদিকে যুদ্ধ ও মুদ্রাস্ফীতি, অন্যদিকে জলবায়ুসংকটসহ নানাবিধ সংকটে পৃথিবী। ফলে আজ জনজীবন, প্রকৃতি এবং সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর মৌলিক সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত। সহজ ভাষায় বর্তমান পৃথিবী তার অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকছে। আশার বিষয় হলো, বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও দার্শনিকের মতে, সংকটের মাধ্যমেই পরিবর্তন আসে, যেই পরিবর্তন সমাজকে বদলানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ঠিক কত বড় সংকটের প্রয়োজন? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দার্শনিক রোমান কার্জনারিক তাঁর বইটিতে এ প্রসঙ্গেই আলোকপাত করেছেন।
এক সাক্ষাৎকারে কার্জনারিককে প্রশ্ন করা হয়, ‘কিসের মাধ্যমে পরিবর্তন আসে?’
প্রত্যুত্তরে নানা বিষয়কে সম্পৃক্ত করে তিনি বলেন, ‘পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের সংকট; যেমন—বন্যা, খরা ও অনেক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এসবের ব্যাপারে সরকারের কোনো রকম মাথাব্যথা না দেখতে পেয়ে আমি সত্যি অনেক বেশি হতাশ হয়েছিলাম। সরকার এসব ক্ষেত্রে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেয় না, তারা বরং ধীরগতির পরিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে পৃথিবীতে সংকটগুলো খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। তো, হতাশা থেকেই আমি ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করলাম। জানতে চাইছিলাম যে আসলে কোন পরিস্থিতিতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল। খুঁজে পেলাম যুদ্ধ বা মহামারির মতো ঘটনাগুলো—যখন কিনা সরকার খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল—সেসব বিষয়ে আমরা জানি। কিন্তু আসলে শুধুই সংকটের মাধ্যমে পরিবর্তন আসে না, এ জন্য আরও কিছু বিষয়ের প্রয়োজন; আমি আসলে সেগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টাই করেছি।’
২০ জুন ২০২৪-এ প্রকাশিত ‘দ্য ডিসরাপশন অব নেক্সাস’ নামের প্রবন্ধে রোমান কার্জনারিক বলেন, ‘ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে এ ধরনের বড় পরিবর্তন তখনই হয়, যখন তিনটি জিনিস একত্রে কাজ করে, ঠিক একটা ত্রিভুজের তিনটি কোনার মতো। এক কোনায় থাকবে কোনো একটা সংকট; যেমন অর্থনৈতিক সংকট বা জলবায়ুর পরিবর্তন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো, আন্দোলন। মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করবে। আর তৃতীয় যা দরকার তা হলো, শক্তিশালী ও স্বপ্নদর্শী চিন্তা-ধারণা, যা পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করবে।’
তাঁর মতে, যখন ওপরের তিনটি গুণক একত্র হয়, তখনই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়; যেমনটি ১৯৮৯-এ বার্লিন ওয়ালের পতনের সময় হয়েছিল। ওই সময় এ তিনটি বিষয় একত্রে কাজ করেছিল। প্রথমত, ১৯৮৯-এর গ্রীষ্মে একটি রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানের নেতৃত্বে তখন বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। মূলত ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্বর্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সোভিয়েত প্রধান মিখাইল গর্বাচেভের প্রবর্তন করা সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক এর প্রধান কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা-ধারা চলছিল, যেমন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বাসনা, চলাফেরার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি। সবশেষে, তৃতীয় গুণক আন্দোলন। ১৯৮৯-এর অক্টোবরে জার্মানের লিপজিগে ১ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিল। তারপর নভেম্বরের ৯ তারিখে প্রতিবাদের জেরে বার্লিন ওয়ালের পতন ঘটেছিল। আন্দোলন আসলে বেশ কিছু বছর ধরেই চলছিল। কিন্তু সংকট ও চিন্তা-ধারণা ছাড়া শুধু আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব হতো না বা হলেও অনেক দীর্ঘ সময়ের দরকার হতো। এভাবেই আসলে যোগসূত্র তৈরি হয়।
আমাদের নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে স্কুলের নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে জহির রায়হানের একটা লেখার অংশ ছিল—একজন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্র যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কেন যুদ্ধ করছেন। উত্তর এসেছিল, সময়ের প্রয়োজনে। শব্দটি অনুধাবনের জন্য খুব গভীর। অনুরণন আরও তীব্র।
রোমান কার্জনারিককে প্রশ্ন করা হয়, ‘আমাদের এখানে সমস্যাটা কোথায় বলে আপনি মনে করেন? এখানে কি চিন্তাধারা বা আন্দোলন পরিবর্তন আনার জন্য যথেষ্ট বড় নয়?’
কার্জনারিক বলেন, ‘মাঝেমধ্যে সেগুলো পরিমাণে বেশি হওয়া দরকার। মানে, আপনি যদি ষাটের দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা চিন্তা করেন, সেখানে কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিপক্ষেও অনেক প্রতিবাদ হয়েছিল। সেগুলো মানুষের মতামত পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট হলেও সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। সিস্টেম অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল এবং তা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেই ছিল।... আমাদের এখানেও এ রকম বেশ কিছু আন্দোলনের দরকার রয়েছে। আমি জানি, অনেকেই এ রকম আন্দোলনের ফলে রাস্তা বন্ধ থাকাকে বিড়ম্বনার মনে করেন। কিন্তু আমি নিজেও আমার মেয়েকে নিয়ে লন্ডনের হাউস অব পার্লামেন্টের সামনে শুয়ে পড়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। অনেকেই বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় হর্ন বাজায়। যদিও আমি আমার বেশির ভাগ সময় লাইব্রেরিতে বসে বই লিখে কাটাতে পছন্দ করি; কিন্তু আমার মনে হয় একজন ভালো পূর্বপুরুষ হওয়ার জন্য এ ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাটা খুবই জরুরি।’
মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই আন্দোলনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা যদি আরেকটু বেশি গভীরে ঢুকি, সম্মিলিত মানুষের সংহতি থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রবেশ করি, দেখব ভ্রূণতত্ত্বেও ভ্রূণকে মাতৃ জঠরে যথেষ্ট পরিশ্রমের সঙ্গে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হয়। যদি যমজ থাকে তাহলে তো কথাই নেই। মানবকুল এবং পশুর সমাজে মাতৃগর্ভে যমজ বা একাধিক সন্তানের পারস্পরিক পুষ্টির জন্য দেহকোষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলনের কথা গবেষণানির্ভর উপাত্তভিত্তিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই আন্দোলন ও পরিবর্তন ভালো এবং খারাপ দুটোই হতে পারে!
ইতিহাসবিদ হোয়ারড যিন খুব সুন্দর করে বলেছেন, ‘আমাদের সময়ের গুরুতর সমস্যাগুলো ধীরেসুস্থে সমাধানের জন্য ফেলে রাখা ঠিক হবে না। বর্তমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে এ ক্ষেত্রে আন্দোলন অনেকাংশেই কাজ করে।’
বর্তমানে আবার আমরা একটি সময়ের প্রয়োজনে কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়েছি। আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা আমাদের প্রয়োজন। আমাদের সন্তানের চোখে যে উচ্চশিক্ষার কাজল আমরা আঁকি, সেটা যেন মোহের অঞ্জন না হয়। আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আমাদের সন্তানেরা যেন নিজ ভূমিতে নিরাপদে থাকে।
লেখক: অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
চিকিৎসক, কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার, বাংলাদেশ
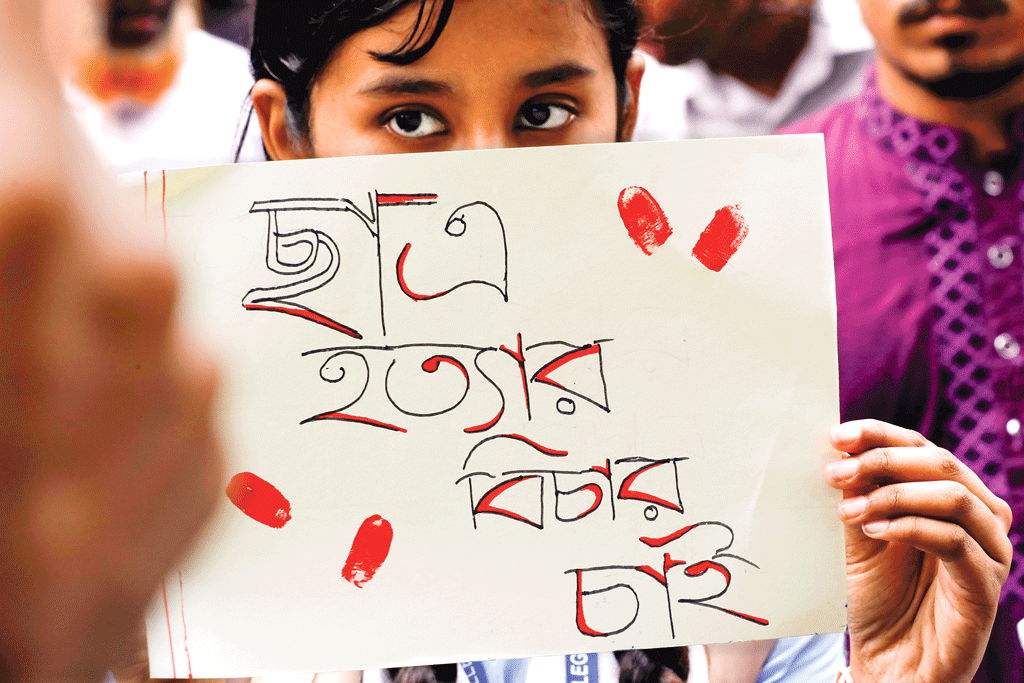
সামাজিক পরিবর্তনের ওপর রোমান কার্জনারিকের বই ‘হিস্ট্রি ফর টুমরো: ইন্সপিরেশন ফ্রম দ্য পাস্ট ফর দ্য ফিউচার অব হিউম্যানিটি’ বইটিতে রোমান কার্জনারিক তুলে ধরেছেন কীভাবে অতীত আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারে। সহজ কথায়, এই বই বলে আমরা কে এবং আমরা কী হতে পারি।
বৈশ্বিক চালচিত্রে একদিকে যুদ্ধ ও মুদ্রাস্ফীতি, অন্যদিকে জলবায়ুসংকটসহ নানাবিধ সংকটে পৃথিবী। ফলে আজ জনজীবন, প্রকৃতি এবং সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর মৌলিক সম্পর্ক ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত। সহজ ভাষায় বর্তমান পৃথিবী তার অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকছে। আশার বিষয় হলো, বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও দার্শনিকের মতে, সংকটের মাধ্যমেই পরিবর্তন আসে, যেই পরিবর্তন সমাজকে বদলানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমূল সামাজিক পরিবর্তনের জন্য ঠিক কত বড় সংকটের প্রয়োজন? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দার্শনিক রোমান কার্জনারিক তাঁর বইটিতে এ প্রসঙ্গেই আলোকপাত করেছেন।
এক সাক্ষাৎকারে কার্জনারিককে প্রশ্ন করা হয়, ‘কিসের মাধ্যমে পরিবর্তন আসে?’
প্রত্যুত্তরে নানা বিষয়কে সম্পৃক্ত করে তিনি বলেন, ‘পৃথিবীর বিভিন্ন রকমের সংকট; যেমন—বন্যা, খরা ও অনেক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং এসবের ব্যাপারে সরকারের কোনো রকম মাথাব্যথা না দেখতে পেয়ে আমি সত্যি অনেক বেশি হতাশ হয়েছিলাম। সরকার এসব ক্ষেত্রে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেয় না, তারা বরং ধীরগতির পরিবর্তন নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে পৃথিবীতে সংকটগুলো খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। তো, হতাশা থেকেই আমি ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করলাম। জানতে চাইছিলাম যে আসলে কোন পরিস্থিতিতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল। খুঁজে পেলাম যুদ্ধ বা মহামারির মতো ঘটনাগুলো—যখন কিনা সরকার খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিল—সেসব বিষয়ে আমরা জানি। কিন্তু আসলে শুধুই সংকটের মাধ্যমে পরিবর্তন আসে না, এ জন্য আরও কিছু বিষয়ের প্রয়োজন; আমি আসলে সেগুলো অনুসন্ধানের চেষ্টাই করেছি।’
২০ জুন ২০২৪-এ প্রকাশিত ‘দ্য ডিসরাপশন অব নেক্সাস’ নামের প্রবন্ধে রোমান কার্জনারিক বলেন, ‘ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে এ ধরনের বড় পরিবর্তন তখনই হয়, যখন তিনটি জিনিস একত্রে কাজ করে, ঠিক একটা ত্রিভুজের তিনটি কোনার মতো। এক কোনায় থাকবে কোনো একটা সংকট; যেমন অর্থনৈতিক সংকট বা জলবায়ুর পরিবর্তন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো, আন্দোলন। মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পরিবর্তন আনতে বাধ্য করবে। আর তৃতীয় যা দরকার তা হলো, শক্তিশালী ও স্বপ্নদর্শী চিন্তা-ধারণা, যা পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করবে।’
তাঁর মতে, যখন ওপরের তিনটি গুণক একত্র হয়, তখনই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়; যেমনটি ১৯৮৯-এ বার্লিন ওয়ালের পতনের সময় হয়েছিল। ওই সময় এ তিনটি বিষয় একত্রে কাজ করেছিল। প্রথমত, ১৯৮৯-এর গ্রীষ্মে একটি রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানের নেতৃত্বে তখন বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। মূলত ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্বর্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সোভিয়েত প্রধান মিখাইল গর্বাচেভের প্রবর্তন করা সংশোধনী নিয়ে বিতর্ক এর প্রধান কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা-ধারা চলছিল, যেমন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বাসনা, চলাফেরার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি। সবশেষে, তৃতীয় গুণক আন্দোলন। ১৯৮৯-এর অক্টোবরে জার্মানের লিপজিগে ১ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছিল। তারপর নভেম্বরের ৯ তারিখে প্রতিবাদের জেরে বার্লিন ওয়ালের পতন ঘটেছিল। আন্দোলন আসলে বেশ কিছু বছর ধরেই চলছিল। কিন্তু সংকট ও চিন্তা-ধারণা ছাড়া শুধু আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব হতো না বা হলেও অনেক দীর্ঘ সময়ের দরকার হতো। এভাবেই আসলে যোগসূত্র তৈরি হয়।
আমাদের নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে স্কুলের নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে জহির রায়হানের একটা লেখার অংশ ছিল—একজন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্র যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কেন যুদ্ধ করছেন। উত্তর এসেছিল, সময়ের প্রয়োজনে। শব্দটি অনুধাবনের জন্য খুব গভীর। অনুরণন আরও তীব্র।
রোমান কার্জনারিককে প্রশ্ন করা হয়, ‘আমাদের এখানে সমস্যাটা কোথায় বলে আপনি মনে করেন? এখানে কি চিন্তাধারা বা আন্দোলন পরিবর্তন আনার জন্য যথেষ্ট বড় নয়?’
কার্জনারিক বলেন, ‘মাঝেমধ্যে সেগুলো পরিমাণে বেশি হওয়া দরকার। মানে, আপনি যদি ষাটের দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা চিন্তা করেন, সেখানে কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিপক্ষেও অনেক প্রতিবাদ হয়েছিল। সেগুলো মানুষের মতামত পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট হলেও সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। সিস্টেম অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল এবং তা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেই ছিল।... আমাদের এখানেও এ রকম বেশ কিছু আন্দোলনের দরকার রয়েছে। আমি জানি, অনেকেই এ রকম আন্দোলনের ফলে রাস্তা বন্ধ থাকাকে বিড়ম্বনার মনে করেন। কিন্তু আমি নিজেও আমার মেয়েকে নিয়ে লন্ডনের হাউস অব পার্লামেন্টের সামনে শুয়ে পড়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। অনেকেই বিরক্ত হয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় হর্ন বাজায়। যদিও আমি আমার বেশির ভাগ সময় লাইব্রেরিতে বসে বই লিখে কাটাতে পছন্দ করি; কিন্তু আমার মনে হয় একজন ভালো পূর্বপুরুষ হওয়ার জন্য এ ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাটা খুবই জরুরি।’
মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই আন্দোলনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা যদি আরেকটু বেশি গভীরে ঢুকি, সম্মিলিত মানুষের সংহতি থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রবেশ করি, দেখব ভ্রূণতত্ত্বেও ভ্রূণকে মাতৃ জঠরে যথেষ্ট পরিশ্রমের সঙ্গে নিজের অবস্থান তৈরি করতে হয়। যদি যমজ থাকে তাহলে তো কথাই নেই। মানবকুল এবং পশুর সমাজে মাতৃগর্ভে যমজ বা একাধিক সন্তানের পারস্পরিক পুষ্টির জন্য দেহকোষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলনের কথা গবেষণানির্ভর উপাত্তভিত্তিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই আন্দোলন ও পরিবর্তন ভালো এবং খারাপ দুটোই হতে পারে!
ইতিহাসবিদ হোয়ারড যিন খুব সুন্দর করে বলেছেন, ‘আমাদের সময়ের গুরুতর সমস্যাগুলো ধীরেসুস্থে সমাধানের জন্য ফেলে রাখা ঠিক হবে না। বর্তমান সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি যে এ ক্ষেত্রে আন্দোলন অনেকাংশেই কাজ করে।’
বর্তমানে আবার আমরা একটি সময়ের প্রয়োজনে কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়েছি। আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা আমাদের প্রয়োজন। আমাদের সন্তানের চোখে যে উচ্চশিক্ষার কাজল আমরা আঁকি, সেটা যেন মোহের অঞ্জন না হয়। আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আমাদের সন্তানেরা যেন নিজ ভূমিতে নিরাপদে থাকে।
লেখক: অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
চিকিৎসক, কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার, বাংলাদেশ

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...
১২ জুন ২০২৫
ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।
১৯ মে ২০২৫
আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
০৮ মে ২০২৫
পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...
০৮ মে ২০২৫