চিররঞ্জন সরকার
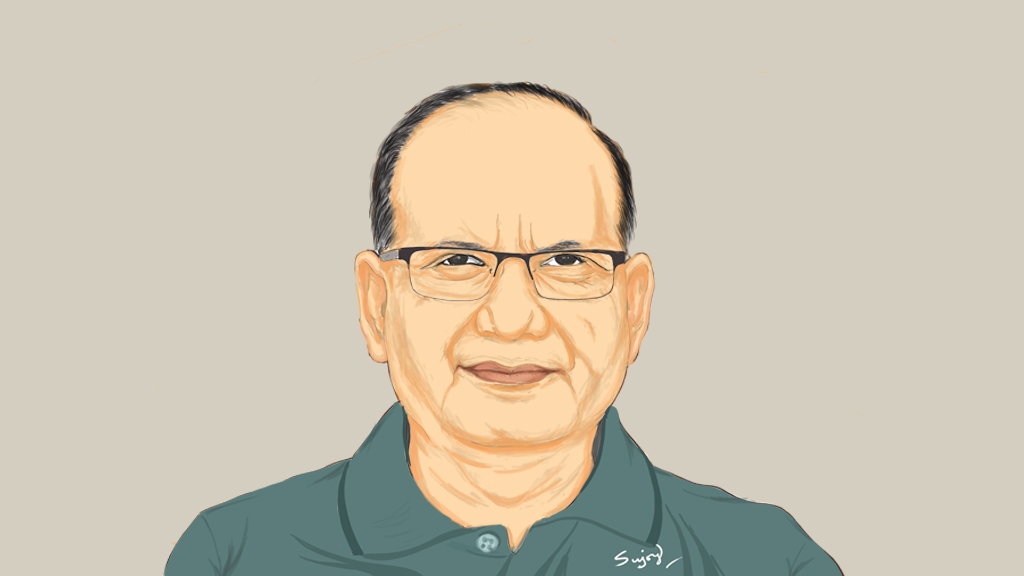
ধরা যাক একটা জেলায় ১০০ লোক বসবাস করে। তাদের মোট বার্ষিক আয় ৫ লাখ টাকা। যদি আমরা তাদের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য তাদের মাথাপিছু আয়ের হিসাব করি, তাহলে ৫ লাখ টাকাকে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করব। দেখব যে তাদের প্রত্যেকের এক বছরের আয় হচ্ছে ৫ হাজার টাকা (৫০০০০০ ÷ ১০০)। দেখে মনে হয় যে একটা জেলায় একজনের আয় যদি ৫ হাজার টাকা হয়, তাহলে মন্দ নয়। কিন্তু এবার যদি আপনি জানতে পারেন যে ওই জেলায় ছোট একটা প্রশাসন আছে, যেখানে চারজন কর্তাব্যক্তি আছেন এবং তাঁদের অধিকারেই আছে বার্ষিক আয়ের ৪ লাখ টাকা। তাহলে চিত্র পাল্টে যাবে। ৪ জনের মাথাপিছু আয় হবে ১ লাখ টাকা এবং বাকি ৯৬ জনের মাথাপিছু আয় হবে ১ হাজার ৪১ টাকা মাত্র। তাহলে মাথাপিছু আয়ের হিসাব এই জেলায় বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থা বোঝাচ্ছে না কোনোভাবেই। সম্পদ কত আছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বটে; তবে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কার অধিকারে সম্পদ কতটুকু আছে এবং কে কতটুকু সম্পদ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার বা ভোগ করতে পারছেন, সেটা। আর এখানেই আসে সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি। অর্থনীতিতে সম্পদ অর্জনের চেয়ে সম্পদের বণ্টন অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। মাথাপিছু আয় একটা দেশের অর্থনীতির আকার কতটুকু, সেটা বুঝতে সাহায্য করে কিন্তু লোকজন কেমন আছে, তারা সবাই ভালো আছে কি না, সেটা বুঝতে সহায়তা করে না; যদি না আমরা জানতে পারি তাদের কার অধিকারে কতটুকু ভোগযোগ্য সম্পদ আছে। শুধু তা-ই নয়, যার যতটুকু ইনকাম, তা দিয়ে কে, কতটুকু জিনিস বাজার থেকে কিনতে পারছে, সেটাও ভালো থাকার একটা মানদণ্ড। যদি আপনার দৈনিক আয় ১০০ টাকা হয়, এই ১০০ টাকা যদি এক কেজি চাল কিনতেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেই আয় আপনার তেমন কোনো কল্যাণ করতে পারে না। অথচ আপনার আয় যদি ৫০ টাকা হয়, সেই টাকা দিয়ে যদি আপনি চাল, ডাল, তেল, মাছ, তরকারি সবই কিনতে পারেন, তাহলে ৫০ টাকা আয়ই অনেক ভালো। কাজেই মজুরি বা আয় বৃদ্ধি হলেই ভালো থাকা যায় না। সেই টাকায় প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারার সামর্থ্য হচ্ছে ভালো থাকা।
বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালে ছিল প্রায় ১২৯ ডলার, যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৯১, অর্থাৎ স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় অন্তত ২০ গুণ বেড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়াবে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি। ওই সময়ে হতদরিদ্রের হার কমে শূন্যের ঘরে নেমে আসবে। আর মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হবে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে ‘বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।
করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। প্রশ্ন হচ্ছে, মাথাপিছু আয় বেশি থাকলেই কি মানুষ ভালো থাকে, নাকি সম্পদের সুষম বণ্টন মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে?
কার্ল মার্ক্স শিখিয়েছেন কীভাবে পুঁজি পুঁজিকে আকর্ষণ করে এবং কীভাবে শ্রমজীবীরা পুঁজিপতিদের হাতে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হন। আমাদের দেশে একটা মিশ্রিত অর্থনীতির চর্চা হয়। এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সর্বোচ্চ ধাপ নয় ঠিকই, কিন্তু পুঁজি সঞ্চালন, পুঁজি আহরণ ও একত্রীভবনের প্রক্রিয়া একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতোই। তা ছাড়া, সুশাসনের অভাব, অন্যায়, দুর্নীতি, জবাবদিহিহীনতা, স্বজনপ্রীতি, মিথ্যাচার, অপচয় এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত খাতে অসৎ-অদক্ষতা, পুঁজির অন্যায় আহরণকে ত্বরান্বিত করেছে, করছে। ফলে বাড়ছে বৈষম্য। অল্প কিছু লোকের হাতে সিংহভাগ সম্পদ। এই সম্পদ সুস্থ ও নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকে ন্যায়-নিষ্ঠভাবে উপার্জন করলে সমস্যা প্রকট হতো না। দেখা যায়, সমাজের একটা শ্রেণির উত্থান হয়েছে, যারা সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, তাদের কাছ থেকে অযৌক্তিক ও অন্যায্যভাবে সম্পদ আহরণ করছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় তারা সহায়তা পাচ্ছে, এমন একটা শ্রেণির কাছ থেকে, যারা কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।
বাংলাদেশে আয়বৈষম্য বাড়ছে দ্রুত। অর্থনীতিবিদদের মতে, গত ১০ বছরে আয়বৈষম্য বেড়েছে ১০ থেকে ১৬ শতাংশ। কোনো দেশের আয়বৈষম্য কতটা, তা পরিমাপ করা হয় গিনি সহগ দিয়ে। গিনি সহগের মান শূন্য হলে বোঝায় যে দেশের সবার মধ্যে চরম সমতা বিরাজ করছে; আর এর মান বাড়তে বাড়তে শূন্য দশমিক ৫ (০.৫) বা বেশি হলে বোঝায় যে দেশে আয়বৈষম্য চরমতম অবস্থায় পৌঁছেছে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭৪ সালে দেশে গিনি সহগের মান ছিল ০.২৪, যা করোনা লকডাউনের আগে বেড়ে হয়েছে ০.৪৮৩। আর লকডাউনের পরে হয়েছে ০.৬৩৫।
গবেষকেরা মনে করেন, বাংলাদেশে যেহেতু গবেষণার সময় ধনী পরিবারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, সেহেতু বৈষম্যের সত্যিকার চিত্র আরও ভয়াবহ বলে অনুমান করা অসংগত নয়।
বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বাড়লেও এর সুবিধা ভোগ করছে খুব কমসংখ্যক মানুষ। দেশে ধনী আরও ধনী হলেও দরিদ্রের হাতে অর্থ থাকছে না। বিভিন্নভাবে দরিদ্র লোকের হাত থেকে টাকা চলে যাচ্ছে ধনীদের পকেটে, ফলে আয়বৈষম্য বাড়ছেই। দরিদ্ররা যা আয় করছে, মূল্যস্ফীতির কারণে সেটাও খুব সামান্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি সীমিত আয়ের মানুষদের জীবনে অভিশাপ হয়ে এসেছে।
তাহলে করণীয় কী? আমাদের যাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্র চালান, তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা কেমন রাষ্ট্র চান, যদি চান রাষ্ট্রের কিছু লোক আর্থিকভাবে ভালো থাকবেন, তাহলে যেভাবে চলছে তাতে তাঁরা ভালোই আছেন, সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক সম্পদের সিংহভাগের মালিকানায় আছেন। যদিও সামগ্রিকভাবে সবাই কমবেশি ভালো না থাকলে আজ যাঁরা ভালো আছেন, কাল তাঁরাও ভালো থাকবেন—সেই নিশ্চয়তা থাকবে না। আর যদি চান সামাজিক সুবিধাসংবলিত একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, তাহলে অর্থ ও সমাজের অন্যান্য সুবিধা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন রাষ্ট্র যদি শুধু কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারে, তাহলে সমাজের একটা বৃহৎ গোষ্ঠীর হাতে অনেক টাকার প্রবাহ হবে। গ্রামের ১০ টাকা দামের এক কেজি বেগুন শহরে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়। কৃষক যদি অর্ধেক, অর্থাৎ ২০ টাকাও পেতেন, তাহলে তাঁদের বঞ্চনার পরিমাণ কমে আসত। কিন্তু সেটি হচ্ছে না; অথচ শুধু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সহজেই কাজটি করা সম্ভব।
আমাদের মনোযোগ দিতে হবে দেশের সার্বিক কল্যাণে, দেশের সব মানুষের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির দিকে। সমাজের এক অংশ অন্য অংশকে শোষণ করবে, বঞ্চিত করবে, সমাজের সম্পদ কার্যত লুট করবে এবং এই প্রক্রিয়া সর্বদা চলমান থাকবে, তাহলে সমাজে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠলেও সেই সম্পদ মানুষের কল্যাণে কাজে আসবে না। অর্থনীতির আকার বড় হবে, সামষ্টিক আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে মাথাপিছু আয় বাড়ছে কিন্তু মানুষের জীবনযাপনের গুণগত পরিবর্তন হবে না, বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। সামগ্রিক অর্থনীতি হয়ে পড়বে লুটেরা অর্থনীতি, অসম অর্থনীতি, কিছু মানুষের অন্যায্য-কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত অর্থনীতি। তাই অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের নজর দিতে হবে মানুষের অধিক কল্যাণে। তারা যেন তাদের আয় দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারে। প্রয়োজনীয় সেবাগুলো পায়। তা না হলে মজুরি বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে সেটা গরিব মানুষের কাছে প্রহসন বলেই বিবেচিত হবে।
লেখক: চিররঞ্জন সরকার, গবেষক ও কলামিস্ট
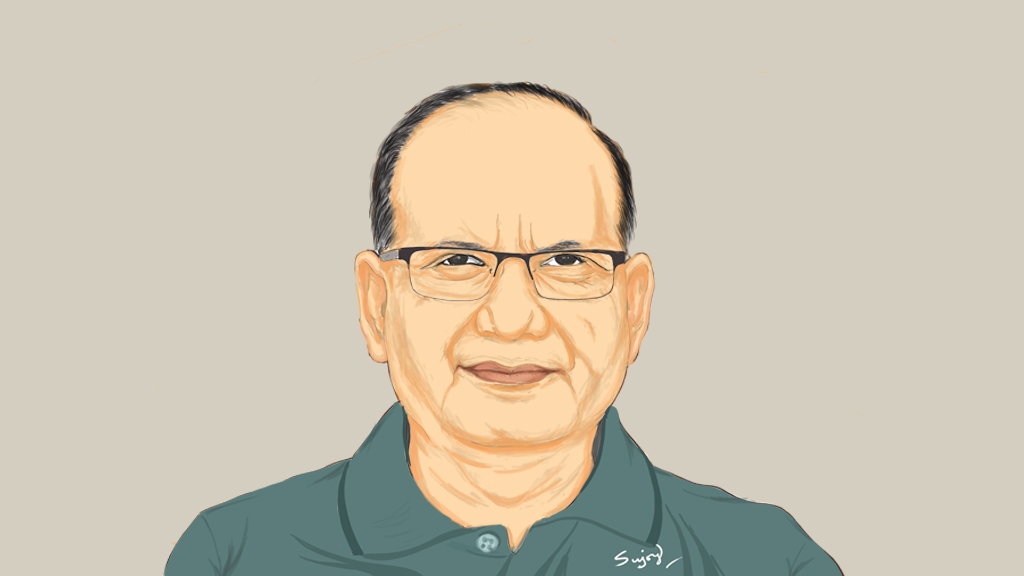
ধরা যাক একটা জেলায় ১০০ লোক বসবাস করে। তাদের মোট বার্ষিক আয় ৫ লাখ টাকা। যদি আমরা তাদের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য তাদের মাথাপিছু আয়ের হিসাব করি, তাহলে ৫ লাখ টাকাকে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করব। দেখব যে তাদের প্রত্যেকের এক বছরের আয় হচ্ছে ৫ হাজার টাকা (৫০০০০০ ÷ ১০০)। দেখে মনে হয় যে একটা জেলায় একজনের আয় যদি ৫ হাজার টাকা হয়, তাহলে মন্দ নয়। কিন্তু এবার যদি আপনি জানতে পারেন যে ওই জেলায় ছোট একটা প্রশাসন আছে, যেখানে চারজন কর্তাব্যক্তি আছেন এবং তাঁদের অধিকারেই আছে বার্ষিক আয়ের ৪ লাখ টাকা। তাহলে চিত্র পাল্টে যাবে। ৪ জনের মাথাপিছু আয় হবে ১ লাখ টাকা এবং বাকি ৯৬ জনের মাথাপিছু আয় হবে ১ হাজার ৪১ টাকা মাত্র। তাহলে মাথাপিছু আয়ের হিসাব এই জেলায় বসবাসরত জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থা বোঝাচ্ছে না কোনোভাবেই। সম্পদ কত আছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বটে; তবে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কার অধিকারে সম্পদ কতটুকু আছে এবং কে কতটুকু সম্পদ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার বা ভোগ করতে পারছেন, সেটা। আর এখানেই আসে সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি। অর্থনীতিতে সম্পদ অর্জনের চেয়ে সম্পদের বণ্টন অধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। মাথাপিছু আয় একটা দেশের অর্থনীতির আকার কতটুকু, সেটা বুঝতে সাহায্য করে কিন্তু লোকজন কেমন আছে, তারা সবাই ভালো আছে কি না, সেটা বুঝতে সহায়তা করে না; যদি না আমরা জানতে পারি তাদের কার অধিকারে কতটুকু ভোগযোগ্য সম্পদ আছে। শুধু তা-ই নয়, যার যতটুকু ইনকাম, তা দিয়ে কে, কতটুকু জিনিস বাজার থেকে কিনতে পারছে, সেটাও ভালো থাকার একটা মানদণ্ড। যদি আপনার দৈনিক আয় ১০০ টাকা হয়, এই ১০০ টাকা যদি এক কেজি চাল কিনতেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেই আয় আপনার তেমন কোনো কল্যাণ করতে পারে না। অথচ আপনার আয় যদি ৫০ টাকা হয়, সেই টাকা দিয়ে যদি আপনি চাল, ডাল, তেল, মাছ, তরকারি সবই কিনতে পারেন, তাহলে ৫০ টাকা আয়ই অনেক ভালো। কাজেই মজুরি বা আয় বৃদ্ধি হলেই ভালো থাকা যায় না। সেই টাকায় প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারার সামর্থ্য হচ্ছে ভালো থাকা।
বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালে ছিল প্রায় ১২৯ ডলার, যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৯১, অর্থাৎ স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় অন্তত ২০ গুণ বেড়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়াবে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি। ওই সময়ে হতদরিদ্রের হার কমে শূন্যের ঘরে নেমে আসবে। আর মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হবে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে ‘বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।
করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। প্রশ্ন হচ্ছে, মাথাপিছু আয় বেশি থাকলেই কি মানুষ ভালো থাকে, নাকি সম্পদের সুষম বণ্টন মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে?
কার্ল মার্ক্স শিখিয়েছেন কীভাবে পুঁজি পুঁজিকে আকর্ষণ করে এবং কীভাবে শ্রমজীবীরা পুঁজিপতিদের হাতে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হন। আমাদের দেশে একটা মিশ্রিত অর্থনীতির চর্চা হয়। এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সর্বোচ্চ ধাপ নয় ঠিকই, কিন্তু পুঁজি সঞ্চালন, পুঁজি আহরণ ও একত্রীভবনের প্রক্রিয়া একটি শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতোই। তা ছাড়া, সুশাসনের অভাব, অন্যায়, দুর্নীতি, জবাবদিহিহীনতা, স্বজনপ্রীতি, মিথ্যাচার, অপচয় এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত খাতে অসৎ-অদক্ষতা, পুঁজির অন্যায় আহরণকে ত্বরান্বিত করেছে, করছে। ফলে বাড়ছে বৈষম্য। অল্প কিছু লোকের হাতে সিংহভাগ সম্পদ। এই সম্পদ সুস্থ ও নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্য থেকে ন্যায়-নিষ্ঠভাবে উপার্জন করলে সমস্যা প্রকট হতো না। দেখা যায়, সমাজের একটা শ্রেণির উত্থান হয়েছে, যারা সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, তাদের কাছ থেকে অযৌক্তিক ও অন্যায্যভাবে সম্পদ আহরণ করছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় তারা সহায়তা পাচ্ছে, এমন একটা শ্রেণির কাছ থেকে, যারা কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।
বাংলাদেশে আয়বৈষম্য বাড়ছে দ্রুত। অর্থনীতিবিদদের মতে, গত ১০ বছরে আয়বৈষম্য বেড়েছে ১০ থেকে ১৬ শতাংশ। কোনো দেশের আয়বৈষম্য কতটা, তা পরিমাপ করা হয় গিনি সহগ দিয়ে। গিনি সহগের মান শূন্য হলে বোঝায় যে দেশের সবার মধ্যে চরম সমতা বিরাজ করছে; আর এর মান বাড়তে বাড়তে শূন্য দশমিক ৫ (০.৫) বা বেশি হলে বোঝায় যে দেশে আয়বৈষম্য চরমতম অবস্থায় পৌঁছেছে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭৪ সালে দেশে গিনি সহগের মান ছিল ০.২৪, যা করোনা লকডাউনের আগে বেড়ে হয়েছে ০.৪৮৩। আর লকডাউনের পরে হয়েছে ০.৬৩৫।
গবেষকেরা মনে করেন, বাংলাদেশে যেহেতু গবেষণার সময় ধনী পরিবারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, সেহেতু বৈষম্যের সত্যিকার চিত্র আরও ভয়াবহ বলে অনুমান করা অসংগত নয়।
বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বাড়লেও এর সুবিধা ভোগ করছে খুব কমসংখ্যক মানুষ। দেশে ধনী আরও ধনী হলেও দরিদ্রের হাতে অর্থ থাকছে না। বিভিন্নভাবে দরিদ্র লোকের হাত থেকে টাকা চলে যাচ্ছে ধনীদের পকেটে, ফলে আয়বৈষম্য বাড়ছেই। দরিদ্ররা যা আয় করছে, মূল্যস্ফীতির কারণে সেটাও খুব সামান্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি সীমিত আয়ের মানুষদের জীবনে অভিশাপ হয়ে এসেছে।
তাহলে করণীয় কী? আমাদের যাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্র চালান, তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁরা কেমন রাষ্ট্র চান, যদি চান রাষ্ট্রের কিছু লোক আর্থিকভাবে ভালো থাকবেন, তাহলে যেভাবে চলছে তাতে তাঁরা ভালোই আছেন, সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক সম্পদের সিংহভাগের মালিকানায় আছেন। যদিও সামগ্রিকভাবে সবাই কমবেশি ভালো না থাকলে আজ যাঁরা ভালো আছেন, কাল তাঁরাও ভালো থাকবেন—সেই নিশ্চয়তা থাকবে না। আর যদি চান সামাজিক সুবিধাসংবলিত একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, তাহলে অর্থ ও সমাজের অন্যান্য সুবিধা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন রাষ্ট্র যদি শুধু কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে পারে, তাহলে সমাজের একটা বৃহৎ গোষ্ঠীর হাতে অনেক টাকার প্রবাহ হবে। গ্রামের ১০ টাকা দামের এক কেজি বেগুন শহরে ৬০ টাকায় বিক্রি হয়। কৃষক যদি অর্ধেক, অর্থাৎ ২০ টাকাও পেতেন, তাহলে তাঁদের বঞ্চনার পরিমাণ কমে আসত। কিন্তু সেটি হচ্ছে না; অথচ শুধু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সহজেই কাজটি করা সম্ভব।
আমাদের মনোযোগ দিতে হবে দেশের সার্বিক কল্যাণে, দেশের সব মানুষের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির দিকে। সমাজের এক অংশ অন্য অংশকে শোষণ করবে, বঞ্চিত করবে, সমাজের সম্পদ কার্যত লুট করবে এবং এই প্রক্রিয়া সর্বদা চলমান থাকবে, তাহলে সমাজে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠলেও সেই সম্পদ মানুষের কল্যাণে কাজে আসবে না। অর্থনীতির আকার বড় হবে, সামষ্টিক আয়কে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে মাথাপিছু আয় বাড়ছে কিন্তু মানুষের জীবনযাপনের গুণগত পরিবর্তন হবে না, বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। সামগ্রিক অর্থনীতি হয়ে পড়বে লুটেরা অর্থনীতি, অসম অর্থনীতি, কিছু মানুষের অন্যায্য-কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত অর্থনীতি। তাই অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের নজর দিতে হবে মানুষের অধিক কল্যাণে। তারা যেন তাদের আয় দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারে। প্রয়োজনীয় সেবাগুলো পায়। তা না হলে মজুরি বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে সেটা গরিব মানুষের কাছে প্রহসন বলেই বিবেচিত হবে।
লেখক: চিররঞ্জন সরকার, গবেষক ও কলামিস্ট

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...
১২ জুন ২০২৫
ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।
১৯ মে ২০২৫
আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
০৮ মে ২০২৫
পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...
০৮ মে ২০২৫