অরুণাভ পোদ্দার
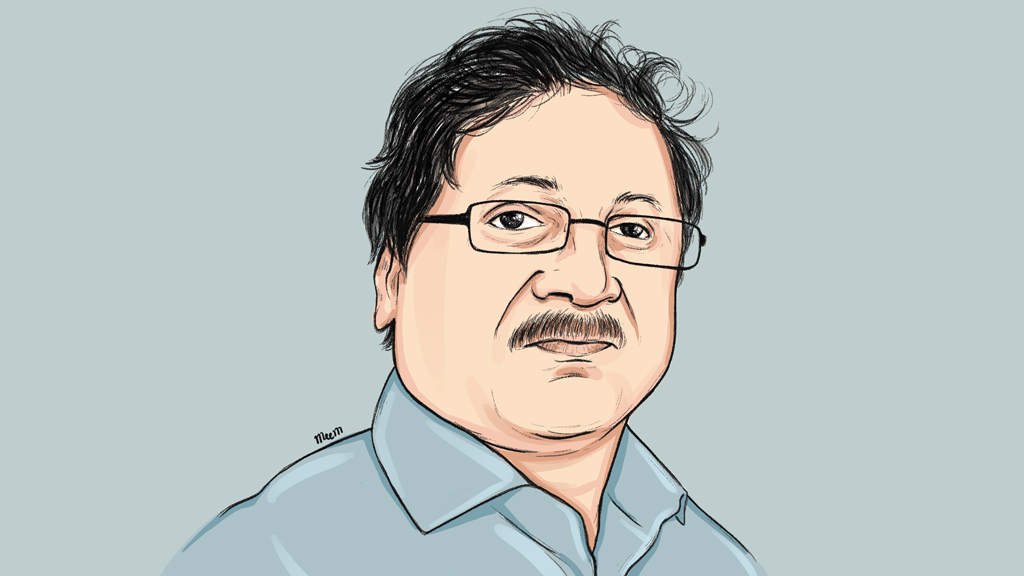
আজ ২২ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের ৮১তম প্রয়াণ দিবস। সুখে, দুঃখে, আনন্দ, বেদনায়, সংকটে, সংগ্রামে তাঁর রচিত সংগীত, সাহিত্য আমাদের পাথেয়। অনেকের মাঝেই একটা ভুল ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথ সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই ছোটবেলা থেকেই বিত্তবৈভবে বেড়ে উঠেছেন।
এটা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার ঘরেই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন তখনকার যুগের একজন সফল শিল্পপতি, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। সেই সময়ই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংক-বিমার ব্যবসা করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গ ও ওডিশায় জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গে এই জমিদারির আওতায় ছিল নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার বিরাহিমপুর (সদর শিলাইদহ), পাবনা জেলার শাহজাদপুর পরগনা (বর্তমান সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত) এবং রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা, পতিসর (বর্তমান নওগাঁ জেলা)। যদিও এর পরপরই তিনি বিপুল দেনা রেখে লন্ডনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বিশাল ঋণের বোঝা পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর বর্তায়। কথিত সেই সময় অনেকে উপদেশ দিয়েছিলেন আদালতে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা দিয়ে বাবার ধারদেনা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কঠোর কৃচ্ছ্র পালন করে, প্রিন্স দ্বারকানাথের সম্পদ নিলামে তুলে ও তাঁদের জমিদারি আয় থেকে ধীরে ধীরে প্রায় ৪০ বছরে সব দেনা পরিশোধ করেন। ফলে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সবাইকে বিলাসী জীবন ত্যাগ করতে হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবন স্মৃতি’তে লিখেছেন, ‘আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়।’ ‘বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোন দিন কোন মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোন দিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই।’
১৮৯০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে প্রথমে শিলাইদহের সেরেস্তার দায়িত্ব দেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল দিন শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখা এবং প্রয়োজনীয় নোট লেখা এবং সপ্তাহান্তে বাবা দেবেন্দ্রনাথকে অবহিত করা। এভাবে পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পরই কেবল তিনি পূর্ণাঙ্গ জমিদারির দায়িত্ব পান।
জমিদারি প্রাপ্তির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ যে বৈপ্লবিক কাজটি করেন তা হলো পুণ্যাহ উৎসবে (পুণ্যাহ হলো জমিদারিতে নতুন বছরের খাজনা আদায়ের সূচনা উৎসব) আসনব্যবস্থায় যে শ্রেণিবৈষম্য ছিল বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের প্রজাদের মাঝে, তার বিলোপসাধন। দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী জমিদার বসতেন মখমলের সিংহাসনে, আর হিন্দু প্রজারা শতরঞ্জির ওপর পাতা চাদরে। ব্রাহ্মণ, আমলা ও নায়েবেরা বসতেন তাঁদের থেকে উচ্চাসনে। আর মুসলমান প্রজাদের স্থান হতো শুধু শতরঞ্জিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর কথা—পুণ্যাহ হচ্ছে মিলন উৎসব, তাই সব প্রজার অধিকার এক কাতারে বসার। কিন্তু সদর নায়েব প্রিন্স দ্বারকানাথের আমল থেকে চলে আসা প্রথা কিছুতেই ভাঙতে চাইলেন না। রবীন্দ্রনাথও জেদ করে রইলেন, তাহলে পুণ্যাহ উৎসবই হবে না। শেষ পর্যন্ত কবির জয় হয়। এই অচলায়তন ভাঙতে পেরেছিলেন তিনি। সাধারণ প্রজারা এ ব্যাপারে খুশি হলেও আমলা, গোমস্তা ও মহাজনেরা খুশি হননি। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম সভায়ই বুঝেছিলেন আসলে কাদের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হবে। প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, ‘সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে, এটাই আমার প্রধান কাজ।’ ‘সাহা’ বলতে তিনি ধনী হিন্দু মহাজনশ্রেণি আর ‘শেখ’ বলতে দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের বুঝিয়েছিলেন, যাঁরা দশকের পর দশক মহাজনদের দাদন ব্যবসার শিকার হয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাই তো তিনি ১৯০৫ সালে পতিসরে উপমহাদেশের প্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। সেই ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের স্বল্পমূল্যে ঋণ দেওয়া হতো। ১৯১৩ সালে সেই ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা থেকে ৭৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা আর তিনি ফেরত পাননি।
 তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। কৃষকেরা যেন ন্যায্যমূল্যে ধান ও পাট বিক্রি করতে পারেন, সে জন্য ১৮৯৫ সালে কুষ্টিয়ায় কবি ‘ট্যাগর অ্যান্ড কোং’ স্থাপন করেছিলেন। কৃষির উন্নয়ন করতে নিজ জামাতা, পুত্র ও বন্ধুপুত্রকে সুদূর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি নিতে। সেই ১৯১০ সালে শিলাইদহ ও পতিসরে জমি চাষে ব্যবহৃত হতো ট্রাক্টর, সেচের জন্য পাম্পসেট, জমিতে ব্যবহৃত হতো সার। উচ্চফলনশীল জাতের ফসল ও কৃষি ল্যাবরেটরির প্রচলন করেন তিনি। পানীয় জলের অভাব দূরের জন্য পর্যাপ্ত পুকুর ও দিঘির ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া পতিসরে হাসপাতাল ও কালিগ্রাম পরগনায় তিনজন চিকিৎসক নিয়োগ দেন। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে হেলথ কো-অপারেটিভের ধারণা দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে মণ্ডলী প্রথার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন। তিনি শিলাইদহের বিরাহিমপুর পরগনায় তিনটি কাছারি গঠনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথার বিকেন্দ্রীকরণ করেন। এই মণ্ডলী প্রথার ফলে প্রজা-জমিদারের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। ফলে জমিদারের আমলাদের ক্ষমতা ও তাঁদের অবৈধ অর্থ আত্মসাতের পথ রুদ্ধ হয়।
তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। কৃষকেরা যেন ন্যায্যমূল্যে ধান ও পাট বিক্রি করতে পারেন, সে জন্য ১৮৯৫ সালে কুষ্টিয়ায় কবি ‘ট্যাগর অ্যান্ড কোং’ স্থাপন করেছিলেন। কৃষির উন্নয়ন করতে নিজ জামাতা, পুত্র ও বন্ধুপুত্রকে সুদূর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি নিতে। সেই ১৯১০ সালে শিলাইদহ ও পতিসরে জমি চাষে ব্যবহৃত হতো ট্রাক্টর, সেচের জন্য পাম্পসেট, জমিতে ব্যবহৃত হতো সার। উচ্চফলনশীল জাতের ফসল ও কৃষি ল্যাবরেটরির প্রচলন করেন তিনি। পানীয় জলের অভাব দূরের জন্য পর্যাপ্ত পুকুর ও দিঘির ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া পতিসরে হাসপাতাল ও কালিগ্রাম পরগনায় তিনজন চিকিৎসক নিয়োগ দেন। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে হেলথ কো-অপারেটিভের ধারণা দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে মণ্ডলী প্রথার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন। তিনি শিলাইদহের বিরাহিমপুর পরগনায় তিনটি কাছারি গঠনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথার বিকেন্দ্রীকরণ করেন। এই মণ্ডলী প্রথার ফলে প্রজা-জমিদারের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। ফলে জমিদারের আমলাদের ক্ষমতা ও তাঁদের অবৈধ অর্থ আত্মসাতের পথ রুদ্ধ হয়।
তিনি মনে করতেন, প্রতিটি পল্লির স্বনির্ভরতার মধ্যেই ভারতের মতো গ্রামীণ সমাজের উন্নতি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ‘পল্লী প্রকৃতি’ পুস্তিকায় লিখেছেন, ‘শিলাইদহ, পতিসর এই সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লী জীবন প্রত্যক্ষ করি।… প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ, দুঃখ, নালিশ, আব্দার নিয়ে আসতো। তার ভিতরটি দিয়ে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়াতরু তলে তাদের কুটির—আর একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত’। এই সংবেদনশীল মননের জন্যই জমিদার হয়েও তিনি ‘দুই বিঘা জমি’র মতো কবিতা লিখতে পেরেছিলেন।
১৯২১ সালে শুধু পতিসরের জমিদারি রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল। সর্বশেষ ১৯৩৭ সালে শেষবারের মতো কবিগুরু তাঁর জমিদারি পরিদর্শনে আসেন। সেবার প্রজাদের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
তাঁরা এই বলে জমিদারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন ‘প্রভুরূপে হেথা আস নাই, তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা। দেবতার দান অক্ষয় হউক। হৃদিপটে থাক স্মৃতিরেখা’। অভিভূত রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, ‘তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না’।...তোমাদের সবার উন্নতি হোক—এই কামনা নিয়ে আমি পরলোক চলে যাব।’
জমিদার ও প্রজার এই মধুর সম্পর্ক বিরল।
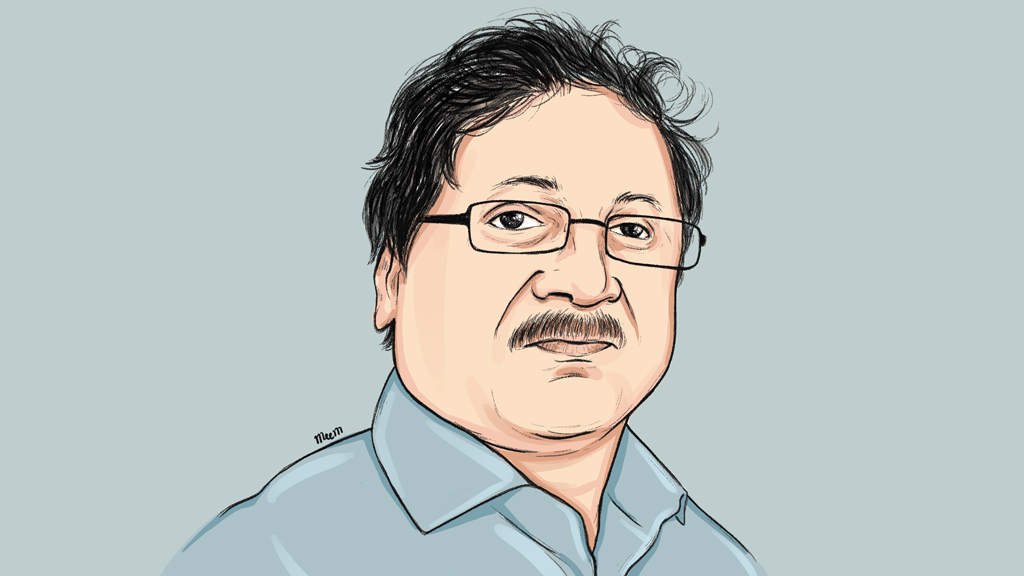
আজ ২২ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথের ৮১তম প্রয়াণ দিবস। সুখে, দুঃখে, আনন্দ, বেদনায়, সংকটে, সংগ্রামে তাঁর রচিত সংগীত, সাহিত্য আমাদের পাথেয়। অনেকের মাঝেই একটা ভুল ধারণা আছে, রবীন্দ্রনাথ সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই ছোটবেলা থেকেই বিত্তবৈভবে বেড়ে উঠেছেন।
এটা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার ঘরেই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) ছিলেন তখনকার যুগের একজন সফল শিল্পপতি, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। সেই সময়ই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংক-বিমার ব্যবসা করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গ ও ওডিশায় জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গে এই জমিদারির আওতায় ছিল নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার বিরাহিমপুর (সদর শিলাইদহ), পাবনা জেলার শাহজাদপুর পরগনা (বর্তমান সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত) এবং রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা, পতিসর (বর্তমান নওগাঁ জেলা)। যদিও এর পরপরই তিনি বিপুল দেনা রেখে লন্ডনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বিশাল ঋণের বোঝা পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর বর্তায়। কথিত সেই সময় অনেকে উপদেশ দিয়েছিলেন আদালতে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা দিয়ে বাবার ধারদেনা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কঠোর কৃচ্ছ্র পালন করে, প্রিন্স দ্বারকানাথের সম্পদ নিলামে তুলে ও তাঁদের জমিদারি আয় থেকে ধীরে ধীরে প্রায় ৪০ বছরে সব দেনা পরিশোধ করেন। ফলে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সবাইকে বিলাসী জীবন ত্যাগ করতে হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবন স্মৃতি’তে লিখেছেন, ‘আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়।’ ‘বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোন দিন কোন মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোন দিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই।’
১৮৯০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে প্রথমে শিলাইদহের সেরেস্তার দায়িত্ব দেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল দিন শেষে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখা এবং প্রয়োজনীয় নোট লেখা এবং সপ্তাহান্তে বাবা দেবেন্দ্রনাথকে অবহিত করা। এভাবে পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পরই কেবল তিনি পূর্ণাঙ্গ জমিদারির দায়িত্ব পান।
জমিদারি প্রাপ্তির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ যে বৈপ্লবিক কাজটি করেন তা হলো পুণ্যাহ উৎসবে (পুণ্যাহ হলো জমিদারিতে নতুন বছরের খাজনা আদায়ের সূচনা উৎসব) আসনব্যবস্থায় যে শ্রেণিবৈষম্য ছিল বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্মের প্রজাদের মাঝে, তার বিলোপসাধন। দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী জমিদার বসতেন মখমলের সিংহাসনে, আর হিন্দু প্রজারা শতরঞ্জির ওপর পাতা চাদরে। ব্রাহ্মণ, আমলা ও নায়েবেরা বসতেন তাঁদের থেকে উচ্চাসনে। আর মুসলমান প্রজাদের স্থান হতো শুধু শতরঞ্জিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর কথা—পুণ্যাহ হচ্ছে মিলন উৎসব, তাই সব প্রজার অধিকার এক কাতারে বসার। কিন্তু সদর নায়েব প্রিন্স দ্বারকানাথের আমল থেকে চলে আসা প্রথা কিছুতেই ভাঙতে চাইলেন না। রবীন্দ্রনাথও জেদ করে রইলেন, তাহলে পুণ্যাহ উৎসবই হবে না। শেষ পর্যন্ত কবির জয় হয়। এই অচলায়তন ভাঙতে পেরেছিলেন তিনি। সাধারণ প্রজারা এ ব্যাপারে খুশি হলেও আমলা, গোমস্তা ও মহাজনেরা খুশি হননি। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই প্রথম সভায়ই বুঝেছিলেন আসলে কাদের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হবে। প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, ‘সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে, এটাই আমার প্রধান কাজ।’ ‘সাহা’ বলতে তিনি ধনী হিন্দু মহাজনশ্রেণি আর ‘শেখ’ বলতে দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের বুঝিয়েছিলেন, যাঁরা দশকের পর দশক মহাজনদের দাদন ব্যবসার শিকার হয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাই তো তিনি ১৯০৫ সালে পতিসরে উপমহাদেশের প্রথম কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন। সেই ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের স্বল্পমূল্যে ঋণ দেওয়া হতো। ১৯১৩ সালে সেই ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা থেকে ৭৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা আর তিনি ফেরত পাননি।
 তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। কৃষকেরা যেন ন্যায্যমূল্যে ধান ও পাট বিক্রি করতে পারেন, সে জন্য ১৮৯৫ সালে কুষ্টিয়ায় কবি ‘ট্যাগর অ্যান্ড কোং’ স্থাপন করেছিলেন। কৃষির উন্নয়ন করতে নিজ জামাতা, পুত্র ও বন্ধুপুত্রকে সুদূর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি নিতে। সেই ১৯১০ সালে শিলাইদহ ও পতিসরে জমি চাষে ব্যবহৃত হতো ট্রাক্টর, সেচের জন্য পাম্পসেট, জমিতে ব্যবহৃত হতো সার। উচ্চফলনশীল জাতের ফসল ও কৃষি ল্যাবরেটরির প্রচলন করেন তিনি। পানীয় জলের অভাব দূরের জন্য পর্যাপ্ত পুকুর ও দিঘির ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া পতিসরে হাসপাতাল ও কালিগ্রাম পরগনায় তিনজন চিকিৎসক নিয়োগ দেন। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে হেলথ কো-অপারেটিভের ধারণা দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে মণ্ডলী প্রথার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন। তিনি শিলাইদহের বিরাহিমপুর পরগনায় তিনটি কাছারি গঠনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথার বিকেন্দ্রীকরণ করেন। এই মণ্ডলী প্রথার ফলে প্রজা-জমিদারের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। ফলে জমিদারের আমলাদের ক্ষমতা ও তাঁদের অবৈধ অর্থ আত্মসাতের পথ রুদ্ধ হয়।
তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। কৃষকেরা যেন ন্যায্যমূল্যে ধান ও পাট বিক্রি করতে পারেন, সে জন্য ১৮৯৫ সালে কুষ্টিয়ায় কবি ‘ট্যাগর অ্যান্ড কোং’ স্থাপন করেছিলেন। কৃষির উন্নয়ন করতে নিজ জামাতা, পুত্র ও বন্ধুপুত্রকে সুদূর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষির ওপর উচ্চতর ডিগ্রি নিতে। সেই ১৯১০ সালে শিলাইদহ ও পতিসরে জমি চাষে ব্যবহৃত হতো ট্রাক্টর, সেচের জন্য পাম্পসেট, জমিতে ব্যবহৃত হতো সার। উচ্চফলনশীল জাতের ফসল ও কৃষি ল্যাবরেটরির প্রচলন করেন তিনি। পানীয় জলের অভাব দূরের জন্য পর্যাপ্ত পুকুর ও দিঘির ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। শিলাইদহে মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ ছাড়া পতিসরে হাসপাতাল ও কালিগ্রাম পরগনায় তিনজন চিকিৎসক নিয়োগ দেন। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষে হেলথ কো-অপারেটিভের ধারণা দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে মণ্ডলী প্রথার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার করেছিলেন। তিনি শিলাইদহের বিরাহিমপুর পরগনায় তিনটি কাছারি গঠনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথার বিকেন্দ্রীকরণ করেন। এই মণ্ডলী প্রথার ফলে প্রজা-জমিদারের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। ফলে জমিদারের আমলাদের ক্ষমতা ও তাঁদের অবৈধ অর্থ আত্মসাতের পথ রুদ্ধ হয়।
তিনি মনে করতেন, প্রতিটি পল্লির স্বনির্ভরতার মধ্যেই ভারতের মতো গ্রামীণ সমাজের উন্নতি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ‘পল্লী প্রকৃতি’ পুস্তিকায় লিখেছেন, ‘শিলাইদহ, পতিসর এই সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লী জীবন প্রত্যক্ষ করি।… প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ, দুঃখ, নালিশ, আব্দার নিয়ে আসতো। তার ভিতরটি দিয়ে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়াতরু তলে তাদের কুটির—আর একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত’। এই সংবেদনশীল মননের জন্যই জমিদার হয়েও তিনি ‘দুই বিঘা জমি’র মতো কবিতা লিখতে পেরেছিলেন।
১৯২১ সালে শুধু পতিসরের জমিদারি রবীন্দ্রনাথের হাতে ছিল। সর্বশেষ ১৯৩৭ সালে শেষবারের মতো কবিগুরু তাঁর জমিদারি পরিদর্শনে আসেন। সেবার প্রজাদের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
তাঁরা এই বলে জমিদারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন ‘প্রভুরূপে হেথা আস নাই, তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা। দেবতার দান অক্ষয় হউক। হৃদিপটে থাক স্মৃতিরেখা’। অভিভূত রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, ‘তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না’।...তোমাদের সবার উন্নতি হোক—এই কামনা নিয়ে আমি পরলোক চলে যাব।’
জমিদার ও প্রজার এই মধুর সম্পর্ক বিরল।

‘দুই দিন আগেই বাড়ি থেকে পাথরঘাটায় চলে এসেছি। এখন পুরোনো জাল সেলাই করছি। এক সপ্তাহের বাজারও করে এনেছি। আজ বিকেলে সাগর মোহনায় যাব, গভীর রাত থেকে জাল ফেলব।’ কথাগুলো বলছিলেন বরগুনা সদরের বাইনচটকী এলাকার জেলে হোসেন আলী। গতকাল বুধবার সকালে বরগুনার পাথরঘাটা মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে কথা হয় তাঁর...
১২ জুন ২০২৫
ভারতের স্থলবন্দর নিষেধাজ্ঞার পর সীমান্তে আটকে থাকা তৈরি পোশাক, খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের ট্রাকগুলো ফেরত আনছেন রপ্তানিকারকেরা। তবে যেসব ট্রাক বন্দরে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো ভারতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব ট্রাক ঢুকতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে।
১৯ মে ২০২৫
আধুনিক যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রত্নসম্ভার। গতকাল বুধবার হংকংয়ে বিখ্যাত আর্ট নিলাম কোম্পানি সাদাবি’স-এর এক নিলামে এগুলো তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
০৮ মে ২০২৫
পাকিস্তানে ভারতের হামলার সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চীনও এই হামলাকে ‘দুঃখজনক’ বলে অভিহিত করেছে। উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘও। উত্তেজনা যেন আরও না বাড়ে, সে জন্য দুই পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ। এদিকে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে...
০৮ মে ২০২৫